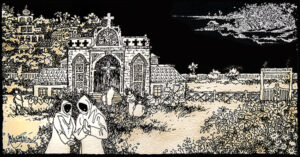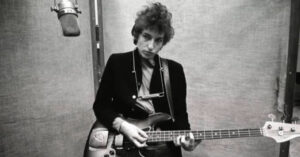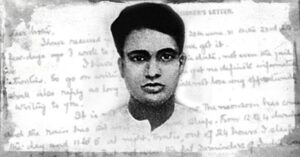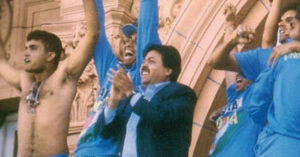সে কী ঝকমারি কাণ্ড, বাপ্পো রে বাপো! বড়-বড় ক্রেন আসছে, ক্রেনের আগায় ঝুলছে দু-মানুষ সমান লোহার ইয়াব্বড় হুক, যুদ্ধের ট্যাঙ্কের মতো চাকাওয়ালা বিভিন্ন যন্ত্র এসে কখনও ঠুকছে, কখনও খুঁড়ছে, কখনও পুঁতছে, চারিদিকে লাগ-লাগ-লাগ ঝনঝনাৎ আওয়াজ, কখনও পিঁইইইই শব্দে কানের পর্দা ফাটিয়ে কাজ করে চলেছে কংক্রিট ফাটানো মেশিন, আর লাগাতার, দিন নেই রাত নেই এইসব কাজকম্ম, মেশিনের জগঝম্পের দৌলতে আমাদের বাড়ির সামনেটা হয়ে রয়েছে আস্ত একটি যুদ্ধক্ষেত্র!
সময়টা হচ্ছে সাতের দশকের শেষ। আমি সবে গুটিগুটি পায়ে ইস্কুল যেতে শুরু করেছি। আমাদের বাড়িটা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোডের ওপর, অর্থাৎ বড়রাস্তার ওপর। বাড়ির উলটো ফুটপাথে কোনাকুনি দুটো সিনেমা হল— বাঁদিকে উজ্জ্বলা (লেখা থাকত উজ্জলা) আর ডানদিকে বসুশ্রী। বাড়ির সামনে ট্রামলাইন, বাসের রাস্তা। ফুটপাথের ওপর দু-ধারে আলোকময় দোকানপাট, নিরন্তর লোকজনের আনাগোনা, আপিসটাইমের বাদুড়ঝোলা বাস-ট্রাম— সবই দেখা যেত আমাদের বাড়ির বারান্দা থেকে, মায় ঠিক কখন উজ্জ্বলা-বসুশ্রীর সিনেমা ভাঙছে, তা-ও। এমন ঘনঘটা-সম্পন্ন এলাকায়, হঠাৎ এক প্রভাতে গাড়িঘোড়া সব বন্ধ হয়ে গেল। কী হল, কী হল! জানা গেল মাটির তলা দিয়ে ট্রেন যাবে, তারই প্রস্তুতি শুরু হবে। বলে কী! আমার ছোট্ট ব্রেনে নানারকম প্রশ্ন উদিত হতে থাকল। দিব্যি মাটির ওপর দিয়ে লোকজন যাচ্ছে, বাস-ট্রাম দৌড়চ্ছে, বাবা অফিস যাচ্ছে সেইসব চড়ে, তা হলে খামখা মাটির তলা দিয়ে ট্রেন যাবে কেন? কী করেই-বা? আমি তো জানি মাটির তলায় পাতাল বলে একটা আলাদা সেট-আপ আছে। সেটা মোটামুটি জলে পরিপূর্ণ। তার মধ্যেই প্রাসাদ, দেবতা, অসুর, বাসুকি নাগ ঘোরাফেরা করে। আর পাতালের সঙ্গেই সহাবস্থান করে নরক। কারণ দেবতাদের কথা উঠলেই বড়রা মাথায় হাত ঠেকিয়ে ওপরের দিকে তাকাত। অতএব আকাশের ওপারে স্বর্গ। সুতরাং মাটির নীচে নরক হওয়াটা স্বাভাবিক। তাহলে মাটির নীচের দুনিয়াটার কী হবে? মাটির তলা দিয়ে যদি ট্রেন যায়, পাতালটা পুরো উন্মুক্ত হয়ে যাবে? আমরা কি ওপর থেকেই পাতাল দেখতে পাব? তাহলে যারা শাস্তি পেয়ে নরকে গেছে, তাদেরও কি দেখতে পাওয়া যাবে?
প্রথম কোপ পড়ল ট্রামলাইনের ওপর। বড়রাস্তার মাঝখানে সগর্বে যে ট্রামলাইন শুয়ে ছিল, তা খুঁড়ে তুলে ফেলে বসানো হল রাস্তার দু-ধার ঘেঁষে। একদিকে ট্রামলাইন চলে এল প্রায় আমাদের বারান্দার নীচে, অন্যদিকেরটা চলে গেল ওপারের ফুটপাথ ঘেঁষে। কিন্তু লাইনগুলো বোধহয় খুব শক্তপোক্ত করে পাতা হয়নি। কিছুদিন অন্তর-অন্তর ট্রাম বেলাইন হয়ে রাস্তা থেকে সিধে আমাদের বাড়ির গলির মুখে চলে আসত। বাড়ি থেকে বেরোনো দায়। প্রথম দু-একবার মজা পেলেও, পরের দিকে রাগ ধরত। ট্রামের গা-ঘেঁষে স্কুলের ব্যাগ নিয়ে সাইড কাটিয়ে যাতায়াত করা পোষায়? একটু পরে অবশ্য ট্রাম কোম্পানির লোক এসে মেট্রো রেলের কাজকে যথাযথ গাল পেড়ে ট্রামকে লাইনে তুলত। আবার উলটো ফুটপাথের ট্রাম মাঝেমাঝে বোর হয়ে বসুশ্রী সিনেমা হলের দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিত। হল থেকে লোক বেরিয়ে দেখত, সামনেই ট্রাম তাদের মুখ নিরীক্ষণ করছে। এ তো তবু হাসির ঘটনা। কিন্তু ট্রামলাইন সরাতে গিয়ে প্রথম কোপ পড়ল আমার জানলার পাশের দেবদারু গাছটার ওপর। আমার দেখা মেট্রোরেলের প্রথম শহিদ। অনেকদিন মন খারাপ ছিল গাছটার জন্য।
মাঝখান ফাঁকা করে ট্রামলাইন তো দু-দিকে সরে গেল। সেই বৃহৎ মাঝখান, যার তলা দিয়ে পাতাল রেল চলাচল করবে, তার ব্যবস্থা করতে এল দলে-দলে মাটি-কাটা শ্রমিক। শুরু হল রাস্তা খোঁড়া। এবং যে বিশালাকার গর্ত তৈরি হল, তার নামকরণ হল— মেট্রোরেলের গর্ত। শ্রমিকদের থাকার আস্তানা হল অস্থায়ী টিনের চাল আর দরমার বেড়া দেওয়া চালাঘর। রাতে তাদের ইটের উনুনে রান্না চাপত। সেই রান্নার জ্বালানি কী ছিল? গভীর গর্ত কাটতে-কাটতে মাটির তলা থেকে উঠে আসত হাফ কাঠ-হাফ কয়লার মতো টুকরো। প্রচুর, প্রচুর। যত গভীর গর্ত কাটা হয়, তত কাঠ-কয়লা বেরোতে থাকে। সেই নিয়েও কম শোরগোল হয়নি! নতুন-নতুন ফান্ডা পাড়ায় ভাসতে থাকল। কাঁপা-কাঁপা গলায় বড়রা বলতে লাগল, হাজার-হাজার বছর ধরে গাছ মাটির তলায় মিশে গিয়ে ধীরে-ধীরে কয়লায় রূপান্তরিত হচ্ছিল। আর কিছু বছর মাটির তলায় চাপা থাকলে, পুরোপুরি কয়লা হয়ে যেত! মাঝপথে ব্যাটা মেট্রোরেল মাটি খোঁড়াখুঁড়ি করে দেশের সম্পদ তুলে নিয়ে লেবারদের রান্নার কাজে লাগিয়ে দিল! ফক্কড় ছেলেও কম ছিল না। তারা পাড়ার এক দাদুকে প্রায়শই জিজ্ঞেস করত, ‘আরও কিছু বছর থাকলে এমনকী হিরেও পাওয়া যেত, না? কেমন সুন্দর পাড়ায় একটা হিরের খনি থাকত, ঘুরতাম-ফিরতাম হিরে তুলে নিতাম, ফুল তোলার মতো!’ দাদু গরগর করতে করতে প্রস্থান করত। আর সেই কাঠ-কয়লা জ্বালানোর একটা আশ্চর্য গন্ধ ছিল। সেটা এখনও মাঝে-মাঝে পাই। ওই গন্ধের সঙ্গে আমার বড় হওয়ার দিনগুলোর একটা আত্মীয়তা আছে।
রাতের বেলায় লেবারদের একদিকে ভাত ফুটত, অন্যদিকে একটা ছোট ঢোলের সঙ্গে চলত খালি গলায় গান। একজনের গান সারা পাড়ার মনে ধরেছিল। সে ছিল রফি-কন্ঠী। বিভিন্ন বাড়ির আলোর জ্যামিতি দিয়ে মেট্রোরেলের কাজের জায়গায় একটা আশ্চর্য মায়াবী কাটাকুটি তৈরি হত, আর গান ভেসে আসত একের পর এক, ‘ও দুনিয়া কে রাখওয়ালে’, ‘চাহে কোই মুঝে জংলি কহে’, ‘তু গঙ্গা কি মৌজ’। সন্ধের সময় যখন ঝপ করে লোডশেডিং হয়ে যেত, সত্যি কথা বলতে কী, অত খারাপ লাগত না। মনে হত, কোনও আদিম সময়ে বাস করছি। অন্ধকারে বিভিন্ন মেশিনের হুক, ক্রেনের লম্বা শুঁড়, মাঝে বিশাল এক গর্ত, দু-ধারে উঁচু করে কাটা মাটি ঢিপি করে রাখা, অন্যপাশে ডাঁই করে রাখা পাইপ আর ট্যাঙ্কারের চাকার মতো অদ্ভুত সব জিনিস। আলো-আঁধারিতে এগুলোকে কিছুটা দেখা যেত, আর কল্পনা দিয়ে অনেকটা বাড়িয়ে নেওয়া যেত। নিস্তব্ধতা ভেঙে কখনও-কখনও একটা ট্রাম ঘটাং-ঘটাং শব্দে করে চলে যেত। সব মিলিয়ে মনে হত একটা অবাস্তব জগতে রয়েছি।
প্রথম কোপ পড়ল ট্রামলাইনের ওপর। বড়রাস্তার মাঝখানে সগর্বে যে ট্রামলাইন শুয়ে ছিল, তা খুঁড়ে তুলে ফেলে বসানো হল রাস্তার দু-ধার ঘেঁষে। একদিকে ট্রামলাইন চলে এল প্রায় আমাদের বারান্দার নীচে, অন্যদিকেরটা চলে গেল ওপারের ফুটপাথ ঘেঁষে। কিন্তু লাইনগুলো বোধহয় খুব শক্তপোক্ত করে পাতা হয়নি। কিছুদিন অন্তর-অন্তর ট্রাম বেলাইন হয়ে রাস্তা থেকে সিধে আমাদের বাড়ির গলির মুখে চলে আসত।
তারপর এক সময় আমরা খানাখন্দ, বড় গর্ত, মেট্রোরেলের আওয়াজে ধীরে-ধীরে অভ্যস্ত হয়ে গেলাম। দিন যত গেল, আগের বড়রাস্তা ভুলে, মেট্রোরেলের সিনারি গেড়ে বসে গেল মনের মধ্যে। এদিকে একদল মাটি কেটে চলে গেল তো আরেক দল এল, সঙ্গে এল ট্রান্সফর্মারের মতো বিশাল বিশাল মেশিন। তাদের কী দাপট! কী আওয়াজ! এল দশতলা বাড়ির সমান বড়-বড় লোহার খাঁচা। সেই খাঁচা দমাদ্দম-দমাদ্দম পিটিয়ে-পিটিয়ে মাটির ভেতরে সেঁধিয়ে দেওয়া হত যখন, মনে হত আমাদের বুকেই কেউ হাতুড়ি পিটছে। তার ওপর হল কংক্রিটের ঢালাই। তৈরি হল মাটির নীচে দেওয়াল। ততদিনে আমাদের বাড়ি সহ অন্যান্য বহু বাড়ির ভিত নড়বড়ে হয়ে গেছে। মেশিনের একটা করে ঘা পড়ে আর বাড়ি কেঁপে-কেঁপে ওঠে, সঙ্গে আমরাও। অন্তরাত্মা কাঁপে, বুক ধড়ফড় এবং কান ঝালাপালার দিন শুরু হয়। রাতেও কাজ চলত এবং বিভিন্ন নিত্যনতুন মেশিনের আওয়াজ, কোনওটার পিঁইইইইই, কোনওটার খ্যাড়খ্যাড়খ্যাড়খ্যাড়, কোনওটার বিকট পাম্পের মতো— সেসব শুনে আমাদের কানে-ব্রেনে ঝিলমিল লেগে যেত এবং ঘুমের সাড়ে চারটে তো বাজতই, কারণ ঠিক সেই ঘটিকায় কালীঘাট ট্রাম ডিপোয় হাওড়া যাওয়ার প্রথম ট্রাম গা-ঝাড়া দিয়ে নিজস্ব অর্কেস্ট্রা চালু করে ডিপো থেকে বেরোত!
কিন্তু মেট্রো রেলের কাজ চলছে বলে তো আর অমিতাভ বচ্চন অপেক্ষা করবে না। সে বীরদর্পে ফি-সপ্তাহে ‘ডন’, ‘ত্রিশূল’, ‘ইয়ারানা’ বাজারে ছেড়ে যাচ্ছে। এবং রুপোলি পর্দা ও বচ্চনের টানে সিনেমাপ্রেমী যুগল, অফিস-ফেরত মাঝবয়সি কেরানি, রাতের রুটি-তরকারির পাট দুপুরে চুকিয়ে দিয়ে বড় জা-ছোট জা— সব্বাই পাতাল রেলের গর্ত, সারি-সারি লোহার বিম, জল ভরা মিনি-ডোবা— এক্কাদোক্কা স্টাইলে পাশ কাটিয়ে উজ্জ্বলা-বসুশ্রীতে ভিড় জমাত। এই মারমার কাটকাট সিনেমা পাতে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে কারা হয়ে যেত আসলি হিরো? টিকিট ব্ল্যাকার। গড প্রমিস বলছি, এরা ছিল একটা অন্য ক্ল্যান। সারারাত টিকিট কাউন্টারের সামনে লাইন দিয়ে, ধুন্ধুমার মারপিট জিতে, পুলিশের লাঠি খেয়ে, জামা-প্যান্ট ছিঁড়ে, শুধু অন্তর্বাস পরেও টিকিট কাউন্টারের জানলা ধরে ঝুলে থাকত, কাউন্টার খুললেই টিকিট তুলে নেবে বলে। ম্যাটিনি-ইভনিং-নাইট। শো শুরুর আগে বচ্চনের মতো পেটিকোটের সমান ঘেরের বেল-বটম পরে কানঢাকা চুলে হলের সামনে, হলের উলটোদিকের পান-সিগারেটের দোকানের গা-ঘেঁষে, আড়াই টাকার টিকিট কখনও দশ, কখনও বারো, এমনকী পনেরো টাকায় বিক্রি করত। এরাই আবার মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, বিএ-বিএসসি-র রেজাল্ট বেরোলে ব্যানার্জি বুক সিন্ডিকেট থেকে গেজেট তুলত। ফার্স্ট ডিভিশন পাঁচ, সেকেন্ড তিন, থার্ড দু-টাকা, কম্পার্টমেন্টাল বা ফেল হলে কোনও টাকা নয়। আশ্চর্য একটা ব্যাপার ঘটল, আমাদের ব্ল্যাকারকুল আর পাতাল রেলের লেবারকুলের মধ্যে প্রবল সখ্য গড়ে উঠল। ‘ভাই আমার! বুকে আয়’ টাইপ। সান্ধ্য গানের আসরের শ্রোতা ও গায়ক— দু-য়েরই সংখ্যা বেড়ে চলল। ঢোলের ছোটভাই নাল-এর আমদানি হল। একটা লটে একটি ছোট্ট লেবার এল, সে আবার খুব ভাল বাঁশি বাজাত।
তারপর একদিন হইহই-রইরই। মেট্রোরেলের বৃহৎ গর্ত ঘিরে প্রচণ্ড গুজগুজ-ফুসফুস গুনগুন। পাড়ার ছেলে-বুড়ো খতিয়ে দেখার জন্য পাজামার ওপর বুশ-শার্ট চাপিয়ে সটান সেই ভিড়ে। খানিকক্ষণ পর জানা গেল, স্বয়ং মহাদেব উঠে এসেছেন পাতাল ফুঁড়ে। সত্যি, তিনটে পাথর উঠে এসেছে গভীর গর্ত থেকে। একটি হুবহু শিবলিঙ্গ (গৌরীপট্ট ছাড়া), অন্য দুটি গোল গোল। সেগুলোকে তক্ষুনি নন্দি-ভৃঙ্গি বাতলে নেওয়া গেল। ভগবান নিজে মর্তে উঠে এসেছেন, অতএব তাঁকে তো অসম্মান করা যায় না। পাপের ভয় নেই? কিন্তু পাড়ার লোকেরা কেউ এগিয়ে এসে বাবা ভোলানাথের দায়িত্ব নিল না। বলল, অনেক হ্যাপা। ফলস্বরূপ, ভদ্দরলোকেদের কাঁচকলা দেখিয়ে ব্ল্যাকার ও শ্রমিক বন্ধুদল ভগবানের দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিল। অচিরেই আমাদের বাড়ির ঠিক উলটোদিকে একটা বটগাছের তলায় দরমার বেড়া ঘেরা মন্দির গড়ে উঠল এবং তাতে দেবতা স্থাপন হল— বাবা বটেশ্বর।
নতুন উন্মাদনা শুরু হল। রোজ ধূপধুনো দিয়ে পুজো। ক্রমে শিবরাত্রি এল। তখন একটা কাণ্ড হল বটে। ব্ল্যাকার-লেবার জয়েন্ট ক্লাব একত্রিত হয়ে সবুজ টিউবলাইট, সাউন্ডবক্স লাগিয়ে ঘটা করে শিবরাত্রির পুজো শুরু করল। কোথা থেকে খোলা চুলের মেয়েরা হাতে ঘটি নিয়ে বাবা বটেশ্বরের মাথায় জল ঢালতে এল। ওদিকে ভক্তবৃন্দের গান চালিয়ে সে কী নাচ! এমন অঙ্গ-ভঙ্গিমায় নাচ আমরা দেখিনি তখনও। বড়রা তো ছ্যাছ্যা করতে লাগল, কালচার হাতছাড়া হয়ে গেল বলে রকে-রকে সে কী চিন্তা! কিন্তু ওদের যেটা সবচেয়ে ভাল ছিল এবং যেটা বাঙালি ‘ভদ্রলোকদের’ ছিল না, তা হল, পরের দিন জয়েন্ট ক্লাব থেকে ঢালাও প্রসাদ খাওয়ানোর রীতি। খিচুড়ি, তরকারি, চাটনি সহযোগে কত লোককে যে ওরা খাওয়াত, তা গুনে শেষ করা কঠিন। কালীঘাটের পথের ভিখিরি থেকে বস্তির মানুষজন, সব্বাই খেত ও একগাল হেসে বটেশ্বরকে প্রণাম করত। উদ্যোক্তারা প্রসাদ বিলিয়ে বিকেলের দিকে বিভিন্ন তক্তপোশের ওপর গা এলিয়ে শুয়ে আড্ডা মারত। এখনও সেই মন্দির স্বমহিমায় বিরাজমান। বিগ্রহ নিত্য পূজিত।

এইভাবেই দিনের পর দিন কেটে গেল, প্রায় পাঁচ-ছ’বছর তো হবেই। তদ্দিনে মেট্রোরেলের কল্যাণে আমাদের বাড়ির সবাই খুব জোরে কথা বলে। হবে না কেন, মেট্রোরেলের আজব সমস্ত যন্ত্রের উদ্ভট আওয়াজ ছাড়িয়ে আমাদের কথা বলতে হত। তাই মা’র কাছে তরকারি চাইলেও সেটাকে প্রায় আন্দোলনের স্লোগানের পর্যায়ে না নিয়ে গিয়ে উপায় ছিল না। হাতখানেকের দূরত্বের লোকের সঙ্গেও বিকট চিৎকার করে কথা বলেটলে এমন ডেসিবেলে আমাদের অভ্যেস হয়ে গেল, এখন তা শুনে লোকে ভাবে, এরা হোল ফ্যামিলি কালা?
ইস্কুলের উঁচু ক্লাসে উঠতে উঠতে খেয়াল করলাম, বাড়ির সামনে মেশিনের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। শ্রমিকদের ডেরা উঠে যাচ্ছে। একটা সময় মেট্রোর সেই গভীর গর্ত মাটি ফেলে বোজানো শুরু হল। একদিন দেখলাম পিচ ঢালাও হচ্ছে রাস্তার মাঝামাঝি। তারপর একদিন কাছের ট্রামলাইন হাত ছাড়িয়ে, শেকড় উপড়ে, ফের রাস্তার মাঝামাঝি গিয়ে বসল। শুনলাম যদুবাবুর বাজারের কাছে (অনেকে বলে জগুবাবুর বাজার) মেট্রোরেলের স্টেশন হয়েছে। সেখান থেকেই নাকি প্রথম মেট্রো চলবে। স্টেশনের নাম ভবানীপুর, পরে যাকে আমরা চিনব ‘নেতাজী ভবন’ নামে। আর আমাদের বাড়ির পাশের মেট্রো স্টেশনটা (যতীন দাস পার্ক) আর কিছু দিনের মধ্যেই হয়ে যাবে। ১৯৮৪ সালে প্রথম মেট্রো রেল বা পাতাল রেল চলল ভবানীপুর থেকে ধর্মতলা অবধি।
আমাদের বাড়ির সামনের চেহারাটা বদলে গেল। চওড়া রাস্তা, বাস যাচ্ছে, ট্রাম যাচ্ছে, ট্যাক্সি যাচ্ছে। আগে এরকমই ছিল, কিন্তু আমার তা খুব একটা মনে পড়ত না, আমি ভাবতাম, যাঃ চেনা ঝঞ্ঝাটগুলো কোথায় হারিয়ে গেল দুম করে? ভেতরে একটা কষ্ট হত। বাচ্চার কাছ থেকে ভাঙা খেলনাও কেড়ে নিলে তার যেমন কষ্ট হয়, ঠিক তেমন! তার কাছে তো গোটা আর ভাঙার ফারাক থাকে না, সে তার চেনাকে জড়িয়ে থাকতে চায়। হতেই পারে, মেট্রোর ঝক্কি পোয়াতে বড়দের জঘন্য লাগত। আমার তো স্কুল যাওয়া আর নাচের ক্লাসে যাওয়া ছাড়া আর কোনও দায় ছিল না, তাই আমার মেট্রো তৈরির অ্যাডভেঞ্চারটা বেশ লেগেছিল। যখন সব আবার ঠিকঠাক সাফসুতরো হয়ে, মেট্রো রেল চলতে শুরু করল, মনে হল, আমার কিশোরীবেলার কিছু অংশ যেন মাটি চাপা পড়ে পাতালে চলে গেল।