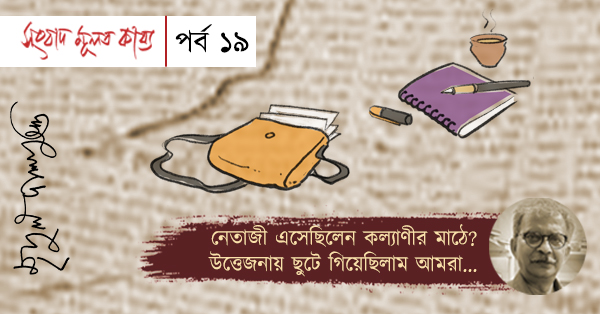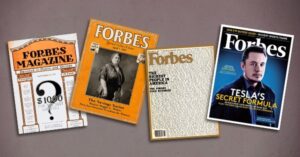‘পরিবর্তন’-এ আমার লেখা প্রথম প্রচ্ছদ কাহিনি— চাকরিতে মেয়েরা। পরিবর্তনের কয়েকটি সংখ্যা বেরোনোর পর ধীরেনদা, সংযুক্ত সম্পাদক ধীরেন দেবনাথ আমাকে এই বিষয়টি নিয়ে লিখতে বললেন। একটি প্রচ্ছদকাহিনি লিখতে বিষয়টি নিয়ে পড়াশুনো করা, ঘোরাঘুরি, খোঁজখবর নেওয়া, সাক্ষাৎকার নেওয়া ইত্যাদির জন্য আমাদের মাসাধিক কাল সময় দেওয়া হত। মেয়েদের চাকরি— বিষয়টি ভাবলে, আজকের যুগে কোনও বিষয়ই নয়। কিন্তু সেই ১৯৭৮/৭৯ সালে সমাজক্ষেত্রে চাকরিরতা মহিলারা ছিলেন ব্যতিক্রমী। সবরকম চাকরিতে মেয়েদের এখনকার মতো এত দেখা যেত না। মনে রাখতে হবে, আমি প্রায় ৫০ বছর আগের কথা বলছি। সে-সময়ে আমাদের শ্রীরামপুর শহরের নিকটবর্তী চন্দননগরে গিয়ে বিহ্বল বিস্ময়ে দেখতাম তরুণীরা সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছেন। স্বাধীনতার আগে চন্দননগর ছিল ফরাসি শাসনাধীন, তাই সেকালে আমাদের চেয়ে সংস্কৃতিতে এগিয়ে। সেই আমলের প্রথম মহিলা বিমান চালিকার নামটি স্মরণে আছে, দূর্বা ব্যানার্জি। আরও বলার, আমরাই প্রথম প্রজন্ম, যাঁরা সহপাঠিনীদের তুই-তোকারি করেছি, তাঁরাও তুই-তোকারি করেছেন আমাদের। তখন, সেই তখন, মেয়েরা, যাঁরা চাকরি করতেন, বেশির ভাগই শিক্ষিকা, ডাকঘরগুলিতেও দু-একজন মহিলা ছিলেন কর্মরতা। এছাড়া বিভিন্ন অফিসে কর্মরত অবস্থায় কোনও কর্মচারীর মৃত্যুতে তাঁর নিকটজন, এক্ষেত্রে কন্যা বা স্ত্রী নিযুক্ত হতেন। তৎকালে, ১৯৭৮ বা ’৭৯-তে পরির্বতনে প্রথম প্রচ্ছদকাহিনি বা কভার স্টোরি লিখেছিলাম আমি।
ওই সময় থেকেই বিদ্যুৎগতিতে, পরবর্তী বছরগুলিতে দুর্দাড় এগিয়ে গিয়েছেন বাংলার মেয়েরা। আমি বলবই, রাজনৈতিক রণাঙ্গণে বহু রক্তপাত ঘটিয়ে, অনেক অশ্রুপাতে মুখ থুবড়ে পড়েছে যাবতীয় বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা। কিন্তু মেয়েরা বাংলার সমাজক্ষেত্রে একটি নীরব বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছে বিগত তিন-চারটি দশকে। তাঁদের কুর্নিশ।
সন্ধ্যা রায় অভিনীত ‘বাবা তারকনাথ’ নামে একটি চলচ্চিত্র সে-সময়ে বিপুল জনপ্রিয় হয়েছিল। সিনেমা হলগুলিতে সপ্তাহের পর সপ্তাহ হাউসফুল হওয়া ওই চলচ্চিত্রে লক্ষ করেছিলাম আমাদের এই হুগলি অঞ্চল দিয়ে তারকেশ্বরগামী ধাবমান তীর্থযাত্রায় তৎকালে বিপুল জনস্রোত। বাম শাসনকালের সূচনাকালে বিস্ময়কর ওই জনস্রোত। ‘পরিবর্তন’-এর প্রচ্ছদকাহিনি লিখেছিলাম, ‘বাবা তারকনাথ।’ এ-লেখার রসদ সংগ্রহে আলোকচিত্রী দীপক ভট্টাচার্যকে নিয়ে মধ্যরাতে কৈকালা থেকে লোকনাথ তীর্থযাত্রার কিছুটা পথ হেঁটেওছিলাম। পড়েছিলাম শ্রীপান্থের লেখা ‘মোহান্ত ও এলকেশী সম্বাদ’। তারকেশ্বর মন্দিরের ইতিহাসও পড়লাম।
১৮৭৩ সালে তারকেশ্বর মন্দিরের প্রধান, মোহন্ত মাধব গিরির ফাঁদে পড়ে ওই অঞ্চলের এক গ্রামবধূ এলোকেশী অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ায় স্বামী নবীনচন্দ্রের হাতে খুন হন। এরপর নবীনচন্দ্র পুলিশের কাছে আত্মসমর্পন করেন। সেকালে এ-ঘটনা নিয়ে বাংলায় বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। কালীঘাটে পটশিল্পীরা ওই ছবি আঁকেন, লোককবিরা গান বাঁধেন। মোহন্ত বিরোধী গণ আন্দোলনও জাগে। গণ সমর্থন জেগে যায় নবীনচন্দ্রের প্রতি। সে-সময়ে ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষে হুগলি আদালতের বিচারে নবীনচন্দ্রের যাবজ্জীবন দণ্ড হলেও দীর্ঘকাল তুমুল গণ-আন্দোলনে নবীন মুক্তি পান। অবৈধতার কারণে মোহন্ত মাধব গিরির তিনবছর কারাদণ্ড হয়। এরপর ১৯২৪ সালে তারকেশ্বর মন্দিরের আরেক মোহান্ত সতীশচন্দ্র গিরির বিরুদ্ধেও তুমুল গণরোষ জেগে যায় নারীঘটিত অভিযোগে। সাধুসন্ন্যাসীদেরই সংগঠন মহাবীর দল এই আন্দোলনের সূচনা করার পর তৎকালে স্বাধীনতা সংগ্রামরত কংগ্রেস অভিযোগ করে মোহান্তর প্রতি ব্রিটিশ প্রশাসনের মদতের। কংগ্রেস তারকেশ্বরে সত্যাগ্রহে নামে। ১৯২৪-এর ৮ এপ্রিল চিত্তরঞ্জন দাশ, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু তারকেশ্বরে বিশাল জনসভা করেন। বাংলা জুড়ে তীব্রতা বাড়ে গণ আন্দোলনের। গান বেঁধে কাজি নজরুল ইসলাম তারকেশ্বরের পথে-পথে গাইতে থাকেন:
‘জাগো আজ দন্ড হাতে চন্ড বঙ্গবাসী।
ওই ডুবালো পাপ চন্ডাল তোদের বাংলাদেশের কাশী।
জাগো বঙ্গবাসী।
মোহের আর নাইকো অন্ত পূজারী সেই মোহান্ত
মা বোনের সর্বস্বান্ত করছে বেদীমূলে।…’
পরিস্থিতির চাপে জনসাধারণের সামনে এসে মোহান্ত সতীশ জোড়হস্তে ক্ষমা চান, তারপর মন্দির ছেড়ে চলে যান। ওই সময়েই সিদ্ধান্ত হয়, একটি পরিচালন সমিতি গড়ে তারই দেখভালে কাজ চালাবেন তারকেশ্বরের পরবর্তী মোহান্তরা। ‘পরিবর্তন’-এ প্রচ্ছদ কাহিনি লেখার জন্য আমি যখন তারকেশ্বর মন্দিরে যাই, তখন যিনি মোহান্ত ছিলেন, দেখেছিলাম মোহান্তের রাজসিক বৈভব। মোহান্তের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। তিনি মধ্যাহ্নভোজে আপ্যায়িত করেছিলেন আমাকে। সেই নিরামিষ অন্নব্যঞ্জনের সুস্বাদ স্মরণে আসছে। তখনও মন্দির কর্তৃপক্ষের কিছু-কিছু আর্থিক নয়ছয়, শিবের গলার রুপোর সাপ উধাও হওয়ার খবর পেয়ে, লিখেছিলাম।
বহুকাল আগে হুগলির এসব অঞ্চল যখন ধু-ধু প্রান্তর, তখন এক দুপুরে গরু চড়াতে এসে এক রাখাল ঘাসে ঢাকা শিবলিঙ্গটি আবিষ্কার করে। কথিত আছে, রাখালের গাভিগুলি ঘাসের ঝোপের ভেতর একটি শিলাখণ্ডের ওপর দুধ ঢেলে দিচ্ছে দেখে রাখাল ওই শিবলিঙ্গটি খুঁজে পায়। মল্লরাজ ভারামল্লের কাছে খবর পৌঁছোয়। তিনিই তারকেশ্বরে তারকনাথ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। ১৭২৯ সালে পাকাপোক্তভাবে তারকেশ্বরের এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব তিনশো, সাড়ে তিনশো বছর আগের কথা। এসব অঞ্চলে ইতিহাসের ধুলো ওড়ে। কবিতারও কণা ওড়ে।
’৮০/’৯০ দশকে, তারপরেও বছর কয়েক, তারকেশ্বরের তীর্থযাত্রী সংখ্যা বছর-বছর বেড়েই চলছিল, মনে হয় করোনার পর একটু ভাটা পড়েছে।
‘পরিবর্তন’-এর ওই তারকনাথ সংখ্যাটি প্রচারে একলাখ ছাপিয়ে গিয়েছিল। অনেক চিঠি এসেছিল। মন্দির কর্তৃপক্ষ দুর্নীতির অভিযোগ অস্বীকার করে চিঠি দিয়েছিল, তার জবাবও দিয়েছিলাম। রত্নখচিত চক্ষুদ্বয়ের রূপার সর্পটির সন্ধান অবশ্য আর পাওয়া যায়নি।
সে-সময়ে অগণন ভক্তের এক ব্রহ্মচারীর আশ্রম ছিল কলকাতার কাছেই। সারা বাংলা বৈপ্লবিক বাসনায় ভরিয়ে দেওয়ালে-দেওয়ালে তাঁর সন্তানেরা, মানে ওই ভক্তরা মেতে উঠতেন মফস্সল বাংলায়। আমাদের কম বয়সে, ছয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ে, তখন স্কুলের সিক্স-সেভেনে পড়ি যখন, ওই ব্রহ্মচারী এক ২৩শে জানুয়ারি বালকোচিত ঘোষণা করেছিলেন, কল্যাণীর মাঠে নিজের জন্মক্ষণটিতে বেলা ১২টা নাগাদ ফিরে আসবেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। মনে আছে, হাজার-হাজার মানুষ ওই দিন কল্যাণীর মাঠের দিকে রওনা হয়ে গিয়েছিল। আমাদের বাড়ির উলটোদিকের মিহিরলাল সাহার তাঁত কারখানার তাঁতি, কর্মচারীরা, তাঁদের পরিবারের সকলে গিয়েছিলেন। শ্রীরামপুরের পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তু কলোনিগুলি থেকে দলে-দলে নারী-পুরুষ গিয়েছিলেন কল্যানীতে। তাঁদের প্রত্যাগমনের অপেক্ষায় আমরা স্কুল-বালকের দল অনেকেই গঙ্গাতীরে অপেক্ষায় ছিলাম, আশাব্যাকুল, উচ্চগ্রীব। নৌকোয়, লঞ্চে পর-পর ফিরে আসেন তাঁরা সন্ধ্যাকালে। নিরাশ, বিধ্বস্ত। নেতাজি ফিরে আসেননি।
শুধু ছয়ের দশক, সাতের দশকেও মাঝে-মাঝে নেতাজির ফিরে আসার আশাটি বাংলার হাওয়ায় ঘুরপাক দিত। রটত শৈলমারির সাধুই নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু। সাংসদ সমর গুহ একবার দাবি করেছিলেন, নেতাজি বেঁচে আছেন, ফিরেও আসবেন। একটি ফটো দেখেছিলাম, প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর শেষশয্যার পাশে সমাগত মানুষজনের ভেতরে একজন, ঠিক নেতাজির মতো দেখতে। কে জানে, জাল ছবিও হতে পারে। ধীরে-ধীরে নেতাজির ফিরে আসার সম্ভাবনা একেবারেই মিলিয়ে গিয়েছে।
তা, ওই ব্রহ্মচারী ও তাঁর আশ্রম নিয়ে ‘পরিবর্তন’-এ আমার লেখা প্রচ্ছদকাহিনি বের হয়েছিল। ব্রহ্মচারীর একটি সাক্ষাৎকারও নিয়েছিলাম। পরিবর্তন সম্পাদক অশোক চৌধুরী ও সংযুক্ত সম্পাদক ধীরেন দেবনাথ উচিত কারণেই ওই প্রচ্ছদকাহিনি আমার নাম ব্যবহার করেননি। লেখাটি পরিবর্তন নিউজ ব্যুরোর তরফে লেখাটি বের হয়। ব্রহ্মচারীর সন্তানেরা অনেকে লেখাটিতে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তাঁরা একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। পুস্তিকাটির নাম: ‘পরিবর্তন’-এর সাংবাদিককে ঝাঁটা মারো। ‘পরিবর্তন’-এর সম্পাদক অশোক চৌধুরী ওই পুস্তিকা পেয়েই, আমাদের পালোয়ান গোছের এক সহকর্মী রামকে আমার সামনে নিয়ে এসে বলেন, তুমি বাইরে বেরোলেই এই রামকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরবে। বাড়ি ফেরার সময় রাম তোমাকে হাওড়ায় পৌঁছে দেবে। এখন থেকে রাম তোমার বডি গার্ড। আমি অবশ্য এতে রাজি হইনি।