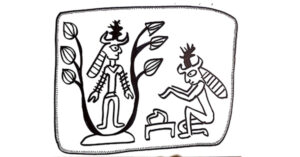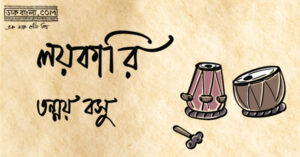বোল বদল, ভোল বদল
ঢাক বাজাতে অসম্ভব ভালবাসতাম আমি। কথাটা ভাবলে এখন নিজেরই বিশ্বাস হতে চায় না, কেননা প্রায় গত দু’দশক ঢাকের কাঠি হাতে নিইনি বললেই চলে। কিন্তু একটা সময়ে আমার কাছে পুজোর প্রধান আকর্ষণ ছিল ঢাকের কাঠি হাতে পাওয়া এবং ঢাকের আওয়াজে নিত্যনতুন বোল তোলার চেষ্টা। খুলেই বলি তাহলে।
আমাদের গড়িয়ার বাড়ি থেকে মিনিট দশেক হাঁটা পথে বিধানপল্লি, সেখানে আমার এক মামাবাড়ি ছিল। মায়ের কাকা-কাকিমার বাড়ি বস্তুত, সেই সূত্রে আমার মামাবাড়ি। বেশ কয়েক ভাই এক বাড়িতেই এদিক-ওদিক ঘরে বাস করতেন; তাঁদের বোনেরা, অর্থাৎ আমার মাসিরাও কাছাকাছিই বিবাহ-পরবর্তী জীবনে আবদ্ধ। এই মামাবাড়িতে বহু বছরই দুর্গাপুজো চালু ছিল, এখনও আছে। কতদিন আগে শুরু হয়েছে জানি না, কিন্তু আমার জ্ঞান হওয়া ইস্তক সে-পুজোর রমরমা দেখে আসছি। বাড়ির একপাশে ঠাকুরদালান, তার মধ্যেই দুর্গামন্দির। প্রতি বছর সেখানেই শিল্পী এসে ঠাকুর গড়তেন। একই শিল্পী, ঠাকুরেরও একই গড়ন। কিন্তু প্রতিবার ওই খড়ের কাঠামো তৈরি করা থেকে মায়ের চক্ষুদান পর্যন্ত যে-শৈল্পিক সফর, তা কিছুতেই দেখে দেখেও পুরনো হত না।
আরও পড়ুন: বিশ্বকর্মা পুজোর আকাশে সে-সময়ে আলাদা করা যেত না পাখি আর ঘুড়ি! লিখছেন শ্রীজাত…
তখন মণ্ডপে বা প্যান্ডেলে গান বাজত না, সে-কথা বলব না। নতুন বেসিক বাংলা গান বা হিন্দি ছবির গান বাজানোর একটা চল তখনও ছিলই। কিন্তু যেটা অবশ্যম্ভাবী ছিল, সেটা হল প্রত্যেক পুজোয় এক বা দু’জন ঢাকির আগমন। কোন সব দূর দেশ, নাম-না-জানা গ্রাম থেকে তাঁরা আসতেন, পালকের ঝালর লাগানো ঢাক অনায়াসে কাঁধে তুলে নিয়ে হাসিমুখে বাজিয়ে যেতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। পাড়া থেকে রাজপথ সেজে উঠত সেই রাজকীয় ধ্বনিমাধুর্যে। যত দিন গেছে, বুঝেছি, আমাদের এই উৎসবের আবহ বোঝাতে ঢাকের কোনও বিকল্প নেই।
আমার সেই মামাবাড়ির পুজোয় ঢাকির অবশ্য ভালই বিকল্প ছিল। আমার মাসি আর মামারা প্রত্যেকেই ভাল ঢাক বাজাতে পারতেন। ভাল বললে কম বলা হয়, কম-বেশি দুর্দান্ত বাজাতেন প্রত্যেকেই। গানবাজনার বাড়ি হওয়ার সুবাদে তাল-লয়-ছন্দজ্ঞান সকলেরই দিব্যি পাকা ছিল, আর বাড়িতে পুজোর চল থাকায় ঢাকের বোলও পরিবারের সম্পত্তির মতো উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন সকলে। তাই খামোকা ঢাকিকে এনে বসিয়ে রেখে কোনও লাভ হত না। মামা-মাসিরা পালা করে বাজালে ষষ্ঠী থেকে বিসর্জন অবধি দিব্যি চলে যেত। আর এইখানেই ছিল আমার সবচাইতে বড় আগ্রহ। বা আকাঙ্ক্ষাও বলা যেতে পারে। তখন নেহাতই ছোট। সন্ধ্যারতি, ধুনুচি নাচ, বরণ বা বিসর্জনের মতো প্রাইম টাইমে আমার মতো খুদেকে ঢাকের স্লট কেই-বা দেবে! কিন্তু আমরা যারা কচিকাঁচা ভাইবোনেদের দল, তাদেরও তো প্রত্যেকের হাতে কচি-কচি ঢাকের বোল খেলছে ততদিনে। সেই অপেক্ষার কি কোনও সুরাহা হবে না তবে?
হত। অপেক্ষাকৃত কম জনপ্রিয় স্লটে আমরা ভাগ করে-করে ঢাক বাজানোর সুযোগ পেতাম। হয়তো সন্ধ্যারতি সবে শেষ হয়েছে, ধুনুচি নাচ শুরু হতে তখনও দেরি, মেজমামা বা বড়দা গোছের কেউ একজন ঘণ্টাখানেক নাগাড়ে তুলকালাম বাজানোর পর ঢাকের ওপর কাঠি শুইয়ে রেখে স্নানে গেছেন, সেই সময়টা আমরা ঢাক বাজালে কেউ কিছু বলতেন না। ওই ছাড়ে পাওয়া এক কি দেড় ঘণ্টায় আমাদের দিব্যি প্র্যাকটিস হয়ে যেত। এই করতে-করতে যখন মাধ্যমিক টপকালাম, তখন একটা-দুটো প্রাইম স্লটে বাজানোর সুযোগ আসতে লাগল, ওই মামাবাড়িতেই। ততদিনে এ-মণ্ডপ সে-প্যান্ডেল ঢাক প্রতিযোগিতায় দেদার বাজিয়ে পাউডারের কৌটো, পেনসিল বক্স, চিরুনি এইসব জিতে ফেলেছি। ফলে আত্মবিশ্বাস এবং অহংকার, দুটোই জন্মেছে। তাও, মনে আছে, প্রথম-প্রথম সন্ধ্যারতির সময়ে বাজানোর ডাক পেয়ে রীতিমতো ঘাবড়ে গেছিলাম। পুরুতমশাই মন্ত্র আওড়াবেন, ধুনুচিতে একটু-একটু ক’রে আঁচ লাগবে, শঙ্খ আর ঘণ্টা পাল্লা দিয়ে বাজবে, তার মধ্যে ঢাক বাজানোর সুযোগ পাব আমি? যদি হাত কেঁপে যায়? যদি ভুল হয় বোলে? এও তো একরকম পরীক্ষাই! একরকম পারফরম্যান্স। পাস না করতে পারলে আর সুযোগ মিলবে না কক্ষনও।
ততদিনে এ-মণ্ডপ সে-প্যান্ডেল ঢাক প্রতিযোগিতায় দেদার বাজিয়ে পাউডারের কৌটো, পেনসিল বক্স, চিরুনি এইসব জিতে ফেলেছি। ফলে আত্মবিশ্বাস এবং অহংকার, দুটোই জন্মেছে। তাও, মনে আছে, প্রথম-প্রথম সন্ধ্যারতির সময়ে বাজানোর ডাক পেয়ে রীতিমতো ঘাবড়ে গেছিলাম। পুরুতমশাই মন্ত্র আওড়াবেন, ধুনুচিতে একটু-একটু ক’রে আঁচ লাগবে, শঙ্খ আর ঘণ্টা পাল্লা দিয়ে বাজবে, তার মধ্যে ঢাক বাজানোর সুযোগ পাব আমি? যদি হাত কেঁপে যায়?
উতরে গেছিলাম অবশ্য। মামা-মাসিদের স্নেহের চাউনি বলে দিয়েছিল, তাঁদের পরিবারের নাম ডোবাইনি পুরোপুরি। এরপর থেকে আরও ঘন-ঘন ঢাক বাজানোর বরাত পেতে থাকলাম, সকলে ভরসা করে ছেড়েও দিতেন। কেবল একটা সময়ে আমরা ছোটরা কেউ ঢাক বাজানোর ডাক পাবার কথা ভাবতেও পারতাম না, সে হল বরণ থেকে বিসর্জন। কী যে এক আশ্চর্য আবহ তৈরি হত গোটা বাড়িজুড়ে। বিকেল নামার পর থেকে বাড়ির মহিলারা সকলে লাল পাড় সাদা শাড়ি পরে বরণডালা হাতে মা-কে বিদায় জানাচ্ছেন, সকলের চোখের কোণ চিকচিক। মাটির মূর্তিতে যে এত বেশি প্রাণ থাকে, ওইদিন সেটা টের পাওয়া যেত। মায়ের হাত থেকে একে-একে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে অস্ত্রের ঝাঁক, ভার কমিয়ে নেওয়া হচ্ছে তাঁর।
আর সঙ্গে-সঙ্গে বোল বদলাতে-বদলাতে চলেছে ঢাক। নেহাতই ঘরোয়া বাজনা বলে তাকে মনে হচ্ছে না আর। বরং সে-বাজনার ধরন বলে দিচ্ছে, কত-কত বছরের লোকজ সংস্কৃতির ধারা দিয়ে তৈরি এই শিল্প, যার একটা বোলও ইতিহাস-বিচ্ছিন্ন নয়। এই বাংলার নদীদের ধারে-ধারে বয়ে চলা সময়ের কাহিনি বয়ান হচ্ছে, ওই ঢাকের বদলাতে থাকা বোলের মধ্য দিয়ে। অষ্টমী বা নবমীর রাতে যে-ঢাক ছিল উচ্চকিত, উচ্ছ্বল, উদ্দাম— এই বরণবেলার রাঙা রোদ্দুরে সেই ঢাকই হয়ে উঠেছে বিষাদসিন্ধু যেন। তার বোলের পরতে-পরতে বিদায়ের বিষণ্ণতা, বিচ্ছেদের বৈভব। যেন-বা ঢাকেরও আছে চোখের জল।
সেই বাজনাও বদলে যেত, যখন প্রতিমা তোলা হত ট্রাকে আর মিছিল করে সপরিবার যাওয়া হত পাশের পাড়ার শান্ত দিঘির দিকে, যার বুকে মায়ের সমাধি হবে। আর সত্যিই যখন সেই মুহূর্ত সমাগত, যখন সকলে মিলে একচালা প্রতিমাকে নামিয়ে আনছে জলের ধারে, যখন উলুধ্বনি মিশে যাচ্ছে ঝিঁঝির ডাকে, যখন অসহায় হাতেদের আলতো ঠেলায় প্রতিমা ‘ঝুপ’ শব্দে শুয়ে পড়ছেন জলের গায়ে, আর তাঁর শান্ত দু’চোখ তাকিয়ে আছে হেমন্তের রাতের আকাশের দিকে, তখন ঢাকের বাদ্যি একেবারে বদলে গেছে। সেই বোল গত পাঁচদিনের সমস্ত বাজনা থেকে আলাদা। বিসর্জন যে সমাপ্তি পর্যায়, তা বলে দেবার জন্য আলাদা কোনও শব্দের দরকার হচ্ছে না আর। ওই ঢাকই যথেষ্ট।
এখন সে-পুজোয় যাওয়া হয় না আর। মামা বা মাসিরা অনেকেই বিদায় নিয়েছেন। দুর্গার মতো পরের বছর আবার ফিরে আসার তাগিদ নেই তাঁদের। আমিও ঢাকের কাঠি থেকে হাত সরিয়ে নিয়েছি অনেকদিন হল। মনে-মনে কত কী বিসর্জন দিতে হল এই ক’বছরে, আর কানে-কানে শুনতে পেলাম সেই ম্লান ঢাকের বাদ্যি, সে আর বলার না। বিষণ্ণতা আসলে এক শেষ-না-হতে-চাওয়া পূজা পর্যায়, আর দূর থেকে ভেসে আসা ঢাকের আওয়াজ আসলে হেমন্তকালের ডাক, যাকে এড়িয়ে চলা যায় না কিছুতেই।
ছবি এঁকেছেন শুভময় মিত্র