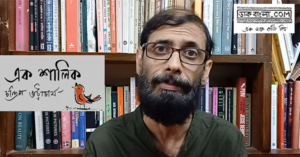২০১৫ সালের এপ্রিল মাসে আমি বাসু চ্যাটার্জির একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। সেই সাক্ষাৎকারে আমি প্রশ্ন করেছিলাম, যে যে সংগীত পরিচালকদের সঙ্গে আপনি কাজ করেছেন জীবনভর, তাঁদের মধ্যে আপনার প্রিয় কে? একটু থেমে উত্তর দিয়েছিলেন বাসু চ্যাটার্জি, ‘সলিল চৌধুরী, এসডি বর্মন, আরডি বর্মন।’
এরও কিছু বছর আগে বাসু চ্যাটার্জির আরও একটি সাক্ষাৎকার আমি পড়েছিলাম, সেখানে এই প্রশ্নের উত্তরেই, একটিমাত্র নাম বলতে হত তাঁকে। বাসু চ্যাটার্জির উত্তর ছিল, ‘সলিল চৌধুরী।’
এই যুক্তিক্রমগুলি থেকে একটি বিষয় অন্তত আমার কাছে স্পষ্ট, সলিল চৌধুরীকে তাঁর চলচ্চিত্রর সঙ্গে একাত্মই করে ফেলেছিলেন বাসু চ্যাটার্জি। বিষয়টা খুব একটা অস্বাভাবিক-ও নয়। সেই ১৯৬৯-এ ‘সারা আকাশ’ থেকে ১৯৯৪-এর ‘ত্রিয়াচরিত্তর’ পর্যন্ত, বাসু চ্যাটার্জির সাড়ে সাতখানা ছবিতে কাজ করেছেন সলিল চৌধুরী; ১৯৯০-এর ‘হামারি শাদি’-র কথা যদি মাথায় রাখি, যে-ছবির সুর করেছিলেন সলিল-পুত্র সঞ্জয় চৌধুরী, কিন্তু আবহসংগীত তৈরি হয়েছিল সলিল চৌধুরীর স্টক মিউজিক থেকেই।
কিন্তু বাসু চ্যাটার্জির সঙ্গে সলিল চৌধুরীর এই যোগাযোগ হল কী করে? এর একটা পটভূমি আছে।
১৯৫৩ সালে মুক্তি পেয়েছিল বিমল রায়ের ‘দো বিঘা জ়মিন’। সেই ছবির চিত্রনাট্য লেখার জন্য সলিল চৌধুরী এসেছিলেন বম্বে-তে। কালক্রমে হয়ে উঠলেন এই ছবির সংগীত পরিচালকও। ইন্ডাস্ট্রির দীর্ঘদিনের পোড় খাওয়া সংগীতকার অনিল বিশ্বাসের প্রাথমিকভাবে এই ছবিটির সংগীত করার কথা ছিল। তাঁর পরিবর্তেই এলেন সলিল। যেমন বাণিজ্যিক সাফল্য পেল এই ছবি, তেমনই শৈল্পিক কদরও এই ছবির জন্য বিন্দুমাত্র কম পড়ল না। সঙ্গে সঙ্গে কদর বাড়ল বিমল রায়েরও। বোরিভালিতে ১৯৫৩ সালের দুর্গাপুজোয়, বিমল রায়কে সাম্মানিক সভাপতির পদ দেওয়া হল। আর এই পুজোতেই নিজের কয়্যার নিয়ে হাজির হলেন সলিল চৌধুরী।
বোরিভালির বাসিন্দা বাসু চ্যাটার্জির সঙ্গে, সলিল চৌধুরী ও তার সুরের সেই প্রথম মোলাকাত।
ক্রমে বিমল রায় শিবিরের সদস্য হলেন সলিল চৌধুরী। বেতন পেতেন সেখান থেকেই, আবার কিছু ফ্রিলান্স কাজও করতেন। এরপর বিমল রায়ের অন্যতম বিশ্বস্ত সহকারী হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায় যখন তাঁর প্রথম ছবি ‘মুসাফির’ (১৯৫৮) বানালেন, তখন সেই ছবিরও সংগীত পরিচালক হলেন সলিল চৌধুরী। ভারতীয় চলচ্চিত্রর কিঞ্চিৎ মানবতাবাদী ও কিঞ্চিৎ উঁচুদরের ছবির ধারায়, সংগীতকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেন সলিল চৌধুরী।
বাসু চ্যাটার্জির প্রথম ছবি ‘সারা আকাশ’-এর কাঠামোটা বিমল রায়ের ধারার কিছুটা অনুসারীই ছিল। ফলে, এই ছবির সংগীতকার হিসেবে অবধারিত পছন্দ ছিলেন সলিল।
অনেকেই হয়তো জানেন না, ‘সারা আকাশ’-এ সংগীত হয়তো শেষমেশ সলিল করতেনই না। এই ছবির জন্য প্রথম পছন্দ ছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। বাসু চ্যাটার্জির সঙ্গে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের এই বন্ধুত্বের শুরু পাঁচের দশকের প্রথম দিকে। গীতিকার শৈলেন্দ্র ছিলেন বাসুর স্কুলের সিনিয়র, মথুরায় তাঁর স্থানীয় অভিভাবক-সম। বাসুকে বোম্বাইয়ের সিনেমা জগতে প্রবেশ করান শৈলেন্দ্রই। এবং সেই সূত্রেই এই সৌম্যদর্শন বাঙালি সুরকার-গীতিকারের সঙ্গে পরিচয় ঘটে বাসু চ্যাটার্জির।

‘হেমন্তদা আমাদের কাচের গ্লাসে চা খাইয়েছিলেন,’ স্মৃতি রোমন্থন করতেন বাসু চ্যাটার্জি, ‘সেদিনই বন্ধুত্ব পাকাপোক্ত হয়ে গেল।’
‘সারা আকাশ’-এর কাজ চলাকালীন বাসু চট্টোপাধ্যায় পুনের ফিল্ম ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউটে যাতায়াত করছিলেন, ওঁর ছবির প্রধান নারী চরিত্র ‘প্রভা’-র জন্য জয়া ভাদুড়ীকে নেবেন বলে। কিন্তু তৎকালীন প্রিন্সিপাল জগত মুরারি প্রতিষ্ঠানের রীতিনীতি ভাঙতে রাজি হলেন না। স্নাতক হওয়ার আগে, ছাত্রছাত্রীরা বাইরের প্রযোজনায় অভিনয় করতে পারবে না— এই ছিল নিয়ম। এক বন্ধুর পরামর্শে বাসু চ্যাটার্জি পৌঁছে যান সলিল চৌধুরীর ভাই সমীর চৌধুরীর কাছে। তাঁর কনিষ্ঠ শ্যালিকা, যিনি শিশুশিল্পী হিসেবে কিছু বাংলা ছবিতে অভিনয় করেছিলেন— তখন তাঁর ছুটি, ও নতুন কাজে চাইলেই শামিল হতে পারেন।তিনি হলেন মধুছন্দা চক্রবর্তী। পর্দায় যিনি ‘মধু’ নামে পরিচিত হন এবং প্রভার ভূমিকায় অভিনয় করেন। এভাবেই বাসু চ্যাটার্জির সঙ্গে সলিলের প্রথম সরাসরি সাক্ষাৎ।
সলিল চৌধুরী তখন বাসু চ্যাটার্জিকে বলেছিলেন, ‘ছবিটা আমাকে দিন, আমি ১০,০০০ টাকায় করে দেব।’ এরপরেই চুক্তি পাকাপোক্ত হয়ে যায়। সলিল আগ্রায় গিয়ে লোকেশন দেখেন এবং ব্রজভাষার কয়েকটি লোকগান রেকর্ড করে আনেন, যা পরে ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোরে ব্যবহৃত হয়। উল্লেখ্য, ছবিটায় কোনও গান ছিল না। ঠাকুরের কাছে বিপদে মোরে রক্ষা করো গোছের প্রার্থনা, বা গাছের আড়াল থেকে উঁকিঝুঁকি মারা গোত্রের কোনও পরিস্থিতিও ছিল না যদিও সেই ছবিতে।
মাত্র আড়াই লাখ টাকা বাজেটে তৈরি ‘সারা আকাশ’— যা তখনকার দিনে গড়ে একটি হিন্দি ছবির একটিমাত্র গানের চিত্রায়ণের খরচের সমান— সমালোচকদের প্রশংসা পায় এবং দিল্লিতে বাণিজ্যিকভাবেও বেশ সফল হয়।
সম্ভবত, গান না-থাকাই বাসু চ্যাটার্জিকে আবার সলিলের কথা মনে করিয়ে দেয় ‘রজনীগন্ধা’ (১৯৭৪) করার সময়ে। প্রথমে এটিও গানবিহীন ছবি হিসেবে ভাবা হয়েছিল। কিন্তু পরিবেশকরা আপত্তি তোলেন, এবং ব্যাকগ্রাউন্ডে ব্যবহারের জন্য দু’টি গান যুক্ত করা হয়।
আদতে, বম্বের মূলধারার ছবিতে গান না থাকা, তখন প্রায় ধর্মবিরোধী ব্যাপার। যদিও ‘নওজওয়ান’ (১৯৩৭), ‘কানুন’ (১৯৬০) এবং ‘ইত্তেফাক’ (১৯৬৯) ছিল ব্যতিক্রম। মজার ব্যাপার, এর মধ্যে ‘কানুন’ ও ‘ইত্তেফাক’-এর সংগীতও সলিলই করেছিলেন।
যাই হোক, ‘রজনীগন্ধা’-তে শেষত গান যোগ হয়। এখন শ্রোতা হিসেবে মনে হয়, আরও কয়েকটা গান থাকলে মন্দ হত না।
সেই সময়ে দাঁড়িয়ে, অত সাহসী আখ্যান ও অভিনব নির্মাণশৈলীর জন্য ‘রজনীগন্ধা’ স্মরণীয়, তবে এই ছবিকে মনে রাখার আসল চাবিকাঠি ছবিটির অপূর্ব সংগীত। ‘রজনীগন্ধা ফুল তুমহারি’ সলিল চৌধুরীকে ফিরিয়ে আনে ‘বিনাকা’ কাউন্টডাউনে। আর ‘কাহি বার ইউঁ ভি দেখা হ্যায়’ এনে দেয় মুকেশের প্রথম এবং একমাত্র জাতীয় পুরস্কার।
অনেকেই হয়তো জানেন না, ‘সারা আকাশ’-এ সংগীত হয়তো শেষমেশ সলিল করতেনই না। এই ছবির জন্য প্রথম পছন্দ ছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। বাসু চ্যাটার্জির সঙ্গে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের এই বন্ধুত্বের শুরু পাঁচের দশকের প্রথম দিকে। গীতিকার শৈলেন্দ্র ছিলেন বাসুর স্কুলের সিনিয়র, মথুরায় তাঁর স্থানীয় অভিভাবক-সম। বাসুকে বোম্বাইয়ের সিনেমা জগতে প্রবেশ করান শৈলেন্দ্রই। এবং সেই সূত্রেই এই সৌম্যদর্শন বাঙালি সুরকার-গীতিকারের সঙ্গে পরিচয় ঘটে বাসু চ্যাটার্জির।
পরবর্তী আলোচনা ও সাক্ষাৎকারে জানা যায়, এই শেষোক্ত গানটি পরে যোগ করা হয়েছিল, এবং এটি ছিল সম্পূর্ণ সংলাপহীন আবেগ প্রকাশের মাধ্যম। সলিল ও গীতিকার যোগেশ, এই সূক্ষ্ম আবেগকে বুঝেই সুর-শব্দ মিলিয়ে দেন। প্রীতা মাথুর—অভিনেতা দীনেশ ঠাকুরের স্ত্রী আমাকে এ-প্রসঙ্গে কী বলেছিলেন, ফিরে দেখা যাক—
“এই গানটা স্ক্রিপ্টে ছিল না। শুধু অভিনেতাদের বলা হয়েছি, ‘এই হল গিয়ে ছবির আবেগ। তোমাদের তা অভিব্যক্তির মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে।’ কিন্তু পর্দায় গানটির চিত্রায়ণ যে অভিনেতাদের অভিব্যক্তির সঙ্গে এমনভাবে মিশে গেছে, এখানেই পরিচালক ও সম্পাদকের কৃতিত্ব। প্রথম অংশে তাল নেই, তাল আসে দৃশ্যে ট্যাক্সি চলতে শুরু করলে। এটি ছিল সলিল চৌধুরীর নিজস্ব পরিকল্পনা। কারণ দৃশ্যটি আগেই শুট হয়েছিল, তাকে সেই অনুযায়ী সুর বাঁধতে হয়েছিল।
শিরোনাম-গানটিও শটের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী যোগেশকে আংশিকভাবে পুনর্লিখন করতে হয়েছিল।
এরপর আসে ‘ছোটি সি বাত’ (১৯৭৫)। এই ছবি যেন সর্বতোভাবে ‘রজনীগন্ধা’-রই একরকমের বিস্তার। একই নায়িকা, একই দ্বিধাগ্রস্ত সম্পর্কের গল্প, আর একই ধরনের ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক— যেখানে আবার একইরকম ব্রাস ইন্টারলিউডের প্রাচুর্য। ছবিটি ভয়ংকর জনপ্রিয় হয়। আজও প্রতিটি নবীন গায়িকা ‘না জানে কিউঁ’-র দরদি ওঠানামা গায়কিতে ধরতে পারলে, গর্ব বোধ করেন। আর বয়স্কদের কোনও আড্ডায় কেউ যদি ‘জানেমন জানেমন’ গেয়েই না উঠলেন, তবে সেই আড্ডা আর কী করে সম্পূর্ণ হবে!
এই ছবির মাধ্যমেই হিন্দি সিনেমা পেয়েছিল যেসুদাসকে। যদিও তাঁর প্রথম রেকর্ড করা হিন্দি গান ছিল, আরেক পরিচালক বাসু ভট্টাচার্যর ‘আনন্দ মহল’-এর জন্য— যা মুক্তিই পায়নি। পরে ‘চিতচোর’ (১৯৭৬)-এ তিনি হয়ে ওঠেন অমল পালেকরের স্বাক্ষর কণ্ঠ। যদিও সেই ছবির সংগীত করেছিলেন রবীন্দ্র জৈন, কিন্তু এ-কথা অস্বীকার করা কঠিন, যেসুদাসের উপস্থিতি ছাড়া, সেই সংগীতের কোনও জাদুই থাকত না। ফলে, সলিল চৌধুরীকে একেবারে কৃতিত্ব না দিয়েও উপায় নেই।
সত্তরের শেষদিকে সলিল বেশিরভাগ সময়টাই কাটাতেন কলকাতায়। তবে বাসু চ্যাটার্জি তাঁর ছবি ও সিরিয়ালে সলিলের স্টক মিউজিক বারবার ব্যবহার করতেন। ‘মঞ্জিল’ (১৯৭৯, সুর: আরডি. বর্মন)-এর টাইটেল স্কোরে, আবার ‘দো লড়কে দোনো করকে’ (১৯৭৯, সুর: হেমন্তকুমার)-এর ব্যাকগ্রাউন্ডে— সলিল চৌধুরীর স্বাক্ষর-সুরগুলি কিন্তু স্পষ্ট শোনা যায়।
‘মন পসন্দ’ (১৯৮০)-এ কাজ শুরুর সময় বাসু ও প্রযোজক অমিত খান্না সলিলের পরামর্শ নেন। বম্বের পেডার রোডে, সলিল চৌধুরীর বাড়ি হিমগিরিতে কয়েক দফা আলাপ-আলোচনাও হয় এই ছবি নিয়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রহস্যজনক কারণে সেই ছবির সংগীত করেন রাজেশ রোশন। ভাবতে ইচ্ছে হয়, সলিল চৌধুরী থাকলে সেই ছবির সুরকাঠামো কেমন হত।
সাতের দশকের শেষদিকের কথা এলেই মনে পড়ে, বাসু চ্যাটার্জির প্রিয় ছবি ‘জিনা ইয়াহাঁ’ (১৯৭৯)-র কথা। নরম, স্নিগ্ধ, সলিল চৌধুরীসুলভ কিছু অত্যন্ত সুন্দর গান ছিল ছবিতে। কিন্তু মুক্তিতে দেরি হওয়া আর পরিবেশকের নিরুৎসাহ ছবিটিকে আড়ালেই ঢেকে দেয়।
আটের দশক আরও ম্রিয়মান হয়ে পড়ল। ‘জেভার’-এর (১৯৮৬) কথা আজ প্রায় কেউ মনে রাখে না। প্রায় দাগ কেটে না যাওয়া একটি ছবি। প্রভাব হয়তো ফেলতে পারত ‘কমলা কি মওত’ (১৯৮৯), কিন্তু অকারণ একটি ‘এ’ সার্টিফিকেট আর পরিবেশকদের অনীহায় এই ছবিটিকেও ডুবতে হয়। দুটো ছবিতেই কোনও গান ছিল না। এই দশকে, সান্ত্বনা বলতে শুধু ‘দর্পণ’ টিভি ধারাবাহিকের টাইটেল স্কোরের কথাই মনে পড়ে, যা এখনও জনপ্রিয়।
নয়ের দশকে বাসু চ্যাটার্জির পক্ষে সময় অত্যন্ত কঠিন হয়ে ওঠে। বাজেট কমে যায়, বড় তারকা বা প্রযুক্তিবিদকে পাওয়া কঠিন। ব্যতিক্রম ‘ত্রিয়াচরিত্র’ (১৯৯৪)— যেখানে নাসিরুদ্দিন শাহ, ওম পুরীর মতো অভিনেতা ছিলেন। তাছাড়া এই ছবির প্রেক্ষিত ছিল বেশ অস্বস্তিকর, এবং চূড়ান্ত অভিঘাতপূর্ণ। তবুও ছবিটি সাড়া ফেলতে পারেনি। প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তনের যুগে বাসু চ্যাটার্জির সেই পুরনো ‘জুম’-এর কৌশলে অটল থাকা তাঁকে সময়ের বাইরে ঠেলে দিতে থাকে। ভুলে গেলে চলবে না, সেই দশকজুড়ে, চলচ্চিত্রর চিত্রগ্রহণে কীসব সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটাচ্ছিলেন বিনোদ প্রধান ও সন্তোষ শিবনরা। এইসব পিছিয়ে পড়ার কারণে হারিয়ে যেতে থাকে বাসু চ্যাটার্জি-সলিল চৌধুরী জুটির সাংগীতিক জাদুও।
তবুও নয়ের দশকে বাসু-সলিল জুটিকে নিয়ে একটি স্মৃতি রয়েছে, যা এই জুটির চিরন্তনতা বুঝতেও সাহায্য করে। ‘হামারি শাদি’ (১৯৯০)-র রেকর্ডিংয়ে কুমার শানু সঞ্জয় চৌধুরীর সুরকে ‘কঠিন’ বলে অভিহিত করে, মন্তব্য করে বসেন— ‘তুমি নিজেকে সলিল চৌধুরী ভাবছ নাকি!’
তিনি জানতেনই না, যাঁকে বলছেন, তিনি সলিল চৌধুরীরই ছেলে।