
ফিল্মফিরিস্তি : ১
‘দেশ-বিদেশের এত চলচ্চিত্র, কিন্তু সব ছবিই কি সমানভাবে দেখা গুরুত্বপূর্ণ? কী দেখব, কেন দেখব, কী না দেখলেও চলে, পাশাপাশি এবারের চলচ্চিত্র উৎসবে একান্তই যেগুলো দেখা প্রয়োজন, তা নিয়েই এই আলোচনা।’

‘দেশ-বিদেশের এত চলচ্চিত্র, কিন্তু সব ছবিই কি সমানভাবে দেখা গুরুত্বপূর্ণ? কী দেখব, কেন দেখব, কী না দেখলেও চলে, পাশাপাশি এবারের চলচ্চিত্র উৎসবে একান্তই যেগুলো দেখা প্রয়োজন, তা নিয়েই এই আলোচনা।’

ঋত্বিকের ক্ষেত্রে প্রথম আমাকে যা আকৃষ্ট করেছিল, তা ঋত্বিকের ফর্ম। চলচ্চিত্র নির্মাণে ঋত্বিক একেবারেই বাঁধা নিয়মের বাইরে। ঋত্বিক চলচ্চিত্রজুড়ে আখ্যান নির্মাণ করেন না চেনা ছকে। সত্যজিৎ রায়ের মন্তব্য এক্ষেত্রে স্মৃতিধার্য। সত্যজিৎ বলেছিলেন, ঋত্বিক মুহূর্ত নির্মাণে অনবদ্য, মহৎ।

‘ঋত্বিকের আখ্যান নিছক অভিযানের নয়, পরিযানের। যে-পালানোর যন্ত্রণা এই আখ্যানের পরতে-পরতে মিশে আছে, তাকে অতিক্রম করার নাছোড় জেদই তার শক্তি, তার স্পিরিট। শেষ দৃশ্যে হরিদাসের দেওয়া দাড়ি পরে নৌকো বেয়ে চলতে থাকে কাঞ্চন, কারণ পথ তো খুঁজতে হবে পথেই!’

জগদ্দলের প্রান্তরজুড়ে অপূর্ব ছুটে চলা। বিশাল পর্দার কখনও এক কোণে, কখনও একেবারে প্রান্তে, কালো শরীর নিয়ে অপূর্ব জেগে থাকা। জগদ্দল যেন তার প্রেমিক, তার অর্ধাঙ্গিনী, সবটাই মান-অভিমানের খেলা। আদর করে তার গা মুছিয়ে দেওয়া। ছবির শুরুই হয় এক পাগল বরকে দিয়ে, যে তার টোপর আর ধুতি সামলাতে ব্যস্ত।

‘‘পুনের ফিল্ম ইনস্টিটিউটের ভাইস প্রিন্সিপাল এবং ‘ডিরেকশন’ অর্থাৎ, নির্দেশনা বিভাগের শিক্ষক হিসেবে তাঁর ভূমিকা ভোলার নয়। আমার মনে পড়ে না, কখনও ক্লাসে তিনি তাত্ত্বিকভাবে চলচ্চিত্রকে দেখতে শিখিয়েছেন বলে। ফিল্ম থিওরির চেয়ে সবসময়েই ঋত্বিক জোর দিয়েছিলেন হাতে-কলমে চলচ্চিত্রশিক্ষার ওপর।’’

ঋত্বিক ঘটকের মৃত্যুর ঠিক পরে লেখা একটি কবিতায় শক্তি চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন, ‘… আর কেউ নেই যে কড়কাবে/বিদ্যুচ্চাবুকে এই মধ্যবিত্তি, সম্পদ, সন্তোষ/মানুষের, তুমি গেছ, র্স্পধা গেছে,
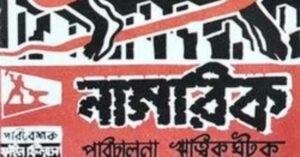
ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্র নির্মাণের আড়াই দশক ও তৎপরবর্তী চলচ্চিত্রভাষার বাঁকবদলের প্রস্তুতির উপাদান— ‘নাগরিক’-এর নিরীক্ষা, ত্রুটি ও ভাষার মধ্যে নিহিত রয়েছে।

‘সিনেমা ও উপন্যাস মিলিয়ে আমরা দু’রকমের কারণে ‘বাড়ি থেকে পালিয়ে’ আসা দেখতে পাব; আপাতভাবে দুটো আলাদা হলেও, শেষপর্যন্ত দুই-ই গিয়ে দাঁড়ায় ছেড়ে আসার যন্ত্রনায়, যার মূলে রয়েছে ভয়, আতঙ্ক।’
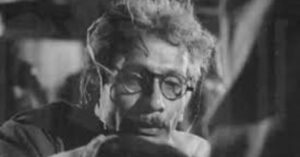
আজ শ্রাবণের এই অবিশ্রান্ত জলধারায় আমরা আর বিজন ভট্টাচার্যকে পাব না। যে বিজন ভট্টাচার্য ‘সুবর্ণরেখা’-য় বলেছিলেন, ‘ঈশ্বর, আমারে কইলকাতায় নিয়া যাবা?’ সেই কলকাতায় আমরা আর
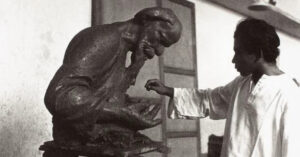
কিঙ্করদা ঐখানে এসে কোনও একটা বিরূপ উক্তি করে থাকবেন। সেই ইংরেজির অধ্যাপক রেগে গিয়ে, তার হাতের লাঠিটা দিয়ে কিঙ্করদাকে দু’এক ঘা লাগিয়েছিলেন!

‘ভাল করে ভেবে দেখুন, জগদ্দলের ‘মানবিকীকরণ’-এর প্রচেষ্টা খুব একটা নেই ছবিতে। যখনই সেরকম মনে হচ্ছে, সেখানে বিমলের পয়েন্ট অফ ভিউ থাকে। কার্বুরেটরে জল ভরার সময়ে ঢকঢক করে জলের আওয়াজ যার মধ্যে সবচেয়ে মনে থাকে।’

‘‘ফিয়ার’ ছবিটির ভাবনা ও বিন্যাস, সময়ের থেকে অনেক এগিয়ে, কিন্তু বিষয়টি চিরকালীন। ভয় দেখিয়ে আর ভয় পেয়ে বেঁচে থাকার ইতিহাস তো চিরন্তন। গুটিকয় মানুষের তৈরি করা ভয়ে, শিরদাঁড়া ঝুঁকিয়ে, বেঁচে থাকার গল্পের কোনও শেষ নেই।’
This Website comprises copyrighted materials. You may not copy, distribute, reuse, publish or use the content, images, audio and video or any part of them in any way whatsoever.
©2026 Copyright: Vision3 Global Pvt. Ltd.