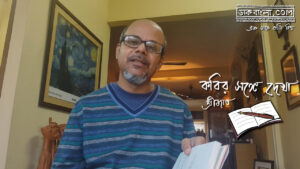মাধ্যমিক পাশ করে একাদশ শ্রেণি। ২০১৩ সাল। ফেসবুকে কবি চিনি, কলেজ স্ট্রিটে গিয়ে কিনি বই। মাঝে মাঝে নন্দনচত্বর। কফি হাউস। নেশা করি না। দাদারা না পারে ঝেড়ে ফেলতে, না পারে পুরোপুরি ধরতে। ফেলবে কী করে, কবিতা ভালবাসি যে! বয়সে অনেক ছোট বলে, কেউ-কেউ স্নেহ করে। ওইটুকুই। বলে, লেগে থাক। লেগে থাকি। জমায়েতে কবিতা পড়া হলে আমিও দু-একটা কাঁচা কবিতা পড়ি সবশেষে। দিন কাটে। হঠাৎ ঠিক হয়, কয়েকজন মিলে একটা নতুন কাগজ হবে। দলে ভিড়ি। নাম ঠিক হয়: ‘দশমিক’। সম্পাদকমণ্ডলীর এক কোণে গুটিয়ে থাকি। অথচ উৎসাহে কমতি নেই। কলকাতার এ-মাথা থেকে ও-মাথা চষে বেড়াই। আলাপ-পরিচয় বাড়ে। কতরকম মানুষ, কত-কত বই! ভাল লাগে। আর এই সময়েই, তালগোল-পাকানো আমার মন, কবিতার মধ্যে যখন খুঁজে বেড়াচ্ছে মুক্তি, পরিচয় হয় কবি রাহুল পুরকায়স্থের সঙ্গে।
রবিবারের সকাল। ফোন করে বেলঘরিয়ার বাড়ি। প্রস্তাব, ‘আমরা একটা নতুন কাগজ করছি, আপনার একটা কবিতা পাওয়া যাবে কি?’ ওপাশ থেকে উত্তর আসে, ‘চা খাবে? না মদ?’ ঘাবড়ে যাই। চায়ের কথা বলতেই, কানে আসে জড়ানো গলায় বলা একটা বাক্য, ‘শান্ত বালক সব, এসে গেছে বাংলা কবিতায়…’। পড়ার টেবিলে ভদকার গ্লাস। পাশে খুলে রাখা যে-বই, সেখান থেকে পাঠ করে শোনাচ্ছেন তিনি। বলছেন, ‘শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প পড়েছ? না পড়লে কোনওদিন জানতেও পারবে না, জীবনের অর্থ কী হতে পারে! বড় করে বাঁচতে হবে, নাহলে এইসব বাংলা কবিতা, কাগজ-ফাগজ সব অর্থহীন। শ্যামলদা জানতেন, কীভাবে বাঁচতে হয়…।’ আরও কিছু কথা হয়েছিল কি? মনে নেই। খুঁটিনাটি মুছে গিয়ে, জেগে আছে একটা সকাল শুধু। কবিতা সেদিন পাইনি। উপহার পেয়েছিলাম তাঁর লেখা কবিতা-বই, ‘আমার সামাজিক ভূমিকা’। তারও চারদিন পরে যেতে বলেছিলেন, শ্যামবাজারের এক কবিসভায়। কবিতা পাই সেখানে। নাম: ‘নেশাবিরতির দিনে’।
চিঠির যুগ পেরিয়ে এসেছি। দলিলহীন। কথারা অনাথ। হাওয়ায় ওড়ে। যে যার মতো রং চড়ায়। ভুল ব্যাখ্যায় ব্যক্তিত্ব ভাঙে। গড়েও কখনও-বা। জন্ম নেয় মিথ। ২০১৬ সালের ৭ সেপ্টেম্বর। ততদিনে ‘আপনি’ থেকে ‘তুমি’। রাহুলবাবু থেকে রাহুলদা। নির্মল হালদার সংখ্যা পড়ে মেসেঞ্জারে বার্তা আসে, ‘কাগজ ভাল লাগল। অনেকগুলি ভাল লেখা। নির্মলদার ইন্টারভিউ ভাল লাগেনি। তবে নির্মলদাকে চেনার জন্য এই ইন্টারভিউ খুব জরুরি ছিল। যে-মানুষটি জানান, জরুরি অবস্থা সাধারণ মানুষের কোনও ক্ষতি করেনি, তার মনুষ্যত্ব নিয়ে সন্দেহ কি জাগে না?’ সপাট, রাখডাকহীন। একজন নাগরিকের ‘সামাজিক ভূমিকা’ ঠিক কী হওয়া উচিত, এই নিয়ে এর পরেও বহু কথাবার্তায় দেখেছি, কত অকপটে সে ঘোষণা করে চলেছে তার বিশ্বাস। ভানের চাদরে মোড়া মুখোশসর্বস্ব জটিল পৃথিবীতে রাহুলদা ছিল সেই মানুষ, যে কখনও আপস করেনি। প্রতারণা করেনি নিজের আদর্শ কিংবা স্বপ্নের সঙ্গে। প্রতিটা দিন-রাত্রি, নিজের শর্তে বাঁচা। পুরনো কথাবার্তা ঘাঁটতে গিয়ে দেখি, এক জায়গায় লিখেছিল, ‘আসলে একজন কবির যে-কোনও ক্ষমতাকেন্দ্র থেকে দূরে থাকা দরকার। যা ইচ্ছে তাই লেখার সাহস থাকা দরকার। কবির সমাজ ব্যক্তিগত অর্থহীনতার আয়না, যার কথাবার্তা একমাত্র মৃত্যুর সঙ্গে।’ কবিতায় নিজেকে যে বলতে পারে ‘স্বপ্নক্রীতদাস’, প্রাজ্ঞের সরল হাসি নিয়ে যে আজীবন চাইতে পারে মায়ের আঁচলের মতো এক পৃথিবী— তাকে ভালবাসা ছাড়া আর কোনও পথ কি পড়ে থাকে, কবিতা-লিখিয়ে এক তরুণের কাছে?

আলোকচিত্রী: সন্দীপ কুমার
রাহুল পুরকায়স্থ যে-কলকাতা চিনত, আমি সেই কলকাতাকে চিনি না। যে-শহরে প্রেম আসে এবং উল্কাপাত হয়, সেই শহর আমাদের চির-অপরিচিত। যে-চরিত্রদের সঙ্গে মেলামেশা ছিল তার, তাদের অধিকাংশকেই মনে হত রূপকথার রাজ্যের বাসিন্দা। আকর্ষণ অনুভব করতাম। ঘরোয়া আড্ডায় পুরনো নেগেটিভ তুলে ধরত সে, আর আমরা, রাহুলদার অনুজ বন্ধুরা, ঢুকে পড়তাম সেই আশ্চর্য মায়াবী দুনিয়ায়। সময়ের অনেক দূরত্বে বসে টের পেতাম, আমরা অভাগা। পানশালার আড্ডায় তাকে পাইনি কোনওদিন, না পেয়েছি ময়দানের ঘাসে— আত্মীয়তা নিবিড় হয় হাসপাতালে। নতুন জীবনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার গল্পে, তার শরিক হয়ে পড়ি। মাঝে পড়ে থাকে কিছু অশ্রুজল, কামনাকঙ্কাল। ওষুধের গন্ধমাখা দিনগুলোয়, এসএসকেএম হাসপাতালের ঘরে, চুপ করে বসে থাকার দিনগুলো মনে পড়ে। ট্রলি ঠেলে রক্তপরীক্ষা করাতে নিয়ে যাওয়ার সময়কার কথা মাথার ভেতরে জেগে ওঠে আচমকা: ‘কয়েকটা কবিতা ছাড়া, এই জীবনের কাছে কী চাইছ তুমি!’
ছোট-ছোট মেসেজ আসত। সংক্ষিপ্ত। কাটা-কাটা। যেমন, ‘যেখানে বেঁচে থাকাটাই অর্থহীন, সেখানে শিল্পের আবার অর্থ কী’, ‘শক্তিদাকে না পাওয়াটা তোদের একটা বড় ক্ষতি’, ‘যোগাযোগহীনতার ভাইরাস এখন প্রবল’, ‘কথামৃত নিজেরা আবার প্রকাশ করলে কেমন হয়?’, ‘বিচ্ছিন্নতা একমাত্র অসুখ’, ‘সভ্যতা শব্দটা আপাদমস্তক সন্দেহজনক এবং মানবদরদী শিল্প-সাহিত্য সব ভুয়া’, ‘একটা পিকনিক কর, অদূরে যেখানে খুশি’, ‘ঘুম হঠাৎ চলে গেল’, ‘কতদিন দেখি না, ওয়েটিং ফর গোডো’। এইরকম, অজস্র। ‘কেমন আছ?’ জিজ্ঞাসা করলেই উত্তর, ‘বিভিন্ন প্রকার’। ফোন আসত মাঝে মাঝেই। দরকারে কিংবা অদরকারে। কোনও ভাল বই পড়লে বা ভাল নাটক-সিনেমা দেখলে, অন্যদেরও জানানো কর্তব্য বলে মনে করত রাহুলদা। যা-কিছু ভাল, তা ছড়িয়ে দিতে পারলে এক অদ্ভুত খুশি অনুভূত হত তার। আমাদের বন্ধু তন্ময় ভট্টাচার্যকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছিল, ‘টেকনোলজি এত উন্নত হচ্ছে, এতে মানুষে-মানুষে সম্পর্ক আর কতটুকু থাকে! কবিতা তো এক ধরনের সম্পর্ক। সম্পর্কই যদি না থাকে, তাহলে সাহিত্যের কী হবে?’ সাহিত্যের সূত্রে, জীবনের সূত্রে, আজীবন এই সম্পর্কগুলোই লালন করে গেছে সে। এ-ই ছিল স্বভাবধর্ম। লিখেছে, ‘আমার শব্দেরা দেখো/শিকারের রক্তে ভেসে যায়’। সে-ই শিকার সম্পর্কের। বারংবার বলত মণিভূষণ ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, উৎপলকুমার বসু, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, অরুণ মিত্র প্রমুখের কবিতার কথা। প্রস্তাব আসত, ‘চল, কিছু কাজ পড়ে আছে, সেরে ফেলি এইবার!’ অগ্রজদের প্রতি, ফেলে আসা সময়ের প্রতি যে-ঋণ, তা আমৃত্যু কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করতে দেখেছি তাকে।
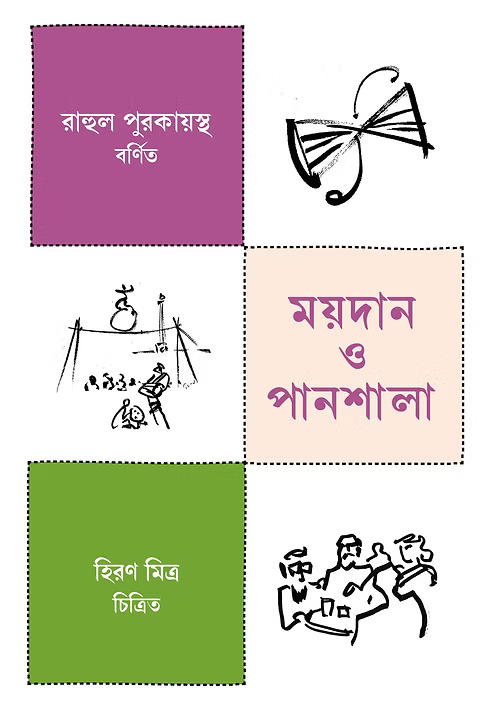
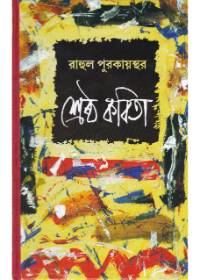
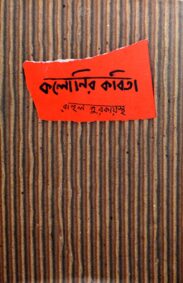
নিজের কবিতা নিয়ে বরাবর সংশয় ছিল রাহুলদার। একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে, ‘সংশয়’, ‘সন্দেহ’, ‘ভ্রম’ কিংবা ‘মায়া’— এই জাতীয় কিছু শব্দ ঘুরপাক খেত তার কবিতাশরীরে। স্মৃতি ও স্বপ্নের কাটাকুটি। এমনকী পাঠকপ্রিয়তার প্রশ্নে আড্ডা কিংবা সাক্ষাৎকারে বলতও সে-কথা, ‘আমার দশজন পাঠক ভাল। একশোজন পাঠক হলে আমি নিজেকে সন্দেহ করব।’ জনপ্রিয়তার হাতছানিতে, যেখানে কবিরা স্বধর্মচ্যুত হয়ে পড়ছে দিন-দিন, সেইখানে রাহুলদা সারাজীবন লাইটহাউসের মতো পথ দেখিয়ে গেছে আমাদের। শুধু কবিতার জন্যই বাঁচতে শিখিয়েছিল। আর শিখিয়েছিল ভালবাসতে। সমস্ত অপমান ফুল-মেঘ-পাখি করে দেওয়া সেই ভালবাসায়, কখনও-বা মনে পড়ে যায় শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সেই অমোঘ পঙ্ক্তি: ‘ভালোবাসা ছাড়া কোনো যোগ্যতাই নেই এ-দীনের।’ ‘শান্ত ইশারায় জাগে/বিকৃতি আমার/আমি তাকে শিল্প বলে ডাকি’— বিশ্বাস করত সে। যে-শিল্পের দেশে জখম বিড়াল লাট খায়, সেই যন্ত্রণার ধারাবিবরণীই লিখে রাখতে চেয়েছিল আজীবন। প্রেম আর প্রতিবাদকে মিলিয়ে দিতে চেয়েছিল। ‘মনোসংযোগঘটিত ক্ষয়ক্ষতি’ নিয়েই গড়ে তুলেছিল এক নিজস্ব ভাষাপৃথিবী। তার কবিতা অস্থির, ছটফটে; একইসঙ্গে নৃত্যরত সময়ের হাহাকার নিয়ে তা যেন ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইত পাঠক-হৃদয়ে। হ্যাঁ, আর ছিল ‘নাচ’। মেধার শরীর কিংবা শরীরের মেধা ভেঙে তাই সে কবিতায় লিখতে পেরেছিল, ‘যদি তুমি চাও/আমার শরীর নিয়ে রাক্ষস নাচাও।’ লিখেছিল, ‘ঘুরে ঘুরে নাচো তুমি বসন্তবাতাসে/সম্পর্কময়ূর তুমি নাচো, সম্পর্কবিড়াল তুমি নাচো/সম্পর্কচড়াই তুমি উড়ে উড়ে নাচো…’। নাচ-সংক্রান্ত দুটো কথা মেসেজ হাতড়ে উঠে এল। অপ্রাসঙ্গিক হবে কি? উদ্ধৃত থাক বরং: ১. ‘একটা সাউন্ড সিস্টেম উপহার পেয়েছি। এখন জোরে জোরে গান শুনি আর খুব নাচতে ইচ্ছে করে।’ ২. ‘কেউ আর নাচে না। নাচবুদ্ধি দিয়ে সব গিলে ফেলে! কিন্তু প্রকৃতি নৃত্যময়।’

ছবি সৌজন্য: ফিরোজ বসু
৩২ বছরের ফারাক। তবু কেন এই জিজ্ঞাসা: ‘লেখাগুলো কিছু হল রে?’ এ কেমন জানতে চাওয়ার তরিকা? বিনয়? ফোনে কেন ওই সকাতর প্রার্থনা, ‘প্লিজ, কিছু বল। আমি বুঝতে পারছি না, কবিতাগুলো কিছু দাঁড়াল কি না’? প্রথম-প্রথম বুঝতে পারতাম না। এখন বুঝি, ওই আত্মসমীক্ষা, ওই অতৃপ্তি-ই তাকে কবি করে তুলেছিল। একজন খাঁটি কবি। অস্থিরতার নাগরদোলায় ঘুরপাক খেতে-খেতে, সংশয়ের আগুনে পুড়তে-পুড়তে যে এগিয়ে যাচ্ছিল সামনের দিকে। আরও পরিণতমনস্কার দিকে। স্ব-চেতনাকে তরুণ কবির চোখ দিয়ে পড়তে চাওয়া, যে-কারণে আরও জরুরি হয়ে উঠেছিল তার কাছে। স্তাবকতা পছন্দ করত না। ‘নিরীহ ভ্রমের দেশ’ যখন ছাপা হচ্ছে, দেখতাম, বার বার পাণ্ডুলিপি কাটাকুটি করছে সামান্য পরামর্শের ভিত্তিতেই। মেসেজ পাঠাচ্ছে এই বলে: ‘এবার একটা বেশি ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছি। বইটি খারাপ হলে লোকে বলবে নিরীহ ভামের বই।’
রাহুল পুরকায়স্থর মতো কবির চলে যাওয়া মানে, একটা বড় ইতিহাস হারিয়ে যাওয়া। সময়ের পোকা যেখানে কেটে দিত ব্যক্তিত্বের রঙিন প্রতিকৃতি, তা জ্যান্ত হয়ে উঠত তার বয়ানে। একবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিল রাহুলদা এই লিখে, ‘যাদের সঙ্গে মিশেছি, একটা রূপকথার মতো গদ্য লিখতে চাই এদের নিয়ে। সবাইকে মিলিয়ে মিশিয়ে, সময়কে ভাঙচুর করে।’ প্রথম লাইনটাও ঠিক হয়ে গেছিল: ‘রাস্তার যে-অংশে রোদ পড়েছে, সেটা আমার।’ বইয়ের নাম, ‘অর্থহীনতার দিনলিপি’। ২৫ জুলাই, মুষলধারে বৃষ্টি-হয়ে-চলা কলকাতায়, রাহল পুরকায়স্থর মরদেহ যখন শ্মশানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, হাজার কথার ভিড়ে কেবল মনে পড়ছিল ওই একটাই লাইন, ‘রাস্তার যে-অংশে রোদ পড়েছে, সেটা আমার।’ রোদ না-ওঠা রাস্তা, রাহুলদার নয়। ছিলও না কখনও…