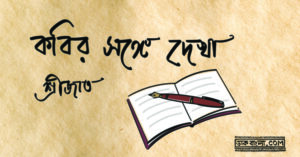বারান্দা-বৃত্তান্ত
কালো বারান্দা একটা সময়ে মনে হত অনেক লম্বা। আস্তে-আস্তে ছোট হতে লাগল। আসলে আমার পা-টা লম্বা হতে লাগল তো। ওই বারান্দাতেই তো বাবার সঙ্গে দৌড়োদৌড়ি খেলা করতাম। আমি তখন ছোট্টটি। বাবা তো ধুতি পরা। ধুতিটা চেপে ধরতাম। এই বারান্দাতেই ক্রিকেট খেলা হত, বারান্দার শেষপ্রান্তে ঝুলবারান্দায় যাওয়ার কাঠের দরজাটা বন্ধ করে চক দিয়ে তিনটে দাগ কেটে উইকেট। আন্ডারহ্যান্ড বল। অন্য ভাড়াটে বাবুদা, আমার ছোটকাকু, পিসতুতো দাদা, যাকে রাঙাদা বলতাম— এরা সবাই আমার চাইতে বড়। বেশ বড়। এছাড়া আত্মীয়-টাত্মীয়রা তো থাকতই সর্বদা। পিসেমশাইয়ের ভাগ্নেরা, বাবার মামাতো ভাইয়েরা ঠাকুরমার ছোট ভাইদের ছেলেরা… এমন সব। আমার মেজপিসেমশাইয়ের শ্বশুরবাড়ির লোকেরাই বেশি। আমাদের পরিবারটাও তো ওর শ্বশুরবাড়ির দিকেরই।
এই কালো বারান্দাতেই এক্কা-দোক্কার ছক কাটা হত চক-খড়িতে। ওখানে খেলত আমার বোনেরা, অন্য ভাড়াটেদের মেয়েরা। আমার সেজপিসেমশাই, মানে যাদের এই বাড়িটা, ওঁর একটিমাত্র ছেলে। রাঙাদা কলেজে পড়ছে। আরও দুই পিসি ছিল। বড়পিসি, ছোটপিসি, বড়পিসি নিঃসন্তান। ছোটপিসি প্রায়ই এ-বাড়িতে এসে থাকত। ছোটপিসেমশাই কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরি করতেন। উনি অন্যত্র বদলি হলে ছোটপিসি এখানেই থাকত। এই বাড়িটা যেন সেই দাদুর দস্তানা। কী করে যে এত লোকের সংকুলান হত, এখন ভাবলে অবাক লাগে। কালো বারান্দা, লাল বারান্দা মিলে ক’ফুট হতে পারে? পঞ্চাশ ফুটের বেশি নয়। স্মৃতি জুড়ে পড়ে আছে ওই পঞ্চাশ ফুট। ওখানে চোর-চোর খেলা, কানামাছি খেলা, লুকোচুরি খেলা, ফুটবলও। কাগজের বল তৈরি করতে শিখিয়েছিল বাবলুদা। পুরনো খবরের কাগজগুলিকে দলা পাকিয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে তৈরি হত। গোলাকৃতি বল। এতেই তো দিব্য খেলা হত। চোর-চোর খেলায় চোর নির্ধারণ করার একটা ছড়া-মন্ত্র ছিল, যেটা দীপুদির মুখেই শুধু। মনে পড়ে গেল।
কালীঘাটের কালী
ধূপ-ধূনা জ্বালি
হরপদতলে
মুণ্ডমালা গলে
কার বাড়িতে গিয়েছিলি মা,
কে করেছে পূজা
ইল্লা মিল্লা বিল্লাপত্র
তার ওপরে জবা।
যে জবা হবে, সেই চোর। কিন্তু ‘ইল্লা মিল্লা বিল্লাপত্র’ কথাটার অর্থ কী ভাবিনি তখন! এখন ‘বিল্লাপত্র’ মানে যে বিল্বপত্র, সেটা বুঝি, কিন্তু ‘ইল্লা মিল্লা’ আসলে, কী ছিল জানার কোনও উপায় নেই।
আমাদের ইস্কুলের শুরুতে আমরা লাইন দিয়ে হাতজোড় করে বলতাম, হে ভগবানসনা দেবী হে তব পশোবিতা…। অনেক পরে, প্রৌঢ় বয়সে জেনেছিলাম ওটা আসলে সরস্বতীর একটি স্তব। শ্বেতপদ্মাসনা দেবী শ্বেতপুষ্পশোভিতা।

রবীন্দ্রনাথ ‘জীবনস্মৃতি’-তে লিখছেন উনি স্কুলে প্রেয়ার করতেন— কলোকী পুলোকী সিংগিল মেললিং মেললিং মেললিং…। পরে জানতে পেরেছিলেন কথাটা হচ্ছে ফুল অফ গ্লি, সিংগিং মেরিলি, মেরিলি, মেরিলি। চোর-চোর খেলার অন্য একটা ছড়াও ছিল। সা রে গা মা পা ধা নি/ বোম ফেলেছে জাপানি/ বোমার ভেতর কেউটে সাপ/ ব্রিটিশ বলে বাপ রে বাপ।
এই ছড়া তৈরি হয়েছিল ১৯৪৪-’৪৫ সালে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে। আর আমি, এখন বলছি হয়তো ১৯৫৮-’৫৯ সালের কথা। এই কালো বারান্দায় একটা লোহার তার ছিল, তাতে শাড়ি ঝুলত শুকোবার জন্য। মা-ঠাকুরমা-পিসিদের, অন্য ভাড়াটেদের ঝোলানো শাড়ির দুই প্রান্ত সরিয়ে মাঝখান দিয়ে হেঁটে যাওয়া ছিল আমার খুব প্রিয় খেলা। একটু ভিজে, ঠান্ডা ঠান্ডা… এর মাঝখান দিয়ে পথ রচনা করে এগিয়ে যাওয়া। মায়ের শাড়িটার মাঝখান দিয়ে যাওয়ার সময়ে আমি মায়ের গায়ের গন্ধ পেতাম। কালো বারান্দায় কখনও-কখনও বিছানাও পাতা হত, আত্মীয়-স্বজন বেশি হয়ে গেলে।
কাছেই ছিল আরজিকর হাসপাতাল। ওখানে দেখানোর জন্য আত্মীয়-স্বজন এলে আমাদের বাসাতেই থেকে যেত। একবার, বাবার কেমন যেন মামাতো ভাই, মনে আছে, তাঁর নাম আদিনাথ, ওঁকে বাস ধাক্কা দিয়েছিল। পায়ে প্লাস্টার। পরে প্লাস্টার কাটা হবে। সেই একমাস আমাদের কাছেই থেকে গেল। মাঝের ঘরে উনি শুয়ে থাকতেন মেঝেতে, দাদু কালো বারান্দায়।

লাল বারান্দায় একটা টেবিল-চেয়ার, আর একটা চার পায়া, মানে চৌকি। কালো রং। দাদু বলতেন লোহাকাঠের। লোহাকাঠ আসলে কী কাঠ, জানি না আজও। ওই চৌকিতে নাকি শুত আমার কাকামণি, আর টেবিলে পড়াশোনা। কাকামণি স্কুল ফাইনালে ষষ্ঠ হয়েছিল। বৃত্তি পেয়েছিল। তারপর শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে ইঞ্জিনিয়র হয়েছিল। চাকরি করত। বেশিদিন কিন্তু নয়। পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল।
আমার মনে পড়ে, মাঝের ঘরে শুয়ে আছে কাকামণি, মেঝেতে। জ্বর, বমি। ডাক্তার আসছেন। প্রকাশবাবু ছিলেন বাড়ির ডাক্তার। তখন ডাক্তাররা কিন্তু বাড়িতে আসতেন। চার টাকা না আট টাকা ফি মনে নেই। তারপর আরও বড় ডাক্তার। কাকামণির গায়ে কেমন ছোপ-ছোপ দাগ। তারপর প্রস্রাব বন্ধ। এলেন আরও বড় ডাক্তার। অমল রায়চৌধুরী। তাঁর বোধ হয় ৩২ টাকা ফি ছিল। বাড়ি এলে ৬৪ টাকা । উনি নাকি বলেছিলেন বড় দেরি হয়ে গেছে। তারপর এলেন যোগেন কবিরাজ। যোগেন কবিরাজ নাড়ি ধরে অনেকক্ষণ বসে রইলেন। তারপর ঠোঁট উল্টে দিলেন। বাবার কানে-কানে কী যেন বলছিলেন।
পরদিন খেতে বসেছি, মেঝেতে দুপুরবেলা, বেশ মনে আছে ডাল আর আলুসেদ্ধ। এসে বলল তিনু কেমন করছে। সবাই উঠে পড়ল। আমিও। কাকামণি হেঁচকি তুলছে। ঠাকুরমা, পিসিমা— সবাই মেজপিসিদের ঠাকুরঘরে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছে বিগ্রহের সামনে। আমি এ-ঘর, ও-ঘর ছুটোছুটি করছি। বাবা-কাকামণিকে ঠেলা দিয়ে তিনু, তিনু ও তিনু করে ডাকছে, আমার দাদু-কাকামণির মাথায় হাত দিয়ে কিছু বিড়বিড় করছে। মুখে জল দিল পিসিমা, জল গড়িয়ে পড়ল ঠোঁটের পাশ দিয়ে। ঠাকুরমা অজ্ঞান হয়ে গেল। বাবা দেওয়ালে মাথা ঠুকতে লাগল।
লাল বারান্দায় একটা টেবিল-চেয়ার, আর একটা চার পায়া, মানে চৌকি। কালো রং। দাদু বলতেন লোহাকাঠের। লোহাকাঠ আসলে কী কাঠ, জানি না আজও। ওই চৌকিতে নাকি শুত আমার কাকামণি, আর টেবিলে পড়াশোনা। কাকামণি স্কুল ফাইনালে ষষ্ঠ হয়েছিল। বৃত্তি পেয়েছিল। তারপর শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে ইঞ্জিনিয়র হয়েছিল। চাকরি করত। বেশিদিন কিন্তু নয়। পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল।
এর আগে আমি কখনও মৃত্যু দেখিনি। মরণ কাকে বলে জানতাম না। দেখলাম। আমার বয়স তখন বছরছয়েক। এটাই আমার প্রথম আঘাত। কাকামণির নাম ছিল অমৃতলাল চক্রবর্তী। ভীষণ ভালবাসত আমাকে। হারালাম। আমার দ্বিতীয় বইটা, ‘অষ্ট চরণ ষোলো হাঁটু’ কাকামণিকে উৎসর্গ করেছিলাম।
কাকামণির মৃত্যুর পর আমার ঠাকুরমা পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিল। ‘হে ভগবান আমাকে ন্যাও, তিনুর কাছে পৌঁছাইয়া দ্যাও…’, ‘আমার মাথায় বাড়ি দে তোরা… কী পাপ কইরাছিলাম গত জনমে…’— এইসব বলত। খাওয়াদাওয়া প্রায় বন্ধ। দাদু পাথরের মতো। বাবা আর কী করবে, এত বড় পরিবারটাকে সামলাতে হবে তো! বাবা স্কুলে যেত, তারপর কয়েকটা টিউশনি করে বাড়ি ফিরত। হয়তো রাত আটটা বেজে যেত। বাবা স্কুলে কাজ করত। যদিও সরকারি স্কুল, কিন্তু কতই-বা মাইনে তখন? বাবা সরকারি স্কুলে চাকরি পেয়েছিল অবিভক্ত ভারতে। ১৯৪৪-’৪৫ সাল নাগাদ। দেশভাগ হওয়ার পর অপশন দিয়ে ভারতে আসে।