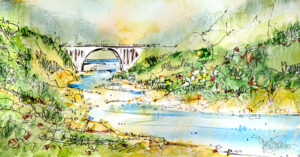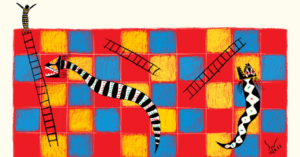উনিশ শতকের বাংলা তথা কলকাতার বাঙালি ‘সেলেব’দের যদি একটা তালিকা করা হয়, তাহলে প্রথমেই হুড়মুড় করে এসে পড়বে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিমের নাম। সঙ্গে দ্বারকানাথ বা দেবেন ঠাকুরই-বা বাদ যাবেন কেন? ঈশ্বর গুপ্ত, গিরিশ ঘোষ, দীনবন্ধু মিত্র, শিবনাথ শাস্ত্রী, রাধাকান্ত দেব, কেশবচন্দ্র সেনের পাশাপাশি নির্বিকল্প ভাবে থাকা উচিত প্যারীচাঁদ মিত্রের নামও।
বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে কথা শুরু হয় ‘হুতোম-আলালের’ প্রসঙ্গ ধরেই। তারপর সেই কথার সূত্র ধরে কেমন করে যেন আলোচক (সঙ্গত কিংবা অসঙ্গত ভাবে) ঝুঁকে পড়েন হুতোমের দিকে। এই লেখায় হুতোমের হুজুগ নয়, বরং আলালের সঙ্গেই খানিক অন্যভাবে আলাপ করা যাক।
উনিশ শতকের বাবু কালচারকে আমরা পট থেকে বটতলা কিংবা অতিসরলীকৃত পিরিয়ড ড্রামার সূত্রে যেভাবে জানি, সেখানে অভিজাত বাবু মাত্রই মদ্যপ, লম্পট, শিক্ষার ধার ধারেন না, আর নারী মাত্রেই হয় ‘পতিপরায়ণা’ নয়তো বহির্মুখী। ইতিহাসের চরিত্ররা যে বাস্তবে কখনওই ‘টাইপ’ চরিত্র হতে পারে না, তার অন্যতম উদাহরণ প্যারীচাঁদ মিত্র। কারণ তাঁর জীবন ও লেখালেখিতে বাঙালির রেনেসাঁস প্রদীপের আলো ও তার তলার অন্ধকার— দুটোই বড্ড স্পষ্ট। প্যারীচাঁদের চরিত্রের যে-স্ববিরোধ, তা নিয়ে হুতোম ব্যঙ্গ করলেও আমরা সেটিকে তাঁর স্বভাবের বৈচিত্র্য হিসেবে দেখব; তাঁর জীবনে আধুনিক কার্যকলাপেরই পাল্লা ভারী, যার ফলে তাঁর রক্ষণশীল আচরণ খানিক দরদের সঙ্গেই এড়িয়ে যাওয়া যায়।
পিতামহ গঙ্গাধর মিত্র হুগলি থেকে কলকাতায় এসে, কোম্পানির আমলে দেওয়ানগিরি করে পয়সা করেছিলেন বিস্তর। প্যারীচাঁদের বাবা রামনারায়ণ মিত্রও কোম্পানির কাগজ আর হুণ্ডির কারবার করে ফুলেফেঁপে ওঠেন। অর্থাৎ প্যারীচাঁদ ছিলেন আক্ষরিক অর্থেই ‘আলালের ঘরের দুলাল’। কিন্তু এই আখ্যানের নায়ক মতিলালের মতো ‘বখে’ যাননি তিনি। ব্যক্তিজীবনে প্যারীচাঁদ ছিলেন যথেষ্ট সুশৃঙ্খল। এমনকী হিন্দু কলেজে পড়তে গিয়ে হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও ও ‘ইয়ং বেঙ্গল’দের সঙ্গ করার পরেও তাঁর জীবন অদ্রোহী। তাঁর ‘ইন্সপিরেশন’ ছিলেন হেয়ার সাহেব। পরবর্তীতে ইংরেজি ও বাংলায় কলম ধরেছেন তাঁকে নিয়ে। সময়ের হিসেব মতো প্যারীচাঁদ (যিনি হিন্দু কলেজে ভর্তি হন ১৮২৭ সালে) সরাসরি ডিরোজিওর ছাত্র। প্যারীচাঁদ লিখিত ডেভিড হেয়ারের জীবন চরিতে ডিরোজিওর প্রসঙ্গ ও প্রশংসা আছে। তবু তিনি কখনওই ‘ডিরোজিয়ান’ নন।
নিষিদ্ধ খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করাটাই যে ‘আধুনিকতার’ একমাত্র পরিচয় নয়, সে-কথা সমকালেই দেখিয়ে দিয়েছিলেন প্যারীচাঁদ। তিনি আর তাঁর বন্ধু রাধানাথ শিকদার ‘মাসিক’ নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করতেন ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে। সেই পত্রিকার ঘোষিত নীতি ছিল, ‘এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদের জন্য ছাপা হইতেছে, যে ভাষায় আমাদিগের সচারচর কথাবার্ত্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান, পড়িবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নিমিত্তে এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই।”
আজকের লিঙ্গ চেতনায় এই নীতি মেয়েদের জন্য অবমাননাকর মনে হতে পারে, কিন্তু উনিশ শতকের সমাজ পরিস্থিতিতে নারী শিক্ষার হার ছিল সত্যিই একেবারে তলানিতে। মেয়েদের পড়ার জন্য তখন প্রয়োজন ছিল ‘সহজ’ ভাষার। এহেন পরিস্থিতি যে বেদনাদায়ক তাতে দ্বিমত নেই, কিন্তু বাস্তবকে মাথায় রেখে শুধু নারী এবং স্বল্পশিক্ষিত পুরুষের জন্য পত্রিকা প্রকাশের ঘটনাটিই যথেষ্ট বৈপ্লবিক বলে মনে হয়। তাতেও আবার ‘বিজ্ঞ পাঠকদের’ পড়ার ব্যাপারে নিমরাজি হয়েও, সম্পাদকদ্বয় স্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছেন যে, তাঁরা না পড়লেও তাঁদের কিচ্ছু যায় আসে না! উনিশ শতকের খুব কম পত্রিকাই ‘বিজ্ঞ’ পাঠকদের এমন বুড়ো আঙুল দেখিয়েছেন বলে মনে হয়।
এই ‘মাসিক’ পত্রিকাতেই ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল ‘আলালের ঘরের দুলাল’। এটি বাংলার প্রথম উপন্যাস কিংবা প্রথম বাস্তবধর্মী আখ্যান নাকি উপন্যাসের পূর্বসূরি, সে-নিয়ে বিস্তর তর্ক ও চর্চা আছে। প্যারীচাঁদ নিজে তাঁর ভূমিকার ইংরেজিতে ‘নভেল’ আর বাংলায় ‘উপন্যাস’ ব্যবহার করেছেন। দেখুন, আলালে কাহিনি নিঃসন্দেহে আছে, কিন্তু উপন্যাসের মতো জোরদার প্লট নয়, চরিত্রগুলিও একপেশে। ভাষা নিশ্চয়ই সরল কিন্তু সাধু-চলিতের জগাখিচুড়ি প্রতি পাতায় চোখে পড়বে। তা সত্ত্বেও প্রথম সার্থক বাংলা উপন্যাসের রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্র, প্যারীচাঁদকে যে ‘সার্টিফিকেট’ দিয়েছেন, তাতে বাংলা সাহিত্যে ‘আলালের’ স্থান নিয়ে সংশয় কেটে যাবে।
তাঁর ‘ইন্সপিরেশন’ ছিলেন হেয়ার সাহেব। পরবর্তীতে ইংরেজি ও বাংলায় কলম ধরেছেন তাঁকে নিয়ে। সময়ের হিসেব মতো প্যারীচাঁদ (যিনি হিন্দু কলেজে ভর্তি হন ১৮২৭ সালে) সরাসরি ডিরোজিওর ছাত্র। প্যারীচাঁদ লিখিত ডেভিড হেয়ারের জীবন চরিতে ডিরোজিওর প্রসঙ্গ ও প্রশংসা আছে। তবু তিনি কখনওই ‘ডিরোজিয়ান’ নন।
১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্যানিং লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত ‘লুপ্তরত্নোদ্ধার’ বা ‘বাবু প্যারীচাঁদ মিত্রের গ্রন্থাবলী’তে ভূমিকা অংশে বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন— ‘যে ভাষা সকল বাঙ্গালীর বোধগম্য এবং সকল বাঙ্গালী কর্তৃক ব্যবহৃত, প্রথম তিনিই তাহা গ্রন্থপ্রণয়নে ব্যবহার করিলেন। এবং তিনিই প্রথম ইংরাজি ও সংস্কৃতের ভাণ্ডারে পূর্ব্বগামী লেখকদিগের উচ্ছিষ্টাবশেষের অনুসন্ধান না করিয়া, স্বভাবের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে আপনার রচনার উপাদান সংগ্রহ করিলেন।…আলালের ঘরের দুলালের দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের যে উপকার হইয়াছে, আর কোন বাঙ্গালা গ্রন্থের দ্বারা সেরূপ হয় নাই এবং ভবিষ্যতে হইবে কিনা সন্দেহ।’
বাস্তবিকই বিষয় ও ভাষাভঙ্গি উভয় ক্ষেত্রেই ‘আলাল’ বাংলা কথাসাহিত্যে পথপ্রদর্শক— এটা খুব কঠোর সমালোচককেও স্বীকার করতে হবে। কিন্তু সমকালে ‘আলালি’ ভাষা যথেষ্ট সমালোচিত হয়েছিল। রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁর ‘বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব’এ (১৮৭২) প্যারীচাঁদের ভাষা ও রচনারীতির যথেষ্ট সমালোচনা করেছেন। শোনা যায় মাইকেল মধুসূদনেরও এই ভাষা নিয়ে অনুযোগ ছিল। নগেন্দ্রনাথ সোম তাঁর ‘মধুস্মৃতি’তে জানাচ্ছেন, মধুসূদন নাকি ‘পোষাকী’ ভাষা তুলে দিয়ে, ঘরে বাইরে এই আটপৌরে ভাষার ব্যবহার মোটেই পছন্দ করেননি। তাঁর মতে সংস্কৃত থেকে বিপুল আমদানি ছাড়া এটি ‘the language of fishermen’। উত্তরে উত্তেজিত প্যারীচাঁদ সপাটে জবাব দিয়েছিলেন, ‘তুমি বাঙ্গালা ভাষার কী বুঝিবে? তবে জানিয়া রাখ, আমার প্রবর্তিত এই রচনাপদ্ধিতিই বাঙ্গালা ভাষায় নির্বিবাদে প্রচলিত এবং চিরস্থায়ী হইবে।’ ‘আলালি’ ভাষা চিরস্থায়ী হয়নি বটে, কিন্তু সেই থেকে লেখার ভাষাকে সহজ করার ওই চেষ্টাটা আজও ‘আধুনিকতার’ চিহ্ন হিসেবেই বজায় আছে।
তবে উল্লেখের কথা, ‘আলালের ঘরের দুলাল’ (১৮৫৮) ও ‘মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়’ (১৮৫৯) এই বই দু’টি প্রকাশের পর, প্যারীচাঁদ আর সেই অর্থে ‘আলালি’ ভাষায় ফেরেননি। ১৮৬০-এ প্রকাশিত বই ‘রামারঞ্জিকা’থেকেই ভাষা আর বিষয়বস্তুর বাঁকবদল শুরু হয়; পরবর্তীতে ‘যতকিঞ্চিৎ’, ‘অভেদী’, ‘আধ্যাত্মিকা’র মত বই পড়ে তাজ্জব বনে যেতে হয়, এগুলিও প্যারীচাঁদের লেখা! ১৮৬০ সালে স্ত্রীর মৃত্যু তাঁর অন্তর্জীবনকে পালটে দিয়েছিল। ১৮৮১তে ইংরেজি বই ‘অন দ্য সোল: ইটস নেচার অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট’- এর ভূমিকাই তিনি নিজেই লিখেছেন, ‘In 1860, I lost my wife, which convulsed me much. I took to study of spiritualism…’ । ব্রাহ্মদের খুব কাছাকাছি থাকা, ‘গীতাঙ্কুর’ এর মত ব্রহ্মসঙ্গীতের রচয়িতা প্যারীচাঁদের মন ক্রমে নিবিষ্ট হয় প্ল্যানচেটে, পরলোকচর্চায়। প্ল্যানচেটের সঙ্গীরাও সব তালেবর ব্যক্তিত্ব— দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজা দিগম্বর মিত্র, ‘ইন্ডিয়ন মিরর’ এর সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন, ‘অমৃতবাজার’ এর প্রতিষ্ঠাতা শিশিরকুমার ঘোষ। শোনা যায়, প্রেতাবেশ ভাল হত নিত্যরঞ্জন ঘোষের। সম্পর্কে যিনি প্যারীচাঁদের ভাগ্নে, পরবর্তীতে শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য নিরঞ্জনানন্দ।
তবে প্যারীচাঁদের আধ্যাত্মিকতা যে শুধু তুকতাক, ভূতপ্রেত, ঝাড়ফুঁকেই ঘেরা তা নয়, ঈশ্বরপ্রীতি ও সংসারে নিরাসক্তির চিন্তা, তাঁকে কখনও সমকালে প্রচলিত সমাজ কাঠামোর বাইরে ভাবতে উস্কে দিয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ‘আধ্যাত্মিকা’ রচনাটির কথা। এই আখ্যানের নায়িকা বারাণসী প্রবাসী এক গৃহস্থের কন্যা আধ্যাত্মিকা উপনিষদের যুগের ব্রহ্মবাদিনীদের মতো বিয়ে না করে, ঈশ্বরচিন্তায় সারাজীবন কাটিয়েছে, এবং গঙ্গার তীরে সজ্ঞানে স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করেছে। যে-সমাজে বলা হয়, ‘পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা’ অথবা ‘স্বামীর কোলে পুত্র দোলে/ মরণ যেন হয় গঙ্গাজলে’—সেই সমাজে একজন অবিবাহিত মেয়েকে উপন্যাসের নায়িকা করা এবং তাঁর পুরুষ-অধীনতাহীন জীবনকে উপন্যাস জুড়ে উদ্যাপন করা উনিশ শতকে দাঁড়িয়ে যথেষ্ট ব্যতিক্রমী চিন্তাভাবনা বলেই মনে হয়, হোক না তা আধ্যাত্মিকতার সূত্রে।
প্যারীচাঁদ মিত্রের এই ঈশ্বর-বিশ্বাসী আবেগী আচরণই, রসিক তরুণ হুতোমের কাছে ব্যাঙ্গের উপকরণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বস্তুত হুতোমের ‘রেলওয়ে’ নকশাটি প্যারীচাঁদের ‘যৎকিঞ্চিৎ’ (১৮৬৫) নামক ধর্মীয় উপন্যাসের প্যারোডি। ‘যৎকিঞ্চিৎ’ এর বিষয়বস্তু দুই ধার্মিক ঈশ্বরবিশ্বাসী বন্ধু প্রেমানন্দ ও জ্ঞানানন্দের উত্তর ভারত ভ্রমণ, সেই সূত্রে ঈশ্বর বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নানা চরিত্রের সংস্পর্শ ও তাদের মধ্যে ঈশ্বর মহিমা প্রচার। হুতোম তাঁর নকশায় প্যারীচাঁদ মিত্রকে প্রেমানন্দ ও প্যারীচাঁদের আবাল্যবন্ধু ও পরবর্তীকালে বৈবাহিক শিবচন্দ্র দেবকে সাজিয়েছেন জ্ঞানানন্দ। এই দুই চরিত্রকে নিয়ে যারপরনাই ব্যঙ্গ তো রয়েছেই, এমনকী প্যারীচাঁদেরই অপর একটি রচনা ‘রামারঞ্জিকা’র প্রসঙ্গ এনে অহেতুক তীর্যক মন্তব্য রয়েছে। ব্যক্তিজীবনে প্যারীচাঁদ মিত্রের কোনও রকম ‘গর্হিত’ কর্মে রুচি ছিল না। এমন নিপাট ‘ভদ্রলোক’কে নিয়ে কালীপ্রসন্নের এহেন ‘ফচকেমি’র খুব একটা প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয় না।
শুধু লেখালিখি নয়, প্যারীচাঁদ মিত্রের জীবন ছিল আরও নানান ইতিবাচাক কর্মে ভরপুর। তিনি ছিলেন ‘দ্য ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি’র উপ-গ্রন্থাগারিক ও পরে গ্রন্থাগারিক। উনিশ শতকের কলকাতায় বহু সভা-সমিতি-সংস্থার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। ‘জ্ঞানোপার্জিকা সভা’, ‘ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন’, ‘পশুক্লেশ নিবারণী সভা’, ‘মদ্যপান নিবারণী সভা’, ‘বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা’, ‘স্কুল বুক সোসাইটি’— সবেতেই ছিলেন।
বাংলা গদ্যের মোড় ফিরিয়ে দেওয়া এই লেখক একদা তাঁর দুই ছেলেকে নিয়ে শুরু করেছিলেন ব্যবসা, নাম দিয়েছিলেন ‘প্যারীচাঁদ মিত্র অ্যান্ড সন্স’!
নকশা জাতীয় লেখার আলোচনায়, হুতোমের সঙ্গে টেকচাঁদের তুলনা চলেই আসে। আর তাতে বেশিরভাগ সমালোচকেরই পক্ষপাত থাকে হুতোমের দিকে। এটা সত্যিই যে, ব্যঙ্গের কশাঘাতে হুতোমের সঙ্গে পেরে ওঠা মুশকিল; কিন্তু হুতোমের মতো তাঁর রচনা নেহাতই আক্রমণ-সর্বস্ব নয়। ব্যঙ্গের উত্তেজনার বিকল্পে টেকচাঁদের লেখায় জ্ঞানের স্নিগ্ধতা অনেক বেশি সুলভ। প্যারীচাঁদের লেখার সংখ্যা ও বৈচিত্র্যও অনেক বেশি। আর তাছাড়া, ‘সহজ করে কথা কওয়া’-র পথটি তো দেখিয়েছেন আলালই। টেকচাঁদের তৈরি করা শৈলী কি মসৃণ করেনি কালীপ্রসন্নের নকশা লেখার পথকে? হুতোম, প্যারীচাঁদের মতন দীর্ঘজীবন পেলে কী হত বলা যায় না; শুধু যেটুকু বলা যায় তা হল, গদ্যের মানের নিরিখে সত্যিই হুতোম টেকচাঁদকে টেক্কা দিতে পেরেছেন কিনা, এই বিতর্কটা বরং চলতে থাকুক।