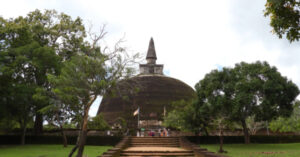মানুষকে আমরা চেতনার ঘরে একাকী ফেলে রেখে, হেঁটে চলে গেছি বহুদূর। বন্ধ ঘর, চতুর্দিকে ছড়ানো করোটি, নির্জন-শীতল চাঁদ; হেমন্তের রাতে নিজেকে সহস্রবার খুন করেও মরিনি বলে, বোঁচকা-বুঁচকি বেঁধে পালিয়ে এসেছি অপরূপ জ্যোৎস্নার উঠোন পরিত্যাগ করে। সেই থেকে নিরীহ বেড়ালের মতন সিঁড়ির আঁধারে বসে, হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগানো আমাদের এক প্রিয় স্বভাব। তার একদিকে জমে ওঠে নয়ানজুলি অন্যদিকে দ্বাররুদ্ধ প্রাণ। ভেতর আসলে বোধিহীন, রক্তশূন্য, পারম্পর্যহীন। পড়ে-পড়ে — উত্থানক্ষমতাহীন মেরুদণ্ডের পুনর্বাসন ছাড়া, ভিন্ন কোনও অভিঘাত এখন ধোপে টিকবে না।
তবু এক-একটা রাত আসে। নিঃশব্দ মৃত্যুর রাত। উপনিষদের অনপোযাচিত কান্না, যা নীতার কণ্ঠ রোধ করে, সে জীবন ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী রিক্ততা, এক-একদিন এই অন্ধকার কুয়োর জলে, আপন বেদনারীতিতে গড়ে তোলে অসহায় ম্যামথের কাহিনি। সে খুব বেশি অচেনা দিনের কথা নয়, পঁচিশ কিম্বা পঁয়ত্রিশ, তারও চেয়ে পুরনো, হতে পারে পঞ্চাশ-পঁচাত্তরের অনির্বাপিত দিনগুলোর কথা। যখন আপন সহোদরার রক্ত গায়ে মেখে, ঈশ্বর স্বয়ং এসে দাঁড়িয়ে থাকে চৌকাঠে। তখনই, অস্তপারে ভাঙছে— সভ্যতার চূড়ান্ত ম্যাসাকারের দৃশ্য, দৃশ্যের মন্তাজ, অর্থাৎ নিষ্ফলতার ভয়াবহ ধ্বংসকার্য। সে অধঃপতিত চিত্রাবলীর অনায়াস পতন, যিনি অবিরাম স্তম্ভনে অস্বীকার করেছেন, সংঘাত গড়ে তুলেছেন, ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন, তিনি ঋত্বিক।
‘দেয়ার ইজ নাথিং আন্ডার দ্য সান!’ অর্থাৎ, ইতিহাসের শোকাবহ নদী বয়ে যায় শুধু ঝরে পড়া অঢেল নক্ষত্রের জলরাশি নিয়ে। এ-কথা ততক্ষণ সমর্থনযোগ্য, যতক্ষণ ইতিহাসের পশ্চাদভূমি স্থির। সচল হলেই জন্ম নেয় বিকৃতি বা ডিস্টরশন। ঋত্বিক এই অনায়াসপতনের ধারা রুখে দিয়ে বৈপরীত্য-তর্জনী তুলে বারবার দেখিয়েছেন— জীবন কখনওই নিয়তির একমুখী প্রবাহ নয়। তার ভিন্নতর দর্শন আছে। নিজস্ব চলন ও গতি আছে। এক উদ্বাস্তু কলোনি থেকে উঠে আসা সীতা, বেশ্যালয়ের চৌকাঠে এসে দ্বি-খণ্ডিত হয়, সেই একই শরণার্থী শিবির থেকে ভেসে আসা আজাদগড় কলোনির নীতা, কিম্বা অনসূয়া— নিয়তির সাবজেক্টিভ ন্যারেশন ভেঙে বেরিয়ে যায়। যার মূল আধার— পার্সপেকটিভ। গতি ও দৃশ্য-বিন্যাসের একাধিক সম্ভাবনাময় কম্পোজিশন। যার চারটি প্রকারভেদ ঋত্বিক দেখিয়েছেন — ১. দৃশ্যমান বস্তু বা জীবের ঘোরাফেরার গতি ২. চিত্রগ্রহণ ও যন্ত্রের নিজস্ব গতি ৩. গতির স্তম্ভন ৪. মানসিক গতি।
আরও পড়ুন: এপিকের ঢং কীভাবে ধরা পড়েছিল ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ ছবিতে? লিখছেন অভীক মজুমদার…
মোদ্দা কথা, যেখানে ক্যামেরার গতি যত বেশি, জীবনের ফ্লো-ও তত অস্থির। ক্যামেরার এই গতিকে কাজে লাগিয়ে, কীভাবে দৃশ্যের বিনির্মাণ করবেন, তা একান্তই স্রষ্টার আত্মাধ্যায়ের বিষয়। যেমন, ‘অযান্ত্রিক’–এ গতির এই প্রেক্ষণগুলো খুব সুষ্টভাবে সেখানে দেখানো হয়েছে।
দুই অপরিচিত যুবক-যুবতী। যাদের ডাকবাংলোতে পৌঁছে দিতে যাচ্ছে জগদ্দল। সেই অচেনা যুবতীর সঙ্গে, বিমলের কিম্বা জগদ্দলের তখনও কোনও মানসিক সংঘাত ঘটেনি। ঋত্বিক এখানে যন্ত্র এবং জীবনের গতিময় অবস্থাকে বর্ণনা করার জন্য ওয়াইড অ্যাঙ্গেলে সাবজেক্ট হিসেবে তুলে ধরছেন একটা আপেক্ষিক আলোছায়াময় বনানীর দৃশ্য। যার সমান্তরালে এক পাশ থেকে অন্যপাশে তীর বেগে ছুটে চলে যাচ্ছে জগদ্দল। এখানে ক্যামেরা কাউকে অনুসরণ না করে, সেই বনানীতলেই নিশ্চল হয়ে পড়ে রইল। এই নিশ্চলতার বিপক্ষে জগদ্দলের গতিময়তা ফুটিয়ে তুলছে ঋজু প্রাণশক্তির পরিচয়।
ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের আর পাঁচটা আধুনিক গাড়ি যা পারে, জগদ্দলের যান্ত্রিক সক্ষমতা যে তাদের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। সেটা সে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেল। (বস্তুত এক-এক জায়গায়, চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার প্রশ্ন আসে।)
‘সুবর্ণরেখা’য় সীতা যখন আত্মহত্যা করল, যেখান থেকে ঈশ্বর বঁটি হাতে টলতে-টলতে বাইরে এল, বিনু সমেত অন্যান্য চরিত্র ভয়ে স্তব্ধ, যেখানে ঈশ্বরের পটভূমি অতলান্ত অন্ধকারে বিলীন। খালি ঈশ্বরের ঘর্মাক্ত মুখটা ফ্যাকাশে সাদা আলোয় উদ্ভাসিত। সে রক্তমাখা বঁটিটা তুলতে-তুলতে, কতকগুলো জান্তব শব্দসহ, হঠাৎ মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ে যাওয়া মাত্রই, ক্যামেরা দ্রুত গতিতে অনেক উপরে উঠে গেল, তারপর আছাড়ি-পিছাড়ি খাওয়া ঈশ্বরকে ছেড়ে দিয়ে সোজা নেমে এল উদভ্রান্ত, বিস্ফারিত-নেত্র বিনুর মুখের উপর। দেখানো হল সমস্ত ট্রাজেডির ফলশ্রুতি ওই বিনু। আর সব এহ-বাহ্য।


আবার কোথাও একটা ফ্রেমে একাধিক চরিত্রের অবস্থান; সেখানে তাদের মানসিক অবস্থা ও গতির সাযুজ্য গঠন করা হচ্ছে শুধুমাত্র ক্যামেরার ফোকাস স্থির রেখে।
‘মেঘে ঢাকা তারা’-য় নীতা যখন জানতে পারল তার যক্ষ্মা হয়েছে, সে ভেতর বাড়ি ছেড়ে, বাইরের ঘরে আশ্রয় নিল। সে একেবারে ক্যামেরার সামনে উপুড় হয়ে শুয়ে কাশছে, এমন সময়ে তার মা এসে যখন বোম্বাইয়ে শঙ্করের সুখ্যাতির কথাগুলো বলতে শুরু করে, তখন নীতা কাশির দমকগুলোকে লুকোতে থাকে। মা প্রশ্ন করে — ‘হয়েচে টা কী? অ্যাঁ, রাতদুপুরে বাইর-বাড়িতে এয়ে বিছানা পাতস।’ নীতা চমকে উঠে রক্তভরা কাপড়টা লুকিয়ে উত্তর দেয় — ‘এটা তো একটা নির্বান্ধব পুরী। এইটার আবার বাইর বাড়ি এইটার আবার অন্দর বাড়ি।’
দুই কথোপকথনের দৃশ্যে, ক্যামেরার ফোকাস ফ্রোরগ্রাউণ্ড থেকে সরিয়ে, নীতার মায়ের উপরেই রাখা হয়েছে। (সাধারণত কথোপকথনের সময়ে ফোকাস নড়াচড়া করে, বক্তার উপর সরিয়ে আনা হয়।) এখানে ব্যাপারটা কিছুটা উলটো নিয়মে দেখানো হয়েছে এবং সেটা ইচ্ছে করেই। কারণ, দৃশ্যে নীতার যে-মন্তব্য ফুটে উঠেছে, তার জন্ম তীব্র এক বেদনাবোধ থেকে। ক্যামেরায় তার মানসিক অবস্থাকে জাস্টিফাই করতেই প্রচলিত নিয়মের উলঙ্ঘন করে গেছেন।
আসলে, শিল্পের সঙ্গে শিল্পীসত্তার একটা ভাবাদর্শগত বোঝাপড়া থাকে। যার উপর দাঁড়িয়ে থাকে শিল্পরূপ। এই মধ্যবর্তী স্পেস ও স্বাধীনতাটুকু যারা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারেন, তাদেরকে ঋত্বিকের ভাষায় একপ্রকার ‘জোচ্চোর’-ই বলা চলে — ওয়ান অব দ্য সুপ্রিম ব্রেনস, ওয়ান অব দ্য সুপ্রিম টেকনিকস। যা দিয়ে একটা ‘পোটেমকিন’ গড়ে তোলা যায়, একটা ‘সেভেনথ্ সীল’ গড়ে তোলা যায়, ঋত্বিক-মৃণালের জোচ্চোর উপনিবেশ গড়ে তোলা যায়।

২৪.০৯.৬৭ –এর খসড়া : ‘‘নিরালম্ব বায়ুভূত শিল্প কখনো শিল্পের পর্যায়ে ওঠে না। তাকে কোথাও না কোথাও আত্মীকরণ করতে হয়। ভালো না বাসলে শিল্প জন্মায় না। এর প্রকাশভঙ্গী বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে, শিল্পীর মেজাজের উপর নির্ভর করে। কিন্তু মূল সূত্রটি সেই — ‘সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।’ ভালো করে তাকিয়ে দেখুন, প্রথমে সত্য। সত্যসিদ্ধ না হলে কোন শিল্পই শিল্পীর পর্যায়ে ওঠে না। শিবম্ — অর্থাৎ যা কিছু শাশ্বত। যা আপনি দুঃখ দিয়ে অর্জন করেছেন। যেগুলো আপনি আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে খুঁজে পেয়েছেন…
সুন্দর! এর কোন সংজ্ঞা নেই। এটা সম্পূর্ণ আপনার রুচির উপর নির্ভরশীল। সৌন্দর্যের কোন মান নেই। দেশে দেশে কালে কালে সৌন্দর্যের মান বিবর্ধিত হয়েছে কিন্তু সত্য এবং শিবকে অস্বীকার করে যে সুন্দর দাঁড়ায় তাকে ঘৃণা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই।’’
কাজেই দৃশ্যের ভেতরকার অপরিহার্য সত্যকে ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে, শিল্পী যদি তার নৈতিক অবস্থান থেকে সরে যায়, সেটা তখন আর শিল্প থাকে না, ভাঁড়ামোতে পরিণত হয়। যদিও ভাঁড়ামোর অবকাশ অন্যান্য মিডিয়ামের তুলনায় এ-দেশের চলচ্চিত্র-শিল্পে এক্কেবারে জেঁকে বসে আছে, যার অন্যতম কারণ ‘মুনাফা’। কোটি-কোটি টাকা ঢেলে, প্রযোজক যদি সে-টাকা ফেরত না পান, তবে এক্সপেরিমেন্টাল ফিল্মের সলিল সমাধি অবধারিত।
আবার এও সত্য যে, শুধুমাত্র শিল্পের তাগিদে একদল প্রস্তুত দর্শক কোনওকালেই গড়ে ওঠেনি বা গড়ে উঠতে ব্যর্থ। ফলে, অনেক খ্যাতনামা শিল্পীই তাদের অবস্থান থেকে সরে গেছেন। শিল্পের নাম করে, দিনের পর দিন বুজরুকি করে গেছেন। ঋত্বিক এই আপোসটুকু করতে পারেননি বলেই, পুণের ভাইস-প্রিন্সিপলের চাকরি ছেড়ে যে-ছবির জন্য কলকাতায় ফিরে এলেন, সেটি— ‘বগলার বঙ্গদর্শন’ (১৯৬৪)। শেষমেশ সে-ছবিটির প্রযোজকই পাওয়া গেল না। পরবর্তী ছবি ‘রঙের গোলাম’ (১৯৬৮)— সেখানেও মাঝপথে প্রযোজক উধাও।
অথচ, জীবনের এক পর্যায় থেকে আরেক পর্যায়ে, যে-কোনও একটি স্থানে আপোস করে নিতে পারলে, হয়তো তাঁর যাবতীয় সংকট মুছে যেত। কিন্তু ভেতরে যে বহ্নিমান আগুন, তার প্রকাশ এতটা প্রবল হয়ে উঠত কি? জীবনভর বাকতাল্লা মেরে কিম্বা ইমোশনাল সারচার্জের গুলি খাইয়ে তো আর একটা কনটেক্সট-কে শত বছর পরেও প্রসঙ্গক্রমে টিকিয়ে রাখা যায় না। অন্তত: আজকের বাস্তবতার নিরিখে ভেতরে কিছু সারবস্তু আছে বলেই, ঋত্বিক-প্রসঙ্গ এখনও জমছে।
‘নাগরিক’ (১৯৫২-৫৩) ছবিতে মূল প্রোটাগনিস্ট রামু যখন তার আত্মোপলব্ধির মধ্যে দিয়ে বলতে শুরু করে, ‘অনেক বছর পরে, মা; আমার চুলগুলো পেকে যাবে। কুয়োর মতো বাড়িটার ইতিহাস মনে পড়বে। এই দিনরাত্রির কথা মনে পড়বে। হাসব, গল্প গুছিয়ে বলব। বলব, কষ্ট অনেক পেয়েছি, কিন্তু ওপরে ঠেলে ওঠার ইচ্ছেটা কোনওদিন যায়নি। দিন বদল হবে। আবার আমরা বড় বাড়িতে উঠে যাব। এইভাবেই জীবন কাটবে তা আমি মানি না। আমার যত ইচ্ছে আছে, তার অর্ধেকটা— তাতেই অবস্থা বদলে যাবে।’ কথাগুলো যেন ঋত্বিকের শৃঙ্খলাহীন জীবনের অব্যক্ত ইচ্ছাশক্তিকে সাক্ষরিত করে তোলে। যদিও এখানে ব্যক্তি-ইচ্ছার থেকেও সার্বিক-ইচ্ছা ও অস্তিত্বের উপরেই তাঁর যাবতীয় সমীক্ষা। তবু নিজের জীবন সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা ও আত্মবিশ্বাস প্রথম থেকেই তাঁর ছিল। নয়তো, যুবক বয়সেই ‘অয়নান্ত’ (১৯৪৭) গল্পে তিনি কেন লিখবেন – ‘আমার বাইরের রহস্যটা জানতে হলেও তো আগে চাই নিজের সম্বন্ধে পুর্ণ জ্ঞান।’
আমাদের বিড়ম্বনা এই যে, আমরা তাঁকে পাগল সাজিয়ে পাগলাগারদে টেনে নিয়ে গেছি। যে মানুষটা (‘নাগরিক’-এর কথা যদি ছেড়েই দিই) মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে ‘অযান্ত্রিক’ (৫৮) থেকে শুরু করে ‘বাড়ী থেকে পালিয়ে’ (৫৯), ‘মেঘে ঢাকা তারা’ (৬০), ‘কোমলগান্ধার’ (৬১), ‘সুবর্ণরেখা’ (৬২) পাঁচ পাঁচটা আনপ্যারালাল ছবি দিয়ে ভারতীয় তথা বিশ্ব চলচ্চিত্রের নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করছেন, তাঁকে পাগল সাজানোর দরকার ছিল বৈকি! ভীষণভাবেই দরকার ছিল। দারিদ্র আর নীতিহীনতা যেখানে আমাদের নিত্যসঙ্গী, যেখানে কালোবাজারি আর অসৎ রাজনীতিবিদদের রাজত্ব, যেখানে বিভীষিকা আর দুঃখ, মানুষের একমাত্র নিয়তি— সেখানে নিজেকে ক্ষয় করে, বাঙালি অস্তিত্ব, বাঙালির জরাজীর্ণ অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তুলতে চাওয়া, পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কী!
নবারুণ ভট্টাচার্য একদিন কাঁদতে-কাঁদতে বলেছিলেন, ‘আমি সকাল, দিবস, রাত একজন বুদ্ধকে দেখেছি।’ বুদ্ধ মানে তো সেই— যে দুঃখশূন্য এক জগতের স্বপ্ন দেখছেন । যিনি জন্মের সংস্কারসমূহ ক্ষয় করে, প্রকৃতির শাশ্বত সত্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছেন। যিনি জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খলা থেকে মুক্ত হয়ে, নির্বাণ বা বোধি লাভ করেছেন। এখন ঋত্বিক এই সত্যে কতখানি পৌঁছতে পেরেছেন, তা তাত্ত্বিকরা ভাবুন। আমরা ‘অযান্ত্রিক’ দেখেছি, সেখানে জগদ্দলের উপর আরোপিত প্রতীত্যসমুৎপাদ— The theory of conditional existence of things-এর অসাধ্য সাধন ঘটিয়েছেন। একটি সেকেলে জরাজীর্ণ বস্তু, যার ভেতরে মানবিক সত্তা প্রয়োগ করে, প্রথমেই নিহিলিস্টদের হাত থেকে গাড়িটিকে কেড়ে নিয়েছেন; তাকে ভেঙে টুকরো-টুকরো করে লস্করওয়ালার হাতে তুলে দিয়েছেন।
বুদ্ধের মতবাদ অনুসারে, এটি শাশ্বতবাদ ও উচ্ছেদবাদের মধ্যবর্তী পথ। যে-পথে জগদ্দলের কম্পোজিট এনটিটিকে ভেঙে, তাকে নির্বাণের দিকে ঠেলে দেওয়া হল, যাতে তার দুঃখের অবসান ঘটানো যেতে পারে। ছবিতে সেই ফলশ্রুতিই তুলে ধরা হল। শুধু রয়ে গেল পরিত্যক্ত ভেঁপুটি, সেটিকে তুলে দেওয়া হল এক শিশুপ্রতিম মানবের হাতে। কারণ ওই ভেঁপুটি আসলে জগদ্দলের প্রাণশক্তি, আত্মা— দ্য স্ট্রীম অব কনশাসনেস ।

ঋত্বিক এখানে পুনর্জন্মবাদকে স্বীকৃতি না দিলেও, জীবনের যে প্রবহমান নীতি, তা একপ্রকার অবিকৃতই রেখেছেন। কারণ তার উৎপত্তি কোনও ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পৃথক কণা থেকে নয়, এ এক পারমার্থিক সত্য, যা অদ্বৈত মতে নাম, রূপ, স্থান ও কালের অতীত। এই সব দর্শন ও তার ইলাস্ট্রেশন ঋত্বিক তাঁর প্রতিটি ছবিতে একাধিকবার প্রয়োগ করেছেন। এমনকী, হাস্য-কৌতুকভরা ‘বাড়ী থেকে পালিয়ে’ ছবিতেও।
কাঞ্চন যখন জানতে পারে মাসি মারা গেছে, সে এসে বসে একটি বিলের ধারে, যেখানে অসংখ্য পরিযায়ী পাখি এসে আশ্রয় নিয়েছে। তারই মাঝে একটি শ্বেত রাজমরালের ছবি তুলে ধরা হয়। মরালটি ভাসছে, সাব-কনসাস তরঙ্গমালার উপর। এক নির্বাণ শাশ্বত রূপ। এটুকুই নিত্য আর সবই বিলের পরিযায়ী পাখির মতন আসবে, ফিরে যাবে। বিলের অদ্বৈতরূপ চেতনার গভীরে, চির প্রবহমান ধারায় বয়ে চলবে। সে-কথাই হরিদাস কাঞ্চনকে বলছে— ‘এই হচ্ছে আমার দাড়ি, এই হচ্ছে আমার ঝোলা। নাও। অর্থাৎ তোমার সঞ্চয়, জীবনের রোজগার। এই নিয়ে তুমি নতুন দেশ খুঁজতে বের হবে আর আমি ওই বিল। ‘তোর মতো কত পাখি আসবে— বসবে, আবার চলে যাবে। আমি বুক পেতে থাকব।’ জীবনের নিত্যতা এবং অনিত্যতা এই দু’য়ের মাঝে যে স্ব-উজ্জ্বল চেতনা, সর্বোচ্চ বাস্তবতা, তাই-ই ব্রহ্ম, তাই-ই আত্মা। এগুলোই ঋত্বিক বয়ে নিয়ে গেছেন দুর্ণিবার স্রোতের মতন। নিজেকে বারবার ভেঙেচুরে , বিনির্মাণ করে গড়ে তুলেছেন এক শৃঙ্খলাহীন ঋত্বিকে।


অনেকেই হয়তো ১৯৬৫ সালে তাঁর তত্ত্বাবধানে নির্মিত ‘রাঁদেভু’ তথ্যচিত্রটি দেখেননি, দেখলে বুঝবেন, তাঁর ভেতরকার দর্শন ও আত্মবীক্ষণ কতখানি গভীরে প্রোথিত। আবার কোথাও চিন্তাসূত্রের গভীরতা এতখানি গভীর, যার তল পাওয়া মুস্কিল।
মনে হয়, সবই আদতে বায়ুভূত। কিন্তু না, ঠিক তখনই এক-একজন মহাকাল রূপী ‘চৈতন্য’ (কো-ইন্সিডেন্স) এসে হাজির হবে। তার ভয়াল জিভ খুলে, বাস্তবের সরলীকৃত অবস্থাটিকে পুনর্স্থাপিত করে বলে যাবে— ‘ভয় দেখাই নাই, দিদিমণি সামনে পড়ে গিয়েছিল।’ বা এমন কোনও বেখাপ্পা লো-অ্যাঙ্গেল ফ্রেম, যেখানে বিলো দ্য আই লাইনে পূর্ববর্তী ভিজ্যুয়ালস ভেঙে দিয়ে, অনুজার মহীরুহ-সমান জীবন ছায়া থেকে বেরিয়ে আসাকে, নিজের পলায়নবৃত্তিকে, সুমহান করে তোলার চেষ্টা করে বলে যাবে— ‘আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি। যদিও এ-বাড়ির আমি ফালতু। তবুও, আমি সহ্য করতে পারলাম না। আমি পোর্টেস্ট করে গেলাম। তোরা মুখ বুজে সহ্য কর। পিষে মর।’ মুহূর্তে ফুটে ওঠে নিঃস্ব এক অন্ধকারময় রাতের প্রান্ত দৃশ্য — ‘যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে।’ আদতে ভাঙল আপামর বাংলা ও বাঙালির দুর্ভেদ্য প্রাচীরগুলো। এই হেমন্তের মধ্যরাতে, সকাতর কোলাহল ও করুণ পায়ের শব্দে-শব্দে, মানুষ ঊর্ধ্বশ্বাসে বেরিয়ে গেল দিগন্তে বিচ্ছুরিত বজ্রানলের দিকে। দীর্ঘ আশ্বিনের চাঁদ সীমান্তে ঝুলে রইল ঠান্ডা হয়ে।
এখানে ঋত্বিকের প্রশ্ন, ইতিহাসের সবচেয়ে বড় গণশত্রুদের দিকে নয়। প্রশ্ন, বিপন্ন এক জাতির দিকে, তাদের আত্মসমীক্ষার প্রতি। সামান্য কিছু বাড়ন্ত আত্মসম্মানের ভয়ে আমরা ঈশ্বর কিম্বা শঙ্করের মতন পালিয়ে এলাম মহানগরের কুয়োতলায়। উচ্চকিত জীবনের মোহে। নাকি, পাতালে সূর্যালোক পৌঁছে যাবে! আহা, ভাল থাকার কী প্রবল বাসনা! তা সে আত্মবাসনার যথাযথ সার্থসিদ্ধি হল কি? ভাল থাকার মতন সুরক্ষিত দেওয়াল গড়ে তোলা গেল? এর উত্তর— আজ পরিত্যক্ত কুয়োতলাগুলো থেকে পাওয়া যাবে হয়তো…
নীতার এসব বাসনা ছিল না। সে মুক্ত, সে ধরিত্রী, আদি-অন্তহীন ক্রন্দসী। তাঁর শূন্য প্রান্তরের পাশে কোনও বলয় নেই। পৃথিবীর অগণিত সনৎ, ভৃগু— আজকের ঘুঘু ফিঙে নীলকন্ঠ পাখি। নীতা ইউনিভারসাল সাইকি। ইতিহাসবহনের পথে সত্ত্বরজস্তমসাংসাম্যবস্থা প্রকৃতি। নীতা এই ত্রিগুণাত্মিক প্রকৃতিরই নিত্যরূপ যার উৎপত্তি বিনাশরহিত। তাই শুরুতেই, প্রথম দৃশ্যে দেখানো হচ্ছে, তমসাচ্ছন্ন তরঙ্গে, ঝিলমিল দুলতে থাকা তারার চূর্ণ আবলী। যেন এক পরাবাস্তব চেতনার রূপ। ক্রমে আলো ফুটে উঠছে। আলো এবং অন্ধকার; বাস্তব এবং পরাবাস্তব; রিয়েল এবং সাররিয়েল— এই দু’য়ের মধ্যে সংযোগ গড়ে তুলছে একটি অপার্থিব রাগ, রাগ হংসধ্বনি। সঙ্গে জুড়ে যাচ্ছে কিছু কসমোসেন্ট্রিক সাউন্ড, ভোরের কলকাকলি। লং শটে দেখানো হচ্ছে বিরাট এক বৃক্ষতলের নীচ থেকে নীতা উঠে আসছে। যেন অযোনিসম্ভূতা সেই প্রকৃতি— অকারণবশত এগিয়ে আসছে অনিত্যতার দিকে। যাকে আশ্রয় করে জগতের যত নাগপাশ দুঃখ বিষাদ। অথচ সে নিজে অব্যক্ত ও অনাশ্রিত।
দ্বিতীয় দৃশ্য, ডীপ-ফোকাসে নীতার মুখ। দূরে স্প্লিট ফীল্ডে হেমন্তের কুয়াশামদির একটা ঝিল, চারপাশে জমে ওঠা কচুরিপানা তারই কিনারে বসে শঙ্কর, রাগ সাধনায় মগ্ন। কণ্ঠে মিশে যাচ্ছে ওপার থেকে ছুটে আসা রেলের ছেঁড়া-ছেঁড়া শব্দ, সরালির ডাক — দ্য কলস অব সোয়ান। এই লার্জ-স্কেলটিকে ঋত্বিক তুলে ধরছেন মাত্র দু’টি শটে। কেবলমাত্র ক্যামেরার গতি বাড়িয়ে-কমিয়ে এবং শব্দের আলংকারিক দ্যোতনা (ডিজাইন বাই ইনফারেন্স) ব্যবহার করে।
আবার কোথাও চিন্তাসূত্রের গভীরতা এতখানি গভীর, যার তল পাওয়া মুস্কিল। মনে হয় সবই ওই আদতে বায়ুভূত। কিন্তু না, ঠিক তখনই এক-একজন মহাকাল রূপী চৈতন্য (কো-ইন্সিডেন্স) এসে হাজির হবে। তার ভয়াল জিভ খুলে বাস্তবের সরলীকৃত অবস্থাটিকে পুনর্স্থাপিত করে বলে যাবে — ‘ভয় দেখাই নাই, দিদিমণি সামনে পড়ে গিয়েছিল।’
শব্দের প্রসঙ্গে আরেকটি দৃশ্যের কথা না বললেই নয়, বালি হাসপাতালের সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসা নীতার সেই বিধ্বস্ত দৃশ্যটির কথা। একটি মেয়ে, যার চূড়ান্ত দুঃখের মুহূর্তে, তার ভেতরের যত পিষে যাওয়া অব্যক্ত-যন্ত্রণা কেবলমাত্র চাবুকের আঘাতে-আঘাতে ফুটিয়ে তুলেছে নীতার চোখে-মুখে।
এমন অসংখ্য অনন্যতা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তাঁর ছবিগুলোতে। প্রথম, ‘নাগরিক’-এর ড্রাম পেটানোর দৃশ্য থেকে— শেষ, ‘তিতাস’এর ধানক্ষেতে ছুটে যাওয়া বাচ্চাছেলেটির— কোমরের ঘুনসি পর্যন্ত শব্দ-গতি-মন্তাজের এক ঋত্বিকময় ভুবন।


‘মেঘে ঢাকা তারা’-য় নীতাকে, যদি প্রকৃতি অর্থাৎ দ্য লাভিং মাদার হিসেবে ধরে নেওয়া হয়, তবে তার বিপ্রতীপ আদল হিসাবে নির্মাণ করেছেন ‘তিতাস একটি নদীর নাম’। ছবিতে বাসন্তীর চরিত্রটিকে — দ্য টেরিবল মাদার অর্থাৎ প্যারাডক্সিক্যাল কালী। অনার্য এক কালকুণ্ডলিনী। সে শুধু অজ্ঞতা ও অন্ধকারের প্রতিরূপ নয় বরং অসীম মাহাজাগতিক শক্তি ও শক্তিময়তার প্রকাশ। যার পায়ের নীচে এসে ভেঙে পড়ে, চেতন-অচেতন জগতের যাবতীয় তরঙ্গ।
সভ্যতা ভাঙছে, নব্য সভ্যতা গড়ে উঠছে, নদী মরছে, চর ডুবছে, অন্যত্র চর জাগছে। বিশ্ব চরাচরের এই ভয়াবহ ধ্বংসলীলার মাঝে, সত্যের এবং শক্তির একমাত্র প্রতীক হিসেবে স্থায়ী হয় বাসন্তীর চরিত্রটি। তার ক্ষয় আছে, বিনাশ নেই। শেষ দৃশ্যে সেই অবিনাশী শাশ্বত চিত্রটিই তুলে ধরেছেন, ওয়াইড অ্যাঙ্গেলে।
তিতাসের জল শুকিয়ে গেছে, সে মরতে বসেছে। তিতাস অবলম্বিত মানুষের অহংকারের অবসান ঘটছে। রুগ্ন, মরা নদী— জীবনের অন্তিম শ্বাস ফেলছে (এখানেও ব্যবহার হয়েছে— শব্দের ডিজাইন বাই ইনফেরেন্স) বাসন্তীর শরীরে। ধ্বংসের এক অনিবার্য রূপ। তিতাস এখানেই শেষ হতে পারত (অন্ততঃ অদ্বৈত মল্লবর্মনের আখ্যান অনুযায়ী)। কিন্তু ঋত্বিক খুব ভাল করেই জানতেন, জীবন কখনও অবক্ষয়ের মধ্যে দিয়ে সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হয় না। তার একটা বহমান তরঙ্গ থাকে। সময়ের এই কালচক্রকে প্রতিস্থাপন করবার জন্য দেখানো হয়েছে আরেকটি দৃশ্য। ভরা ফসলের ক্ষেত পেরিয়ে, বাঁশি হাতে ছুটে আসছে একটি শিশুপ্রতিম দৃশ্য অর্থাৎ— নতুন জীবনের সূচনার ইঙ্গিত।


এই যাবতীয় দর্শন-আদল-আর্কেটেইপ সহ ঋত্বিকও লুটিয়ে পড়লেন তিতাসের শুকনো বালির চরে। আর একদল মানুষ অক্লান্ত প্রচেষ্টায় রটিয়ে গেলেন ঋত্বিক ঘটক একজন অবক্ষয়ের শিল্পী। কিন্তু যা উত্তরঙ্গ স্রোত, তা কোনও নুড়ি পাথরের বাধায় থেমে যায় না, বরং আরও বিধ্বংসী ও সম্ভয়াবনায় প্রবাহে বয়ে যেতে থাকে। ঋত্বিকও বয়ে চলেছেন। চেতনার পথে অনন্ত স্রোতোগামী এক নদী। তাঁর শেষ কথা – ‘জীবন-জীবিতের বহতা অমোঘ— দুর্নিবার।’