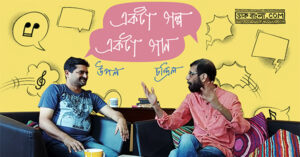সাহিত্য-পুরাণের ইতিহাসে বিশ্বকর্মা এক শ্রেণির কাছে প্রতারক। মনসার প্ররোচনায় লোহার বাসর-ঘরে একটা সামান্য ছিদ্র— উথাল-পাতাল করে দিল মনসামঙ্গলের পুথি। আজীবন দোষের ভাগীদার হলেন বিশ্বকর্মা। ভেলা ভেসে চলল গাঙুরের উজান বেয়ে। তাঁরই বানানো শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাও ডুবল এক সময়ে। আকাশে কি তখন ঘুড়ি উড়ছিল? কেউ কি চিৎকার করেছিল ‘ভোকাট্টা’?
মানুষের ওড়ার শখ বহুদিনের। এরোপ্লেন আকাশে ওড়ানোর আগে নাকি ঘুড়ি উড়িয়েছিল মানুষ। পাখিদের বিস্তীর্ণ ডানা, তার পাশে উড়ে চলছে ‘পেটকাটি’, ‘চাঁদিয়াল’, ‘মোমবাতি’, ‘বগ্গা’! এক সময়ে এই ঘুড়ি মানুষকেও উড়িয়েছে। বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বিপক্ষের সেনা-শিবিরে নজরদারিতেও ব্যবহার করা হয়েছিল ঘুড়ি। একবার উড়তে পারলে, ওড়াতে পারলে, কত কী-ই না হাতের মুঠোয় চলে আসে!
চিনে প্রথম ঘুড়ি তৈরি হয়। মানুষ স্বপ্ন দেখেছিল, বাতাসের থেকে ভারী কিছু যদি আকাশে ওড়ানো যায়। সে-ঘুড়ি ছিল কাঠের। সেখান থেকে কাগজ হয়ে আজকের প্লাস্টিকের ঘুড়ি। কয়েকশো বছরের ইতিহাস। কিন্তু আজ কি আগের মতো আকাশে এত ঘুড়ি ওড়ে? এক সময়ে ঘুড়ি কিন্তু শুধু খেলাই নয়, ছিল নানা বিশ্বাস-ব্যঞ্জনার প্রতীক। ধরা যাক, চিনের ড্রাগন ঘুড়ির কথা। ড্রাগন হয়তো কাল্পনিক, কিন্তু এই ড্রাগনকে চিনারা এমনভাবে কল্পনা করল, যেন উড়ন্ত এক দর্শন। ড্রাগনের শিং আঁকা হল প্রাণোচ্ছল হরিণের মতো। দাড়ি মানুষের মতো— যা, বুদ্ধি, বিবেচনা শৌর্যের প্রতীক। কীরকম যেন মহাভারতে রথের এক-একটা অংশের প্রতীক-বর্ণনার সঙ্গে মিলে যায়।
সন্ধ্যা নামে, শরতের আগেই ভাদ্র-দুপুরে সুতোয় মাঞ্জা দেওয়ার তোড়জোড় শুরু হয়। ভাঙা টিউবলাইট, কাচের টুকরো, সাবু— হামান দিস্তায় ঠুং-ঠুং আওয়াজ সারা দিনরাত। কার সুতোর ধার কত বেশি। একের পর এক গাছ, মাঠে গোলপোস্ট-এর বার জড়িয়ে গেল সুতো শুকোতে দেওয়ার ধুমে। যারা মাঞ্জা দিতে পারল না, যাদের হাতের আঙুল কেটে যাওয়ার ভয় শালুকপাতা থেকে জল ঝরে যাওয়ার মতো পিছল, তারা সন্ধের লন্ঠন-আলোয় জড়িয়ে ধরল দিদা-ঠাকুমার সাদা কাপড়ের আঁচল। যদি সেলাই করার সুতো থেকে খানিকটা পাওয়া যায়! লাটাই নেই, একটা কাঠির চারপাশে জড়িয়ে রইল একটা মুঠোর মতো সুতো। সে-ঘুড়ি সুতোর ভারে আকাশে উড়বে না, তবুও তো সারা-মাঠ ছুটে বেড়ানো, অত দূরে না হলেও, মাটি থেকে তো উড়ল খানিক! তা-ই আনন্দ।
প্রতি উদ্যাপনের সঙ্গে মিলেমিশে যায় কিছু শব্দ। যেমন ঘুড়ির সঙ্গে যুদ্ধবাজ, গোত্তা, লাট— এ-ধরনের শব্দবন্ধ। ভাবা যায়! ঘুড়ির নাম একইসঙ্গে ‘ময়ূরপঙ্খী’ আর ‘মুখপোড়া’। সাধারণত ভারতে যে-ঘুড়িগুলি দেখা যায়, সেগুলি ভারতীয় যুদ্ধবাজ; একইসঙ্গে জাপানের ক্ষেত্রে জাপানি যুদ্ধবাজ, কোরিয়া-র ক্ষেত্রে কোরিয়ান যুদ্ধবাজ। ঘুড়ির এহেন যুদ্ধবাজ বিশেষণ ঘুড়ির বাঁক নেওয়া, হাওয়ার সঙ্গে যুঝে নেওয়া, গোত্তা খাওয়ার বৈশিষ্ট্যর জন্য। ঘুড়ির সঙ্গে এভাবে যুদ্ধ জড়ালেও ঘুড়ি কিছু জায়গায় শান্তি-স্মৃতির চিহ্ন।
অনেকে বলে বিশ্বকর্মা পুজো আসলে শ্রমিক শ্রেণির পুজো। দিন কিংবা রাতের বেলা মদ খেয়ে উদ্দাম নাচ, হিন্দি কিংবা বাংলা লাড়েলাপ্পা গানের সঙ্গে পায়ের তাল। একটা রাত যেন এই শ্রেণির কাছে নিজের মতো করে বেঁচে নেওয়ার রাত, যেখানে পুঁজির দাপট নেই, নেই সুশীল সাজতে চাওয়ার মেকি ভড়ং! আছে মুক্তির স্বপ্ন। স্মৃতির ভোকাট্টা পেরিয়ে স্পর্ধা-ঘুড়ির উড়ান।
অবিভক্ত ভারত, পঞ্জাবে, অধুনা পাকিস্তানে এক প্রকার ঘুড়ি উড়ত এবং এখনও ওড়ে, যার নাম ‘তুক্কল’। একটু বড় মাপের ঘুড়ি, সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয় লেজাকৃতি এক অংশ। কথায় বলে, যে ‘তুক্কল’ ওড়াতে পারে, সে সব ধরনের ঘুড়ি ওড়াতে পারে। এই লেজাকৃতি অংশের সঙ্গে প্রদীপ বেঁধে, সন্ধ্যায় উড়িয়ে দেওয়ার হয় আকাশে। আজও, এখনও। দু-দেশের মাঝে সীমান্ত-কাঁটাতার বসলেও ঘুড়ির উড়ান মিলিয়ে দেয় সংস্কৃতি। কেন কে জানে, যে-শব্দের মধ্যে একটা দার্শনিক বিস্তার বা ব্যঞ্জনা আছে, তা কখনও কোনও বাধাবিপত্তি মানে না। সে ‘সুরের দেশভাগ হয় না’-র মতো ভাবনাই হোক কিংবা আকাশে ‘তুক্কল’ ঘুড়ির উড়ান। শুধু পঞ্জাব-পাকিস্তান প্রদেশের ‘তুক্কল’-ই নয়। ঘুড়ির সঙ্গে জড়িয়ে ‘ঢাউস’ নামের ঘুড়ির সংস্কৃতিও। মূলত, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের মানুষরা এ-ধরনের ঘুড়ি বানিয়ে থাকেন। যদিও এখন ‘ঢাউস’ নানা জায়গায় ছড়িয়ে গেছে। মকর-সংক্রান্তি কিংবা বিশ্বকর্মা পুজোর দিন সীমান্তের কাছে ঢাউস ওড়ানো হয় ফেলে আসা দেশ, স্মৃতির তর্পণ হিসেবে। জল-ই শুধু পূর্বপুরুষের স্মৃতিতে ভেসে যায় না। পূর্বপুরুষ, ফেলে আসা ভিটে-মাটিকে আকাশের উঠোনে ধরে রাখে ঢাউসের মতো ঘুড়িও।
বলা হয়, কলকাতায় প্রথম ঘুড়ি আসে লখনউ-এর নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ্-র হাত ধরে। কলকাতায় নির্বাসনের পর নবাবের রুচিতেই যেমন শহর বিরিয়ানির স্বাদ পেয়েছিল, তেমনি নবাবের অবসর যাপনের অঙ্গ হিসেবে কলকাতার আকাশে উড়ল ঘুড়ি। তবে এই ঘুড়ি কিন্তু প্রথমে গরিব বা মধ্যবিত্ত কারও নাগালেই ছিল না। নবাবের পর বিভিন্ন রাজা-জমিদাররা নিজেদের মধ্যে ঘুড়ি ওড়াতে শুরু করেন। মাটিতে অস্ত্রের লড়াই তো খাতায়-কলমে ঘুচে গেছিল। শুরু হল আকাশে ঘুড়ির লড়াই। উনিশ শতকে কলকাতার আকাশ ঘুড়িতে ছেয়েছিল বাবুদের শখ-আহ্লাদের জন্যই। বাবুদের ঘুড়ির লেজ তৈরি হত বড়-বড় অঙ্কের নোট দিয়ে। একজনের ঘুড়ি কাটলেই যে ‘ভোকাট্টা’ রব ওঠে, সেই ‘ভোকাট্টা’ রবের সূচনা এখান থেকেই। ‘ভোকাট্টা’ মূলত সে-সময় থেকেই ক্ষমতার প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত হত। মজার ব্যাপার, ঘুড়ি কাটলেই-বা কী! ঘুড়ির লেজ কত বেশি পরিমাণ টাকা দিয়ে বানানো হবে, সে-নিয়ে প্রতিযোগিতা চলত। ফলত ঘুড়ি কাটলেও বিশেষ দুঃখ নেই, হাওয়ায় তো টাকা ওড়াচ্ছেন বাবু! সে-ও তো একপ্রকার ক্ষমতারই প্রতিফলন। মজার ব্যাপার এই বাবুদের ভাড়া করা ঘুড়িয়াল থাকত। ঘুড়ি মূলত তাঁরাই ওড়াতেন। বাবুরা মাঝে-মধ্যে শুধু লাটাই ধরতেন। তবু একবার অন্যের ঘুড়ি কাটলেই জয়।
কলকাতার ক্লাব-সংস্কৃতির যে-ইতিহাস, তার সঙ্গেও জড়িয়ে ঘুড়ি ওড়ানো। আগে নানা মানুষ বাড়ির ছাদ ব্যতিরেকে ময়দানে ঘুড়ি ওড়াতেন। ময়দানে যাঁরা ঘুড়ি ওড়াতেন, তাঁদেরই কয়েকজনের উদ্যোগে— ১৯৫৪ সালে কলকাতার ৩ নং জেলেপাড়ায় জন্ম নেয় ‘ওয়েস্ট বেঙ্গল কাইট অ্যাসোসিয়েশন’। সংগঠনের সভাপতি ও মূল হোতা পতিতপাবন দত্ত। এই সংগঠনের উদ্যোগেই কলকাতায় ঘুড়ি ওড়ানোর প্রতিযোগিতা একটা প্রতিষ্ঠানিক রূপ নেয়। এর আগে ঘুড়ি মূলত উনিশ শতকে বাবুদের বাড়ির ছাদেই ওড়ানো হত। ঘুড়ি ওড়ানোর প্রাতিষ্ঠানিক রূপ বা এই সংক্রান্ত ক্লাব বিশ শতক থেকেই শুরু হল বলা যেতে পারে। ধর্মতলা কাইট ক্লাব, বউবাজার কাইট ক্লাব, এন্টালি কাইট ক্লাব, সেন্ট্রাল কাইট ক্লাব— এরকম ক্লাবের তখন ছড়াছড়ি। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল যেমন দুই যুযুধান প্রতিপক্ষ, তেমনই ঘুড়ির ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ ছিল ধর্মতলা আর সেন্ট্রাল কাইট ক্লাব। ১৯৯১-তে কলকাতাতেই অল ইন্ডিয়া কাইট কম্পিটিশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
গোটা নয়ের দশক, একুশ শতকের প্রথম ভাগ দেখেছিল— সারা আকাশে ছড়িয়ে আছে ঘুড়ির ঝাঁক! যারা তেমন ঘুড়ি ওড়াতে পারত না, তারা হাতের ঢিলে একটা সুতো বেঁধে ছুটে বেড়াত এ-পাড়া থেকে ও-পাড়া। কয়েক বছর হল তাও দেখা যায় না। তাহলে কি ঘুড়ি ওড়ানো কমে যাচ্ছে ধীরে-ধীরে? আকাশের রঙিন ঘুড়ির ঝাঁক, ‘ভোকাট্টা’ ডাক, কোনওটাই আর তেমন বিকেল হলে শোনা যায় না। শহরে তো নয়-ই, মফস্সলেও নয়। মুক্তির ঘুড়ি খবর পাঠায় কাকে? অনেকে বলে বিশ্বকর্মা পুজো আসলে শ্রমিক শ্রেণির পুজো। দিন কিংবা রাতের বেলা মদ খেয়ে উদ্দাম নাচ, হিন্দি কিংবা বাংলা লাড়েলাপ্পা গানের সঙ্গে পায়ের তাল। একটা রাত যেন এই শ্রেণির কাছে নিজের মতো করে বেঁচে নেওয়ার রাত, যেখানে পুঁজির দাপট নেই, নেই সুশীল সাজতে চাওয়ার মেকি ভড়ং! আছে মুক্তির স্বপ্ন। স্মৃতির ভোকাট্টা পেরিয়ে স্পর্ধা-ঘুড়ির উড়ান।