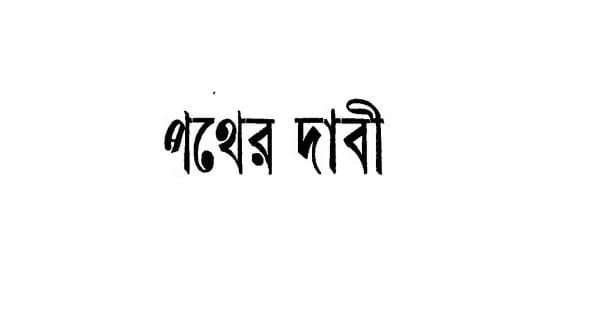সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত। বইয়ের আখ্যাপত্রে এই শব্দগুলো কিংবা এই মর্মে কপিরাইট-ঘোষণা আকছার দেখা যায়। কিন্তু পত্রিকার ধারাবাহিক উপন্যাসের প্রতিটি কিস্তির শিরোনামে তারকাচিহ্ন দিয়ে ফুটনোটে এমন ঘোষণা করতে হয় যখন, তখন বোঝা যায় সে-উপন্যাসের জনপ্রিয়তা। সে-উপন্যাস পত্রিকায় শেষ হলেই, প্রকাশকেরা ঝাঁপিয়ে পড়বেন বই করতে। এমন সম্ভাবনা না থাকলে, অমন ঘোষণার দরকারই বা কী!
ঘোষণাটা থাকত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘পথের দাবী’-র কিস্তিতে, ‘বঙ্গবাণী’ পত্রিকায়। মাসিক পত্রিকায় ১৩২৯ সালের ফাল্গুন মাস থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে শুরু হয় এবং শেষ হয় ১৩৩৩ সালের বৈশাখ সংখ্যায়। ‘বঙ্গবাণী’ পত্রিকাটি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে তাঁর পুত্রদের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হত।
আরও পড়ুন: খাদ্য আন্দোলনের ইতিহাস আড়াল করেছে মধ্যবিত্ত-ই? লিখছেন সম্প্রীতি চক্রবর্তী…
১৩২৯-এর ফাল্গুন, মানে ১৯২৩। বছর দু’য়েক আগেই মহাত্মা গান্ধীর ডাকে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়েছিল দেশে। সে আন্দোলন প্রত্যাহার করেছেন গান্ধী আগের বছর ১৯২২-এ চৌরিচৌরার হিংসার ঘটনায়। সেই বান-ডাকা দিনে, সব্যসাচীর বিপ্লবের স্বপ্ন অন্তত অর্ধেক বঙ্গের মনের কথা তো ছিলই। তাই জনপ্রিয়তা এমন স্তরে পৌঁছেছিল যে, গোপালচন্দ্র রায়ের কাছে উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতি বলছে, ‘ঐ সময় একখানা বই বহুগুণ দাম দিয়ে ১০০ টাকাতেও বিক্রি হতে দেখেছি। আবার বই-এর অভাবে হাতে লেখা সম্পূর্ণ বইয়ের কপিও আমি লোকের হাতে হাতে ঘুরতে দেখেছি।’
দেখারই কথা। বাংলার মাটি, বাংলার মন তখন স্বাধীনতার স্বপ্নে উত্তাল। আর তার ভেতরে বিষম চলার প্রেরণা জুগিয়ে যাচ্ছে যে ‘পথের দাবী’, তাকে বাজেয়াপ্ত করে কতটুকু রোখা যায়। ১৩৩৩ সালের ১৬ ভাদ্র, ৩১ আগস্ট ১৯২৬ প্রথম বই হয়ে প্রকাশ পেল ‘পথের দাবী’। প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে একদিনের মধ্যেই সমস্ত বই কলকাতা ও কলকাতার বাইরে দোকানে দোকানে দিয়ে দেওয়া হয়, যাতে সব বই পুলিশ বাজেয়াপ্ত করতে না পারে। প্রথম সংস্করণের হাজার কপি শেষ হয়ে গেল নিমেষে।
প্রকাশক ছিলেন উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। আরও বেশ কয়েকজন প্রকাশক এগিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু পুলিশের ভয়ে পিছিয়ে যান। ‘বঙ্গবাণী’তে ধারাবাহিক প্রকাশের সময়েই এমসি সরকার অ্যান্ড সন্স বই করতে চেয়ে অগ্রিম এক হাজার টাকা দিয়েছিলেন শরৎচন্দ্রকে। কিন্তু শেষে সরকারি জুলুমের ভয়ে সে বই ছাপতে আর রাজি হলেন না। পরে শরৎচন্দ্র ওই এক হাজার টাকার জন্য তাঁদের ‘ছেলেবেলার গল্প’ নামে একটি বই দিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের অন্যান্য অনেক বইয়ের প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ও বই ছাপতে সাহস করেননি। শেষে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের তৃতীয় পুত্র উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রকাশক হলেন। পুলিশের নজর এড়িয়ে বাংলার বিপ্লবীরা অবশ্য নাম-না-জানা প্রেস থেকে ‘পথের দাবী’ প্রকাশ করতে থাকেন এবং গোপনে তা বিক্রিও হতে থাকে।
উপন্যাস লেখার সময়েই শরৎচন্দ্র নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন, ‘পথের দাবী’ নিষিদ্ধ হবেই। সে-কথা পত্রিকার পরিচালকদের জানিয়েওছিলেন। ইন্দ্রমিত্র লিখছেন, ‘শরৎচন্দ্র সেসময়ে একদিন উমাপ্রসাদকে বললেন— যদি জেল হয়, কি করবে? উমাপ্রসাদ বললেন— ‘হলে তো আর একা প্রকাশকের হবে না, লেখকেরও হবে। দুজনে জেলে একসঙ্গে থাকব— আপনার সঙ্গে থাকা, সে তো মহা ভাগ্যের কথা।’ শরৎচন্দ্র গম্ভীরভাবে বললেন— ‘দেখো, আমার গড়গড়াটা যেন সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি।’
‘বঙ্গবাণী’তে ধারাবাহিক প্রকাশের সময়েই এমসি সরকার অ্যান্ড সন্স বই করতে চেয়ে অগ্রিম এক হাজার টাকা দিয়েছিলেন শরৎচন্দ্রকে। কিন্তু শেষে সরকারি জুলুমের ভয়ে সে বই ছাপতে আর রাজি হলেন না। পরে শরৎচন্দ্র ওই এক হাজার টাকার জন্য তাঁদের ‘ছেলেবেলার গল্প’ নামে একটি বই দিয়েছিলেন।
কিন্তু পত্রিকায় প্রকাশের সময়ে ইংরেজ সরকার বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখায়নি। বই বেরোলেই তাদের টনক নড়েছে। সে কালের সংবাদপত্র ‘আত্মশক্তি’, ১৯২৭-এর ১৪ জানুয়ারি লিখছে সে কথাটাই, “গত বুধবার সরকার এক ঘোষণাপত্রে জানাইয়াছেন শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত উপন্যাস পথের দাবীর প্রচার আজ হইতে বন্ধ হইল এবং উহা সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করা হইল। কারণ ঐ পুস্তক পাঠে ১২৪এ ধারায় বর্ণিত রাজদ্রোহ করিবার ইচ্ছা পাঠকের মনে জাগ্রত হইবার সম্ভাবনা আছে।… ‘পথের দাবী’ দুই বৎসরের অধিককাল হইল ‘বঙ্গবাণী’ পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু তখন উহা পাঠে রাজদ্রোহ হইবার সম্ভাবনা হয় নাই। তারপর আজ প্রায় পাঁচ মাস হইল উপন্যাসখানি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে— এতদিন ত রাজদ্রোহের সম্ভাবনা হয় নাই; আজ হঠাৎ পৌষের শীতার্ত, ঘন ঘটাচ্ছন্ন মলিন প্রভাতে চা পান করিতে করিতে ভারতে রাজদ্রোহ-সংরোধের একমাত্র কর্তা শ্রীলশ্রীযুক্ত লাটসাহেব চিন্তা করিয়া দেখিলেন ‘পথের দাবী’তে রাজদ্রোহের বীজ রহিয়াছে! বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত অহিফেন প্রসাদাৎ পৌষের প্রভাতে কেন, চৈত্রের নিশাশেষেও যদি এরূপ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতেন তাহা হইলে আপত্তির কথা ছিল না। কিন্তু সপারিষদ লাট সাহেব গৌরচন্দ্র আজ তিন বৎসর পর বহাল তবিয়তে থাকিয়াও যদি এরূপ দিবাস্বপ্ন দেখেন এবং লজ্জার মাথা খাইয়া যদি তাহা গেজেটে প্রকাশিত করিয়াও থাকেন— তাহা হইলে যত না ভাবিত হইতে হয় গৌরচন্দ্রের জন্য—তদপেক্ষা অধিক ভাবিতে হয় তাঁহার হস্ত পদ, কর্ণ চক্ষু সদৃশ গৌর-আমলক-কালমাণিকবর্ণচ্ছটাচ্ছন্ন তাঁহার কর্মচারীদের জন্য। বৎসরের পর বৎসর যাহাদের রাজদ্রোহের বীজ অনুসন্ধান করিতে হয়রান হইতে হয় তাহাদের উপরই নির্ভর করে বাঙলার শাসন ও প্রজাপালন! নমঃ গৌরচন্দ্রায়!”
রবীন্দ্রনাথ অবশ্য পথের দাবীর প্রচার নিষিদ্ধ করার ব্রিটিশ আদেশের বিরুদ্ধে কিছু লিখতে রাজি হননি। শরৎচন্দ্রের অনুরোধের উত্তরে ১৯২৭-এর ১০ ফেব্রুয়ারি লিখেছিলেন, ‘তোমার পথের দাবী পড়া শেষ করেছি। বইখানি উত্তেজক। অর্থাৎ ইংরেজের শাসনের বিরুদ্ধে পাঠকের মনকে অপ্রসন্ন করে তোলে। লেখকের কর্তব্য হিসাবে সেটা দোষের না হতে পারে— কেন না লেখক যদি ইংরেজ-রাজকে গর্হণীয় মনে করেন তাহলে চুপ করে থাকতে পারেন না। কিন্তু চুপ করে না থাকার যে বিপদ আছে সেটুকু স্বীকার করাই চাই। ইংরেজ-রাজ ক্ষমা করবেন এই জোরের উপরেই ইংরেজ-রাজকে আমরা নিন্দা করব সেটাতে পৌরুষ নেই। আমি নানা দেশ ঘুরে এলেম— আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েচে তাতে এই দেখলেম একমাত্র ইংরেজ গভর্ণমেন্ট ছাড়া স্বদেশী বা বিদেশী প্রজার বাক্যে বা ব্যবহারে বিরুদ্ধতা আর কোনো গভর্ণমেন্টই এতটা ধৈর্য্যের সঙ্গে সহ্য করে না। নিজের জোরে নয় পরন্তু সেই পরের সহিষ্ণুতার জোরেই যদি আমরা বিদেশী রাজত্ব সম্বন্ধে যথেচ্ছ আচরণের সাহস দেখাতে চাই তবে সেটা পৌরুষের বিড়ম্বনামাত্র তাতে ইংরেজ রাজের প্রতিই শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয় নিজের প্রতি নয়। রাজশক্তির আছে গায়ের জোর, তার বিরুদ্ধে কর্তব্যের খাতিরে যদি দাঁড়াতেই হয় তাহলে অপর পক্ষে থাকা উচিত চারিত্রিক জোর—অর্থাৎ আঘাতের বিরুদ্ধে সহিষ্ণুতার জোর।’
এ চিঠি নিয়ে বিতর্ক হয়েছে বহু। বিতর্ক হয়েছে উপন্যাস হিসেবে ‘পথের দাবী’-র মান নিয়েও। বই প্রকাশের শতবর্ষে আজ পড়ল যে পথের দাবী তার শতায়ু জীবন এ ভাবেই জীবন্ত হয়ে আছে।