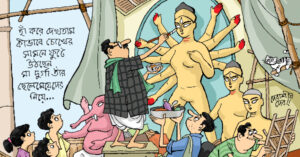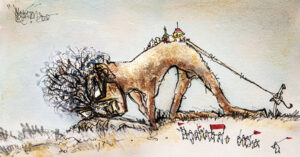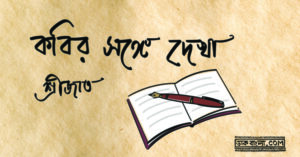অস্থিরতার রাজনীতি
‘নিউ পলিটিক্স অফ ইনস্টেবলিটি’। বলছেন পল স্তানিল্যান্ড নামে এক রাজনৈতিক তাত্ত্বিক। বিষয়, নেপাল। নেপালে সাম্প্রতিকে যা ঘটে গিয়েছে, তাকে সকলেই এককথায় চিহ্নিত করছেন ‘জেন-জি’ বিপ্লব বলে। জেন-জি কী, খায় না মাথায় দেয়, এ-কথা এখন কমবেশি অনেকেই জানেন। তাও, সংজ্ঞা দিতে গেলে বলতে হয়, নয়ের দশকের শেষভাগ থেকে ২০১০, অর্থাৎ কিনা একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত কালপর্বে যাদের জন্ম, তাদেরই এই নামে ডাকা হয়। নেপালের এই গণঅভ্যুত্থান নেপালের সাধারণ মানুষের জাগরণ ও লড়াই হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে না, চিহ্নিত হচ্ছে এই প্রজন্মের আন্দোলন হিসেবে। কেন?
৪ সেপ্টেম্বর নেপাল সরকার একটি নির্দেশিকা জারি করে। সেই নির্দেশে বলা হয়েছিল, ফেসবুক, এক্স (আগের টুইটার), ইউটিউব, রেডিট, স্ন্যাপচ্যাট-সহ ২৬টি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম নেপালে নিষিদ্ধ। কারণ খুবই সহজ, তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রকের নিয়মানুসারে এরা কেউই নথিভুক্ত হতে পারেনি। এর ঠিক পরপর নেপাল উত্তাল হয়ে ওঠে। তরুণ প্রজন্ম রাস্তায় নেমে পড়ে। পরিস্থিতি এমনদিকে যায়, ৯ তারিখ রাজা জ্ঞানেন্দ্র শাহ-কে আসরে নামতে হয়, দেশের পরিস্থিতি শান্ত রাখার আহ্বান জানাতে হয়। ওইদিনই প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা ওলি-র নেতৃত্বাধীন সরকার পদত্যাগ করে। নেপালের সংসদ জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যায় জনরোষের আগুনে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ঝালানাথ খানালের স্ত্রী রাজ্যলক্ষ্মী চিত্রকর অগ্নিদগ্ধ হন জীবন্ত অবস্থায়, তাঁদের বাসভবনে আগুন লেগে যাওয়ার ফলস্বরূপ। সমাজমাধ্যমে ভিডিও ভেসে আসে, অর্থমন্ত্রী হেলমেট পরা অবস্থায় নদীতে নেমে গণক্ষোভ থেকে বাঁচার চেষ্টা করতে গিয়েও ব্যর্থ হচ্ছেন। কোথাও আবার দেখা যায়, জ্বলন্ত সংসদের সামনে এক প্রতিবাদী নৃত্যরত।
উত্তমকুমারের চিঠি থেকে পোশাক, এই প্রদর্শনী চেনাল এক অন্য মহানায়ককে!
পড়ুন ‘চোখ-কান খোলা’ পর্ব ১৩…
কেবলই সমাজমাধ্যম নিষিদ্ধ হওয়ার দরুন এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল? না কি সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, প্রশাসনিক অপদার্থতা, জনগণের অর্থর অপব্যবহারের মতো একরাশ গম্ভীর, ‘সিরিয়াস’ প্রশ্নও জুড়ে গেল এই আপাত-স্বেচ্ছাচারী রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তটার সঙ্গে? জেন-জি-র কি আদৌ সেসবে কিছু যায় আসে? না কি ধারণাটা কতকটা এরকম যে, জেন-জি-র নিজের গায়ে আঁচ না লাগলে জেন-জি সচেতন হবেই না?

জেন-জি-র আগের প্রজন্মকে বলা হয় মিলেনিয়াল, তার আগের প্রজন্ম নব্বইয়ের অংশীদার। একটু ভেবে দেখলে, আজ থেকে দেড়-দু’দশক আগে এই দেশে, অর্থাৎ ভারতে যে-প্রজন্ম বড় হয়েছে, তারা রাজ্য থেকে দেশ— সর্বত্র রাজনৈতিক টালমাটাল দেখেছে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই রাজনৈতিকভাবে ততটা সচেতন হয়ে ওঠেনি। ২৬/১১ থেকে নির্ভয়ার ঘটনা হয়ে লোকপাল বিল আন্দোলন, আস্তে আস্তে নব্য প্রজন্ম রাজনীতির আঁচকে উপেক্ষা করা বন্ধ করল। দুর্নীতি, সন্ত্রাসবাদ, ধর্ষণের মতো ঘটনা থেকে সচেতন হওয়া নতুন প্রজন্ম এক নতুন আখ্যানে বিশ্বাসী হল, যাতে ক্রমে সাম্প্রদায়িকতার রং চড়ল, যার বাসরঘরে জাতীয়তাবাদী উগ্রতা সিঁধ কাটতে শুরু করল ক্রমে। এই সমস্তকিছুতে ক্রমশ সহায়ক হয়ে উঠেছিল ইন্টারনেটের অবাধ গতায়াত, সমাজমাধ্যমের সহজ চণ্ডীতলা। ফলে, বিপ্লব বা অভ্যুত্থানের হিসেবগুলো ওলটপালট হতে শুরু করল।
ফরাসি বিপ্লব থেকে শুরু করে দেখলে ইতিহাসে গণআন্দোলন আর নৈরাজ্যর ইতিহাস দীর্ঘকালীন। সাম্প্রতিকে বাংলাদেশ আর নেপালে যে নৈরাজ্য দেখা গেল, বা আরও বেশ কিছু আন্দোলনের যে চেহারা বিভিন্ন দেশে কয়েক বছরে চোখে পড়েছে, তাতে এই ইতিহাসের ধারাবাহিকতার রেশ কতটুকু মিলছে? তুরস্কের এরদোগান-বিরোধী আন্দোলনে পিকাচু সেজে রাস্তায় নামা, বাংলাদেশে বিপ্লব-পরবর্তী সময়ে ব্যাটম্যান সেজে ডাকাতির পাহারা দিতে নামা বা হালে নেপালে জ্বলন্ত সংসদের সামনে এক যুবকের নাচ— কোনওটাই কি চিরাচরিত নৈরাজ্য থেকে ফ্ল্যাশ মবের যে রাজনৈতিক প্রকৃতি, তার সঙ্গে কোথাও মিলছে?


না কি, এর নেপথ্যে রয়েছে আরও বড় কোনও খেলা? মার্কিন পুঁজিবাদের ইন্ধনের গন্ধ খুঁজে পাওয়া কি নেহাতই ষড়যন্ত্র-তত্ত্ব? সোভিয়েতের শেষ থেকে যে কালার রেভোলিউশনের সূত্রপাত, তা কি নতুন চেহারায় ফিরে আসছে? এই প্রশ্ন উঠে আসতে বাধ্য, কারণ সেই আরব বসন্ত থেকেই তথাকথিত ‘অরাজনৈতিক’ আন্দোলনের যে রূপরেখা তুলে ধরা হল, তা তো সত্যিই অরাজনৈতিক হতে পারে না। তাহলে সেইসব আন্দোলনের রাজনীতিটা কী? জেন-জি বিপ্লব নামক একটি ভাবনা-বেলুন ভাসিয়ে দিলেই কি খেলা শেষ? আবিশ্ব তরুণ প্রজন্মই তো বারবার লড়াইয়ের গতিপথ নির্ধারণ করেছে। সোরবোর্ন থেকে আমেরিকায় কাউন্টারকালচার ও ভিয়েতনাম যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন, সর্বত্র তো সেই তরুণরাই কাণ্ডারী! কিন্তু এই সমস্ত আন্দোলনেরই নির্দিষ্ট মতাদর্শগত অভিমুখ ছিল। তাহলে এই জেন-জি বিপ্লব নামে অভিহিত নতুন ধারাটি কী?
এখানে আমরা প্রথম বাক্যটিতে আবার ফিরে যেতে পারি। পল স্তানিল্যান্ড বলছেন, নিউ পলিটিক্স অফ ইনস্টেবলিটি, অস্থিরতার নব্য রাজনীতি। স্থিতিশীলতার ভেতর দুর্নীতি আছে, রাষ্ট্রীয় পচন রয়েছে, তাই অস্থিরতাই সম্বল এই নতুন রাজনীতির? কিন্তু তারপর? এমন তো নয়, এই নতুন অস্থিরতার রাজনীতিই বিশ্বব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করবে। দুনিয়াজোড়া ক্ষমতাতন্ত্রর শিরোমণিরা কিন্তু স্থিতাবস্থাই চায়। তবে এক স্থিতাবস্থাকে আক্রমণ করে নতুন স্থিতাবস্থার জন্ম-সম্ভাবনা কি এই নতুন, তথাকথিত অস্থির রাজনীতির আড়ালেই লুকিয়ে?
কেবলমাত্র বাংলাদেশ (সেখানে আবার ‘গেঞ্জি’ নামে রসিকতাও করা হয় এই প্রজন্মকে) বা নেপাল দিয়ে আমরা একটি গোটা প্রজন্মের রাজনীতিকে চিহ্নিত করে দিতে পারি কি আদৌ? যে-প্রজন্ম নাকি ইনস্টাগ্রামে বুঁদ, যাদের কাছে যে-কোনওকিছুর সমাধান বা ‘সলুলু’ হল গিয়ে কেবলই ‘ডেলুলু’ বা ডিলিউশন বা ভ্রান্তিবিলাস, তারা হঠাৎই এমনি-এমনি নৈরাজ্য তৈরি করছে? সরবন থেকে হিপি আন্দোলন, বিট প্রজন্ম থেকে তিয়েনানমেন, সর্বত্রই রাজনৈতিক ইন্ধনগুলো স্পষ্ট হয়। জেন-জি-র নামে টুপি পরিয়ে কোনও বড় রাজনীতিকে আমাদের চোখ ও মন থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না তো?