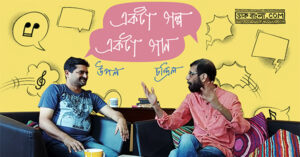কাম ব্যাক, পেপারব্যাক
বাংলা বাজারে বইয়ের দাম কি ক্রমশ আকাশছোঁয়া হয়ে উঠছে? এই কারণেই কি বইবিমুখ হয়ে উঠছে একটা বড় অংশের মানুষ? কেনার ইচ্ছে থাকলেও উপায় থাকছে না? তত্ত্ব-তথ্যের পরিসংখ্যান জানান দিচ্ছে হাজার-একটা কথা। প্রকাশকরা স্বপক্ষে বলছেন, ‘বইয়ের দাম কি ইচ্ছে করে বেশি রাখা হয় নাকি? সব কিছুরই খরচ বাড়ছে যেখানে, বইয়ের বেলাতেই এই কথা শুনতে হবে কেন! আমরা এমন দাম-ই রাখতে চাই, যাতে করে সবাই বইটা কিনতে পারে।’ অন্যদিকে, স্কুল-পড়ুয়া বা মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষ প্রস্তাব রাখছেন, ‘এই ক-টা পাতার বই— মার্জিন রেখে, পৃষ্ঠাসংখ্যা বাড়িয়ে, বোর্ড বাঁধাই করে বের করার আদৌ কি কোনও প্রয়োজনীয়তা আছে? পেপারব্যাক করলেই তো মিটে যায়!’
এই তর্কের কোনও শেষ নেই। কোন বই পেপারব্যাক হবে, আর কোন বই বোর্ড বাঁধাই— এই বিচার ঠিক কী পদ্ধতিতে প্রকাশকেরা করে থাকেন, তা তাঁরাই জানেন। বইয়ের সৌন্দর্য বাইরের না ভেতরের, এই আলোচনারও কোনও শেষ নেই। তবে কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় কান পাতলে কানাঘুষো শোনা যায়, পেপারব্যাক বইতে লাভ প্রায় নেই বললেই চলে। উপরন্তু তা বিকোয়ও কম। অনেক পাঠকও নাকি বোর্ড বাঁধাই বই কিনতেই ভালবাসেন। কেন এই চাওয়া? অনুমান, তাঁরা ভাবেন, যে-পয়সা লগ্নি করছি বইয়ের পিছনে, তা যদি সুখের-ই না হয়, তাহলে আর লগ্নি করে লাভ কী! অর্থাৎ, বোর্ড বাঁধাই বই ক্রেতাকে ‘কিনলাম বটে কিছু একটা!’-ভাবনার সুখ দেয়; শুধু ক্রেতা থেকে উপভোক্তা হয়ে ওঠার সুযোগ দেয়। কিন্তু পড়ার সুখ? তা তো পেপারব্যাকেই লুকিয়ে! হাত-পা ছড়িয়ে, শুয়ে-বসে-গড়িয়ে, রাজদ্বারে-শ্মশানে, যে-বই আয়েস করে পড়া যায়— এই বন্ধুতা পেপারব্যাক ছাড়া কেই-বা দেবে? অথচ বইপাড়ায়, পেপারব্যাক বইতে অনীহা।
অ্যালেন লেন পেঙ্গুইনের বই বাজারে এনে যে-বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছিলেন আজ থেকে প্রায় নব্বই বছর আগে, সেই দূরদর্শিতা আজ কোথায়! অ্যালেন তরুণ বয়সে জর্জ বার্নার্ড শ-র অটোগ্রাফ নিতে গেলে শ তাঁকে বলেছিলেন, ‘Young man, why don’t you spend your time in making your autograph worthwhile instead of going round collecting other people’s.’ ব্যাস, এরপর সেই অ্যালেন, বইবাজারের চারিদিক ভাল করে দেখলেন এবং জয় করলেন। সহজ কি ছিল তাঁর পথ? প্রকাশক, দোকানদার এবং সর্বোপরি লেখক-লেখিকা— বিরোধিতা করেছিলেন প্রত্যেকেই। প্রকাশকরা ভেবেছিলেন, অ্যালেন-পরিকল্পিত ছ’পেনির বইয়ের বাজারে কাটতি বাড়লে, তাঁদের হার্ড কভারের বইগুলো মার খাবে। বইয়ের দোকানদাররা আপত্তি করেছিলেন এই বলে, যা কমিশন তাঁরা পেয়ে থাকেন সাধারণত, পেপারব্যাক বেচে সেই লাভ তাঁরা তুলতে পারবেন না। আর লেখকদের প্রশ্ন ছিল, রয়্যালটি নিয়ে। এতদসত্ত্বেও ১৯৩৫ সালের ৩০ মে দশখানা পেঙ্গুইন বই প্রকাশ পেল। বাকিটা ইতিহাস। এই অনুষঙ্গে, আরও একটা প্রশ্ন উঠে আসে। একজন লেখকের কাছে কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ, টাকা না পাঠক? বোর্ড বাঁধাই বইয়ের একশো কপিতে লেখক যে-টাকা পাবেন, পেপারব্যাক থেকে সেই টাকা তুলতে গেলে অন্তত দুশোটা বই বিকোতে হবে ঠিকই, কিন্তু দুশোজন পাঠক সেক্ষেত্রে প্রাপ্তি। এরপর, সিদ্ধান্ত নিজেদের।রাস্তা একটা বেছে নিতে হবে।
এই তর্কের কোনও শেষ নেই। কোন বই পেপারব্যাক হবে, আর কোন বই বোর্ড বাঁধাই— এই বিচার ঠিক কী পদ্ধতিতে প্রকাশকেরা করে থাকেন, তা তাঁরাই জানেন। বইয়ের সৌন্দর্য বাইরের না ভেতরের, এই আলোচনারও কোনও শেষ নেই। তবে কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় কান পাতলে কানাঘুষো শোনা যায়, পেপারব্যাক বইতে লাভ প্রায় নেই বললেই চলে।
বাংলায় পেপারব্যাকের ইতিহাসও দীর্ঘ। গুরুদাস লাইব্রেরি যখন বারো আনা সিরিজের বইও বোর্ডে বাঁধাই করে ছাপত, সেখানে বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় চাইতেন বই বাহারি না করে একেবারে সস্তায় সাহিত্যের রত্নরাজি বাংলার ঘরে-ঘরে পৌঁছে দেওয়া হোক। ফলে পেপারব্যাক। বিশ্বভারতী-র অধিকাংশ বই শুরু থেকে এখনও সেইভাবেই প্রকাশিত হয়ে আসছে। ১৯৩৬ সালে বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ কিংবা লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার বইগুলো যখন বেরতে শুরু করে, রবীন্দ্রনাথেরও মনে হয়েছিল, ‘দুর্গম পথে দুরূহ পদ্ধতির অনুসরণ করে বহু ব্যয়সাধ্য ও শ্রমসাধ্য শিক্ষার সুযোগ অধিকাংশ লোকের ভাগ্যেই ঘটে না, তাই বিদ্যার আলোক পড়ে দেশের অতি সংকীর্ণ অংশেই। এমন মূঢ়তার ভার বহন করে দেশ কখনই মুক্তির পথে অগ্রসর হতে পারে না। যত সহজে যত দ্রুত যত ব্যাপকভাবে এই ভার লাঘব করা যায় যে জন্য তৎপর হওয়া কর্তব্য।’
বই পড়া তো কমেই আসছে! তৎপর কি আমরাও একটু হতে পারি না? তাক সাজানোর সামগ্রী না করে, কম দামে, খুব অল্প আড়ম্বরে, বেশি সংখ্যক পাঠকের কাছে বই পৌঁছে দেওয়ার একটা চেষ্টা কি নতুন করে করা যায় না? অবভাস বা থীমা-র মতো প্রকাশনা সংস্থা যেভাবে পেপারব্যাকের প্রতি পক্ষপাত দেখিয়ে বই করে যাচ্ছে, আরও কেউ-কেউ কি এই ভাবনায় বই নির্মাণে ব্রতী হতে পারে না? মুনাফাই কি বই-ব্যবসার একমাত্র লক্ষ্য? বোর্ড বাঁধাইয়ে আপত্তি নেই আমাদের, কিন্তু পাশাপাশি আরেকটা পেপারব্যাক সংস্করণ কি করা যায় না? টিফিনের খরচা বাঁচিয়ে, বাসট্রামঅটোরিকশার ভাড়াবাঁচিয়ে, যে-ছেলেটি বা মেয়েটি বইয়ের দোকান থেকে করুণ মুখে ফিরে যায়, তাদের কথা একটু ভাবা হোক। প্রকাশকরা যেন ভুলে না যান, একটা প্রকাশনাকে বাঁচিয়ে রাখে এই সমস্ত পাঠকরাই…