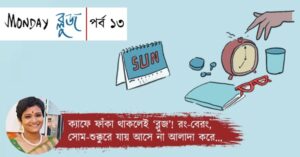হিড়িকের পুজোসংখ্যা
বর্তমানে ‘পুজো’র থেকে ‘পুজোসংখ্যা’ বেড়ে গেছে বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না। একদিকে বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ, আর-একদিকে, একটামাত্র দুর্গা পুজোর সময়ে বারোশো পুজোসংখ্যা! (এই সংখ্যা কম না-হলেও, বেশি হতেই পারে) এর কারণ অবশ্য ‘সম্পাদক’দের বাড়বাড়ন্ত।
বইপাড়ায় কান কিংবা চোখ পাতলে সম্পাদক তৈরি হওয়ার এক আশ্চর্য চক্র লক্ষ করা যাবে। প্রথমে ক্রেতা, পাঠক, ক্রমে সংগ্রাহক এবং এক সময়ে ‘দুম করে’ সম্পাদক। সম্পাদক-সংকলকের পার্থক্য কী, সে-আলোচনার পরিসর এই নিবন্ধ নয়। কিন্তু, এই দুম করে সম্পাদক হয়ে যাওয়ার মধ্যেই ভূরি-ভূরি পুজোসংখ্যা প্রকাশের গপ্পো লুকিয়ে রয়েছে। তবে অনেক বেশি সম্পাদক, অনেক বেশি পুজোসংখ্যা… এতে ক্ষতির কী আছে? আহা! মানুষ খুন তো হচ্ছে না, দুটো পত্রিকাই তো বেরোচ্ছে, একটু শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চাই তো হচ্ছে! এ আর এমন কী!
ব্যাপারটা খানিক এমন দাঁড়ায়, একবার এক জনৈক ব্যক্তি সম্পাদনায় আসবেন বলে ঠিক করলেন, তাঁকে একজন মজা করে বললেন, রাজশেখর বসু ওরফে পরশুরামের বেশ কিছু অপ্রকাশিত উপন্যাস আছে, সম্পাদনা করবে না কি? সম্পাদকমশাই বলে বসলেন, ‘নিশ্চয়ই করব! রাজশেখর বসুর উপন্যাস তো দারুণ ব্যাপার! কী ভাল উপন্যাস লিখতেন!’ তিনি জানেনও না, রাজশেখর বসু ইহজীবনে কোনও উপন্যাস লিখে যাননি! মুশকিলটা এখানেই, অজ্ঞতা কোনও অপরাধ নয়, কিন্তু না জেনে, এবং সেই অজ্ঞতা স্বীকার করেও যখন কোনও ব্যক্তি অশিক্ষা প্রদর্শনের ইস্তেহার খুলে বসেন, সেখানেই হয় সমস্যা।
পুজোর সময়ে, আগে নির্দিষ্ট সংখ্যক পুজোসংখ্যা প্রকাশিত হত, এখন সে-সংখ্যাই সংখ্যাধিক্যের কারণে অনির্দিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে। মূলত করোনা-র প্রকোপের পর থেকেই এই প্রবণতা বাড়তে শুরু করে। কারণ মানুষের হাতে তখন যে অঢেল ‘সময়’! ‘আন্তরিক’ কিংবা ‘সৎ’ সাহিত্যচর্চার থেকে লেখকদের কাছে শখের ‘কলমবাজ’ হওয়াই বেশি স্বপ্নের। ফলও হল তেমনি। শ্যাওলার মতো গজিয়ে উঠল স্বঘোষিত কিছু সাহিত্যপত্রিকা। অবশ্য নামেই ‘সাহিত্য’, কাজের ক্ষেত্রে যে কী হয়, তা দু-চারটে পাতা ওলটালেই সচেতন পাঠক দেখতে পারবেন। তাদের নামও বিচিত্র। ধরা যাক নতুন কোনও সংখ্যা এ-বছর বেরোবে, তার নাম সম্পাদক দিয়ে বসলেন, ‘আত্মপ্রকাশ’ কিংবা ‘নতুন’। মলাটে বড়-বড় করে লেখা ‘আত্মপ্রকাশ ১ ম বর্ষ’ কিংবা ‘নতুন ১ ম বর্ষ’। বিচিত্র তাদের মলাট। পাশাপাশি এঁরা নিজেদের আগমনের সময় হিসেবে দুর্গা পুজোকেই বেছে নেন। ও হ্যাঁ, বইপাড়ার অলিগলিতে ঘুরলে ‘আগমনী ১ ম বর্ষ’ নামের কোনও পত্রিকাও দেখে ফেলতে পারেন।
এত কিছুতেও সমস্যা নেই, তাহলে আপত্তি বা প্রশ্নের অবকাশটা কোথায়? পুজোর এক-দেড় মাস আগে থেকে ফেসবুকের পাতা সরালেই চোখে পড়বে— ‘নতুন লেখা আহ্বান করা হচ্ছে’ এমন কোনও বিজ্ঞাপনী লাইন, এবারে একটু নেমে আসুন, মানে এই বিজ্ঞাপনী লাইনের নীচে লেখা থাকবে কিছু শর্ত। এই শর্তগুলো দেখলে আপনার চোখ কপালে উঠতে বাধ্য। শর্তগুলোর নমুনা খানিক এমন: (১) ‘লেখা নিজের দায়িত্বে পাঠাবেন, প্রুফ দেখে পাঠাবেন’ (২) ‘লেখা পাঠালে কোনও সাম্মানিকের আশা করবেন না, পত্রিকা প্রকাশিত হলে, পত্রিকার সম্পাদক সৌজন্য সংখ্যা পাঠাতে অপারগ। ঠিকানা, নির্ধারিত মূল্য এবং পোস্টাল-চার্জ পাঠালে, দপ্তর থেকে পত্রিকা পাঠিয়ে দেওয়া হবে’— এরকম আরও অনেক বিচিত্র শর্ত! শুধু দুটো নমুনা দেওয়া হল মাত্র। কোনও বিজ্ঞাপনে আবার লেখা থাকে, লেখা প্রকাশিত হলে, লেখককে তিনটি কপি কিনতেই হবে।
এখন প্রশ্ন হল, বানান সম্পর্কে সচেতন হওয়া নিঃসন্দেহে ভাল ব্যাপার, কিন্তু শর্তে লিখে দেওয়া হচ্ছে, ‘প্রুফ দেখে পাঠাবেন’— এই বাক্যের মানে কী দাঁড়ায়? পত্রিকার সম্পাদক বানান দেখতে অপারগ? অবশ্য এহেন শর্ত দেওয়ার পর সম্পাদক নিজে কতটা বানান সম্পর্কে অবহিত সে-বিষয়ে সংশয় জাগে; কারণ কেউ যদি বানান ঠিক করেও পাঠান, তাঁরা তো রুচিভেদে কেউ সংসদ আবার কেউ-বা আকাদেমির বানানবিধি অনুসরণ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে কি পত্রিকায় বানানবিধির কোনও সাম্য থাকবে না? আসা যাক দ্বিতীয় শর্তে, কী স্পর্ধা! আপনাকে যে পত্রিকা প্রকাশ করতেই হবে, এমন মাথার দিব্যি কে দিয়েছে শুনি? আপনি কতগুলো লেখা জুড়ে প্রকাশ করছেন, আদৌ লেখাগুলো আপনি পড়ছেন কি না সন্দেহ, (সন্দেহ এ-কারণেই বলা হল, কারণ, ক’বছর আগে, শান্তিনিকেতন থেকে প্রকাশিত এক পত্রিকার পুজোসংখ্যায় একটি কবিতা বেরোয় এক ব্যক্তির নামে, তাঁর সেই কবিতাংশে, রবীন্দ্রনাথের ‘মাঝে মাঝে তব দেখা পাই’ গানের অংশটুকু সম্পূর্ণ ঝেপে, থুড়ি ছেপে দেওয়া! সম্পাদক যদি সচেতন হতেন এমন ভুল কি হতে পারত?) ঘুরে-ফিরে কিন্তু ‘ভুল’ সেই পুজোসংখ্যাতেই এসে দাঁড়াল! এহেন পুজোসংখ্যা প্রকাশ করে নতুন কিছু পত্রিকা বললেন, তাঁরা লেখককে টাকা তো দেবেনই না, উলটে তাঁদের পত্রিকা লেখককেই কিনতে হবে! যেন সম্পাদক পত্রিকা প্রকাশ করে লেখককে এবং সামগ্রিক বাংলা সাহিত্যকে উদ্ধার করছেন।
সম্পাদক বা প্রকাশক নিজে তো বিক্রি করছেন বইটা, তাঁর তো লাভ-ই হচ্ছে, সেইটাও পাচ্ছেন লেখকের জন্যই! সম্মানটুকু কি লেখকের প্রাপ্য নয়? অবশ্য নাগরিক কবিয়াল কবেই বলে গেছেন, ‘লেখকরা লেখে আর প্রকাশক ছাপে/ সাহিত্য মরে পুজোসংখ্যার চাপে।’
প্রশ্ন হল, লেখকের ‘শ্রম’ কি ‘শ্রম’ নয়? তাঁকেও তো দু-চারটে বই পড়ে, নিজের সময় ব্যয় করে লেখাটা লিখতে হয়। উদ্দেশ্য? ছাপার হরফে নিজের নামটুকু দেখা। সৌজন্য সংখ্যা দূরস্থান, তাঁকেই সে-লেখা অর্থের বিনিময়ে কিনতে হবে? হোক-না সে লেখা গল্প, প্রবন্ধ কিংবা কবিতা। লেখার শ্রমের কি কোনও মূল্যই নেই এসব সম্পাদকের কাছে? সম্পাদক বা প্রকাশক নিজে তো বিক্রি করছেন বইটা, তাঁর তো লাভ-ই হচ্ছে, সেইটাও পাচ্ছেন লেখকের জন্যই! সম্মানটুকু কি লেখকের প্রাপ্য নয়? অবশ্য নাগরিক কবিয়াল কবেই বলে গেছেন, ‘লেখকরা লেখে আর প্রকাশক ছাপে/ সাহিত্য মরে পুজোসংখ্যার চাপে।’ এমনিতে বাংলা বাজারের দুর্নাম আছে যে, লিখে টাকা পাওয়া যায় না। এক সময়ে বড়-বড় লেখককেও প্রকাশকের দরজায় রবাহূতের মতন ঘুরতে হয়েছে, নিজের প্রাপ্য সাম্মানিকের আশায়। এমনকী আজও এ-ধারা প্রবহমান। সেখানে দাঁড়িয়ে নতুন যাঁরা পত্রিকা করতে আসবেন, তাঁদের যদি এই বোধটুকু না থাকে, তবে আগামীদিন যে শোচনীয়, সে-বিষয়ে সংশয় নেই।