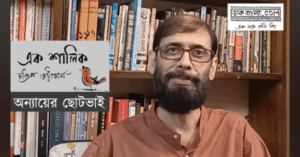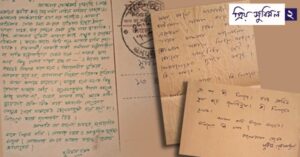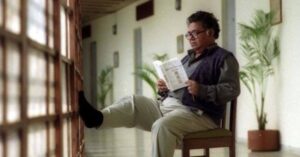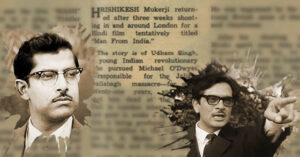আত্মঘাতী বাঙালি
‘ভাষা এমন কথা বলে, বোঝে রে সকলে’— বিষয়টা সহজ। কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে, মানুষ মানুষের ভাষা ঠিক বুঝে নিত যে-পৃথিবীতে, সেই পৃথিবী এখন আর আছে কি? এখনও হয়তো পাওনাদার দেনাগ্রস্তর ভাষা ঠিকই বুঝে নেবে, হয়তো বিপন্ন মানুষ আর-এক বিপন্নর ভাষা টের পেয়ে যাবে, সোশ্যাল মিডিয়ার দুর্বোধ্য কমেন্টও দিনের শেষে ঠিকই বোঝা যাবে। কিন্তু ভাষা যে-দেওয়াল আগে দুটো মানুষের মধ্যে তুলত, মানুষ তা অতিক্রমের চেষ্টা করত। দিনকয়েক ধরে যে-শোর উঠেছে, অর্থাৎ কিনা, বাংলা বললেই পশ্চিমবঙ্গের মানুষ পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অত্যাচারিত হচ্ছে, সেখানে ভাষা আদৌ কতটা নির্ধারক? দেশকালের সীমানা, জাতির প্রশ্ন, ইতিহাসের নানাবিধ বেইমানির মিথ, মিথ্যে, সত্যি সব মিলিয়ে যে ঘন্টটা পাকিয়ে আছে, তার ফল কারা ভুগছে? মধ্যবিত্ত বাঙালি? না। সংস্কৃতির ধারকবাহক বাঙালি? না। এটার একেবারে হাতেগরম নির্মমতাটা টের পাচ্ছে পরিযায়ী শ্রমিকরা, নিম্নবিত্তরা, যারা কাজের সন্ধানে ছড়িয়ে পড়েছে বাংলার বাইরে। খেয়াল করার জায়গাটা হল, এদের অধিকাংশেরই পরিচয়পত্রর ঠিক নেই, সবটা তাদের দোষে না কর্তৃপক্ষর দোষে, কেউ জানে না। এরা অধিকাংশই নিঃসহায়।
শান্তিনিকেতনের হেরিটেজ ওয়াকে একজন গাইডের ঠিক কী ভূমিকা হওয়া উচিত? পড়ুন: চোখ-কান খোলা পর্ব ১…
ঘটনা হচ্ছে, ভাষার গৌরব, ভাষা আন্দোলনের গরিমা— এই সবটাই সংস্কৃতিবান বাঙালির আত্মাভিমানে খানিক সুড়সুড়ি দেওয়ার মশলাপাতি। কিন্তু কেবল মাতৃভাষার জন্য যাদের দেশকাল নিয়েই সন্দেহ দানা বাঁধছে, খোদ বাঙালির একাংশই যাদের সহজেই ‘অনুপ্রবেশকারী’ বলে দাগিয়ে দিচ্ছে, তাদের উদ্ধার করবে ভাষার অহংকার? এমন প্রস্তাবনা শুনলে ঘোড়ায়ও হাসবে বুঝি। এর দোষ কেবলই রাজনৈতিক নেতৃত্বকে দিয়ে দেওয়া সহজ, কিন্তু আমবাঙালি আয়না দেখতে শিখেছে কি আদৌ?
যে-দেশে কয়েক মাইলের তফাতে বদলে যায় ভাষার গড়ন, ভাষার আদল, সেই দেশে কোন গজদন্তমিনারে বসে শহুরে বাঙালি নির্ধারণ করছে যে, পরিযায়ী রাজমিস্ত্রি, শ্রমিকরা আদতে এদেশি-ই নয়? এই ঘৃণাবোধের শিকড় কি কেবলই দেশ বা ভাষার সীমায় বাঁধা? না কি এর আড়ালে আসলে সুপ্ত শ্রেণিঘৃণাও ডগমগিয়ে ওঠে? আর সঙ্গে যে-ঘেন্না সহজেই আসে, যার মধ্যে সাম্প্রদায়িক আঁশটে গন্ধ ভরপুর, কিন্তু ফুলেল ঘ্রাণ ভেবে যাকে বরণ করতে দু’বার ভাবে না বাঙালি। অন্য ধর্মের মানুষ যে আমার রাজ্যে আমার পড়শি হতে পারে না, এই বিশ্বাস এতটাই গাঁথা, যে তাতে কোনও টোল পড়ে না সহজে। জটিল ডেমোগ্রাফির থেকে শত্রু ভাবার ডেমোক্রেসি সবসময়েই স্বাগত।
সুভাষ মুখোপাধ্যায় একসময় সওয়াল করেছিলেন ‘কাজের বাংলা’-র জন্য। চেয়েছিলেন ভাষার এমন যৌথতা, যা শ্রেণি-নির্বিশেষে তার জমি প্রস্তুত করবে।আমরা এখনও চেষ্টা করলে সব ভাষাই বুঝি, অন্য ভাষার সিনেমা-ওয়েব সিরিজ বুঝে নিই সাবটাইটেল হাতিয়ার করে, অথচ নিজভাষীদের কাউকে-কাউকে, কেবল শ্রেণির হেরফেরে আমরা সহজেই ভিনদেশি বলে বাতিল করি।
বলা কঠিন। কিন্তু এ-কথা ঠিক, এই শ্রমিকরাই বিভিন্ন রাজ্যে গিয়ে আগে সেখানকার ভাষা আয়ত্ত করে। হয়তো নিজের রাজ্যের, নিজের ভাষার লোক পেলে খানিক হাঁফ ছাড়ে, কিন্তু নিজের মাতৃভাষা পেরিয়ে গিয়ে আর যে-ভাষায় তারা কথা বলতে শেখে, তা ইংরেজিও নয়, কোনও মান্য ভারতীয় ভাষাও নয়, আদৌ যদি তেমন কিছুর অস্তিত্ব থেকে থাকে। তামিলনাড়ু থেকে গুজরাত, কেরল থেকে অসম— সর্বত্র স্থানীয় ভাষাই আয়ত্ত করতে হয় তাদের একটু-একটু করে। একজন প্রবাসী আইটি কর্মী আদৌ তা করবে কি না, তা নিয়ে কিন্তু সংশয় থেকে যেতে পারে। কিন্তু বাধ্যতাই হোক বা দায়, এই শ্রমিকদের তো পৌঁছতেই হবে কাজের ভাষার কাছে।
এখানেই লুকিয়ে আদত সমস্যাকূট।
সুভাষ মুখোপাধ্যায় একসময় সওয়াল করেছিলেন ‘কাজের বাংলা’-র জন্য। চেয়েছিলেন ভাষার এমন যৌথতা, যা শ্রেণি-নির্বিশেষে তার জমি প্রস্তুত করবে। আমরা এখনও চেষ্টা করলে সব ভাষাই বুঝি, অন্য ভাষার সিনেমা-ওয়েব সিরিজ বুঝে নিই সাবটাইটেল হাতিয়ার করে, অথচ নিজভাষীদের কাউকে-কাউকে, কেবল শ্রেণির হেরফেরে আমরা সহজেই ভিনদেশি বলে বাতিল করি। এই বাতিল করার রাজনীতির প্রেক্ষিত অবশ্যই প্রোথিত দেশভাগের অতীতে, কূটনীতির রক্তমাংসে। কিন্তু নিজের মননে যে বিদ্বেষকে আমরা জলহাওয়া দিয়েছি, বাড়তে দিয়েছি যে রক্তবীজের ঝাড় আমাদের মাথার মধ্যে, তাকে ফেসবুকে, বৈঠকখানায়, পাড়ার রোয়াকে ছড়িয়ে দিচ্ছি, প্রতিবেশীকে বিষাক্ত করে দিচ্ছি কোন ভাষায়?
কাজেই, আমরা আমাদেরই ভাষার মানুষদের কোণঠাসা করছি, আমাদেরই ভাষা দিয়ে। এক নেতা যে কয়েকবছর আগে সদর্পে বলেছিলেন, রাজমিস্ত্রির চিঁড়ে খাওয়া দেখে তাকে তিনি বাংলাদেশি ঠাওরেছেন, সেই নেতা তো বাঙালি ছিলেন না। কিন্তু বাঙালিদের কেউ-কেউ, আদতেই মনে-মনে সে-কথাকেই সমর্থন করেনি তো? নীরদচন্দ্র চৌধুরীর বইয়ের নামটিই দিনে দিনে আরও শক্তপোক্ত হচ্ছে, আশা রাখা যায়, তেমনটাই হবে।