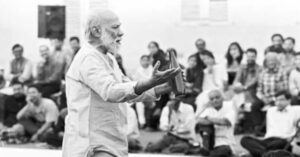‘আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে আসে নাই কেহ অবনী পরে/ সকলের তরে সকলে আমরা/ প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।’ কামিনী রায়ের লেখা ‘সুখ’ কবিতাটি পড়েছিলাম যখন আমি স্কুলে পড়ি। আমাদের পাঠ্য তালিকায় ছিল। আজ এতকাল পরে পুরো কবিতাটি মনে না থাকলেও শেষ স্তবকটি আজও মনে আছে। কবি কামিনী রায়কে স্মরণ করতে গিয়ে এই কবিতাটির কথা মনে পড়ে গেল।
কামিনী রায় জন্মেছিলেন বরিশালের বাসণ্ডা গ্রামে, ১৮৬৪ সালে। মাত্র আট বছর বয়স থেকে তিনি সাহিত্য রচনা শুরু করেন আর এভাবেই তাঁর কবিপ্রতিভার স্ফুরণ ঘটে। সেই সময় থেকেই তিনি ছিলেন মেধাবী, ভাবুক প্রকৃতির এবং কল্পনাপ্রবণ। তাঁর পিতা চণ্ডীচরণ সেন ছিলেন একজন ঐতিহাসিক উপন্যাস-লেখক, ব্রাহ্ম-ধর্মাবলম্বী এবং পেশায় বিচারক। অতি শিশু বয়স থেকে কামিনীর বিদ্যাভাস শুরু হয়েছিল। তাঁর পিতামহ তাঁকে কবিতা ও স্তোত্রপাঠ শেখাতেন। জননী তাঁকে গোপনে বর্ণমালা শিক্ষা দিতেন। কারণ সে-যুগে হিন্দু পুরমহিলাদের লেখাপড়া শিক্ষাকে একান্তই নিন্দনীয় এবং গর্হিত কাজ হিসেবে বিবেচনা করা হত। চণ্ডীচরণও কন্যার শিক্ষার ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত যত্নবান। পিতার কাছে গণিতশাস্ত্র শিখে তিনি এ-বিষয়ে এত দূর পারদর্শী হয়ে ওঠেন যে গণিত-শিক্ষক শ্যামাচরণ বসু তাঁকে ‘লীলাবতী’ আখ্যা দিয়েছিলেন। শুধু গণিত নয়, তিনি ইংরেজি, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি বিষয়েও শিক্ষালাভ করেছিলেন।
আরও পড়ুন : প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারকে স্বাধীনতা সংগ্রামীর মর্যাদা দেয়নি ভারতীয়দেরই একাংশ? লিখছেন সম্প্রীতি চক্রবর্তী…
পিতা-মাতার সহায়তায় কামিনী কলকাতার বেথুন স্কুলে ভর্তি হন। এই স্কুল থেকেই ১৮৮১ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং এর দু-বছর পরে এফএ পরীক্ষায় সংস্কৃত ভাষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। মাত্র ১৫ বছর বয়সে তাঁর প্রথম কাব্য গ্রন্থ ‘আলো ও ছায়া’ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছিলেন সে-যুগের খ্যাতনামা কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন, ‘এই গ্রন্থের কবিতাগুলি আমার বড়ই সুন্দর লাগিয়াছে, স্থানে স্থানে এমন মধুর ও গভীর ভাবে পরিপূর্ণ যে পড়িতে পড়িতে হৃদয় মুগ্ধ হইয়া যায়। বাংলা ভাষায় এমন কবিতা আমি অল্প পাঠ করিয়াছি। বস্তুত কবিতাগুলোর ভাবের গভীরতা, ভাষার সরলতা, রুচির নির্মলতা এবং হৃদয়গ্রহিতাগুণে আমি অতিশয় মোহিত হইয়াছি।’
এই গ্রন্থ প্রকাশের পরে কামিনীর খ্যাতি দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি একসময়ে আবার ‘জনৈক বঙ্গমহিলা’ ছদ্মনামেও লিখেছেন।

১৮৮৬ সালে বেথুন কলেজ থেকে সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্য নিয়ে সম্মান-সহ স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন কামিনী। তিনি ছিলেন ভারতের এই ডিগ্রিধারী প্রথম মহিলা। স্নাতক হওয়ার পর তিনি বেথুন স্কুলে শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। পরবর্তীকালে তিনি বেথুন কলেজে অধ্যাপনাও করেছেন। কামিনী রায় প্রচলিত শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেকে কিন্তু সাধারণ জীবনযাপনে বেঁধে রাখেননি। ‘ইলবার্ট বিল’-এর আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কারাবরণের সময়ে বিলের সমর্থনে ঐক্যবদ্ধ হতে কামিনী বেথুন স্কুল, কলেজের ছাত্রীদের নেতৃস্থানীয় হয়ে উঠেছিলেন। লর্ড রিপন ভারতে আসার আগে কোনও ভারতীয় বিচারকের অধিকার ছিল না কোন ইংরেজ অভিযুক্তর বিচার করা। এই বৈষম্য দূর করার উদ্দেশ্যে লর্ড রিপনের পরামর্শে ইলবার্ট বিলের খসড়া প্রস্তুত হয়। এই বিলের বিরুদ্ধে ইংরেজরা আন্দোলন শুরু করলে ভারতীয়রা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের নেতৃত্বে পাল্টা আন্দোলন শুরু করেন। যদিও ভারতীয়দের সে আন্দোলন সফল হতে পারেনি।
রবীন্দ্রনাথের ন’দি সাহিত্যিক স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা সরলা দেবী চৌধুরাণী তাঁর স্মৃতিকথা ‘জীবনের ঝরাপাতা’ গ্রন্থে জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে কামিনী রায়ের উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, ‘এদিকে স্কুলের উপর ক্লাসের কতকগুলি মেয়েদের নেতৃত্ব-প্রভাবে আমার জাতীয়তার ভাব উত্তরোত্তর বর্ধিত হতে লাগল। তাঁদের মধ্যে অন্যতম নেত্রী ছিলেন— কামিনী দিদি ও অবলা দিদি— কবি কামিনী রায় ও অবলা বসু।’ কামিনী রায়ের কবিতাতেও তাঁর স্বদেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, ‘যেইদিন ও চরণে ডালি দিনু এ জীবন,/ হাসি অশ্রু সেইদিন করিয়াছি বিসর্জন।/ হাসিবার কাঁদিবার অবসর নাহি আর,/ দুখিনী জনমভূমি, মা আমার, মা আমার।’
যে যুগে হিন্দু মহিলাদের শিক্ষা গ্রহণ ছিল এক বিরল ঘটনা, সেই সময়ে কামিনী রায় শুধু যে উচ্চশিক্ষা অর্জন করে ছিলেন তাই নয়, শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সামাজিক উন্নয়নে তাঁর অবদান কিছু কম ছিল না। এরই সঙ্গে কবিতা রচনার পাশাপাশি তিনি হয়ে উঠেছিলেন একজন সাহসী নারীবাদী লেখিকা।
স্ট্যাটুটারি সিভিলিয়ান কেদারনাথ রায় কামিনীর কবিতা পড়ে এতটাই বিমোহিত হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি তাঁকে বিবাহের প্রস্তাব দেন এবং ১৮৯৪ সালে দু-জনে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। কামিনী রায়ের বয়স তখন ৩০ বছর। কনের বয়স নিয়েও সমাজ সমালোচনা করতে ছাড়েনি। কামিনী এবং কেদারনাথ এসবে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করেননি। বিবাহের অব্যবহিত পরে কামিনী রায় তেমনভাবে কবিতা লেখেননি, শুধু ‘গুঞ্জন’ নামে শিশুদের জন্য একটি কাব্য সংকলন প্রকাশ পেয়েছিল। এই সময়ে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, ‘সংসারই আমার কবিতা’। এর পরে একদিন তিনি ছেড়েই দিয়েছিলেন কবিতা লেখা।
রবীন্দ্রনাথের ন’দি সাহিত্যিক স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা সরলা দেবী চৌধুরাণী তাঁর স্মৃতিকথা ‘জীবনের ঝরাপাতা’ গ্রন্থে জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে কামিনী রায়ের উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, ‘এদিকে স্কুলের উপর ক্লাসের কতকগুলি মেয়েদের নেতৃত্ব-প্রভাবে আমার জাতীয়তার ভাব উত্তরোত্তর বর্ধিত হতে লাগল। তাঁদের মধ্যে অন্যতম নেত্রী ছিলেন— কামিনী দিদি ও অবলা দিদি— কবি কামিনী রায় ও অবলা বসু।’ কামিনী রায়ের কবিতাতেও তাঁর স্বদেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়।
১৯০৯ সালে এক দুর্ঘটনায় কামিনীর স্বামী কেদারনাথের অকাল মৃত্যু ঘটে। শোকগ্রস্ত কামিনী নিজেকে সামলাতে কবিতায় ফিরে আসেন। শুরু করেন নতুন করে কবিতা লেখা। তাঁর ‘দিন চলে যায়’ কবিতায় প্রিয়জন হারানোর বেদনা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি লিখলেন, ‘…জীবন আঁধার করি, কৃতান্ত সে লয় হরি/ প্রাণাধিক প্রিয়জনে, কে নিবারে তায়?/ শিথিল হৃদয় নিয়ে, নর শূন্যালয়ে গিয়ে,/ জীবনের বোঝা লয় তুলিয়া মাথায়…।’ বিবাহের পরে যে সংসারকে অবলম্বন করে তিনি একদিন কবিতাকে জীবন থেকে বিসর্জন দিয়েছিলেন, সেই তিনিই আবার একের পর এক প্রিয়জন হারানোর শোক থেকে মুক্তি পেতে সাহিত্য রচনাকে আঁকড়ে ধরলেন। দুঃখ কামিনীর জীবনকে ঘিরে থেকেছে। সেই শোক ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে তাঁর রচনায়। স্বামীর অকাল প্রয়াণের চার বছরের মধ্যে হারালেন পুত্র অশোককে। ১৯২০ সালে হারালেন কন্যাকে। শোক ও হতাশায় নিমজ্জিত কবি আশ্রয় নিলেন ঈশ্বর বিশ্বাস ও তাঁর মহিমায়। ঈশ্বরের উদ্দেশে তিনি লিখলেন, ‘হে ঐশ্বর্যবান, কেড়ে নিলে সর্বশ্রেষ্ঠ দান তব প্রাণের সন্তান!’
সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি কামিনী রায় সাংস্কৃতিক ও জনহিতকর, বিশেষ করে নারীকল্যাণমূলক কাজেও আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর বয়স যখন মধ্য পঞ্চাশ, তিনি তখন নারীশ্রমিক তদন্ত কমিশনের অন্যতম সদস্য পদে যোগদান করেন। ১৯২৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ‘জগত্তারিণী স্বর্ণপদক’ প্রদান করে সম্মানিত করে।
সেই যুগের প্রায় সব বাঙালি কবিই রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত হলেও ব্যতিক্রম ছিলেন কামিনী রায় এবং স্বভাব কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস। কামিনী রায়ের কবিতায় বিশ্বসাহিত্যের অপূর্ব বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। অনেক বিদ্বজ্জন বিষয়ের দিক দিয়ে তাঁর কোনও কোনও কবিতা রবীন্দ্রনাথের পূর্বগামী বলে মত প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্র-সমকালের মানুষ ছিলেন কামিনী রায়। অনেকের মতে কবির সঙ্গে তাঁর একটি অম্লমধুর সম্পর্ক ছিল। ১৯০০ সালের ৫ অক্টোবর প্রিয়নাথ সেনকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ কামিনী রায়ের ‘আলো ও ছায়া’ এবং ‘পৌরাণিকী’ কাব্যগ্রন্থ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছিলেন, ‘লেখিকার ভাব, কল্পনা এবং শিক্ষা আছে, কিন্তু তাঁর লেখনীতে ইন্দ্রজাল নেই, তাঁর ভাষায় সঙ্গীতের অভাব।’ কামিনী রায় আবার মন্মথ ঘোষকে লেখা এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব প্রকাশ করেছেন। তাঁর লেখা কবিতা পড়ে কামিনীর মনে হয়েছিল, রবি ঠাকুরের কবিতায় কীসের যেন একটা অভাব। যদিও তিনি রবীন্দ্রনাথকে অগ্রজর সম্মান দিয়ে লিখেছিলেন, ‘তাঁহার সর্বতোমুখী প্রতিভা, গীত রচনায় অদ্ভুত অনন্যসাধারণ ক্ষমতা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না।… কিন্তু কেবল এইগুলি দিয়াই হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় না। আরও কিছু চাই।’
আবার যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তকে লেখা আর একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কামিনী রায় লিখেছেন, ‘আমার মনে হয় আমি কিছু অকালপক্ক ছিলাম। কতকগুলো বিষয় রবীন্দ্রনাথের পূর্বেই লিখিয়াছি। কিন্তু তিনি যখন লিখিয়াছেন অনেক সুন্দর করিয়া লিখিয়াছেন।’ বাংলা সাহিত্যের সেই সন্ধিক্ষণে যখন নতুন ও পুরনোর মধ্যে এক সৃজনশীল বিরুদ্ধস্রোত বহমান, সেই সময়ে দাঁড়িয়ে কামিনী রায় রবীন্দ্রনাথের দ্বারা অতটা প্রভাবিত হননি, যতটা হয়েছেন হেমচন্দ্র, বিহারীলাল এবং মধুসূদন দ্বারা।
সমাজ-সচেতক কামিনী রায় ছিলেন আধুনিক মানসিকতার প্রতীক। তিনি নারীমুক্তির কথা চিন্তা করেছেন। লিঙ্গবৈষম্য ও নির্যাতনকে নির্মূল করার স্বপ্ন দেখেছেন। সেই সময়ের অবলা নারীর সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না নিয়ে আলোচনা করেছেন। আবার কখনও নারী-পুরুষের সমান অধিকার, তাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা নিয়েও আন্দোলন করেছেন। ১৯২১ সালে বাল্যবন্ধু কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিহার ও উড়িষ্যার কয়লাখনি অঞ্চলে ঘুরে বেড়ান এবং ওই অঞ্চলের নারী ও শিশুদের দুরবস্থার কথা বিস্তারিতভাবে নানা প্রবন্ধে লেখেন। তিনি ব্রিটিশ-শাসিত সময়ে নারীর ভোটাধিকার আন্দোলনের অগ্রভাগে ছিলেন। সেই আন্দোলনের ফলেই ব্রিটিশ সরকার ১৯২৬ সালে বাঙালি নারীর ভোটাধিকার প্রদান করে।
কামিনী রায়ের লেখা ‘বরপণ’ প্রবন্ধটিতে তিনি যে শুধু বরপণ প্রথার দৃপ্ত ভাষায় নিন্দা করেছেন তাই নয়, তিনি এই প্রথা নির্মূল করার একটি পথেরও নির্দেশ দিয়েছেন। প্রবন্ধের শেষ ভাগে কামিনী রায় লিখছেন, ‘কাহারও সামাজিক আচারাদি বা আদবকায়দায় একটু ত্রুটি হইলে অমনি সে একঘরে, বাড়ির অন্য কেহ দুষ্কর্ম করিয়াছে, সে নিজে নির্দোষ, তবু করো ওঁকে একঘরে। এই রকম তো কতই হয়। পণপ্রথা উঠাইবার জন্য যাঁহাদের বিশেষ আগ্রহ, আশা করি তাঁহারা পণগ্রাহী বরদিগকে এবং যাহারা তাহাদের পণ লইতে প্রলুব্ধ ও প্রবৃত্ত করায় তাহাদিগকে সমাজচ্যুত, একঘরের মতো ব্যবহার করিবেন। ইহার ফলে এই দূষিত প্রথা অনেকটা বাধাপ্রাপ্ত হইবে। উত্তরাধিকার বিষয়ে নূতন আইন প্রবর্তন, বাল্যবিবাহ দূরীকরণ ও কন্যাশিক্ষা প্রচলন, এই বরপণ উচ্ছেদে প্রধান সহায়।’ লেখাটি প্রকাশ পেয়েছিল ‘বঙ্গলক্ষ্মী’-তে, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে।
কামিনী রায়ের এইসব লেখা আজও প্রাসঙ্গিক। শেষ জীবনে তিনি বিহারের হাজারিবাগ অঞ্চলে বাস করতেন। ১৯৩৩ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর উনিশ শতকের বিখ্যাত কবি, সমাজকর্মী এবং নারীবাদী লেখিকা কামিনী রায়ের জীবনাবসান ঘটে।
তথ্যসূত্র:
বঙ্গ মহিলা চরিতাভিধান; শ্যামলী গুপ্ত
জীবনের ঝরাপাতা, পৃষ্ঠা ২৮, সরলা দেবী চৌধুরাণী