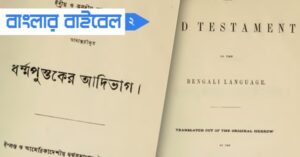‘বাঙালির সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপূজা।’ ঠিক এই কথাটাই ক্লাস ওয়ান থেকে শুরু করে উচ্চমাধ্যমিক অবধি প্রবন্ধ রচনায় তোতা পাখির মত আওড়ে গেছি। কোনও প্রশ্ন ছাড়াই। যেখানে ছোটবেলা থেকেই প্রশ্নটা আসা উচিত ছিল। জ্ঞান হওয়া ইস্তক দেখে আসছি আমাদের রাজগ্রামের অধিবাসীদের কাছে দুর্গাপূজার থেকেও বড়— জ্যৈষ্ঠ মাসের ‘চব্বিশ পরব’। একটা নয় দুটো। একটা তাঁতিদের আর একটা তাম্বুলিদের। ভরা গরমেও মানুষের উত্তেজনার শেষ নেই। মেয়েরা বাপের বাড়ি আসবে। দূরদূরান্তের আত্মীয়তে ঘর ভরে যাবে। গৌর নিতাইয়ের ঘেরা (স্থানভেদে যাকে ‘মাড়ো’ বলা হয়), তার ওপর সাদা কাগজের নিখুঁত নকশা, ঝলমলে আলো, এই পাড়ায় রাক্ষস তো ওই পাড়ায় হাতির জল ঢালা, ফুচকা-ঘুগনি-চটপটি, বেলুন, খেলনাবাটি সবকিছু দেখে আশেপাশের গ্রামের লোকেদের ধন্য-ধন্য। এমনটি আর কোথাও দেখিনি।
কিন্তু মূলধারার আলোচনায় চব্বিশ পরব বলে কোন উৎসব নেই। পরীক্ষায় রচনা সব সময় দুর্গাপূজা নিয়েই আসে। কখনও হয়তো সরস্বতী পূজা। অবশ্য ঈদ, বড়দিন বা সহরাই রচনাও কখনও পরীক্ষায় আসেনি। ইদানিং অবশ্য অনেক তর্ক-বিতর্কের পর ‘করম’-এর ছুটি চালু হয়েছে। আর তাতে খোদ বাঁকুড়া শহরের উচ্চজাতির মানুষজনকে বলতে শুনেছি ‘করম’টা আবার কী? তাহলে কলকাত্তাইয়া ‘বাঙ্গালী’দের কথা ছেড়ে দিন।
আরও পড়ুন: পুজো এলে এখনও ফিরে যাই ছোটবেলার গ্রামে! লিখছেন দেব রায়…
সাম্প্রতিককালে ভিনরাজ্যে বাঙালিদের বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দেওয়া এবং তাদের বর্ডারের ওপারে ছুড়ে ফেলার বেশ কয়েকটি ঘটনা সামনে এসেছে এবং তা আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই ধরনের ঘটনা একেবারেই নতুন নয়। গত কয়েক বছর ধরেই বিক্ষিপ্তভাবে উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষত দিল্লি এবং এনসিআর রিজিয়নের প্রান্তিক অঞ্চলে, অস্থায়ী বাড়ি বানিয়ে বসবাস করতে থাকা মালদা, মুর্শিদাবাদের বহু গরীব (মূলত মুসলিম) মানুষদের বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবং এই নিয়ে মূলধারার মিডিয়ায় কোনও চর্চা হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ২০২০ সালে উত্তর-পূর্ব দিল্লির দাঙ্গার সময়ে বিজেপি নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয় বাঙালি রাজমিস্ত্রিদের চিঁড়ে (পোহা) খাওয়া দেখে তাদের বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দেন।
ঘটনা শুধু উত্তর ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তা নয়, জল কলকাতা অবধি গড়িয়ে গেছে। কখনও কারমাইকেল হোস্টেলের বাঙালি ছাত্ররা অবাঙালিদের হাতে মার খায়। কখনও রেলওয়ে কর্মী বাংলা বলতে অস্বীকার করে। এমনকী দুর্গাপূজার প্যান্ডেলেও অবাঙালিকে বলতে শোনা যায়, ‘ইধার তো সব বাংলা মে লিখা হ্যায়।’ কাউন্টার কালচার হিসেবে বাঙালি অস্মিতার কোথাও-কোথাও প্রকাশ দেখা যাচ্ছে। বিক্ষিপ্ত ঘটনায় অবাঙালিদের ‘সবক’ শেখানোর চেষ্টা চলছে। কিন্তু এই চেষ্টা বিক্ষিপ্ত ঘটনা হিসেবেই রয়ে যায়। ফলস্বরূপ দুর্গাপূজা উপলক্ষে বিরিয়ানির দোকানের হোর্ডিং নামিয়ে নিতে হয় উত্তর ভারতীয় দাদারা নবরাত্রিতে আমিষ খান না বলে। এইভাবেই বাঙালিরা উত্তর ভারতীয় আধিপত্যের বশ্যতা স্বীকার করতে-করতে ‘এগিয়ে বাড়তে’ থাকে।
‘হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্তান’ ন্যারেটিভের কাছে বাঙালি অস্মিতা কল্কে পায় না। উত্তর ভারতীয় দাদাদের কাছে আমরা বাঙালিরা এখনও মচ্ছিখোর দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এই যে, আমরা বাঙালি শব্দটি ব্যবহার করছি, এর মানে কী। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ‘আসে কারা বাঙালি?’ ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য, ভাষা, উপভাষা, খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদি বদলে যেতে থাকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় গেলেই। সুবিশাল পশ্চিমবঙ্গে তাই সাংস্কৃতিক বিভিন্নতা সহজেই দেখা যায়। কিন্তু এখানেও উত্তর ভারতীয় দাদাদের মতো কলকাতা এবং তৎসন্নিহিত গঙ্গা তীরবর্তী অঞ্চলের দাদাগিরি বিশেষভাবে দেখা যায়।
ছোট শহর থেকে কলকাতায় পড়তে গিয়ে প্রথমেই শুনি, তোরা সারাদিন মুড়ি খাস? তোদের ওখানে সকাল থেকেই চপ ভাজা হয়? শহরে বসবাসকারী এবং শহরের বাইরে বসবাসকারী শহুরে মানসিকতার মানুষজনদের অদ্ভুত ঘেন্না দেখি মুড়ির প্রতি। সকালে মুড়ি খাওয়া যেন গ্রাম্য কু-অভ্যাস। অতিথিকে মুড়ি খেতে দেওয়া মানে অপমান। কলকাতা শহরের মানুষেরা খেয়াল রাখেন না যে— হাওড়া, শিয়ালদা শাখার ছোট-ছোট স্টেশনগুলি, যেমন: যাদবপুর, বাঘাযতীন সন্নিহিত স্টেশন রোডে যে বাজার বসে, সেখানে ভোর চারটে থেকেই মুড়ি-ঘুগনি বিক্রি শুরু হয়ে যায়। শহর এবং গ্রাম-গঞ্জের বহু মানুষ সকালবেলা মুড়ি খান এবং মুড়ি খেতে ভালবাসেন। অনেক মানুষ আছেন, যাদের সকালবেলা লুচি-আলুর তরকারি নিয়ে কোন ফ্যান্টাসি নেই। অনেক মানুষ আছেন যারা ইলিশ মাছ ভালবাসেন না। বলিউডের ছবিতে বাঙালি চরিত্র মানেই— ‘আমি তুমাকে বালুবাসি’ জাতীয় ক্যারিকেচার দেখলে যেমন রাগ হয়, তেমনি সমস্ত বাংলার সমস্ত মানুষকে এক ছাঁদে ফেলে দেওয়ার চেষ্টাকেও ধিক্কার জানাই।
সাংস্কৃতিক বৈষম্য থেকে হয়তো সরাসরি কোনও ক্ষতি হয় না। কিন্তু ক্ষতি হয় যখন রাজনৈতিকভাবেও এই বৈষম্য সুস্পষ্ট হয়ে যায়। প্রসঙ্গত গত ২৩ সেপ্টেম্বরের কলকাতায় মেঘভাঙ্গা বৃষ্টি নিয়ে মিডিয়ার যা তৎপরতা দেখা গেল তার বিন্দুমাত্র দেখা যায় না, যখন প্রতিবছর ঘাটাল-মালদা বন্যায় ভেসে যায়, সুন্দরবন-দীঘা সাইক্লোনে উড়ে যায়, বাঁকুড়া-পুরুলিয়া গরমে পুড়ে যায়। কলকাতায় বৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে পুজোর ছুটি এগিয়ে চলে আসে। অথচ পশ্চিমবঙ্গের বাকি অংশ তখন শুকনো। কিছুদিন আগে যখন পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু জেলা ভেসে যাচ্ছিল তখন ছুটি দেওয়া হয়নি। কলকাতায় গরম বাড়লে গোটা পশ্চিমবঙ্গে ছুটি হয়ে যায়, যদিও উত্তরবঙ্গে সে-সময়ে সে রকম গরম থাকে না।
স্বাভাবিকভাবেই এই চাপিয়ে দেয়ার প্রবণতা যে উৎসব অনুষ্ঠানে পড়বে, তা নতুন কিছু নয়। দুর্গাপূজা নিঃসন্দেহে বিরাট উৎসব। কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন স্থানীয় উৎসব থাকে যা সেই সব অঞ্চলের সবচেয়ে বড় উৎসব। ঘটনাচক্রে যে অঞ্চলে জন্মেছি এবং বড় হয়েছি, সেখানে অনেক দুর্গাপূজা দেখেছি। একটি প্রাচীন অঞ্চল হওয়ার সুবাদে এখানে খুব ছোট এলাকার মধ্যে প্রায় ২০-২৫টি পারিবারিক পুজো অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু আশেপাশের অনেকগুলি গ্রাম ছিল, যেগুলোতে এই কয়েক বছর আগেও দুর্গাপূজা হত না, এখন হয়, সাম্প্রতিক আমদানি বলা যেতে পারে। কলকাতার দুর্গাপূজা শুধুমাত্র ধর্মীয় আচার নয়, এক বিরাট সাংস্কৃতিক যজ্ঞ বলা ভাল। কিন্তু কলকাতার বাইরের সমস্ত জায়গায় এই লিবারাল হাওয়া বর্তমান নয়। আমার আশেপাশের পুজোগুলি পারিবারিক হওয়া এবং আমরা সেই পরিবারগুলির অংশ না হওয়ার কারণে এই পুজো গুলিতে দর্শক হওয়া ছাড়া আর কোনভাবে অংশগ্রহণের উপায় ছিল না। কালেভদ্রে হয়তো কাঁসর বাজানো বা চামর দোলানোর সুযোগ পেতাম। যে সুযোগ কখনও পাইনি তা হল অঞ্জলি দেওয়া। একটু বড় হয়ে টিভি এবং পরবর্তীকালে সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে জেনেছি অষ্টমীর অঞ্জলির রোমান্টিকতা এবং তাকে ঘিরে বিভিন্ন প্রেমের গল্প। অথচ আমাদের ছোটবেলার অষ্টমীর অঞ্জলির কোনও স্মৃতি তৈরি হওয়ার সুযোগই হয়নি।
প্রসঙ্গত গত ২৩ সেপ্টেম্বরের কলকাতায় মেঘভাঙ্গা বৃষ্টি নিয়ে মিডিয়ার যা তৎপরতা দেখা গেল তার বিন্দুমাত্র দেখা যায় না, যখন প্রতিবছর ঘাটাল-মালদা বন্যায় ভেসে যায়, সুন্দরবন-দীঘা সাইক্লোনে উড়ে যায়, বাঁকুড়া-পুরুলিয়া গরমে পুড়ে যায়।
ছোটবেলার বড় উত্তেজনার জায়গা ছিল সপ্তমীর সকালে নবপত্রিকা স্নানের সময়ে নদীর ঘাট অবধি যাওয়া এবং দশমীর দুপুরে নবপত্রিকা বিসর্জনের সময়ে আবার নদীর ঘাট অবধি যাওয়া। কলকাতার পূজায় নবপত্রিকা স্নানে হয়তো কেউ-কেউ যান কিন্তু নবপত্রিকা বিসর্জন নিয়ে কোনও কথা হতে দেখি না। অথচ আমাদের এখানে নবপত্রিকা বিসর্জন বিরাট ব্যাপার। যাদের একটাই নতুন জামা হয়েছে তারা সেটা নবপত্রিকা বিসর্জনের সময় পরবে। বুড়িমার চকলেট বোম, মুড়ি পটকা, হাঁড়ি বোম সবকিছু ওই সময়েই ফাটানো হবে।
নবপত্রিকা বিসর্জন ছাড়াও পূজার আর সবচেয়ে উত্তেজনার অংশ হল ‘খ্যান’। মানে সন্ধিক্ষণ। সন্ধিক্ষণে এখানের পুজো গলিতে বলিদান এর প্রথা রয়েছে। সেই বলিদান দেখারই উত্তেজনা। বলিদান বলতে অবশ্য পাঁঠাবলি নয়। এখানে সবজিবলি দেওয়া হয়। শসা, চালকুমড়ো এবং আখ। সন্ধিক্ষণের মুহূর্তে ‘জয় মা!’ বলে তলোয়ার বা খাঁড়া দিয়ে বলিদান হবে। একখণ্ড সবজি মন্দিরে রেখে দেওয়া হবে। বাকি অর্ধেক নিয়ে ভক্তরা কাড়াকাড়ি করবে। আজ অবধি কোনও সাহিত্য বা কোনও সিনেমায় ‘খ্যান’-এর উল্লেখ দেখেছি বলে মনে পড়ে না।
দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকটি বাংলা ছবিও হয়েছে। ঋতুপর্ণ ঘোষের ‘হীরের আংটি’, ‘উৎসব’ তো আছেই, এছাড়াও ‘জয় বাবা ফেলুনাথ’, ‘পথের পাঁচালী’, ‘দেবী’, ‘পরমা’ ইত্যাদি বিভিন্ন ছবিতে দুর্গাপূজার অনুষঙ্গ এসেছে। এই মুহূর্তে দুর্গাপূজা একটি বিরাট বড় অর্থনীতি। একটি রাজ্যের অর্থনীতি কেন শুধুমাত্র উৎসব নির্ভর হবে সে আবার অন্য তর্ক। কলকাতার থিম পূজার সাথে যেমন বেশ কয়েক হাজার পরিবার রুজি-রুটির ব্যাপারে জড়িত, তেমনি এর সঙ্গে জড়িত জামাকাপড় থেকে শুরু করে চপ-চাওমিন-কাবাব-রোল, ফুল-বেলপাতা, বিউটি পার্লার ইত্যাদি সমস্ত ব্যবসা। নামিদামি ব্র্যান্ডগুলির ক্ষেত্রে তাই পুজোর মরশুম আসা মানেই চমকদার বিজ্ঞাপন। শালিমারের বিজ্ঞাপনটি যেমন ধীরে-ধীরে মহিষাসুরমর্দিনীর মতোই আইকনে পরিণত হয়েছে।
লক্ষ করলে দেখা যাবে, এই যে চমকদার বিজ্ঞাপনগুলি আসে, প্রায় সবগুলি যেন একই টেমপ্লেটে ফেলা। একটি বিরাট বনেদি বাড়ি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অবস্থা পড়তির দিকে। পুজো প্রায় বন্ধের মুখে। হঠাৎ করে কেউ এসে পুজো চালু রাখার সিদ্ধান্ত নেয় এবং হ্যাপি এন্ডিং। এই প্রাণঢালা উৎসবে বারবার। এই সিনেমা, বিজ্ঞাপনগুলির কারণেই কিনা জানি না, আজকাল হঠাৎ এক অদ্ভুত আদেখলাপনা তৈরি হয়েছে বনেদি বাড়ির দুর্গাপূজা নিয়ে। এমনকী কিছু ট্রাভেল এজেন্সি ‘বনেদি বাড়ি পূজা পরিক্রমা’র মতো স্পেশাল প্রোগ্রামও শুরু করেছেন। সেই পরিক্রমা এখন আর শুধুমাত্র কলকাতা শহরে সীমাবদ্ধ থাকে না। শ্রীরামপুর, গুপ্তিপাড়া, ছাড়িয়ে কাটোয়া, কালনা, সুরুল, কৃষ্ণনগর বহুদূর তার ব্যাপ্তি। আজ যেগুলি বনেদি বাড়ি, কয়েকশো বছর আগে সেগুলি ছিল জমিদার বাড়ি এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেই বাড়িগুলির পিছনে রয়েছে রক্তাক্ত শোষণের ইতিহাস। শুধু শোষণের ইতিহাসই নয়, কিছু-কিছু ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকারকে খুশি করে বিভিন্ন খেতাব পাওয়ার অদ্ভুত লালসা। এই মুহূর্তের এই বনেদী বাড়ির প্রতি প্রীতি কোথায় যেন সেই শোষণের ইতিহাসকে ভুলিয়ে দিতে চায়। এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ে যাচ্ছে, ‘পথের পাঁচালী’র দুর্গাপূজার দৃশ্য এবং সেখানে অপু ও দুর্গার সংকোচপূর্ণ অংশগ্রহণ। তবু তো অপু-দুর্গা ব্রাহ্মণ ছিল। ভাবুন তো অপু আর দুর্গা যদি দুলে কিংবা বাগদী হতো?
এই বছরেই ফেব্রুয়ারি মাসে শিবরাত্রি উপলক্ষে বর্ধমানের গিধগ্রামের একটি শিব মন্দিরে নিম্ন বর্ণের মানুষেরা প্রথমবার প্রবেশাধিকার পায়। অনুরূপ ঘটনা ঘটে নদীয়ার বৈরামপুর গ্রামের চড়ককে কেন্দ্র করে। তিন দশকের বেশি বাম শাসনে থাকা পশ্চিমবঙ্গ যতটা লিবারাল হওয়া উচিত ছিল, আসলে ততটা হতে পারেনি হয়তো। কলকাতায় পুজোর প্যান্ডেলে যতই আজান বাজুক, প্রদীপের নীচে এখনও অনেক অন্ধকার।
খিলানওয়ালা দুর্গা দালান, উঠোনে এত বড় নিখুঁত আলপনা, ঝাড়লন্ঠন, লাল পাড় গরদের শাড়ি, সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি, গোবিন্দভোগের সুগন্ধি খিচুড়ি ইত্যাদি নিয়ে মূলধারার সংস্কৃতিতে দুর্গাপূজার যে-ছবিটি আঁকা হয়েছে, তাকে সমস্ত বাংলাভাষীর মনের ছবি ভেবে ফেলা হয়তো ভুল হবে। ছোটবেলায় প্রত্যেকবছর সপ্তমীর সকালে নবপত্রিকা স্নানে যাবার সময় দেখতাম, আমাদের পাড়ারই বহু মানুষ ঘুম থেকে তখনও ওঠেনি। কেউ-কেউ সাইকেলে ঝুড়ি, কোদাল, গাঁইতি নিয়ে সাইকেল নিয়ে কাজে যাচ্ছে। আশ্চর্য হতাম এই ভেবে যে, এরা কেন সপ্তমীর সকালে নবপত্রিকা স্নানে যাচ্ছে না। আমার জানাটুকুই যেসব কিছু নয় এইটুকু বুঝতে অনেক সময় লেগে গেছে। ফি-বছর ঘাটাল, মালদার বন্যা বিধ্বস্ত মানুষেরা পুজোয় অংশ নিতে পারে না। কত পরিযায়ী শ্রমিক পুজোয় বাড়ি ফিরতে পারে না। কত-কত কর্পোরেট রিফিউজি পূজায় ছুটি পাবে না হয়তো। কারও-বা হয়তো আর গ্রামে ফিরতে ভালও লাগে না। আরো বিপুল সংখ্যায় মানুষ থাকে যাদের দুর্গাপূজায় অংশ নেবার অধিকারই নেই হয়তো।
আরও বহু মানুষ আছে যাদের ভাষা হয়তো বাংলা কিন্তু প্রধান উৎসব গঙ্গাপাড়ের ‘আসল’ বাঙ্গালীদের মতো দুর্গাপূজা নয়। শহুরে সংস্কৃতির প্রভাবেই হয়তো আজকাল বেশ কিছু আদিবাসী গ্রামে দুর্গাপূজার প্রচলন হয়েছে যেখানে আদিবাসীরা নিজেদের প্রকৃতি পূজারী বলেন এবং সারনা ধর্মের স্বীকৃতিও চাইছেন। সেখানে এই দুর্গাপূজার প্রচলন ভীষণভাবেই চাপিয়ে দেওয়া সংস্কৃতি। হয়তো কেউ জোর করেনি, কিন্তু সমাজব্যবস্থা তাদের এটাই বুঝিয়েছে যে, এটাই আসল সংস্কৃতি, তোমাদেরটা নয়। তবে এ-কথাও সত্যি যে, অনেক জায়গাতেই এখনও পর্যন্ত মূলনিবাসীরা নিজেদের সংস্কৃতি ধরে রাখার জন্য লড়াই করে যাচ্ছেন। গঙ্গাপাড়ের ‘আসল’ বাঙালিরা যখন পুজোর ছুটি কাটিয়ে বেঙ্গালুরুর ফ্লাইট ধরছেন তখন দুঁড়কু, জাহাজপুর, নোয়াগড়, বড়ুয়াকোঁচা, বারোঘুঁটুর মেয়ে-বউরা মাটির দেওয়ালে গোবর লেপছে। ফুল পাখির ছবি আঁকছে। বাঁধনা পরবের যে আর দেরি নাই গো।