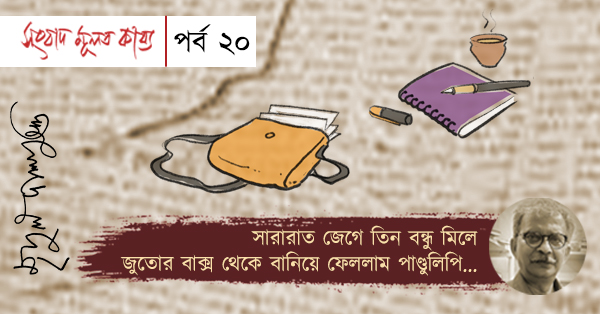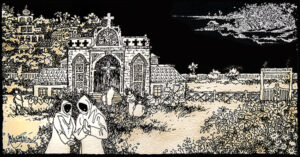‘জলপাই কাঠের এসরাজ’
‘পরিবর্তন’-এর সাংবাদিকের বিরুদ্ধে হুমকি-পুস্তিকা দেওয়া ছাড়া ওই ব্রহ্মচারীর সন্তানপ্রতিম শিষ্যরা আর কিছু না করলেও, ‘আজকাল’ পত্রিকা ভবনটিতে তাঁদের উৎপাত ঘটেছিল ১৯৯৩ সালে, তখন আমি ‘আজকাল’-এ কর্মরত। তবে এ-লেখায় তা বর্ণিত হবে যথাকালে।
‘পরিবর্তন’-এ চাকরি পেয়েই আমি একটু-একটু করে টাকা জমাতে শুরু করেছিলাম। শ্রীরামপুরে একটি ছাপাখানা একেবারে হিসেব কষেই আমাকে জানিয়েছিল, তিন ফর্মার একটি বই ৫০০ কপি ছেপে বাঁধাই করে প্রকাশ করতে ৮০০ টাকা (তৎকালে) লাগবে। ৮০০ টাকা তখন ওই ১৯৭৮/৭৯ সালে অনেক টাকা! আমি টাকা জমাতে শুরু করলাম।
কবিতা আমি লিখতাম যখন হাতের কাছে যে কাগজ পেতাম, সেসব কাগজে। লেখার পর ভাঁজ করে পকেটে রেখে দিতাম। বন্ধুদের, শহরের অগ্রজ কবিতা প্রয়াসীদের পড়াতাম। পকেটে কবিতা পুরনো হয়ে গেলে, জমে গেলে একটি জুতোর খালি বাক্সে রেখে দিতাম। ‘পরিবর্তন’-এ যোগ দিয়ে যখন কাব্যগ্রন্থ বের করার তোড়জোড় করছি, তখন দুটো জুতোর বাক্সয় আমার কবিতা জমে গেছে। কোথাও কবিসম্মেলনে গেলে ওই জুতোর বাক্স থেকে বেছে দু-তিনটি কবিতা নিয়ে যেতাম, আবার বাড়ি ফিরে রেখে দিতাম। কী চমৎকার চমৎকার কবিসম্মেলন হত তখন তমলুকে, মহিষাদলে, কৃষ্ণনগরে, সোনারপুরে, সরশুনায়, এখনকার মতো বাংলা আকাদেমি ছিল না।
আরও পড়ুন: নেতাজী এসেছিলেন কল্যাণীর মাঠে? উত্তেজনায় ছুটে গিয়েছিলাম আমরা! লিখছেন মৃদুল দাশগুপ্ত…
তা ওই দুটো জুতোর বাক্স থেকে একটি রাতে সারারাত জেগে আমার এক রানাঘাটের বন্ধু , হাওড়ার এক বন্ধু আর আমি, আমরা তিনজনায় একটা পাণ্ডুলিপি তৈরি করে ফেললাম। আমার প্রথম সেই কাব্যগ্রন্থের ‘জলপাই কাঠের এসরাজ’ নামটি অবশ্য দু-তিন বছর আগে থেকেই আমি স্থির করে রেখেছিলাম। ওই সময়ে ‘জলপাই কাঠের এসরাজ’ নামে একটি কবিতাও লিখেছিলাম আমি।
জলপাই কাঠ দিয়ে কি এসরাজ তৈরি হয়? আমি জানি না। ‘জলপাই কাঠের এসরাজ’ নামটি আমার মাথায় এসেছিল, অতি সুন্দর কয়েকটি ছবি দেখে। সোভিয়েত ইউনিয়ন দূতাবাসের প্রকাশনী থেকে সে-সময়ে ইংরেজিতে সোভিয়েট ল্যান্ড, বাংলায় ‘সোভিয়েত দেশ’ পত্রিকা বের হত। ঘরে-ঘরে তার গ্রাহক ছিল, আমাদের বাড়িতে আসত ওই পত্রিকা। সেখানেই দেখেছিলাম তৎকালের সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রর আজারবাইজান বা কিরঘিজিস্তানে দীর্ঘ-দীর্ঘ গাছের ছায়ায় রঙিন সাজপোশাকে মানুষজন বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছেন, চারপাশে মুগ্ধ শ্রোতারা। অমনি এক ঝলমলে বাদকের বাদ্যযন্ত্রটিকে মনে হয়েছিল এসরাজ।
‘জলপাই কাঠের এসরাজ’ নামটিতে প্রথম অক্ষর ‘জ’, শেষেও ‘জ’— এতে একটা ধ্বনি জেগে উঠছে, এমনটিতেও পুলকিত হয়েছিলাম।
‘পরিবর্তন’-এ যোগ দিয়ে যখন কাব্যগ্রন্থ বের করার তোড়জোড় করছি, তখন দুটো জুতোর বাক্সয় আমার কবিতা জমে গেছে। কোথাও কবিসম্মেলনে গেলে ওই জুতোর বাক্স থেকে বেছে দু-তিনটি কবিতা নিয়ে যেতাম, আবার বাড়ি ফিরে রেখে দিতাম।
আমাদের সময়ের কবিদের, আমার বন্ধুদের, তখন ওই সময়, মানে ওই ১৯৭৭-৭৮ সালে প্রথম কাব্যগ্রন্থগুলি বেরোতে শুরু করেছিল। কী সব বই! ‘আমাদের লাজুক কবিতা’, ‘কলম্বাসের জাহাজ’, ‘কালক্রম ও প্রতিধ্বনি’। তাই আমারও ইচ্ছে হয়েছিল কবিতার বই বের করার। তাই তোড়জোড় শুরু করেছিলাম। শ্রীরামপুরের প্রেস আমাকে বই বের করার জন্য যে টাকা বলেছিল, তার অর্ধেক মতো টাকা যখন জমিয়েছি, আচমকাই এক কিশোর আমাদের বাড়িতে এসে উপস্থিত হল। আমি কাব্যগ্রন্থ বের করতে চাইছি, এ-কথাটা আমি অনেককেই বলেছিলাম। অল্পবয়সি ছেলেটি কারও মুখে তা শুনে আমার কাছে এসেছিল। বরাহনগরের সিঁথি অঞ্চলে তার বাড়ি, শ্রীরামপুরের লাগোয়া রিষড়ায় তার মামাবাড়ি। মামাবাড়ি থেকেই আমার কাছে সে এসেছে। সবে সে কলেজে ভর্তি হয়েছে, একটি পত্রিকা বের করে। ওই পত্রিকার নামেই প্রকাশনী থেকেই সে বইটি বের করবে। কিশোরটি বলল, আমার বইটি সে বার করবে। বই ছাপতে বাকি টাকা যা লাগবে, সে দিয়ে দেবে। সে প্রকাশক হতে চায়।
তার অল্প বয়স দেখে কিন্তু-কিন্তু ভাব হল আমার। বাকি টাকা কোথায় পাবে সে, মনে হল। তাও সে তাদের সিঁথির বাড়িতে যেতে বলায়, আমি একদিন গেলাম। গিয়ে দেখলাম সে ব্যবসায়ী পরিবারের, মা বাবার একমাত্র ছেলে। ওদের বাড়িতে একতলায় একটি অন্যরকম প্রেস ছিল ওর বাবার। সেখানে প্ল্যাস্টিকের শিটের ওপর ওষুধের লেভেল, সাবানের খাপ, পাউরুটির প্যাকেট এসব ছাপা হয়। ওরা পূর্ববঙ্গীয়। ওর মা-বাবার সঙ্গে বাঙাল ভাষায় বেশ কথা হল আমার। ওর বাবা ছিলেন বিশেষভাবে সক্ষম, হুইল চেয়ারে বসে আক্ষেপ করলেন, ছেলে এই ব্যবসায় না থেকে প্রকাশক হতে চাইছে। হঠাৎই তিনি আমাকে বললেন, তুমি ওকে দেখো। আমার মনে হল, ছেলেটি ‘জলপাই কাঠের এসরাজ’ বের করতে পারবে।
নির্মল হালদারের কাব্যগ্রন্থ ‘অস্ত্রের নীরবতা’র প্রচ্ছদ করে দিয়েছিলেন পূর্ণেন্দু পত্রী, সৈকতের বইয়েরও। সে-সময়ে পূর্ণেন্দু পত্রী, প্রকাশ কর্মকাররা দরাজভাবে আমাদের অনেকেরই কাব্যগ্রন্থের প্রচ্ছদ করে দিচ্ছিলেন। পুরুলিয়ায় নির্মল আমাকে বলল, চল একদিন, পুর্ণেন্দুদা জলপাইয়ের প্রচ্ছদ করে দেবেন। আমি শুনেছিলাম পুর্ণেন্দুদার ছেলে পুণ্যব্রত পত্রী আর্ট কলেজে পড়ে, আমি বললাম, পুণ্য আমার বইয়ের প্রচ্ছদ করে দেবে। পুণ্যর কাছে এ খবর পৌঁছতে সে মহা-উৎসাহে একদিন ওয়েলিংটনে ‘পরিবর্তন’ অফিসে এসে সেই প্রচ্ছদ দিয়ে গেল। রিভার্সে একরঙা প্রচ্ছদ, অলিভ (জলপাই রঙ) রঙে ছাপা হবে। নবদ্বীপ থেকে সে-সময়ের দারুণ লিটিল ম্যাগাজিন ‘অজ্ঞাতবাস’ সম্পাদনা করতেন অরুণদা, অরুণ বসু, তিনি তখন চাকরি করতেন ওয়েলিংটনের অদূরে মঠ লেনে। প্রায়ই তাঁর সঙ্গে আড্ডা হত। সেখানেই ছিল তখনকার কলকাতার সেরা ব্লক তৈরির প্রতিষ্ঠান, অরুণদা সেখান থেকে প্রচ্ছদের ব্লক তৈরি করিয়ে আনলেন। কিন্তু বই ছাপা হচ্ছিল যে ছাপাখানাটিতে, তারা প্রচ্ছদের অলিভ রঙটি দিতে পারল না, সবুজ মতো হয়ে গেল। ১৯৮০ সালের এপ্রিল মাসে বের হয়ে গেল আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ— ‘জলপাই কাঠের এসরাজ’। দাম ৪ টাকা।
ছাপার খরচ আমি অর্ধেক দিয়েছিলাম। আমার বইয়ের সেই কিশোর প্রকাশক আমাকে ৫০০ বইয়ের অর্ধেক কপি দিয়ে দিল। এরপর দুটি বছরে, তখন নবীন বইমেলা, দুটি বইমেলায় সে নিজের হেফাজতে রাখা ২৫০ কপি জলপাই কাঠের এসরাজ বেচে ফেলল। আর এরপর, একদিন আমার বাড়িতে এসে ওই বিক্রি হওয়া বইগুলির রয়ালটি বাবদ আমার প্রাপ্য টাকা দিল। আমার দু’চোখ সজল হল।
‘জলপাই কাঠের এসরাজ’-এর একাধিক সংস্করণ হল। ততদিনে তরুণটি প্রকাশনা গড়ে ফেলেছে। আমার ‘এভাবে কাঁদে না’, ‘গোপনে হিংসার কথা বলি’ কাব্যগ্রন্থগুলি কয়েক বছরে পরপর বের হয়েছে। ‘অমৃত’ পত্রিকায় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় আমার কবিতা প্রকাশ করেছিলেন। আমি নবীন প্রকাশকটিকে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে নিয়ে গেলাম। শ্যামলদা ওকে একটি উপন্যাস দিলেন। ‘প্রতিক্ষণ’-এ লিখতাম, ওকে দেবেশ রায়ের কাছে নিয়ে গেলাম, দেবেশ রায়ও ওকে একটি উপন্যাস দিলেন। দিয়ে বললেন, মৃদুলের সঙ্গে এসেছেন, আমাকে একটি টাকা অগ্রিম দিন।
বছর যত গড়াল, আপাদমস্তক বদল ঘটল সেই কিশোরের। খোলনলচে বদলে যুগোপযোগী হয়ে উঠল সেই নবীন প্রকাশকটি। সদ্যপ্রয়াত সাহিত্যিক প্রফুল্ল রায়ের (যুগান্তরে যখন কর্মরত ছিলাম, তাঁর স্নেহসিক্ত ছিলাম) শেষ বয়সে প্রীতম মুখোপাধ্যায়ের নেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন, ‘বেশিরভাগ প্রকাশকই মেরে দেয় টাকা। উল্টোপাল্টা যা হোক হিসেব দেয়। মেরে-কেটে গোটা তিনেক পাবলিশার অনেস্ট, বাকিরা সব আলু-পটলের কারবারি।’
তখন, সেই ১৯৭৯-৮০ সালেই পরিবর্তনের একটি সংখ্যায় এক লেখক তাঁদের ধর্মের একটি ধর্মগ্রন্থ থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে সমাজ সংস্কারের বিষয়ে একটি লেখা লেখেন। ছোট্ট লেখা, তবু ধর্মীয় মহলে আপত্তি উঠল। বাযফ্রন্ট সরকার, তখন সবে ক্ষমতাসীন, নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দিল ‘পরিবর্তন’-এর ওই সংখ্যাটি।
একদিন লর্ড সিনহা রোড় থেকে কলকাতা পুলিশের দুই গোয়েন্দা অফিসার দুপুর বেলা এলেন আমাদের অফিসে। তাঁদের নিয়ে সম্পাদক অশোক চৌধুরী, সংযুক্ত সম্পাদক ধীরেন দেবনাথ যখন ক্লোজড ডোর মিটিংয়ে বসার জন্য যাচ্ছেন, আমাদের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময়ে, দুই গোয়েন্দার একজন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। আমিও তাঁকে দেখে চিনতে পারলাম, আশিসদা!
উত্তরপাড়া প্যারীমোহন কলেজের আশিস সেনগুপ্ত, আমাদের চেয়ে এক ক্লাস ওপরে পড়তেন, ড্রপ দিয় আমাদের সঙ্গে পার্ট-টু পরীক্ষা দিয়েছিলেন। রিষড়ায় থাকেন। ক্লোজড ডোর মিটিং থেকে আমার ডাক পড়ল। কলকাতা পুলিশ পরিবর্তনের বিরুদ্ধে কোনও মামলা-মোকদ্দমা করেনি।