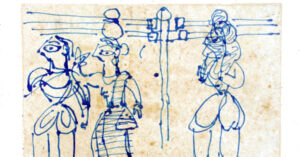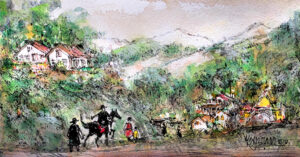আকাশজোড়া কাগজফুল
আমাদের ছোটবেলায় পুজো-পুজো ভাবটা এসে পড়ত মাঝ-সেপ্টেম্বরেই, বিশ্বকর্মা পুজোর হাত ধরে। রিকশা স্ট্যান্ড বা ছোট-ছোট দোকান আর কলকারখানার বাইরে সোনালি মোড়কে মোড়া একহারা প্যান্ডেল, তার মধ্যে দু’হাতে চাঁদমালা ধরে দণ্ডায়মান বিশ্বকর্মা ও তাঁর বাহন হৃষ্টপুষ্ট হাতিটি, সাজানোর সরঞ্জাম বলতে একটা ঘট, কলাগাছ আর কাগজের শিকল। যেটা অনিবার্য, সেটা হল অন্তত একটা লাউডস্পিকার আর তাতে পুজোর নতুন গান। এর সঙ্গে অবশ্যই একখানা গাঢ় নীলচে আকাশ আর তুলোর মতো সাদা মেঘ। এই পুজো শুরু হয়ে গেল। তখনও একটাও নতুন জামা বা জুতো হয়নি, হয়তো চেয়েচিন্তে একখানা পুজোসংখ্যা পাওয়া গেছে, এই অবধি। কিন্তু স্পর্শাতীত অনেক কিছু দিয়েই আসলে পুজোকে ছোঁয়া যেত। তার মধ্যে ওই আকাশ, বাতাসের আশ্চর্য গন্ধ আর পুজোর গানও ছিল।
আর যেটা একরকম আনন্দের নিয়ম হিসেবেই ছিল, সেটা হল ঘুড়ি ওড়ানো। বিশ্বকর্মা পুজোর দিনচারেক আগে থেকে নানান দোকান যে কী চমৎকারভাবে ঘুড়ির পসরায় সেজে উঠত, সে আর বলার না। সেসব দোকান হয়তো সারা বছর অন্যান্য জিনিস বিক্রি করে। কেউ হয়তো বইপত্রের দোকান, কেউ কাঠের আসবাবের দোকান, কেউ মণিহারি দোকান আবার কেউ-বা রোজকার খবর কাগজের স্টল। কিন্তু ওই সময়টায় সক্কলে মিলে ঘুড়ির দোকান হয়ে সেজে উঠত। এ ছিল এক অসাধারণ ব্যাপার। এক পাড়া থেকে অন্য পাড়ায় হেঁটে যেতে গেলে মনে হত, ঘুড়ি দিয়ে বানানো একটা পৃথিবী টহল দিচ্ছি বুঝি। কত রঙের আর কত আকারের ঘুড়ি, সঙ্গে ছোট-বড় সব লাটাইয়ের দল, খদ্দেরের জন্য উন্মুখ হয়ে দোকানে দোকানে বিছিয়ে আছে।
কয়লার উনুনে লুকিয়ে স্মৃতির উপাদান! পড়ুন হিয়া টুপটাপ জিয়া নস্টাল : পর্ব ৪৪…
এখানে বলে নেওয়া ভাল, আমি কোনওদিনই ঘুড়ি ওড়াতে পারতাম না, আজও পারি না। চেষ্টা যে একেবারে করিনি, তা নয়, পাড়ার দাদা-দিদিরাও চেষ্টা করেছে আমাকে সে-বিদ্যে শেখানোর, কিন্তু আমার হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার পর ঘুড়ি কখনওই ‘টেক-অফ’ করেনি, চিরকালই মুখ থুবড়ে ছাদের মেঝেয় আছড়ে পড়েছে। এই তালিম আর ব্যর্থ পারফর্ম্যান্স কয়েক বছর চলেছিল, তারপর আমি নিজে এবং বাকি সকলে হাল ছেড়ে দেওয়ায় আমার ঘুড়ি ওড়ানোর প্রয়াস বন্ধ হয়। কিন্তু নিয়ম ক’রে একটা কি দুটো ঘুড়ি আমাকে কিনে দিতেন বাবা। আজ বুঝি, পারা-না-পারা’র চেয়ে পারতে চাওয়া যে অনেক বড়, তার প্রমাণ ছিল ওই আমার-জন্য-কেনা নিচুমুখ ঘুড়িরা।
দেখেশুনে ঘুড়ি কেনাও যে একরকমের শিল্প, তা বাবাকে দেখে বুঝতাম। বাবাও ভালই জানতেন যে এসব ঘুড়ি আমার হাতে উড়বে না কক্ষনও, শেষমেশ হয়তো অন্যেরাই আমার হয়ে উড়িয়ে দেবে, তাও ভারি খেয়াল করে, মেপেজুকে, বেঁকিয়ে, টেনে, নানা দিক পরখ ক’রে একটা কি দুটো ঘুড়ি আমাকে কিনে দিতেন বাবা। সঙ্গে ছোট একটা লাটাইও থাকত। ওই যে বিশ্বকর্মা পুজোর দু’রাত আগে আমার বালিশের পাশে সঙ্গী হয়ে উঠত দুটো ঘুড়ি, সে-উত্তেজনার কোনও তুলনা আজ আর পাই না। পারব না তাদের উড়ান দিতে, হয়তো কেউ না কেউ তার আকাশচারিতার দাবিদার হবে, তবু যে তারা দুটো রাত আমার পাশে শুয়ে কাটাচ্ছে, এই ছিল স্বপ্নের মতো এক প্রাপ্তি।
ভাল মাঞ্জার জন্য যা যা সরঞ্জাম দরকার সব ওরাই কিনে আনত দোকান থেকে, কিন্তু আসল মন্ত্র ছিল কাচের গুড়ো। ওইটি ঠিকঠাকভাবে সুতোর গায়ে মাখিয়ে রাখতে পারলেই কেল্লা ফতে। এ-বাড়ি ও-বাড়ি থেকে বাতিল বোতল চেয়ে এনে বস্তায় পুরে শিলনোড়া দিয়ে সেসব কাচ ভাঙার কাজ চলত।
আরেকখানা দারুণ মজার ব্যাপার ছিল লাটাইয়ের সুতোর জন্য মাঞ্জা তৈরি করা। এ-বাড়ির ছাদের সঙ্গে সে-বাড়ির ঘুড়ির জবরদস্ত লড়াই হবে। আর কে না জানে, যার সুতোয় মাঞ্জা বেশি, সে-ই কাটবে অন্য সব ঘুড়ি। আর অন্যের ঘুড়ি কেটে দেওয়ার পর তার পতন অনুসরণ করে ঠিক জায়গায় হাজির হয়ে তাকে কুড়িয়ে আনার মধ্যে যে-জয়বোধ, তাও ছিল অতুলনীয়। মাঞ্জা দেওয়ার ব্যাপারে আমি ছিলাম পিন্টুদা আর বুয়াদা-র সহকারী। ওরা দুই ভাই, পোশাকি হিসেবে আমাদের বাড়িওয়ালার দুই পুত্র হলেও, সম্পর্কের হিসেবে নিজের দাদাদের মতোই ছিল। দু’জনেই যুবক তখন, আমি নেহাত কিশোর। তাই জুটে পড়তাম ওদের কাজ সামলাতে।
ভাল মাঞ্জার জন্য যা যা সরঞ্জাম দরকার সব ওরাই কিনে আনত দোকান থেকে, কিন্তু আসল মন্ত্র ছিল কাচের গুড়ো। ওইটি ঠিকঠাকভাবে সুতোর গায়ে মাখিয়ে রাখতে পারলেই কেল্লা ফতে। এ-বাড়ি ও-বাড়ি থেকে বাতিল বোতল চেয়ে এনে বস্তায় পুরে শিলনোড়া দিয়ে সেসব কাচ ভাঙার কাজ চলত। সে এক মহান শিল্প, ধৈর্য যার সহচর। এ-ব্যাপারটা আমার ছোট থেকেই বিস্তর ছিল, তাই সারা দুপুর বস্তা পেটাতে আমার কোনও বিরক্তি ছিল না। বরং বিকেলের দিকে বস্তা খুলে যখন দেখতাম, শরতের পড়ন্ত রোদে হিরের গুঁড়োর মতোই চিকচিক করছে চূর্ণ কাচের ঝাঁক, তখন কারিগর হিসেবে বেশ একটা চাপা গর্ব হতো বৈকি।
কিন্তু এখানেই তো শেষ নয়, সেই গুঁড়ো মাড় আর আঠার সঙ্গে গুলে এক সান্দ্র, ধারালো পদার্থ তৈরি করে সুতোর সারা শরীরে সমানভাবে মাখিয়ে দেওয়া, এইটে ছিল আরও জরুরি। আমাদের সেই বাড়ির আনাচকানাচে অনেক নারকেল গাছ, তাই এ-গুঁড়ি থেকে ও-গুঁড়ি ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে সুতো বেঁধে তাতে মাঞ্জা লাগানোর কাজ চলত। সূক্ষ্ম এই শিল্পে কতবার যে হাত কেটেছে, তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু হাত কাটা মানেই জিনিস ভাল তৈরি হয়েছে। সব শিল্পের পিছনেই যে অনেকখানি রক্তক্ষরণ থাকে, ঘুড়ির মাঞ্জা তার সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

আমার চিরকালই দেরিতে ঘুম থেকে ওঠা অভ্যেস, বিশ্বকর্মা পুজোর ভোরে আমাকে ডেকে তুলত পিন্টুদা আর বুয়াদা, তড়িঘড়ি চোখেমুখে জল ছিটিয়ে গন্তব্য দোতলার বিরাট খোলা ছাদ। আলো ফুটেছে ততক্ষণে, আকাশ জুড়ে কাগজের ফুলের মতো আস্তে আস্তে ফুটে উঠছে আনকোরা সব ঘুড়ি, একটু পরে ছেলেমেয়েদের হইচই আর ‘ভোকাট্টা’ ডাকে ভরে উঠবে পুজোর বাতাস। এই পুরো প্রকল্পেও ততদিনে আমি দক্ষ সহকারী। বাবার কিনে দেওয়া ঘুড়িদুটোও সঙ্গে করে নিয়ে জেতাম, পিন্টুদা আর বুয়াদাই উড়িয়ে দেবে আমার হয়ে। হোক-না অন্যের হাতের কারসাজি, আমারই তো শেষমেশ! এই ছিল ভাললাগা।
মনে আছে, সারা পাড়া, সারা শহরের আকাশ ছেয়ে যেত ঘুড়িতে। একটা সময়ের পর পাখি আর ঘুড়ি আলাদা করা যেত না। বেলা দুটো-তিনটে অবধি এই মাঞ্জার লড়াই চালিয়ে ক্লান্ত হয়ে যে-যার বাড়ি ফেরা, এই ছিল দস্তুর। এ-বছর, এই তো ক’দিন আগে পেরিয়ে গেল বিশ্বকর্মা পুজো। পাড়ার রিকশা স্ট্যান্ডে ছোট্ট একটা প্যান্ডেলও দেখলাম, সঙ্গে লাউড স্পিকারে গান। কিন্তু ঘুড়ি দেখলাম কি একটাও, মেঘ-করে-থাকা কলকাতার আকাশে? মনে হল না। তারপর ভাবলাম, শেষ কয়েক বছরেও কি দেখেছি? যদি বা চোখ মেলে খেয়াল না-ও করে থাকি, ‘ভোকাট্টা’ নামক দলবদ্ধ উল্লাসের চিৎকার কি কানে এসেছে? সেরকমও মনে করতে পারলাম না। আর দোকানগুলো? তারা কেউ বইয়ের দোকান, কেউ মুদির দোকান, কেউ-বা সাজগোজের দোকান হয়ে থেকে গেছে। ঘুড়ির মুখোশে মুখ ঢাকতে আগ্রহী হয়নি কেউ। ঘুড়ি ওড়ানো কি তবে আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গেল? তিনদিন ধরে কাচের গুঁড়ো মাখিয়ে মাঞ্জা দেওয়ার ধৈর্য? বাতাসে মিলিয়ে গেল সে-ও? হবেও-বা। নিজেকে প্রাচীন মনে করার আরেকখানা উপাদান পাওয়া গেল তবে। আমার ব্যর্থ হাত থেকে ভাগ্যিস ঘুড়িগুলো অন্যদের দিয়ে দিয়েছিলাম! তাই আজও বলতে পারি, ওই আকাশজোড়া কাগজফুলের ঝাঁকে আমিও কোথাও ছিলাম একদিন…