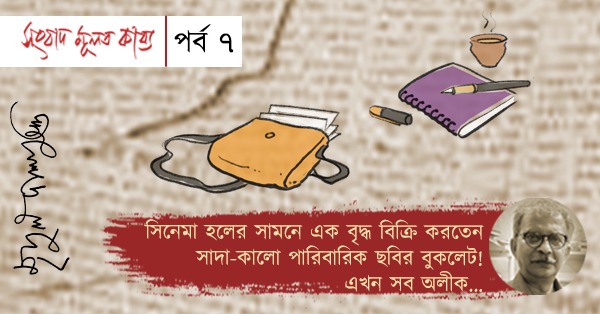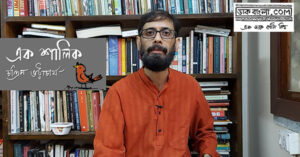মিনি-যুগ
দেশলাই বাক্সের সাইজে, সিগারেটের প্যাকেটের সাইজে, ডিমাই সাইজের অর্ধেকে, লম্বায়-চওড়ায় এমন সব পত্রিকা বের হতে লাগল যখন, আমি কলেজে ভর্তি হওয়ার মাসকয়েক আগে, আমরা খুব মাতামাতি শুরু করলাম। হইহই পড়ে গেল সত্তর দশকের সূচনায়, সেইসব মিনি পত্রিকা নিয়ে। ১৯৭০ সালের জানুয়ারিতে সম্ভবত, নতুন বছরটিতে ‘বিশ্বের প্রথম মিনিপত্রিকা’-র দাবি তুলে বের হল ‘পত্রাণু’, আশিসতরু মুখোপাধ্যায় (পরে এই আশিসদার সহকর্মী ছিলাম আমি, যুগান্তর পত্রিকায়) ও অমিয় চট্টোপাধ্যায়ের (বিশিষ্ট আবৃত্তিকার, ছিলেন আকাশবাণী-তে) সম্পাদনায়। ঝকঝকে পত্রিকা, সত্যজিৎ রায় তার প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন। সাইজ ৪ ইঞ্চি× ২ ইঞ্চি। ‘পত্রাণু’ বের হতেই যেন বিরাট এক দরজা খুলে গেল, কলকাতার উত্তর, দক্ষিণ, মধ্য, পূর্ব, শহরতলি, জেলা-মফসসল, দিগদিগন্ত থেকে বের হতে লাগল মিনি পত্রিকা, অগুনতি।
ছোটদের পত্রিকাও বের হত মিনি সাইজে, সরল দে সম্পাদিত ‘ঝুমঝুমি’ পত্রিকাটি ছিল মিনি পত্রিকা। নকশালপন্থীরা বের করেছিলেন ‘স্ফুলিঙ্গ’ নামে একটি মিনি পত্রিকা। শ্রীরামপুরে আমার বন্ধু পল্লব, পল্লব বন্দ্যোপাধ্যায় বের করেছিল তেমনই পত্রিকা ‘কুহু’। দেশলাই বাক্সের চেয়ে কিছু ছোট আকারে একটি পত্রিকা বের করে দাবি করা হয়েছিল, এই পত্রিকাই ‘বিশ্বের ক্ষুদ্রতম পত্রিকা’। তৎকালীন নামী লেখক-লেখিকা, কবি— সবাই লিখেছেন মিনি পত্রিকাগুলিতে। একটি পত্রিকায় শিবরাম চক্রবর্তীর ছড়া মনে পড়ল, ‘রাজধানী চুপচাপ/ মন্ত্রী পড়ে ধুপ ধাপ/ শুনে সেই শব্দ/ গাছপালা জব্দ।’ একটি মিনি পত্রিকা বিজ্ঞাপন করেছিল, ‘দাম বেড়েছে চিনির/ দাম বাড়েনি মিনির।’ আর একটি মিনি পত্রিকার বিজ্ঞাপন ছিল, ‘এক প্যাকেট সিগারেটের চেয়ে সস্তা।’
মিনি পত্রপত্রিকাগুলির ওই তুঙ্গ সময়ে সত্যজিৎ রায় ‘সন্দেশ’ পত্রিকাটির সাইজ করে দিয়েছিলেন ম্যাক্সি। মস্ত বড় সাইজে, সংবাদপত্রের অর্ধেক আকারে তখন বের হত ছোটদের পত্রিকা ‘সন্দেশ’। তবে খুব বেশি কাল নয়, দু-তিন বছরেই, ধীরে ধীরে মিলিয়ে গিয়েছিল মিনি পত্রিকাগুলি, যেন একটি চলচ্চিত্র শেষ হয়ে গেল।
মর্গে শুয়ে বুলেটবিদ্ধ শম্ভু দাস জানান দিয়েছিল, সে জীবিত! পড়ুন ‘সংবাদ মূলত কাব্য’-র ষষ্ঠ পর্ব…
তবে, ১৯৭০-এ ‘অবাক ফোয়ারা’-র মতো মিনি পত্রিকাগুলি বেরনোর ঠিক মাসখানেক আগে ১৯৬৯-এর ডিসেম্বর নাগাদ আচমকাই সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় বের করেন একগুচ্ছ ‘মিনিবুক’। এক-একটি মিনিবুকে এক-এক জন লেখকের রচনাসম্ভার। হাতে এসেছিল, যখন স্কুলে উঁচু ক্লাসে পড়ি। মনে পড়ছে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা-সংবলিত মিনিবুকটির নাম ছিল ‘লাল রজনীগন্ধা’। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতাগুচ্ছের মিনিবুকটির নাম মনে পড়ছে না। ছিল আল মাহমুদের ‘সোনালী কাবিন’-র কবিতা নিয়ে একটি মিনিবুক, ছিল কমলকুমার মজুমদারের একটি গল্পের মিনিবুক।
এরও আগে মিশনারিরা যে বাইবেল বিলি করতেন, মাও সে তুঙের উদ্ধৃতির রেডবুকটি, পকেট ডিকশনারি, ভাবলে, সেসবও তো মিনিবই।
এই মিনিপত্রিকা, সঙ্গে আরও পত্রিকা দেখা ও কেনার জন্য একেবারে হামলে পড়তাম আমি শ্রীরামপুর স্টেশনের সামনে নন্দন বুক স্টলে। সে ছিল এক অলৌকিক পুস্তক বিপণি। কিশোরবেলায়, সত্তর দশকের সূচনায় যখন নন্দন বুক স্টলে যাওয়া শুরু করি, তখন একদিন, দেখি, রেলের আরএমএস মাঠের বেড়ার রেলিংয়ে সাজানো পুজোসংখ্যা ‘উল্টোরথ’, ‘ঘরোয়া’, ‘প্রসাদ’, ‘নবকল্লোল’ দেখছেন তারাশঙ্কর, বনফুল, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়রা, তখনও তাঁদের চিনতাম না, একটু দূরে দাঁড়িয়ে অমলকাকু, অমলেন্দ্রনাথ ঘটক, শ্রীরামপুরের শিশুসাহিত্যিক ছিলেন, ফিসফিসিয়ে আমাকে বলেছিলেন, ‘দ্যাখ, দ্যাখ, ওই যে উনি, উনি বনফুল, আর ওই যে তারাশঙ্করবাবু…।’ শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরির শতবর্ষে এসেছিলেন তাঁরা। সেই সময় শ্রীরামপুরের বিশিষ্ট মানুষজনের ভেতর ছিলেন কবি হরপ্রসাদ মিত্র, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান ছিলেন, আমি তাঁকে দেখিনি বা মনে পড়ে না।

শ্রীরামপুর স্টেশনের অদূরে ওই নন্দন বুক স্টলে রোজই পত্রপত্রিকার খোঁজে যেতাম যখন, আলাপ হয়ে যায় সমবয়সি একজনের সঙ্গে, একই উৎসাহে সেও যেত নন্দন বুক স্টলে, আমার মতোই সেও উচ্চমাধ্যমিক দিয়ে কলেজে, শ্রীরামপুর কলেজে ভর্তি হয়েছে, বাবা রেলে কাজ করতেন বলে সে থাকত শ্রীরামপুর রেল কোয়াটার্সে। সে, দেবাশিস মুখোপাধ্যায় আমার বন্ধু। এখন সত্যজিৎ-চর্চায় বাংলায় সে বিশিষ্ট গবেষক-লেখক। গভীর অনুসন্ধানী মন তার, বিবিধ বিষয়ে আগ্রহ। ‘আজকাল’ সংবাদপত্রটিতে সে ছিল আমার সহকর্মী। আজকাল তথ্য ও নোটবই-এর কারণে সে সংক্ষেপিত ‘দেমু’ নামে পরিচিত হলেও, আমি তাকে দেবু নামেই ডাকি। এখন চন্দননগরে থাকে, কিছুদিন আগে তার কন্যার বিবাহ অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম।
ভেবে দেখলে, ওই নন্দন বুক স্টল আমার লেখালিখির সূচনাকালের একটি পাঠশালা বলা যায়। তাহলে নন্দন বুক স্টলটি নিয়ে কিছু বলি।
কিশোরবেলায়, সত্তর দশকের সূচনায় যখন নন্দন বুক স্টলে যাওয়া শুরু করি, তখন একদিন, দেখি, রেলের আরএমএস মাঠের বেড়ার রেলিংয়ে সাজানো পুজোসংখ্যা ‘উল্টোরথ’, ‘ঘরোয়া’, ‘প্রসাদ’, ‘নবকল্লোল’ দেখছেন তারাশঙ্কর, বনফুল, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়রা, তখনও তাঁদের চিনতাম না, একটু দূরে দাঁড়িয়ে অমলকাকু, অমলেন্দ্রনাথ ঘটক, শ্রীরামপুরের শিশুসাহিত্যিক ছিলেন, ফিসফিসিয়ে আমাকে বলেছিলেন, ‘দ্যাখ, দ্যাখ, ওই যে উনি, উনি বনফুল, আর ওই যে তারাশঙ্করবাবু…।’
আমি যখন বালক, স্কুলের পঞ্চম-ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ি, তখন দল বেঁধে স্কুল থেকে ফেরার সময় প্রতি বিকেলেই দেখতাম, পথে ‘মানসী’ নামের সিনেমা হলটির সামনে সিনেমার বই বিক্রি করছেন ধবধবে সাদা দাড়িওয়ালা এক অতিবৃদ্ধ, সঙ্গে রয়েছেন এক তরুণ সহকারী। তখনকার দিনে সাদা-কালো পারিবারিক চলচ্চিত্রগুলি মুক্তি পেলেই সিনেমা হলগুলিতে ওই সিনেমার বই পাওয়া যেত। চলচ্চিত্রটির প্রচারমূলক ওই পুস্তিকাগুলিতে সিনেমার কাহিনির ঘনঘটার আভাস দিয়ে কিছু কথার সঙ্গে সিনেমাটির গান ও ছবিটবি দিয়ে বিক্রি করা হত। অনেক দর্শকই কিনতেন। বৃদ্ধের মৃত্যুর পর ওই যুবক ‘মানসী’ সিনেমার সামনের ওই ক্ষেত্রটি ছেড়ে, আরএমএস মাঠের রেলিংয়ে বই পত্রপত্রিকা ঝুলিয়ে বুক স্টলটি সাজিয়ে নেন। আশ্চর্য মানুষটির নাম ষষ্ঠীকুমার নন্দন। পরে তাঁর বুক স্টলটি উঠে আসে কাছেই ডা: চ্যাটার্জি লেনে একটি ঝকঝকে দোকানঘরে। এই নন্দনবুক স্টলটি হয়ে ওঠে পড়ুয়া মানুষজনের বুদ্ধিচর্চার কেন্দ্র। দীর্ঘকায় ষষ্ঠীদা ওই স্টলে বসে বই বিক্রির সঙ্গে সঙ্গে কেবলই বই পড়তেন। ওড়িশায় জন্ম হলেও বাংলায় বসবাসে তিনি বাঙালি হয়ে গিয়েছিলেন। ক্রমে তিনি ওড়িয়া থেকে কিছু কিছু বাংলায় অনুবাদও করেছেন। সেসব অনুবাদ কিছু কিছু বের হয়েছিল ‘অনুবাদ’ পত্রিকায়। আমাকে যেন দেখভাল করতেনই ষষ্ঠীদা। এমনও হয়েছে, শ্রীরামপুর কলেজের এক অধ্যাপক টানাটানি করছেন একটি বই, ছিনিয়ে নিয়ে ষষ্ঠীদা বলেছেন, উঁহু, মৃদুলের জন্য এনেছি এই বই।
অনেকদিনই মারা গিয়েছেন ষষ্ঠীদা। তাঁর ছেলে উদয়ন আর বইয়ের ব্যবসায় যায়নি। ঊর্ধ্বাকাশে মিলিয়ে গিয়েছে নন্দন বুক স্টল।
১৯৬৯-’৭০ সালে আমাদের লেখালিখির সূচনাকালে বাংলা কবিতার আকাশে জ্বলজ্বল করছিলেন পঞ্চাশ দশকীয় কবিরা। ওই বর্ণচ্ছটা সত্ত্বেও আমরা ভিন্নতা অর্জন করেছি, ভাস্কর চক্রবর্তী আমাদের ও পঞ্চাশ দশকীয় কবিদের মাঝে ছিলেন বলে। এই বয়সে বিবেচনা-হেতু এমনটিই মনে করি আমি। অর্থাৎ, পঞ্চাশ দশকীয় তারকাপুঞ্জের প্রভাব বিস্তারিত হল না আমাদের ভেতর, কারণ ভাস্কর চক্রবর্তী একটি দেওয়াল তুলে দিয়েছিলেন ’৫০ ও ’৭০-এর মাঝে। ছন্দহীন হতে চেয়েছিলেন ভাস্করদা, চেয়েছিলেন কবিতার গা থেকে গহনাসকল খুলে ফেলতে। আমরা কেউ-ই তা চাইনি, আমরা সকলেই ছন্দসিক্ত। তবু, ‘শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা’ আলোড়িত করেছিল আমাদের। বইটি ছিল যেন একটি চাবি, যা দিয়ে তালা খুলে আমরা ঢুকে পড়ে ছিলাম কবিতার ধু ধু মাঠে, যে মাঠের শেষেই দিগদিগন্ত।
কলেজে পড়ার সময় প্রায় যেতাম ভাস্করদার বাড়ি, ওই চিলেকোঠায়। ভাস্করদাও কয়েকবার এসেছেন শ্রীরামপুরে, আমাদের বাড়িতেও। আমি যখন কয়েক বছর বরানগরে. ছিলাম, তখন প্রায় দেখাসাক্ষাৎ হত। এখন একটা কথা খুব ভাবি। ভাস্করদার ‘স্বপ্ন দেখার মহড়া’ বের হয়েছিল আনন্দ থেকে। দে’জ থেকে বের হয়েছিল ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’। সাহিত্য অকাদেমি একবার ব্যাঙ্গালোর (তখনও বেঙ্গালুরু হয়নি) নিয়ে গিয়েছিল তাঁকে। রামকৃষ্ণ হেগড়ের সঙ্গে ভাস্কর চক্রবর্তীর ছবি দেখেছি আমি। তবে একটিও পুরস্কার পাননি ভাস্করদা। শঙ্খ ঘোষ খুবই স্নেহ করতেন ভাস্করদাকে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বড়ই অনুরাগী ছিলেন ভাস্করদা। কে না জানে, জীবিতকালে সাহিত্যক্ষেত্রে শঙ্খ-সুনীল দু’জনেরই সর্বমান্যতা ছিল। বড় বিস্মিত হয়েছি। মনে পড়ে গেল, ভাস্করদা লিখেছিলেন, ‘আমি কি চেয়েছিলাম সজ্জিত হয়ে উঠুক জীবন…/ আমি কি চেয়েছিলাম ওইসব ব্রাদার/ আমি কি চেয়েছিলাম, এই…’