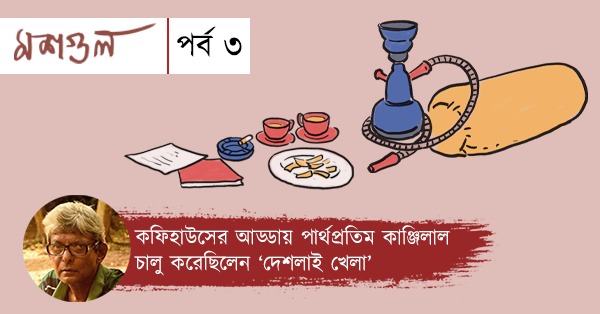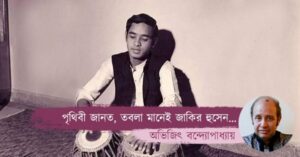কফিহাউসের সেই আড্ডা
শুরু হত মরা বিকেলে, কলেজ স্ট্রিট কফিহাউসের দোতলায়। সোম থেকে শনি, পার্থপ্রতিম, পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলালের নেতৃত্বে। উল্টোদিকের তিনটে খালি চেয়ার আস্তে আস্তে ভরতে থাকে। পুরো ভরে গেলে আশপাশের টেবিল থেকে টেনে জোড়া হয় চেয়ার। লোক বাড়তে বাড়তে ১০/১২, এমনকী, ২২-ও। খাবার বলতে কালো কফি বা ইনফিউসন সঙ্গে পার্থদার প্যান্টের পকেটে রাখা বিড়ি। শার্টের পকেটে আছে বাক্সবোঝাই বিড়ি। সেটা এখানে নয়। কোথায়? সেকথা পরে। তার আগে মনে করার চেষ্টা করি, কারা আসতেন।
প্রসূন, প্রবুদ্ধ, সূর্যদা, অমিতাভ, রণজিৎদা। সিনিয়রদের মধ্যে অরূপরতন বসু বা অরূপদা, ভাস্করদা, খাটো পাজামা, হাতকাটা পাঞ্জাবি, হাতে পাইপ, সদা হাসিমুখ উৎপলকুমার। এছাড়া পার্থদার ঘঞ্চু বা ঘনশ্যাম ওরফে সোমকদা। আমার চাপে পড়ে গৌতম বসু এলে, সবার হাতে ঘুরত ওর অফিস (তাবাক ট্রেডার্স)-এর লম্বা রিজেন্ট। মুখে হালকা বাংলার গন্ধ নিয়ে আসতেন জহরদা, জহর সেনগুপ্ত।
পুরুলিয়া থেকে আসত নির্মল, সঙ্গে ব্যাগবোঝাই কবিতা। পুরন্দরপুর থেকে আসত পার্থদার জানেমন জানে জিগর একু, একরাম। গোড়ার দিকে ২/৪ বার একই সঙ্গে কবি ও কংগ্রেসের মস্তান আজয় সেনকেও দেখেছি। আরও অনেকেই ছিলেন। এতকাল বাদে নাম আর মনে পড়ে না। পার্থদার বাল্যবন্ধু নিশীথদার অফিস তো পাশেই, বাড়িও। কিন্তু কখনও এসেছেন বলে মনে পড়ে না।
আরও পড়ুন : একবারই কামু মুখোপাধ্যায়ের রসিকতা সহ্য করেননি সত্যজিৎ!
পড়ুন বরুণ চন্দর কলমে মশগুল পর্ব ২…
খাবারের কোনও কথা নেই। সেটা কখনওসখনও পুরো ঘেঁটে যেত তুষারদা, মানে তুষার চৌধুরীর মতো কেউ আসায়। ওঁর সম্পাদিত ‘কবিতা দর্পণ’-এ একটা ভাল কবিতা বেরিয়েছে বলে টেবিলসুদ্ধু সবাইকে মাটন স্যন্ডউইচ। তবে এরকম ওই এক-আধবারই। বাকি সময় পার্থদার ধারালো টিপ্পনি, সঙ্গে ঠোঁটচাপা হাসি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কেউ হয়তো বলল, ‘জানেন তো, ওকে সবাই বলছে পুরো জয়েস!’
সঙ্গে সঙ্গে সপাট জবাব, ‘তা তো হবেই! চোখ বুজলেই দেখি, পায়ে বুট, গায়ে ড্রেসিং গাউন আর ভেতরে কিচ্ছুটি নেই, এমনকী, আন্ডারওয়ারও নয়!’
পার্থদার ধারালো বচন ছাড়াও ছিল দেশলাই খেলা। এটা কি পার্থদারই উদ্ভাবিত? জানি না। খেলাটা খুব সহজ! দেশলাই বাক্স পিঠের দিক করে রেখে ছোট্ট টোকা। যদি লেবেলের দিক পড়ে, তাহলে এক পয়েন্ট ও আর-একটা দান। দেশলাই কাত হয়ে পড়লে পাঁচ, খাড়া দাঁড়ালে দশ। এইভাবে যে আগে ২৫ করতে পারবে— তার জিত। বড়রা, বিশেষ করে অরূপদা, অরূপরতনের বকাবকি সত্ত্বেও যে থামতে পারতাম না, তার কারণও পার্থদা। প্রতি দান শুরুর আগে পার্থদা বলে দিতেন, ‘আপনি জিতলে প্রমাণ হবে, অমুক কবির বাপ-মায়ের সত্যি বিয়ে হয়েছিল। আমি জিতলে …’, কথা শেষ না করে ঠোঁট চেপে মিষ্টি করে হাসতেন পার্থদা।

এইখানে প্রথম ইনিংস সেরে দ্বিতীয় ইনিংস প্রেসিডেন্সি কলেজের গাড়িবারান্দায়। কম লোক থাকলে গাড়িবারান্দার বাধাঁনো খোপে, এধার-ওধার করে। আর বেশি হলে সার দিয়ে সিঁড়িতে। এইবার সোমকদা ইত্যাদিরা হাঁটা দিত কলাবাগানে। ছোটন আর ছোটা রাজনের খোঁজে। এরা দু’জনেই চরসের কারবারি। দাম, একটা ছোট বল, এক টাকা ২৫। এর মধ্যে রাজন নাকি পুরাকালের যোগীদের মতো, কাজ করত বোজা চোখে, ধ্যানস্থ অবস্থায়।
চরস নিয়ে এলেই তো হল না, এইবার তাকে পুড়িয়ে ভরতে হবে হাতে রাখা টোব্যাকোর সঙ্গে মিশিয়ে সিগারেটের ফাঁকা খোলে। ভরলেও খাওয়া যাবে না। কেন? কারণ, ক্যাপ্টেনের ইচ্ছেই তাঁর আদেশ। এখন অভিজ্ঞরা ‘চ’-ভরা সিগারেট সামলেসুমলে পকেটে ভরে তীর্থের কাকের মতো তাকিয়ে থাকত পার্থপ্রতিমের দিকে। শুধু অভিজ্ঞ নয়, আমাদের মতো অনভিজ্ঞরাও বাদ যেত না পার্থর কৃপা থেকে।
শুরু হত ম্যাজিক। পকেটের ঝকঝকে এলুমুনিয়ামের কৌটো থেকে বেরতে শুরু করত একের পর এক শুস্তি বা গাঁজা-বিড়ি। পাছে নরম হয়ে যায়, তাই কৌটো। গাঁজা, ছিলিম বা রিফার কি পাইপ খেলেও এই শুস্তির টেস্ট ছিল একেবারে লা-জবাব। আমাদের মল্লিকবাজারে, যাকে বলে ফুলটাইট ফুলছকাস। এরপর চরস। রক্ত টলে যেত মাথায়।
এরপর একটু রাতের দিকে আমরা কয়েকজন হাঁটতাম পার্থদার বাড়ি কৈলাস বোস স্ট্রিটের দিকে। যাবার পথে ক্যাপ্টেনের মুড ভাল থাকলে কপিলাশ্রমের স্বর্গীয় শরবত। দোকানের গায়ে লাগা নোটিসে লেখা— একজনকে তিন গ্লাসের বেশি দেওয়া হবে না।
এটা মাঝেসাঝে হলেও কৈলাস বোসের উল্টোদিকের গলিতে আলুর দম প্রায় রোজই। দোকান তত সাফসুতরো নয়, এটা কেউ জানালে পার্থ বলতেন, ‘যে দোকানে মস্তানরা খায়, সবসময় সেখানে খাবেন, কখনও শরীর খারাপ হবে না।’
এখানেই ঠিক হত, রোববার কোখায় লেখা পড়া হবে। সঙ্গে আড্ডা তো আছেই। সাধারণভাবে প্রসূনের বাগবাজারের বাড়িতে বা অমিতাভর ওয়েলিংটনের দোতলায়। একবার গিয়েছিলাম পছন্দের কবি নিশীথ ভড়ের ২-এ, মাধব দাস লেনের বাড়িতে।
লিখতে গিয়েও সর্বাঙ্গ শিরশির করে, সমুদ্রের ধারে পায়ের তলা থেকে বালি সরে গেলে যেমন, একেবারে সেইরকম। আহা হা! সে এক দিন ছিল আমাদের কৈশোরে কলকাতা!
এই পর্যন্ত পড়ে যদি কারও মনে হয়, এই আড্ডা শুধুই নেশার চক্কর— তাহলে একেবারে ভুল হবে। লেখা, মানে কবিতা প্রায় রোজই পড়া হত। সোমকের মুচমুচে, পার্থর অসামান্য গদ্য শুনেছি। একরাম কি ‘পুনর্বসু’-র গদ্যটা এখানে পড়েছিল? তবে সবসময় যে বাংলা লেখা পড়া হত, এমনটা নয়। অন্তত একবার কাফকার গল্প নিয়ে একটা ইংরেজি প্রবন্ধ পড়েছিলেন রণজিৎ।
এখানেই ঠিক হত, রোববার কোখায় লেখা পড়া হবে। সঙ্গে আড্ডা তো আছেই। সাধারণভাবে প্রসূনের বাগবাজারের বাড়িতে বা অমিতাভর ওয়েলিংটনের দোতলায়। একবার গিয়েছিলাম পছন্দের কবি নিশীথ ভড়ের ২-এ, মাধব দাস লেনের বাড়িতে। আমার চাপাচাপিতে নিশীথদা শুনিয়েছিলেন, প্রায় শোনা যায় না, এমন নরম গলায় প্রিয় কবিতা, ‘শ্রাবণের লোপামুদ্রা’।
এবার একটা গল্প বলা যাক। ইনফিউসন কালো কফির লাস্ট রাউন্ড চলছে। সকলেই ব্যস্ত প্রেসিডেন্সিতে, আড্ডার সেকেন্ড ইনিংসের জন্য। এহেন সময় বাংলাদেশের কবি দাউদ হায়দার (তখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত) হাজির। জানালেন, ‘একটু ওই টেবিলে আসুন।’
‘কী ব্যাপার?’
‘বিলেত থেকে এসেছেন বিখ্যাত কবি সৈয়দ শামসুল হক, আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে চান।’
ডানদিকে একা বসে আছেন শামসুল। ড্রেস শুধুমাত্র ইংরেজি ছবিতে দেখা জিনসের প্যান্ট, জ্যাকেট। লাল ব্যানলনের গেঞ্জি। ঠোঁটে ঝুলছে লম্বা সিগারেট।
—কথা বলতে চাইলে আসতে বলুন।
—না মানে , উনি এত দূর থেকে এসেছেন!
অল্প হেসে পার্থ জানান, ‘তাহলে তো কোনও সমস্যাই নেই। ওঁকে আর-একটু দূর মানে, কষ্ট করে এই টেবিল অবধি আসতে বলুন।’
আমতা-আমতা করছেন দাউদ। সমাধান-সূত্রটা কে বের করল ? একরাম না কি অন্য কেউ? কে জানে! কথাটা সহজ, আপনারা আপত্তি না থাকলে আমাদের সঙ্গে প্রেসিডেন্সির গাড়িবারান্দায় যেতে পারেন।
ওখানে যাবার পর কেউ বলে, ‘আমরা তো এখন গাঁজা খাব! আপনার ওই বিলিতি সিগারেট তো…’

কথা শেষ করার আগেই দু’প্যাকেট স্টেট এক্সপ্রেস হাওয়ায় উড়িয়ে দেন শামসুল। ‘আরে মশাই, গাঁজা খাবার জন্য একবছর হাসপাতালে কাটিয়েছি। আর এই সিগারেট? এটা ভদ্দরলোকে খেতে পারে? দিন দেখি একটা গ-বিড়ি।’
এই পর্যন্ত শুনে এক তরুণ বন্ধু জিজ্ঞেস করলেন, ‘আপনাদের টাইমে খিস্তিখাস্তার তেমন চল ছিল না?’
একেবারেই কি ছিল না?
একদিন পার্থদা বললেন, ‘নাহ্, আর মিনিবাসে চড়া যাবে না।’
—সে কী! কেন?
মনে রাখতে হবে, এইসময় মিনি বেশ কেতাদুরস্ত ব্যাপার। স্ট্যান্ডিং নট অ্যালাউড। এমনকী, মেজাজে সিগারেটও ধরানো যায়। তাহলে?
না, এসব কিছু নয়। ওঁর আপত্তি কন্ডাক্টরের ভাষা নিয়ে।
—ভাবুন, পাশের মিনি আমাদেরটাকে পেরিয়ে যাওয়ার সময় বলে গেল, ধনতলা হাওড়া , ধনতলা হাওড়া। এই অবধি তবু ঠিক ছিল! আমাদের ধর্মতলা হাওড়া মিনি ওকে টপকে যাওয়ার সময় কী বলল, জানেন? ভাবতে পারবেন না! বলল, ধর্মটা ল্যা*ড়া, ধর্মটা ল্যা*ড়া ।