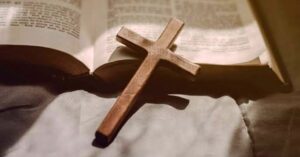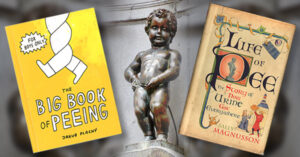এ-কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্রে রয়েছে আপাত পরিসরের বাইরে এক ব্যাপ্তি। এবং সময়। কাল বললে যার অধিবিদ্যক ব্যাপ্তি বোঝা যেতে পারে। সামান্য জীবন যখন সভ্যতার অসামান্য বাঁকবদলে দীর্ণ হয়ে পড়ে, সেই ধ্বংসের জ্যান্ত শোকস্তম্ভ মানুষের আখ্যানকে ঋত্বিক সেই কালচক্রে দেখান। কখনও চরাচরব্যাপী জলভাগ, ক্রমে সভ্যতার হৃত অবশেষ, শুকনো নদীখাত, কখনও হেরো মানুষরা আপাতত টিকে থাকতে চেষ্টা করছে আর তাদের বিক্ষত রক্তাক্ত হাতের মুঠো খালি পিছলে যাচ্ছে জীবনের থেকে। সেখানে দেশভাগের পর বাস্তুচ্যুত হওয়ার বিপুল শোক ও যন্ত্রণাশোক প্রত্যক্ষ, যা তাঁর আখ্যানের বিষয়। এবং এই শোক প্রজন্মাতীত ও স্মৃতিতে জাগরূক।
যেমন শোক জাগরূক, তেমনই প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে গড়িয়ে যায় দুর্মর আশা। কাহিনিতে জীবন শেষ হয়ে গেলেও, জীবন কখনওই এক জীবনে ফুরিয়ে যায় না। এদিকে সমগ্র মালোপাড়া যখন খরায়-ক্ষুধায় একটি প্রাচীন সভ্যতার মতো শেষ হয়ে যাচ্ছে, ‘তিতাস একটি নদীর নাম’-এ ধানের ক্ষেতে ভেঁপু বাজায় একটি দামাল শিশু। কারণ এই গোষ্ঠী মরেহেজে উজাড় হয়ে গেলেও অন্য কোথাও, অন্য কোনও নদীর ধারে ফের অন্য বসতি গড়ে উঠবে। আরেকবার জীবনচক্র শেষ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত। তাই নির্দিষ্ট ইতিহাসে এইসব কাহিনি ঘটলেও, এমনকী দেশভাগের মতো সুনিশ্চিত একটি অভিজ্ঞতা হলেও, ঋত্বিকের ছবিতে একটা চিরায়ত গতিবেগ দেখায়। যা নেই, হবেও না নিশ্চিত, যেমন ধরা যাক নিজেদের বাড়ি, সেইদিকে আখ্যান বেঁকে যায়। বোন সীতার ছেলেকে নিয়ে সুবর্ণরেখা ধরে চলে যেতে-যেতে শিশুটির মুখে তার মামা ঈশ্বর সেই নিজেদের বাড়ির কথা শুনতে পায়। একটা জীবনে যাত্রাপথ ফুরোয় না। এক প্রদীপ থেকে আরেক প্রদীপে আলো চলে যাওয়ার মতো করে প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে চলে আশা। অন্য কোনও রূপে।
আরও পড়ুন: এপিকের ঢং কীভাবে ধরা পড়ে ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ ছবিতে?
লিখছেন অভীক মজুমদার…

এইখানে রৈখিক-একরৈখিক কাহিনিতে একক জীবনের বাইরের কিছু একটা রয়েছে। আর তার মধ্যে রয়েছে চক্রাকার প্রলম্ব। তা মিথলজিক্যাল। যেমন অভিরাম বা সীতার নাম। যেমন অনসূয়া ও ভৃগুর নাম। ‘অসময়ের দিন গনাইয়া আইলাম নদীর পারে’ গায়নকালে ইব্রাহিম বয়াতির ক্যামেরার সামনেও যে আত্মস্থ তুরীয় দশা, তা এক প্রতীকী মারিফতি নদীর পারে অপেক্ষমান এক সত্তা। তেমনই তাতে ছেড়ে আসা নদীগুলির ঢেউ গায়ে এসে লাগে। রিফিউজি বাড়ির তুচ্ছ মেয়েটির সংসার টিকিয়ে রাখার অদম্য লড়াই তো প্রাত্যহিকী। কোনও আর্কাইভের গোপন তাকের অনাবিষ্কৃত ফাইল ঘাঁটার দরকার পড়ে না নীতাকে খুঁজতে। সে কলকাতার রিফিউজি কলোনি হোক বা জেলায়-জেলায় ইস্ট পাকিস্তান থেকে আগত শরণার্থীদের একের পর এক পাড়া— প্রতিটি পরিবারে নীতা উপস্থিত।
এইখানে এটিও খেয়াল করার যে, পাঁচ ও ছয়ের দশকে রিফিউজি পরিবারগুলি ক্রমে কলকাতায় আসার প্রাবল্যে মহানগরের ভেঙে-পড়া ব্যবস্থায় সংসারের হাল ধরতে বাড়ির বউকে বা বোনকে চাকরি খুঁজতেই হয়। কিন্তু শরণার্থী প্রায় প্রতিটি পরিবারের যে-নীতা, সে তার থেকেও অন্যতর কিছু। সে-ই টুকরো করে দেওয়া বঙ্গভূমি, বিখণ্ডিত বঙ্গবালা। আর অন্যদিকে সে-ই বাপের আদরের মেয়ে। বাবা এখন সম্বলহীন। মেয়েকে অরক্ষিত দেখে যন্ত্রণা পান, ‘অ্যাকিউজ’ করে যান, কিন্তু কাকে ‘অ্যাকিউজ’ করবেন ভাগ্যকে ছাড়া!


যেমন ঈশ্বর ‘সুবর্ণরেখা’-য়, তেমনই ‘মেঘে ঢাকা তারা’-য় পিতৃস্নেহের রূপ বড়দাদা শঙ্কর প্রজন্মভেদে ধারণ করে নেয়। নীতার সঙ্গে মিলে যায় মাতৃকাকে ঘরের মেয়ে ধরে নেওয়ার অপূর্ব মিথীয় ভক্তি-প্রণোদনা। ক্যামেরা নীচু অ্যাঙ্গেল থেকে নীতার মুখ ধরে নিয়ে যে একটা পেডেস্টালের আবহ তৈরি করে, তাতে নীতা তার জেদ নিয়ে, ক্লান্ত ও ঘর্মাক্ত শরীর নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। দর্শক বুঝতে পারে, মেয়ে থেকে দেবী এই আবহমানতায়, দেবী ভগবতীর এই দুর্দশায় আমরা আরেকবার মা কী ছিলেন, আর কী হইয়াছেন— এই অন্ত্যমিলে ফিরে এলাম, যদিও এ এক অন্য প্রবর্তনায়। ভিটেমাটি হারানো বাবার স্নেহ দিতে অপারগতা, মেয়েকে তার ঘরে স্বামী-সন্তান সহ থিতু করতে না পারার গ্লানি, অন্য এই প্রবর্তনায় রয়েছে। যে-গ্লানিতে দষ্ট হয় দাদা শঙ্করও। কিন্তু যখন এই সমাজবদলের ‘বিলডুংরোমান’ (শিক্ষিত হওয়ার আখ্যান) হয়ে ওঠে, সেখানে সে-ই নির্বাচিত হবে উপযুক্ত চরিত্র হিসেবে; যার পথ চলে যাবে সামনে, শুধুই সামনে।
তাই কাহিনিগুলিতে উমা হোক কি দুর্গা বা সীতা, আখ্যানের গড়িয়ে যাওয়ার পথে যথাসময়ে তাদের এলিমিনেশন ঘটে। কারণ এই চলায় তাদের নায়কোচিত দীপ্রতা ধারণ করতে তৈরি করা হয়নি। এক তো এই পৃথিবী জানে না দুর্গার দৃষ্টিক্ষুধা ও স্বাদতৃষ্ণা, যা তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় কাঁচা উন্মুক্ত প্রকৃতিতে, তাকে নিয়ে ঠিক কী করা যাবে। ‘কী নিষ্ঠুর লেখক!’ বলার সঙ্গে-সঙ্গে আমরা কি প্রকারান্তরে বিভূতিভূষণকে কৃতজ্ঞতা জানাইনি? দুর্গার অসময়ে মৃত্যু না লিখে, যদি তার আমূল দ্বিধাহীন আনন্দময় বালিকার শারীরিকতাকে বিয়ে-শ্বশুরঘর-সন্তানাদি দিয়ে বলগা দেওয়া হত, যে পোষ মানানোর গল্প আমাদের চারিদিকে এত প্রচুর, তাতে আরেকখানা নামহীন নাম যোগ হত বই আর কিছু সাধিত হত না। দুর্গার চরিত্রে এত তীব্রতা থাকলেও, সে তো আর অপু হয়ে একাকী ভ্রমণে বেরিয়ে যেতে পারে না। বারণ করলেও, মায়ের প্রহার পেলেও সে যে যাবেই, এই জেদ তার বা আখ্যানের কোনও কাজে লাগে না।

নীতার ক্ষেত্রে এক্ষুনি বললাম বটে জেদ কিন্তু ফিরে ভেবে দেখলাম, নীতার মনোভঙ্গি জেদের নয়। নীতা ফলাফল। কোনও সিদ্ধান্ত তার নয়। দেশভাগের ফলাফলের ঘানি সে বয়ে বেড়ায় শুধু। সে দেশভাগের প্রকৃত ভিকটিম। সীতার ভবিতব্যের ক্ষেত্রে যেমন কাহিনিকে জাতপাত ও কয়েকবার স্থানচ্যুতির স্তর পেরিয়ে যেতে হয়েছে, সেই তুলনায় নীতার পরিস্থিতি অনেক সরাসরি। সুযোগ বুঝে নেওয়া নির্মম মা, সম্পূর্ণ নিস্ক্রিয় অসহায় অপারগ বাবা, স্নেহপূর্ণ অথচ অকেজো বড়দাদা, নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্য দিদির প্রেমিককে কবজা করে নেওয়ার মতো জাঁকজমকপূর্ণ আবেদনময়ী ছোটবোন গীতা, সংসারের যূপকাষ্ঠে নিবেদিত নীতার মনের গভীরতা না বুঝতে পেরে চটকায় ডুবে বিশ্বাসভঙ্গকারী প্রেমিক/বাগদত্ত সনৎকে দিয়ে নীতাকে ক্রমে কোন ঠাসা করে এই চরিত্রের ভিকটিমহুড তৈরি হয়। শেষে আসে এই দশকগুলির অবধারিত রাজরোগ টিবি এবং স্যানাটোরিয়ামে ক্রমে ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া নীতা দেশভাগের পরে বেঁচে থাকার গ্রাসাচ্ছাদনের ভয়াবহ অনিশ্চয়তা, কুটিল স্বার্থপরতা, আগের জীবনের সাধারণ সম্ভ্রম হারিয়ে ফেলার প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়ায়। হাহাকার হয়ে দাঁড়ায়। উমার চিরবিদায় অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।
নীতার কি প্রাণোচ্ছলতা আছে? গীতার যৌন আবেদনময় প্রগলভতার পাশে এই যে নীতা স্থির তার গাম্ভীর্য নিয়ে, তা তার পিষে যাওয়ার, হেরে যাওয়ারই প্রতিলিপি। যেহেতু তার পালাবার পথ নেই, তাই সে সবটুকু ক্লেশ ও হতাশা গিলে দিন কাটায়। তার কোনও জগৎ আছে বলে আমরা জানতে পারি না। নীতার জন্য, স্বভাবতই, এই মামুলি ও শ্বাসরোধকারী পরিসর থেকে অন্যত্রে কোনও এস্কেপ রুট নেই। যা শঙ্করের থাকতে পারে, বা আছেই। আর তা সম্ভব হয়েছে নীতার আত্মত্যাগেই।

এখানে তাই সমীকরণটি স্পষ্ট। যেমন ইফিজেনিয়াকে পিতা আগামেমনন বলি না দিলে ইজিয়ান সাগরে হাওয়া বইবে না, গ্রিসের রণপোত ট্রয়ের দিকে এগোতে পারবে না— তেমনই নীতার ভিকটিম হওয়ার সক্ষমতার ওপর দাঁড়িয়ে আছে এই সংসারের ভেসে থাকার সম্ভাবনা। যেন তা মিথোজীবিতায় নিষ্পন্ন। একদিকে তা শঙ্করের। নীতার সংগীত-পারঙ্গমতাকে কাহিনিতে কোনায় পাঠিয়ে মূক না করলে, শঙ্করের সংগীতশিল্পী হওয়া সাধিত হবে না। তাই শঙ্করকে শিল্পী হতে এগিয়ে দিয়ে শুধু পরিবারের হাল ধরে না নীতা, সে একটি প্রক্রিয়ার অন্য পিঠে নিজের কিছু গুণাবলি নিজেই ধ্বংস করে বটে। কারণ একমাত্র তার আত্মবিনাশই এই পরিবারের সদস্যদের উদ্বর্তন ঘটাবে। যেমন সনতের গীতার দিকে এগিয়ে যাওয়ার শর্তই হল নীতাকে একেবারে অস্বীকার। একটা নৈকট্যের ইতিহাসকে অস্তিত্বহীন করে দেওয়া।
এই হল ব্যক্তি নীতার কাহিনি। আর যখন ছবিটি শেষ পর্যায়ে আসে? এই সমস্ত পৃথিবী যখন ফুলে-ফলে ভরা, নীতা শিলং পাহাড়ে স্যানাটোরিয়ামে; টিবি হলে যখন বাঁচার সম্ভাবনা একেবারে ক্ষীণ, তখন যেমন হয় আর কি! এত সহমর্মী দাদা, যে এই বোনটিকে চেনে, তার আত্মত্যাগকে সম্মান করে, সে কি করে গীতা-সনতের ছেলের দৌরাত্মের কথা চোখের পাতা একটুও না কাঁপিয়ে নীতাকে বলে যায়, যখন নীতার দিনগুনতি আয়ু? যখন এরা নীতারই বাগদত্ত ও বোন, এবং যে সন্তানকে নীতা কামনা করেছিল? এই সিকোয়েন্সে আমাদের ভয়াবহ অস্বস্তি হতে থাকে। প্রায় দম বন্ধ হয়ে আসে এই আচরণকে অসংবেদী ভেবে। যদিও আমরা জানি, শঙ্কর না বললে পরিবারের কথা নীতার জানতে পারার কথা নয়। আর এই কথা পর্দায় জোরে-জোরে উচ্চারণ হলে, তবেই-না এই পরিস্থিতির ক্রূরতা টের পাওয়া যাবে! তবেই-না স্বল্পভাষী-সংযত নীতা জীবন-আকাঙ্ক্ষাকে ঘোষণা করে দেবে পাহাড়ে-পাহাড়ে, ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে!
এইখানে মেয়েটির এই নীচু হওয়া, সেফটিপিন লাগানো, এটা একটা নতুন বৃত্ত তৈরি করে। আর ভিকটিমহুড ছকে তাকে সম্পূর্ণভাবে রাখাই যায় না। সেই বৃত্তে ব্যক্তি নীতারা শেষ হয়ে যেতে পারে। তবে আমরা তো জানিই, ঋত্বিক ব্যক্তি নীতার বাইরে আমাদের একটা কালের কাহিনির দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু সেখানে তখনও তারা ভিকটিম। তাদের জন্য বিশুদ্ধ করুণায় শঙ্করের মন ভরে উঠতে থাকে। কিন্তু এ-দৃশ্য শুধু করুণা উদ্রেককারী নয়।
আখ্যানের প্রয়োজনে শঙ্করের এই না-ভেবে-করে-বসা নিষ্ঠুরতা দিয়ে আমরা কিন্তু শঙ্করকে বিবেচনা করি না। বোনের মৃত্যুর পরে সে পাড়ায় ফিরে এলে আমরা তার শুকনো শোকাচ্ছন্ন মুখ দেখি। সবাই জানে, ভাগ্য এই শান্ত মাইয়ার প্রতি অবিচার করেছে। সে চটি ফটাশ-ফটাশ করে রোজ কাজে যেত, আর তার দিনমান সেই দিয়ে নিক্তি মেপে ফেলেছিল। তার জীবন শেষ হয়ে গেছে।
এইবার একাকী ব্যক্তি নীতার জীবন শেষ হলেও, সময়ের চক্র ফিরে আসে ঋত্বিকের নিজস্ব আখ্যান-চেতনায়। যেমন পিতৃগৃহ থেকে বিদায় নিয়ে উমার হিমালয়ে ফিরে যাওয়ার নকশায় নীতা গেছিল পাহাড়ের স্যানাটোরিয়ামে, তেমনই সে নিজেও একটি নতুন ক্রিয়া। তারই প্রতিধ্বনিতে আমরা কলোনির পথে আরেকটি মেয়েকে কাজে যেতে দেখি। তার চটি ছিঁড়ে যায়। সে নীচু হয়ে সেফটিপিন লাগায়। এও আরেকজন বলিপ্রদত্ত, এই ভেবে শঙ্কর নিজের বোনের প্রতি, এই মেয়েটির প্রতি মায়ায় কাঁদতে থাকে। আর আমরা একটা ব্যক্তিভিত্তিক জীবন থেকে ঋত্বিক কীভাবে শরণার্থী সমাজের সামগ্রিক দৃষ্টান্ত তৈরি করলেন, সেটা দেখতে থাকি।
অবশেষে এইখানে মেয়েটির এই নীচু হওয়া, সেফটিপিন লাগানো, এটা একটা নতুন বৃত্ত তৈরি করে। আর ভিকটিমহুড ছকে তাকে সম্পূর্ণভাবে রাখাই যায় না। সেই বৃত্তে ব্যক্তি নীতারা শেষ হয়ে যেতে পারে। তবে আমরা তো জানিই, ঋত্বিক ব্যক্তি নীতার বাইরে আমাদের একটা কালের কাহিনির দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু সেখানে তখনও তারা ভিকটিম। তাদের জন্য বিশুদ্ধ করুণায় শঙ্করের মন ভরে উঠতে থাকে। কিন্তু এ-দৃশ্য শুধু করুণা উদ্রেককারী নয়। এই দৃশ্য বলে, জনপথে নীতাদের স্রোত আর থামবে না। আর সেই অদম্য প্রজন্মের মেয়েদের নিশানা ওই একখানা সেফটিপিন। দুর্ভাগ্য ও ভিকটিমহুডের চিহ্ন না হয়ে এই সেফটিপিন কি এই প্রজন্মের রিফিউজি পরিবারের মেয়েদের জেদ ও প্রাণোচ্ছলতার নিশানা নয়?
‘মেঘে ঢাকা তারা’-র কাহিনির চক্রগতির কাঠামোয় শঙ্কর তাই নীতা বা এই চটি-ছিঁড়ে-যাওয়া মেয়েটির দুর্দশাই শুধু দেখতে পায়। এর দুর্দশার দিনলিপির মধ্যে ক্রমে যে হার-না-মানা মানসিকতা তৈরি হয়, আসলে যা রিফিউজি পরিবারের মেয়েদের মধ্যে প্রজন্ম-পরম্পরায় বয়ে যেতে থাকবে, তার ইশারা ‘মেঘে ঢাকা তারা’-য় শেষ অবধি অলক্ষিত ও অধরা থেকে যায়।