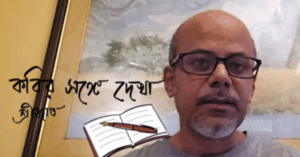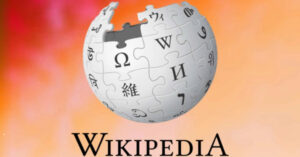শবর জাতি তথা সম্প্রদায় তথা গোষ্ঠী কতটা প্রাচীন, তা আজ অনেকেই ততটা জানেন না। তথাকথিত আদিবাসী জনজাতি ও মূলনিবাসীদের নিয়ে নানারকম ভ্রান্ত প্রচার আজও অব্যাহত। কিন্তু ইতিহাস ফিরে দেখাও তাই আজ জরুরি হয়ে পড়ছে।
বৈদিক সাহিত্যের প্রাচীনতম রচনা ‘ঐতরেয় ব্রাহ্মণ’ গ্রন্থে শবরগণের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় (৮/৩/৫) অসুর-রাক্ষসদের সমসাময়িক হিসাবে। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্দশ শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে রচিত আদিকাব্য ‘রামায়ণ’-এ মহর্ষি বাল্মীকি আমাদের ‘শবরীর প্রতীক্ষা’-র কথা শুনিয়েছেন। আবার ওই যুগেই মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ রচিত মহাকাব্য ‘মহাভারত’-এও শবরদের কথা উল্লেখ করেছেন। মহাভারতের যুগে শবরদের এক পূর্বসূরি ‘জরাসুর’ শ্রীকৃষ্ণের হন্তারক ছিলেন।
খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক প্লিনি-র ‘ইন্ডিকা’ গ্রন্থে, দ্বিতীয় শতকের গ্রিক পণ্ডিত টলেমির ভাষ্যে শবরদের বিশেষ উল্লেখ আছে। সহস্র বৎসর আগের সহজিয়া বৌদ্ধ সাহিত্য সম্ভার ‘চর্যাপদ’-এ (দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে সংকলিত) জনৈক ‘শবরপাদ’ নামে এক সিদ্ধাচার্য ও দেবী পর্ণশবরীর কথা বলা হয়েছে। চর্যাপদের ২৮ ও ৫০-সংখ্যক গীতি ‘শবরপাদানাম্’ নামে চিহ্নিত। এই শবরপাদের প্রণীত দু’টি গীতিগ্রন্থও আছে ‘মহামুদ্রজ্রগীতি’ ও ‘চিত্তগুহ্য গম্ভীরার্থ গীতি’, এখানে যে পর্ণশবরীর কথা বলা হয়েছে, তাঁর প্রসঙ্গেও জানা যায় যে, তিনি শবরদের মতোই ব্যাঘ্রচর্ম ও পত্রবল্কলে ভূষিতা এবং বজ্রকুণ্ডলধারিণী, আপস্মারদলনী, আর একজন শবর দেবীর কথা জানা যায়, যার নাম জাঙ্গলী, ইনি সর্প ও সংগীতের দেবী, বীণাবাদিনী। ‘স্কন্ধপুরাণ’-এর কাশীখণ্ড, দন্ডীর ‘দশকুমারচরিত’, বাণভট্টের ‘হর্ষচরিত’, কবি বাকপতির ‘গৌড়বাহ’ প্রভৃতি রচনায় শবরদের কথা জানা যায়।
আরও পড়ুন: আরবি-ফারসি ছাড়া বাংলা ভাষা হয় না, বলেছিলেন প্রমথ চৌধুরী!
লিখছেন অনল পাল…

‘মীমাংসা দর্শন’-এর ভাষ্যকারের নাম শবরস্বামী, প্রবাদ আছে জৈনদের থেকে দূরে থাকবার জন্য তিনি শবরদের বেশ ধরে শবর বসতিতে বাস করেছিলেন।
বাণভট্টের ‘হর্ষচরিত’ থেকে জানা যায়— হর্ষবর্ধন তাঁর হারিয়ে যাওয়া বোন রাজশ্রীর অনুসন্ধানে বন থেকে বনে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তখন তিনি ‘নির্ঘাত’ নামে এক শবর যুবকের সন্ধান পেয়েছিলেন। বিন্ধ্য পর্বতের শবর সেনাপতির ভাগ্নে সে, নির্ঘাত অরণ্যভূমির গাছ-পাতা সব চিনত। তাকে মনে হত পাহাড়ের চলমান তমালবৃক্ষ (জঙ্গ মমিব গিরিতট-তমালপাদপম্) কিংবা বিন্ধ্য পর্বতের গলন্ত লৌহসার (অয়ঃ সারমিব গিরেবিন্ধ্যস্য গলন্তম্)।
‘কাদম্বরী’-তে বাণভট্ট শবর সৈন্যদের ভয়ংকর মৃগয়া-অভিযানের বর্ণনা করেছেন। একজন বৃদ্ধ শবর কেমন করে নির্দয়ভাবে শুকপক্ষীদের হত্যা করেছিল (জীর্ণ শবরঃ পিবন্নিবাস্মাকমায়ুংষি), তারও বিবরণ আছে সেখানে। আরও জানা যায় যে, শবর রমণীরা ফুলে ফুলে নিজেদের সজ্জিত করতে ভালবাসত (শবরসুন্দরী-কর্ণপূর রচনোপযুক্ত পল্লবস)।
একাদশ শতাব্দীতে সোমদেব-রচিত ‘কথাসরিৎসাগর’-এর একটি কাহিনিতে শবরদের উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজা শ্রীদত্ত তাঁর হৃত স্ত্রী-র অনুসন্ধানে বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। তখন তিনি এক শবর-গোষ্ঠীপতির দেখা পান। শবরাধিপ রাজাকে তাঁর গ্রামে নিয়ে যান। পথশ্রমে ক্লান্ত রাজা সেখানে ঘুমিয়ে পড়েন এবং জেগে দেখেন তিনি বন্দি হয়েছেন। এইভাবে কয়েকদিন থাকার পর শবরপতির এক দাসী তাঁকে জানান যে, শবরপতি কিছুদিনের জন্য বাইরে গেছেন (কার্যাসিবদ্ধসহ সহি ক্কাপি প্রয়াতঃ শবরাধিপঃ, ১০/১৪১) এবং তিনি ফিরে এসে রাজাকে চণ্ডিকার উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন। শবরের দাসী রাজার মুক্তির একটি উপায় বলে দিলেন। রাজা দাসীর কথা শুনে ‘শবরপতি’-র কন্যাকে গান্ধর্ব মতে বিয়ে করলেন (সুন্দরী নাম শবরাধীপতেঃ সুতা) এবং শবরের স্ত্রী তাঁকে স্নেহবশত মুক্ত করলেন।
এমন নানা গল্পকথায় গড়ে উঠেছে শবর জাতির ইতিহাস, ভদ্রলোক সমাজের অনেকটাই অগোচরে যা রয়ে গিয়েছে। নিরন্তর অবহেলা তো আছেই, আজ যখন জাতি-প্রশ্ন নতুন করে দেখা দিচ্ছে ভারতজুড়ে, তখন শবরদের এই ইতিকথা আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। আর্য-অনার্য নিয়ে নতুন করে ঐতিহাসিক প্রতর্কের জন্ম হওয়ার কালে তাই কিছু কথা ফিরে দেখা প্রয়োজন।
‘কাদম্বরী’-তে বাণভট্ট শবর সৈন্যদের ভয়ংকর মৃগয়া-অভিযানের বর্ণনা করেছেন। একজন বৃদ্ধ শবর কেমন করে নির্দয়ভাবে শুকপক্ষীদের হত্যা করেছিল (জীর্ণ শবরঃ পিবন্নিবাস্মাকমায়ুংষি), তারও বিবরণ আছে সেখানে। আরও জানা যায় যে, শবর রমণীরা ফুলে ফুলে নিজেদের সজ্জিত করতে ভালবাসত (শবরসুন্দরী-কর্ণপূর রচনোপযুক্ত পল্লবস)।
শশিভূষণ দাশগুপ্ত ‘বিশ্বভারতী’ পত্রিকায় ‘বাংলা ও বাঙালী’ প্রবন্ধে লিখেছেন, ‘আর্য জাতির যে কিছু কিছু লোকের আগমন ঘটিয়াছিল বাংলাদেশে তাহাদের ভিতরে কোল জাতিই ঐতিহাসিকদের চোখে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। আজকের দিনেও আমাদের জাতি, সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে কোল উপাদান একটা প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছে। এই আদিম কোলগণের ভিতরে শবর, পুলিন্দ, ডোম, চন্ডাল প্রভৃতি এই চর্য্যার যুগে সমাজের একটি বৃহৎ অংশ অধিকার করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। চর্যাগুলির ভিতরে সেই জন্যই তাহার এত প্রধান হইয়া দেখা দিয়াছে।’
উনবিংশ শতাব্দীর সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক-পুরাতাত্ত্বিক মেজর জোনারেল স্যর আলেকজান্ডার কানিংহাম, ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের চিটিয়া নাগপুরের কমিশনার এডওয়ার্ড ট্যুইট ডালটন, ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের হিউবার্ট হিউয়েট রিলে প্রভৃতি পণ্ডিতগণ শবর গোষ্ঠীর সম্বন্ধে বহু অনুসন্ধান করে কালানুক্রমিক বিবরণী দিয়ে গেছেন। শবররা সর্বত্রই অন্ত্যজ বলে অভিহিত হয়ে এসেছে। আবার প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ জি. এ. গ্রিয়ারসন ১৯৬০ সালে ‘লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অফ্ ইন্ডিয়া, ভল. ৪’-এ লিখেছেন কোল বা মুন্ডাজাতীয় উপজাতিগুলি এদেশে এসেছিল দক্ষিণ-পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও মালয় উপদ্বীপ অঞ্চল থেকে। সেক্ষেত্রে ভারতের মূল ভূ-খণ্ড এদের আদি বাসভূমি নয় বলেই ধরে নেওয়া হয়েছে। এই ভাবনার কারণ, ভাষাগত সাদৃশ্য। ভারতের মুন্ডা বা কোলারিয়ান আদিবাসীদের ভাষার সঙ্গে ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলির ও মালয় উপদ্বীপের আদিবাসীদের ভাষার মূল কিছু সাদৃশ্যের ওপর নির্ভর করে অনুমান করা হয়েছে কোলারিয়ানরা ভারতের প্রাচীনতম অধিবাসী।
১৯১৬ সালে মানব জাতিতত্ত্বের বিশেষজ্ঞ আর. ভি. রাসেল ‘ট্রাইবস্ এন্ড কাস্ট অফ্ সেন্ট্রাল প্রভিন্সেস অফ্ ইন্ডিয়া ভল-১’-এ আবার শারীরিক ও ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ রেখে ভারতের অমিশ্র আদিবাসীদের প্রধানত দু’টি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন—দ্রাবিড়ীয় ও কোলারিয়ান (কোল ও মুন্ডা পরিবারভুক্ত)। শবররা এই কোলারিয়ান বা মুন্ডা পরিবারভুক্ত উপজাতিগুলির মধ্যে অন্যতম উপজাতি হিসেবে পরিচিত। পরবর্তীকালে, ১৯৪৪ সালে ভেরিয়ার অলউইন বৃহত্তর অর্থে কোলারিয়ান উপজাতিগুলিকে প্রোটো-অস্ট্রোলয়েড জাতিসমূহের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।
ভারতে আর্য সভ্যতার আরম্ভকাল থেকে সাহিত্যে শবরদের যে জীবন চিত্রিত হয়েছে, সেখানে পুরাকালে এদের জীবনযাত্রার বাস্তব পরিচয় ফুটে উঠেছে যা আমরা আগে দেখেছি। আধুনিক নৃ-তাত্ত্বিকগণ নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে এই পরিচয়কে বিশ্লেষণ করে জানতে পেরেছেন বৈদিক যুগেই শবরেরা আদিম জীবন অতিক্রম করে একটি পরিপূর্ণ সামাজিক জীবন-যাপন করত। এদেশে পাওয়া প্রাচীন ধ্বংসপ্রাপ্ত স্তূপ, পাথর, পোড়ামাটির ফলক প্রভৃতি থেকে তাদের সাংস্কৃতিক জীবন কত উন্নত মানের ছিল, তাও জানা যায়।
উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে নৃ-বিজ্ঞানী, প্রত্নতাত্ত্বিক, ভাষাতাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিকগণ প্রাচীন সাহিত্যের ইতিহাসের উপাদানগুলিকে অবলম্বন করে ভাবতে শুরু করলেন, শবরদের প্রকৃত পরিচয় কী। ভারতের আদিবাসী হিসাবে এদের প্রকৃত পরিচয় কী? প্রাচীন ভারতের কোন কোন অঞ্চলে এদের বসবাস ছিল? বর্তমানের শবর এবং পৌরাণিক শবররা কি একই উপজাতি? আর্যগণ, সকল অরণ্যবাসী অনার্যদের ‘শবর’ নামে চিহ্নিত করত কি না ইত্যাদি প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজা শুরু হয়েছিল।

এ-বিষয়ে আলেকজান্ডার কানিংহাম তাঁর ‘রির্পোট অফ্ ট্যুর ইন্ দ্য সেন্ট্রাল প্রভিনসেস্ এন্ড লোয়ার গানজেটিক ড্যোব ইন ১৮৮১-৮২’-তে একটি উল্লেখযোগ্য দিক তুলে ধরেন, তিনি দেখান, আদিবাসীদের মধ্যে শবরদের যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। আবার তিনি প্রাচীন সাহিত্যে এখনকার প্রধান উপজাতিগুলির উল্লেখ না দেখে বললেন যে, সাঁওতাল, মুন্ডা, ভূমিজ, কোল, ভীল, জুয়াং, হো প্রভৃতি কোলারিয়ান উপজাতিগুলি সম্ভবত সামগ্রিকভাবে ‘শবর’ নামে পরিচিত ছিল।
উপনিবেশের দৃষ্টিতে ইতিহাসকে দেখার যে মুশকিল, তা এক্ষেত্রে বিদ্যমান। মোদ্দায় আমরা অনুমান করতে পারি, আদি মানুষরা বর্তমানের মতো এত বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল না। সে সময়ে শবররা একটি সমৃদ্ধ অনার্য জাতি হিসেবে পরিচিত ছিল। পরবর্তীকালে শবর এবং অন্যান্য জাতিগুলি ভিন্ন ভিন্ন নামে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। এরাই হল সাঁওতাল, কোল, মুন্ডা, ভূমিজ, হো ইত্যাদি। এদের মধ্যে একটি শাখায় ‘শবর’ এই মূল নামটি থেকে যায়। শবররা ক্রমশ সমৃদ্ধি হারাতে থাকে এবং অন্যান্য শাখাগুলি উন্নত ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে।
এর ওপর আছে আর্যদের অনার্য জাতিগুলির ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠার বিরামহীন চেষ্টা। শবরদের সংরক্ষিত নিজস্ব ভাষায় যৎসামান্য দুর্লভ সূত্র ধরে জাতিতত্ত্বের সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারলেও, বর্তমানের শবরদের পর্যক্ষেণ করে অতীতের সামগ্রিক পরিচয়ে পৌঁছনোর তেমন সুযোগ নেই। ইতিহাসের গর্ভে শবররা হারিয়ে গিয়েছে এভাবেই। তাদের দেবী নিয়ে সস্তার হরর হোক, বা নানাবিধ ইতিহাস বিকৃতির মধ্যে প্রকৃত অতীত কতটা রয়েছে, তা আজ অনেকেই আর জানেন না।
পরিশেষে বলার, এখনও স্বাতন্ত্র্য বজায় আছে, এমন শবরদের খুঁজে বের করার জন্য ফ্রেড ফাওচেট, এডগার থারস্টন, সতীন্দ্রনারায়ণ রায়, জি. ভি. সীতাপতি, ভেরিয়ার এল্যুইন নানা প্রদেশের পাহাড়-বনাঞ্চলে অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন এবং শুধুমাত্র ওড়িশার পাহাড়-অরণ্যের গভীরে এক শ্রেণির শবরের সন্ধান তাঁরা পান, যাঁরা পরস্পর খুবই বিচ্ছিন্ন এবং এদের সাংস্কৃতিক জীবনের পরিধিও সংকীর্ণ।