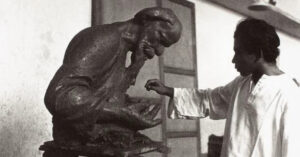‘পথের পাঁচালী’এবং ‘অপরাজিত’ একদিকে যেমন দু’টি আলাদা উপন্যাস, একইসঙ্গে এটি একটিই ধারাবাহিক কাহিনি। অপুর জীবনের পথটিকে পথের দেবতা সাজিয়ে রেখেছেন আশ্চর্য, অসামান্য, নিষ্ঠুর, নির্বিকার অথবা প্রত্যাশিত সব মৃত্যু দিয়ে। অপুর জীবনের পথকে সামনে এগিয়ে দিয়েছিল যে-সমস্ত মৃত্যু, বিভূতিভূষণের মৃত্যুবার্ষিকীতে সেই মৃত্যুগুলিকে আরেকবার মনে করে নেওয়া যাক।
ইন্দির ঠাকরুণ, দুর্গা, হরিহর, অনিল, সর্বজয়া, অপর্ণা এবং লীলা; শুরু করা যাক প্রথম থেকেই।
‘পথের পাঁচালী’, ‘অপরাজিত’এই দুই উপন্যাসকে নানাভাবে পড়া যেতেই পারে, তবে যদি একে একটিই ধারাবাহিক অপু-কাহিনি হিসাবে ধরা হয়, তাহলে সেই আখ্যানে, অপুর জন্মের আগে যেটুকু অংশ পাওয়া যায়, তার সমস্তটুকুই মোটামুটিভাবে এই কাহিনির পটভূমি। ঠিক কোন পরিস্থিতি, পরিবেশ, প্রতিবেশে অপু জন্মাচ্ছে, তার বেড়ে ওঠার সূত্রপাত; সেই বিষয়কে আরও স্পষ্ট করে তোলার জন্যই অপুর জন্মের আগের অংশটুকু লেখা। তবে এও ঠিক যে, সেই আগের অংশটুকু লিখতে গিয়ে অপুর বাবা, ঠাকুরদা ইত্যাদি পূর্বপুরুষদের কথা লিখলেই চলে যেত, পিসিমা ইন্দিরকে নিয়ে আসার প্রয়োজন তবে কী? গল্প-উপন্যাসে মহিলা চরিত্রদের যদি কিছুটা গভীরভাবে না দেখানো হয়, তবে সেই সময়-সমাজ ঠিক কেমন ছিল তা বোঝা খানিক কঠিন হয়ে পড়ে। গ্রামের সাধারণ মানুষদের, বিশেষ করে মহিলাদের জীবনকে যদি খুব কাছ থেকে লক্ষ করা হয়, তাহলে সেই পরিবার, পাড়া, সেই চৌহদ্দি, জনপদ কেমন আছে, বুঝতে কিছু বেশি সুবিধা হয়। উপন্যাসে ইন্দির ঠিক সেই কাজটাই করে থাকেন। ইন্দির ঠাকরুণের জীবনের একেবারে অন্তিমপর্বে জন্মাচ্ছে অপু; এ হল সেই সমাজ, যে-সমাজে স্বামী কোনওমতে বিবাহ করে স্ত্রীকে ফেলে রেখে চলে যান; সেই সমাজে উদারতা নেই।
আরও পড়ুন: ‘জন-অরণ্য’ আমাদের বুকে ঢেলে দেয় এক কঙ্কাল-ক্লান্তি, আর অসহায়তা! লিখছেন চিন্ময় গুহ…
সর্বজয়া-ইন্দিরের সম্পর্কেও সেই অর্থে কোনও উদারতার লেশমাত্র ছিল না একদা, তবে সে অবশ্যই দারিদ্র্যের কারণেই। ফলে ইন্দির ঠাকরুণের জীবনটা আসলে পাঠকের কাছে অপু-পূর্ববর্তী জীবনের পারিবারিক এবং সামাজিক দুই স্তরের সমস্যা, যন্ত্রণার দিকগুলিকে স্পষ্ট করে তোলে। কিন্তু এ কথাও সত্য যে, উপন্যাসের সেই কাজটুকু মিটে যাবার পরে ইন্দিরের আর তেমন কোনও প্রয়োজন থাকে না। যদিও এই নিষ্প্রয়োজনের কথাটুকু খানিক নিষ্ঠুরই শোনায়, তবু কোন গ্রামে, কোন পরিসরে জন্মে, সেই সংকীর্ণতার টানাপোড়েন, যন্ত্রণার ক্ষুদ্র জীবনকে অতিক্রম করে এক সুবিশাল জীবনের ডাকে বাইরে বেরোবে অপূর্বকুমার রায়, সেইটা বোঝার প্রয়োজন রয়ে যায়। এইখানেই উপন্যাসে ইন্দিরের ভূমিকা, সেই ভূমিকা ফুরোলে বিভূতিভূষণ ডেকে আনেন মৃত্যু।
‘এই ভিটার ঘাসটুকু, ঐ কত যত্নে পোঁতা লেবু গাছটা, এই অত্যন্ত প্রিয় ঝাঁটাগাছটা, খুকি, খোকা, ব্রজ পিসের ভিটা—তার সত্তর বৎসরের জীবনে এ সব ছাড়া সে আর কিছু জানেও নাই, বুঝেও নাই। চিরকালের মতো তাহারা আজ দূরে সরিয়া যাইতেছে।’ (‘পথের পাঁচালী’, মিত্র ও ঘোষ, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ২৩)
‘নিশ্চিন্দিপুর গ্রামে সেকালের অবসান’-এর পর থেকে কাহিনি যেভাবে এগোয়, সেখানে দুর্গা এবং অপু, দু’জনকেই যত্নে, ক্রমে-ক্রমে সৃষ্টি করেছেন বিভূতিভূষণ। ‘পথের পাঁচালী’, ‘অপরাজিত’ বিশেষভাবে অপু-কাহিনি হলেও, সর্বজয়া অথবা হরিহর তাঁদের পুত্রসন্তানটিকেই স্পষ্টত বেশি ভালবাসলেও বিভূতিভূষণ ‘আম-আঁটির ভেঁপু’-তে অতি যত্নে বর্ণনা করেছেন দুর্গাকে, কার্পণ্য করেননি যথাসাধ্য মায়াবীভাবে তাকে সৃষ্টি করতে।
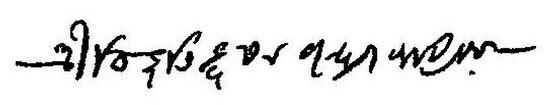
নিশ্চিন্দিপুর গ্রামে দুর্গার সমবয়সি, বাকি মেয়েগুলির থেকে এই নিতান্ত অগোছালো দুষ্টু মেয়েটি যে অন্যরকম, সারাদিন রোদে-জলে, দিনে-রাতে, বনপথে ঘুরেফিরে ফুল-ফল খুঁজে বেড়ানোতেই যার আনন্দ, ভাইয়ের প্রতি যার শিশুমনে অগাধ স্নেহ, তা বুঝতে পাঠকের অসুবিধা হয়নি। কিন্তু ক্রমে-ক্রমে তারও যাওয়ার সময় হয়ে আসে, আকাশে-বাতাসে, প্রকৃতিতে, এমনকী দুর্গার মনেও তারই ইঙ্গিত আসে,
‘দুর্গা আজকাল যেন এই গাছপালা, পথঘাট এই অতি পরিচিত গ্রামের প্রতি অন্ধিসন্ধিকে অত্যন্ত বেশি করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিতেছে। আসন্ন বিরহের কোন্ বিষাদে এই কত প্রিয় গাবতলার পথটি, ওই তাহাদের বাড়ির পিছনের বাঁশবন, ছায়াভরা নদীর ঘাটটি আচ্ছন্ন থাকে। তাহার অপু—তাহার সোনার খোকা ভাইটি, যাহাকে এক বেলা না দেখিয়া সে থাকিতে পারে না, মন হু-হু করে—তাহাকে ফেলিয়া সে বহুদূর যাইবে!’ (‘পথের পাঁচালী’, মিত্র ও ঘোষ, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ১০৯)
অতঃপর মৃত্যু মুহূর্ত উপস্থিত হয়, দীর্ঘ দুর্যোগের রাত্রি পার করে, প্রকৃতিতে যখন বৃষ্টির আর লেশমাত্র থাকে না, চারপাশে যখন গভীর শরৎ, তেমনই এক সকালে ‘অজানার ডাক’-এ সাড়া দিয়ে দুর্গা অনন্তে হারিয়ে যায়। বিভূতিভূষণ মৃত্যু-মুহূর্তের বর্ণনা সেরে ফেলেন অনায়াস নিরুদ্বেগে। শোক ব্যক্তিগতভাবে যত গভীর প্রভাব-বিস্তারীই হোক না কেন, কাহিনিতে মৃত্যুর পরের মুহূর্তগুলিকেও তিনি মিশিয়ে দেন স্বাভাবিকতায়। জলরঙের কাজের মতো অনেকগুলি চিরকালীন অনুভূতি মিলেমিশে শান্ত হয়ে আসে।
তবু চঞ্চল, গাছপালার মতোই সহজ, ছোট্ট মেয়েটির মৃত্যু হলে পাঠকের মনকেমন করে, কিন্তু এ কি অস্বীকার করা যায় যে, ‘পথের পাঁচালী’, ‘অপরাজিত’ বিশেষ করে অপুরই কাহিনি, তাঁরই কথা লিখতে বসেছেন বিভূতিভূষণ। অথচ দুর্গার উপস্থিতি-পর্বে দুই ভাই-বোনের মধ্যে সেভাবে কখনও পক্ষপাতিত্ব করেননি বিভূতিভূষণ। কিন্তু দুর্গার মৃত্যু যদি না হত, সেক্ষেত্রে ‘পথের পাঁচালী’-র মধ্যে দুর্গার একটি উপকাহিনি তৈরি হত। কিন্তু এই উপন্যাসের গতি কেবলমাত্র অপুকে ধরেই এগিয়ে চলে একরৈখিকভাবে। তিনি লিখতে চেয়েছেন ‘অপূর্ব’র অপূর্ব কাহিনি। এই গেল দ্বিতীয় মৃত্যুর কথা।
দুর্গার মৃত্যু না হলে এমন দ্রুত সিদ্ধান্তে হরিহর তাঁর পরিবারসহ বহুকালের ভিটা ছেড়ে অন্য জায়গায় হয়তো চলে যেতেন না। কিন্তু নিশ্চিন্দিপুরের নিরাপত্তার নিভৃত গণ্ডিটুকু থেকে অপুকে বার করে সম্পূর্ণ অচেনা পরিবেশে এনে ফেলার মত বয়স হয়েছে তার ততদিনে। শুরু হয় কাশীপর্ব।
হরিহরের পরিবারের কাশীতে কাটানো প্রথম কয়েকটি দিন কিছুটা স্বস্তিতে কেটেছিল। নিশ্চিন্দিপুরের অভাবনীয় দারিদ্র সাময়িকভাবে যেন কেটেই যায়। এই সময়ে বিভূতিভূষণের ‘তৃণাঙ্কুর’ দিনলিপির কয়েকটি পঙক্তি বড় বেশি করে মনে পড়ে। বিভূতিভূষণ লিখছেন,
‘সেইদিক থেকে দেখতে গেলে দুঃখ জীবনের বড় সম্পদ; দৈন্য বড় সম্পদ; শোক, দারিদ্র্য, ব্যর্থতা বড় সম্পদ, মহৎ সম্পদ। যে জীবন শুধু ধনে মানে সার্থকতায়, সাফল্যে, সুখে-সম্পদে ভরা, শুধুই যেখানে না চাইতে পাওয়া, শুধুই চারিধারে প্রাচুর্য্যের, বিলাসের মেলা—যে জীবন অশ্রুকে জানে না, অপমানকে জানে না, আশাহত ব্যর্থতাকে জানে না, যে জীবনে শেষ-রাত্রের জ্যোৎস্নায় বহুদিন-হারা মেয়ের মুখ ভাববার সৌভাগ্য নেই, শিশুপুত্র দুধ খেতে চাইলে পিটুলি গোলা খাইয়ে প্রবঞ্চনা করতে হয়নি, সে জীবন মরুভূমি। সে সুখসম্পদ-ধনস্মপদ-ভরা ভয়ানক জীবনকে আমরা যেন ভয় করতে শিখি।’ (‘তৃণাঙ্কুর’, মিত্রালয়, তৃতীয় সংস্করণ, প্রকাশকাল অনুল্লেখিত, পৃষ্ঠা ৬-৭)
যে-নিরাপত্তা, আর্থিক স্থিতি অধিকাংশ মানুষের জীবনের প্রধানতম কাঙ্ক্ষিত বিষয়, বিভূতিভূষণ সেসবের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন না তো বটেই, বরঞ্চ তার ঠিক বিপরীত অবস্থান ছিল তাঁর। শোক-ব্যর্থতা-অপমানহীন, সুখসম্পদভরা জীবন যে মরুভূমি, সে কথা তিনি বিশ্বাস করতেন; তাঁর অপুকে যে তিনি সেই ‘ভয়ানক’ জীবন দেবেন না, এ কথা বলার অপেক্ষা থাকে না। ফলে এইবার সময় আসে হরিহরকে সরিয়ে নেওয়ার। হরিহরের কাছেই অপূর্ব পড়াশোনা শেখার সূত্রপাত। নেহাৎ সাধ্যাতীত না হলে যথাসম্ভব পুত্রের এটা-ওটা আবদার, তা বই হোক কিংবা ইশকুলের কাগজে লেখা ছাপাবার খরচ, অনেক সময়ে এমনকী সর্বজয়ার চোখ এড়িয়েও মিটিয়ে এসেছে সে। অপু সারাজীবনে সবচেয়ে বেশি নির্ভর করেছে তার বাবাকে। অপুকে আগলে রাখার এমন নিরাপদ আশ্রয়কে দীর্ঘকালের জন্য রেখে দেওয়ার মানুষ বিভূতিভূষণ নন। এই পথ অপুর নির্জন এককের পথ।

দরিদ্র পরিবারের মৃত্যুগুলি মূলত অসুখের পথে, বিনা চিকিৎসাতেই এসেছে। হরিহর মারা গেলে মণিকর্ণিকার ঘাটে তাকে দাহ করার সময়ে যে-সত্যের সম্মুখীন অপু হয়, সে তার জীবনের পাথেয়।
‘যে বাবাকে সকলে মিলিয়া আজ মণিকর্ণিকার ঘাটে দাহ করিতে আনিয়াছিল, রোগে, জীবনের যুদ্ধে পরাজিত সে বাবা স্বপ্ন মাত্র—অপু তাহাকে চেনে না, জানে না—তাহার চিরদিনের একান্ত নির্ভরতার পাত্র, সুপরিচিত, হাসিমুখ বাবা জ্ঞান হইয়া অবধি পরিচিত সহজ সুরে, সুকণ্ঠে প্রতিদিনের মতো কোথায় বসিয়া যেন উদাস পূরবীর সুরে আশীর্বাচন গান করিতেছে—
কালে বর্ষতু পর্জন্যং পৃথিবী শস্যশালিনী…
লোকাঃ সন্তু নিরাময়ঃ…’ (‘পথের পাঁচালী’, মিত্র ও ঘোষ, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ১৮৪)
ধনসম্পদ, আনন্দ-উল্লাস, সাফল্যে নয়, বেদনার পাথেয়তেই পথের দেবতা ভরে রেখেছেন অপুর যাত্রাপথ।
হরিহরের মৃত্যু অপুকে সম্ভবত প্রথমবারের জন্য জীবনের অপরিহার্য বাস্তবের মুখোমুখি এনে দাঁড় করায়। এই ক’দিন আগে যে-শিশু হাতে একখানি বাঁকা কঞ্চি নিয়ে আপনমনে বকবক করতে করতে হেঁটে বেড়াত বনপথে, তাকে রাতারাতিই ভাবতে হয় অর্থসঙ্কটের কথা। তবু এরপরেও ছেলের সমস্ত বোকামি আর সারল্যের সময়ে ঢাল হয়ে দাঁড়াবার জন্য ছিল সর্বজয়া। পারিবারিক ঝড়ঝঞ্ঝাগুলি যেন তার সন্তানের উপরে এসে না পড়ে, সেই চেষ্টা সচেতনভাবে করে গেছেন সর্বজয়া। অপুর জীবনের এই অধ্যায়ে একইসঙ্গে এক উঠোন লোকের সামনে মার খাওয়ার মতো ঘটনা যেমন ঘটে, আজীবনের বন্ধু লীলার সঙ্গে আলাপও তো এই সময়েরই কথা। হরিহর জীবিত থাকলে এই বহুমূল্য মানবিক অনুভূতিগুলি এ-সময়ে অপুর জীবনে না ঘটার সম্ভাবনাই ছিল বেশি।
মনসাপোতা থেকে বিদ্যালয়-পর্ব শেষ করে কলকাতায় পড়তে আসার পরে সহস্র প্রতিকূলতা, বাসস্থানের অভাব, প্রবল আর্থিক সংকটের মধ্যে অপূর্ব জীবনানন্দে অপুর প্রথম যৌবনের দিনগুলি যখন অতিক্রান্ত হচ্ছিল, সে-রকম সময়েই আলাপ হয় বন্ধু অনিলের সঙ্গে। সেই অনিল, যে কিছুটা অপুরই মতো, কল্পনাপ্রবণ, দূর পথে পাড়ি দেওয়ার স্বপ্ন দেখে সারাক্ষণ, ক্রমাগত কলকাতায় থাকতে-থাকতে অপুর মতোই যার মন হাঁপিয়ে ওঠে। যে-সব আশ্চর্য ভাবনা এতদিন নিজের মধ্যেই জমা করে রেখেছিল অপু, অনিলের সঙ্গে আলাপ হয়ে সেসব কথা বলার লোক জোটে। তবে ‘পথের পাঁচালী’ পড়তে-পড়তে এগোতে শুরু করলে, পাঠক জানেন এই সম্পর্কের একটিই পরিণতি ধার্য করবেন বিভূতিভূষণ। কারণ ‘পথের দেবতা’ যার জন্য একা পথ চলা নির্ধারণ করে রেখেছেন, সেই পথের বৈচিত্র ভাগ করবার একজন সঙ্গী জুটিয়ে দেবেন, এমন উদার মানুষ তিনি নন। ফলে যা হবার তাই হয়। অকস্মাৎ অসুস্থ হয়ে, অপুকে বিস্মিত করে মৃত্যু হয় অনিলের। সেই মৃত্যু-রাত্রে শ্মশানে তারা ভরা আকাশের নিচে বসে, কী অসামান্য অনুভূতির মুখোমুখি হয় অপু।
‘অপু মনের মধ্যে কোনও শোক কি দুঃখের ভাব খুঁজিয়া পাইল না—কিন্তু মাত্র তিনদিন আগে কোম্পানীর বাগানে বসিয়া যেমন অনিলের সঙ্গে গল্প করিয়াছিল, সারা আকাশের অসংখ্য নক্ষত্ররাজির দিকে চাহিয়া বাল্যে নদীর ধারে বসিয়া সন্ধ্যার প্রথম নক্ষত্রটি দেখিবার দিনগুলির মত এক অপূর্ব, অবর্ণনীয় রহস্যের ভাবে তাহার মন পরিপূর্ণ হইয়া গেল—কেমন মনে হইতে লাগিল, কি একটা অসীম রহস্য ও বিপুলতার আবেগে নির্বাক নক্ষত্রজগৎটা যেন মুহূর্তে মুহূর্তে স্পন্দিত হইতেছে।’ (‘অপরাজিত’, মিত্র ও ঘোষ, ২০১৪, পৃষ্ঠা ৮৮)
কলকাতায় কাজ আর ব্যস্ততার মধ্যে অপুর আজন্মের সঙ্গী সর্বজয়ার সঙ্গে সম্পর্কের সেই তীব্র বন্ধন অপুর দিক থেকে ক্ষীণ হয়ে আসতে শুরু করে। সেই মা-এর সঙ্গে সারাক্ষণ খেলতে চাওয়া অপুর নিজস্ব জগৎ সর্বজয়াকে মনে মনে ব্যথিত, দুর্বল, অসুস্থ করে তোলে। কিন্তু অপুর পথে তিনি যেন কোনওমতেই বাধা না হয়ে দাঁড়ান, সে-ভাবনাও সর্বজয়ার ছিল। তবু ছুটিছাটায়, টাকাপয়সার ভীষণ টানাটানির মধ্যেও মায়ের কাছে কখনও দায়িত্ববোধ থেকে, কখনও মনকেমন করায় ছুটে এসেছে অপু। মা অপুর সবচাইতে বড় পিছুটান যখন, তাঁর মৃত্যুও অনিবার্য।
মনসাপোতার ঘরে একাকী মৃত্যু হয় সর্বজয়ার। তবে সে মৃত্যু তেমন দীন নয়।
‘বুঝি মৃত্যু আসিয়াছে। …কিন্তু তার ছেলের বেশে, তাকে আদর করিয়া আগু বাড়াইয়া লইতে…এত সুন্দর…’ (‘অপরাজিত’, মিত্র ও ঘোষ, ২০১৪, পৃষ্ঠা ১০২)
অপুর জীবনে বিবাহও আসে অপ্রত্যাশিতভাবে। কিন্তু কী সুন্দর সেই মেয়েটি, অপর্ণা। একেবারে অপু’র মতোই চমৎকার সে। বিবাহের পরে আচমকা পাওয়া সঙ্গীটিকে নিয়ে অপু আপ্লুত হয় নিঃসন্দেহে কিন্তু জীবনের ঠিক এই পর্যায়েই খানিক অতিরিক্ত সংসার-বন্ধনে জড়িয়ে পড়ে সে। নিত্যদিনের কেরানিবৃত্তি তাকে মনে-মনে ভারি যন্ত্রণায় ফেলে, তবু সে যন্ত্রণার উপশম ছিল একমাত্র অপর্ণা। কিন্তু চিরকালীন সম্পর্কে অপুকে পথের সঙ্গে আবদ্ধ করেছেন পথের দেবতা। তিনি একদিকে উদার হলে অন্যদিকে নিজের হিসেব বুঝে নিতে ভোলেননি কখনও, এক্ষেত্রেও অবশ্যই তিনি প্রত্যাশিত সিদ্ধান্তই নেন। সন্তান-জন্মের সময়ে মৃত্যু হয় অপর্ণার। অপর্ণার মৃত্যু অপুকে বিশেষভাবে বেদনাহত করে;
‘অপূর্ব বুকের ভেতরটা হঠাৎ যেন হিম হইয়া গেল। কেমন করিয়া আপনাআপনি তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল—অপর্ণা নেই?’ (‘অপরাজিত’, মিত্র ও ঘোষ, ২০১৪, পৃষ্ঠা ১৫১)
কিন্তু এ-বন্ধন ছিন্ন হওয়া ছাড়া উপায় যে নেই, পাঠক ততক্ষণে সে-কথা বুঝে ফেলেছেন।
অপু-কাহিনি বলতে-বলতে যার যেখানে প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়, বিভূতিভূষণ তাকে সরিয়ে নেন। একে-একে সকলেই অপুকে ছেড়ে যাবে, পথের দেবতা তাকে ঘর ছেড়ে পথেরই ডাক দিয়েছেন। ফলে ঘরের দিক থেকে যারা তাকে টানে বা টেনে রাখতে পারে, বিভূতিভূষণ তাদেরকে নিয়ে নেন। এই টানের আদর্শ উদাহরণ লীলা, মনে করা যাক সেই সময়টির লীলার সঙ্গে তার বাড়িতে দেখা করে বাইরে এসে অপু ভাবে সেই বিপজ্জনক ভাবনা,
‘অপু বাহিরে চলিয়া আসিল—সে অনুভব করিতেছিল, লীলার মত সে কাহাকেও ভালবাসে না—সেই গভীর অনুকম্পামিশ্রিত ভালবাসা, যা মানুষকে ভুলাইয়া দেয়, আত্মবিসর্জনে প্রণোদিত করে।
লীলাকে যে করিয়া হউক সে সুখী করিবে। লীলাকে এতটুকু কষ্টে পড়িতে দিবে না। নিজেকে ছোট ভাবিতে দিবে না। যাহার ইচ্ছা লীলাকে ছাড়ুক, সে লীলাকে ছাড়িতে পারিবে না। সে লীলাকে কোথাও লইয়া যাইবেই—এ অবস্থায় কলিকাতায় থাকিলে লীলা বাঁচিবে না। বিশ্ব একদিকে—লীলার মুখের অনুরোধ আর একদিকে।
সারাপথ ভাবিতে ভাবিতে ফিরিল।’ (‘অপরাজিত’, মিত্র ও ঘোষ, ২০১৪, পৃষ্ঠা ২২২)
যে-মুহূর্তে অপু বলে সমস্ত পৃথিবী একদিকে এবং লীলা আর-একদিকে, সেই মুহূর্তে পথের দেবতা আর-একটুও দেরি করেন না। এই ঝুঁকি তাঁর পক্ষে নেওয়া অসম্ভব। গোটা পথকে অস্বীকার করে অপু লীলার দিকে ছুটেছে— এরকম বিপর্যয় হতে দেওয়াই যাবে না, অতএব অবিলম্বে তার ‘দিন তিনেক’-এর মধ্যেই লীলাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলেন বিভূতিভূষণ। এবং এ-কথাও উল্লেখযোগ্য, ‘অপরাজিত’-র পত্রিকাপাঠে লীলার সঙ্গে বসে সেই রবীন্দ্রনাথের গান গাওয়া অথবা গভীর আবেগে জীবনে প্রথমবারের জন্য তাকে জড়িয়ে ধরার মুহূর্তগুলি লেখা হয়নি। পরিবর্তিত গ্রন্থ সংস্করণে পুনর্বিবেচনার ফলে বিশেষ করে এই নিবিড় মুহূর্তগুলি নির্মাণ করেন বিভূতিভূষণ এবং করেন লীলাকে অপুর পথ থেকে সরিয়ে আনার জন্যই। যে-অপু সংসার, সন্তান, কলকাতার তুলনামূলক নিশ্চিন্ত, কিছুটা অর্থাভাবহীন নিরাপদ জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছিল, লীলার মৃত্যু তাকে সেই পথ থেকে সরিয়ে পথের দেবতার প্রিয় পথে ফিরিয়ে দেয় পুনরায়। পাঠক জানেন প্রচলিত গ্রন্থপাঠে,
‘ভবঘুরে অপু আবার কোথায় চলিয়া গিয়াছে। হয়ত লীলার মুখের শেষ অনুরোধ রাখিতে কোন্ পোর্তো প্লাতার ডুবো জাহাজের সোনার সন্ধানেই বা বাহির হইয়াছে। গিয়াছেও প্রায় ছ’সাত মাস হইল।’ (‘অপরাজিত’, মিত্র ও ঘোষ, ২০১৪, পৃষ্ঠা ২৬৫)
এভাবেই শিশু কাজলকে রাণুর কাছে রেখে চলে যায় অপু। এই অংশে পৌঁছে লীলার মৃত্যুর অনিবার্যতা তার সমস্ত গুরুত্ব নিয়ে প্রকাশিত হয়। লীলার মৃত্যু না হলে, মাতৃহীন সন্তান কাজলকে মায়াবী নিষ্ঠুর উদাসীনতায় ফেলে রেখে যাওয়া কি সম্ভব হত তার পক্ষে? কিন্তু ‘লীলার মুখের শেষ অনুরোধ’ রাখতে চাওয়ার মতো এমন গুরুতর অজুহাত তার পক্ষে উপেক্ষা করা সম্ভব হয় না। পাঠক এই শব্দচয়নগুলির ফলে এই লেখার প্রতি ক্ষুব্ধ হতে পারেন, এমন সম্ভাবনার প্রতি ক্ষমা চেয়ে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত। তবু এ-কথা কি পাঠক অস্বীকার করবেন, অপুর মতো এমন অসামান্য নিষ্ঠুর (নিজের একমাত্র শিশু সন্তানকে শৈশবের গ্রাম সম্পর্কিত দিদির কাছে অনির্দিষ্টকালের জন্য রেখে কোনও এক সম্পূর্ণ অপরিকল্পিত অজ্ঞাত স্থানে চলে যাওয়ার ঘটনাটি আর কীই-বা বলা যায়), পথের প্রতি এমন গভীর অনুগত কোনও চরিত্র অপু’র আগে বা পরে আর কখনোই পাওয়া যায়নি। তবে এও ঠিক যে, পথের দেবতাই চিরকাল তার যাত্রাপথটি নিজের ইচ্ছেয় সাজিয়ে তুলেছেন, এ-পরিকল্পনা তাঁরই। তবে তাঁর নির্বাচন যে নিখুঁত, তা নিয়ে সংশয় থাকে না।
পথের দেবতার নেহাত মনটা খানিক ভাল বলতে হয়, যে তিনি অপূর্ব যাত্রাপথের অন্যান্য পিছুটানগুলিকে বেশ নির্লিপ্তভাবে সরিয়ে নিলেও, অপুর সন্তান কাজলের সেই পরিণতি দেননি।
ক্রমে অবশ্য পাঠক দেখতে পান, মৃত্যুর সঙ্গে সহজ সম্পর্ক তৈরি হয়েছে অপুর। পথের দেবতার নেহাত মনটা খানিক ভাল বলতে হয়, যে তিনি অপূর্ব যাত্রাপথের অন্যান্য পিছুটানগুলিকে বেশ নির্লিপ্তভাবে সরিয়ে নিলেও, অপুর সন্তান কাজলের সেই পরিণতি দেননি। অপু যদিও সেই শিশুসন্তানকে ফেলে যেতে পিছপা হয়নি, তবু, কাজল রয়ে গেছে। কিন্তু সবার মনে পড়বে সেই দিনটার কথা, কলকাতার রাস্তায় একা কাজল খানিক বেড়াতে বেরোলে হঠাৎই খবর আসে কী এক দুর্ঘটনার, সেখানেও যেন ঠিক কাজলের বয়সি একটি ছেলেই লরি চাপা পড়েছে। অপু প্রায় নিশ্চিত হয়ে যায়, এ কাজল ছাড়া আর কেউ নয়। হাত-পা তার অবশ হয়ে আসে, তবু তারই মধ্যে অপু যেন মৃত্যুকে মেনে নিয়েই কিছু কথা ভাবে,
‘কিন্তু এই সময়ে হঠাৎ অপু হাতে পায়ে অদ্ভুত ধরনের বল পাইল—বোধ হয় যে খুব ভালোবাসে, সে ছাড়া এমন বল আর কেহ পায় না এমন সময়ে। খোকার কাছে এখনি যাইতে হইবে—যদি একটুও বাঁচিয়া থাকে—সে বোধ হয় জল খাইবে, হয়তো ভয় পাইয়াছে।’ (‘অপরাজিত’, মিত্র ও ঘোষ, ২০১৪, পৃষ্ঠা ২৪৪)
সে যাত্রায় অপুর আশঙ্কাকে ভুল প্রমাণ করে প্রাণে বেঁচে যায় কাজল।
উপন্যাসের একেবারে শেষে, নিশ্চিন্দিপুরে ফিরে রানু দিদির কাছে কাজলকে রেখে চলে যাওয়ার আগে অপু কাজলকে কয়েকটি কথা বলে যায়, তার একটি ছিল বাঁশবনের মধ্যে কবেকার সোনার কৌটো পোঁতা থাকার কথাটা। তবে সে-কথা আপাতত আলোচ্য নয়, বলার কথা একখানি বাক্য মাত্র। নিজের সন্তানের মৃত্যু-সম্ভাবনার কথা নিজমুখে উচ্চারণ করতে দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়েন অধিকাংশ মানুষ। কিন্তু মৃত্যুর সঙ্গে যার এমন নিবিড় যোগ, এত দীর্ঘ বন্ধন, সেই অপু নিঃসংকোচেই রাণুকে বলে,
‘আর যদি না ফিরি আর খোকা যদি বাঁচে—বৌমাকে কৌটোটা দিও সিঁদুর রাখতে…’ (‘অপরাজিত’, মিত্র ও ঘোষ, ২০১৪, পৃষ্ঠা ২৬৫)
জীবনের মতোই মৃত্যুও যে-প্রাণের একমাত্র নিশ্চিত পরিণতি, এই সহজ সত্য অপুর আনন্দযাত্রার অর্জন।
বাংলা সাহিত্য পড়ে আনন্দ পেয়েছেন, পাচ্ছেন যে পাঠক, তাঁদের মধ্যে ‘ভবঘুরে’ অপুকে ভালবাসেননি, এমন মানুষ বোধহয় নেই। অপুর জীবনের গন্তব্যটি অনিশ্চিত, কোনও নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছোবার অভিপ্রায় তার নেই। পথের দেবতা এই নিতান্ত ‘মূর্খ’, একদা মায়ের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা বালকটির জন্য সমস্ত জীবনব্যাপী সাজিয়ে রেখেছেন ‘বিচিত্র আনন্দযাত্রা’। তার কপালে এঁকে দিয়েছেন পথ চলার অদৃশ্য তিলক। ঘরছাড়া করে আনার জন্যই যে-জীবন, সেই জীবনকে ‘অপরাজিত’ করে তুলতে এই মহৎ মৃত্যুগুলি অনিবার্য এবং অবশ্যম্ভাবী।