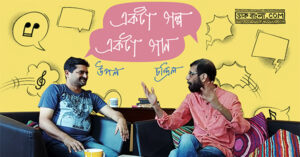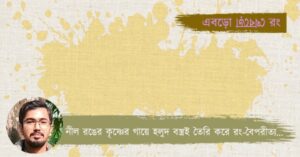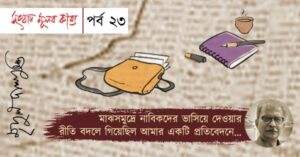থিয়েটারকে নাগরিক বৃত্তের বেড়াজাল থেকে বের করে আনার যে লড়াই লড়েছিলেন বাদল সরকার, তা, বলা যায়, একরকমের মুক্তিযুদ্ধই। সেই লড়াইয়ে বাদল সরকার কিন্তু সফলও হয়েছিলেন। এখনও বাদল সরকারের সেই লড়াই খুবই প্রাসঙ্গিক। সংস্কৃতির সর্বত্র এখন যেভাবে অর্থ ও বৃহৎ পুঁজি চালিকাশক্তি হয়ে উঠছে, সেখানে বাদলবাবুর পথের থিয়েটারের ফর্ম ক্রমশ আরও জরুরি হয়ে উঠছে।
কিন্তু পরবর্তীতে এই ধারাকে বহন করার মতো দক্ষতা যে খুব বেশি দেখা গিয়েছে, তা কিন্তু নয়। প্রসেনিয়ামের সমান্তরালে এই তৃতীয় থিয়েটারের বিকল্পও চলমান থাকা প্রয়োজন, কিন্তু অ্যাজিট প্রপ থিয়েটার হোক, বা এই অন্যধারার থিয়েটার, তার তো একটা বিবর্তন পৃথিবীজুড়েই ঘটেছে। সেই পরিবর্তনগুলোর অভিঘাত স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। যে-সময় বাদল সরকার এই রাস্তা বেছে নিয়েছিলেন, সেই সময় থার্ড থিয়েটার ছিল একটা প্রস্থান। এখনও তার প্রয়োজনের তীব্রতা কিন্তু রয়েছেই, এখনও। বাদলবাবুর যে ইঙ্গিত ছিল, তা হল মূলধারার প্রসেনিয়াম থিয়েটার অর্থনৈতিকভাবে আমাদের জাপটে ধরছে, তা থেকে মুক্তির পথ এইটাই হতে পারে। কিন্তু স্ট্রিট থিয়েটার বা পথনাটক তার দর্শনের ওপরেই নির্ভরশীল। তাছাড়া তার অস্তিত্ব কিন্তু বায়বীয় হয়ে যায়।
তৃতীয় থিয়েটারকে বাদল সরকার এক অন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর লেখনী দিয়ে, নাটকীয় কল্পনাশক্তি দিয়ে। কিন্তু ওই ধরনের নাটক লিখতে গিয়ে বাদলবাবুও একটি ঘেরাটোপে আটকে গিয়েছিলেন। সব ধরনের নাটকই বাদলবাবু অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে লিখতে পারতেন। কিন্তু শুধু এই ফর্মের জন্যই যখন নাটক লিখতে শুরু করলেন বাদলবাবু, তখন হয়তো কিছুটা আটকে গিয়েছিলেন ওই পরিধিতে। কিন্তু এ-কথাও মানতে হবে, ‘পাগলা ঘোড়া’ বা ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ লেখার সময় মঞ্চনাটক মাথায় রেখেই লেখা। কিন্তু মাঠে, ফুটপাথে, কার্জন পার্কে বা মানুষের মাঝে যে নাটক নিয়ে যাচ্ছেন, সেখানে ওই দার্শনিক সূক্ষ্মতা থেকে তিনি নিজেই সরে যাচ্ছেন, এমন নয়, যে সেই ক্ষমতা ওঁর আর নেই। এই প্রস্থানটা উনি তৈরি করছেন নিজেই। কার্জন পার্কে যে নাটক হবে, ওই ভয়াবহ শব্দদূষণ ও কোলাহলের পরিপার্শ্বে, তার টেক্সটও তাই সেইভাবেই লিখছেন।

আরও পড়ুন : বাদল সরকারকে খুঁজে পাওয়ার জন্য সারাদিন ঘুরেছিলাম কলকাতার রাস্তায়!
লিখছেন অঞ্জন দত্ত…
সামগ্রিকভাবে অভিনয়ের একটি পদ্ধতিগত অনুশীলনও তৈরি করেছিলেন বাদল সরকার। প্রশিক্ষক হিসেবে সেই পদ্ধতি, সেই অনুশীলনকে দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন বাদল সরকার। সেই অনুশীলনকে কিন্তু বাদলবাবু দেখছেন সম্পূর্ণ দক্ষিণ-এশীয় একটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই। সেই প্রশিক্ষণের অভিঘাত ছিল সাংঘাতিক। বাদল সরকারের নাট্য-প্রক্রিয়া, রাজনৈতিক ভাষ্য ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।
বাদল সরকার যখন যাদবপুরে তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে মাস্টার্স করতে আসেন, তখন ওঁর সহপাঠী হওয়ার সৌভাগ্য। মাথায় রাখতে হবে, সে-সময় ওঁর নাটক কিন্তু সিলেবাসে পড়ানো হয়— ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’। একজন মানুষ যখন জীবিত কিংবদন্তি, লিভিং লেজেন্ড, বয়সের কোঠা সত্তর বছর পেরিয়ে গেছে, তখন তিনি ফিরে আসছেন পড়াশোনা করতে।
তাঁর সব লেখাই যথাসম্ভব গভীরে গিয়ে অনুধাবনের চেষ্টা করেছি। ওঁর নাটকের অভিনয় নানা জায়গায় গিয়ে দেখেছি— ‘ভোমা’, ‘মিছিল’, ‘ত্রিংশ শতাব্দী’, ‘খাট-মাট-ক্রিং’, ‘গণ্ডি’, ‘পিকনিক’, ‘রক্তকরবী’। জাতীয় দূরদর্শনের জন্য বাদল সরকারকে নিয়ে একটা তথ্যচিত্রও করেছি নয়ের দশকের শেষের দিকে। ‘Theatre Directors at Work’ নামে একটা সিরিজের জন্য। প্রথমটায় ফোনে এই প্রস্তাব দেওয়াতে বাদলবাবু রাজি হননি। কিন্তু বলেছিলাম, আমার চিত্রনাট্য বা চিত্রভাবনা শুনে প্রত্যাখ্যান করুন। শেষে শান্তিনিকেতনে রতনকুঠিতে গিয়ে শুনিয়েছিলাম। ওঁর প্রবন্ধ ‘পাখিরা উড়ে যায়’ ভিত্তি করেই চিত্রবিন্যাস করেছিলাম। উনি বললেন ‘এরকম হলে আমি রাজি।’ বহু সাক্ষাৎকার নিয়েছি এই তথ্যচিত্রের প্রয়োজনে। উনি ট্রেনে ডিলান টমাসের কবিতা পড়ছেন, বা উনি সোনাঝুরি জঙ্গলের মধ্যে একা হেঁটে যাচ্ছেন— আমরা অলক্ষ্যে শুট করছি। বেশ কয়েকটি নাটকের অংশবিশেষ শুট করেছি। তারপরে ওঁর বাড়িতে গিয়েছি বেশ কয়েকবার, উনি কোলাজ করতে ব্যস্ত তখন। এই তথ্যচিত্রটি ইউটিউবে প্রসার ভারতীর আর্কাইভে এখন পাওয়া যায়। বাদলবাবু এস্কাইলাসের ‘ট্রিলজি অরেস্টিয়া’-র অনুবাদ করেছিলেন এবং তার একটি কপি আমাকে দিয়েছিলেন। ইচ্ছে আছে, কখনও এই অনুবাদ ভিত্তি করে একটি প্রযোজনা করব।