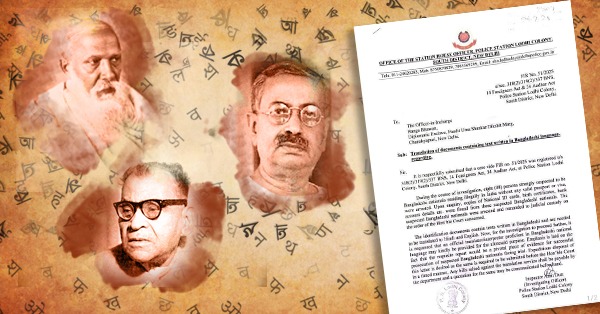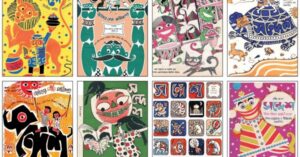দিল্লি পুলিশের একটি সাম্প্রতিক চিঠিকে ঘিরে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ও বুদ্ধিজীবী মহলে ভাষাপ্রেম ও ভাষাবিরোধের এক তপ্ত আবহাওয়া তৈরি হয়েছে। সে-আগুনে ঘি ঢেলেছে এক হিন্দিভাষী রাজনৈতিক নেতার মন্তব্য— বাংলা নামে নাকি কোনও ভাষাই নেই। সমস্যাটি সাম্প্রতিক হলেও এ-বিপত্তির মূল নিহিত রয়েছে প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে। সেই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটিকে ঝালিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যেই বর্তমান রচনার অবতারণা। দুরাশা, হয়তো এই অতীতচেতনা সংকটটিকে আর-একটু তলিয়ে বুঝতে সহায়ক হবে। বলা যায় না, কোনও বুদ্ধিমান পাঠক হয়তো আবিষ্কার করে ফেলতে পারেন এর সমাধানসূত্রও!
এ-কথা মোটেই কষ্ট করে বুঝতে হয় না, এই কাজিয়ায় বাংলার একটি ‘অপর’ (বা যেন প্রায় শত্রুপক্ষ) রয়েছে। আর সে-অপর পক্ষ যে-কোনও ভারতীয় ভাষা নয়, বরং একটি নির্দিষ্ট ভারতীয় ভাষা, হিন্দি। ভাষিক রাজনীতির পরিসরে হিন্দির সঙ্গে বাংলার সম্বন্ধটি ঔপনিবেশিক আমলের শেষ পর্ব থেকেই সমর্থন-প্রতিরোধের টানা-পোড়েনে ধ্বস্ত। কিন্তু সে-প্রসঙ্গে প্রবেশের পূর্বে একটি অন্য প্রসঙ্গ ছুঁয়ে যাওয়া প্রয়োজন।
১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলা মুঘল অধিকারভুক্ত হওয়ার পর ফারসি বাংলার সরকারি ভাষা (অর্থাৎ রাজসভা, আইন-আদালত বা কূটনৈতিক আদান-প্রদানের ভাষা) রূপে স্বীকৃতি লাভ করে। ক্ষমতায় আসার অনেক পরে, ১৮৩৭-এ, ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ফারসির বদলে ইংরেজি এবং দেশীয় (যার মধ্যে অন্যতম বাংলা) ভাষাকে সরকারি ভাষারূপে ঘোষণা করে। মজার কথা হল, অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকেই ন্যাথানিয়েল ব্রেসি হ্যালহেডের মতো ব্যাকরণ-লিখিয়ে (প্রকাশ ১৭৭৮) বা হেনরি পিটার ফস্টারের মতো অভিধানকার (প্রকাশ ১৭৯৯) বাংলার ভাবপ্রকাশের ভাষিক ক্ষমতার তারিফ করে তাকে ফারসির বদলে সরকারি ভাষারূপে ব্যবহারের পক্ষে সওয়াল করছিলেন। কিন্তু উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে কোম্পানি বাহাদুর যখন সে-প্রচেষ্টা করেন, অভিজাত বাঙালিরাই তার বিরোধিতা করেন। তাঁদের সমর্থন ছিল ফারসির প্রতি। হয়তো সেদিন এই বিরোধিতা না হলে হিন্দির তুলনায় বাংলাই সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে অনেক বেশি প্রসার লাভ করত। কিন্তু সেদিন তা হয়নি। আর তার বদলে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে উত্তর ভারতে ক্রমে ঘনীভূত হয়েছে উর্দু-হিন্দি দ্বৈরথ। এবং সে-দ্বন্দ্বে ক্রমে জয়ী হয়ে উঠেছে হিন্দি।
আরও পড়ুন: আরবি-ফারসি ছাড়া বাংলা ভাষাই হয় না, মনে করতেন প্রমথ চৌধুরী! লিখছেন অনল পাল…
ফারসি লিপিতে উর্দুর বদলে নাগরী লিপিতে হিন্দিকে সরকারি ভাষারূপে গ্রহণের দাবিটা প্রথম যুক্ত প্রদেশেই (অধুনা উত্তর প্রদেশ) উঠেছিল। সে-দাবিকে মান্যতা দিয়ে নাগরী লিপির হিন্দি ক্রমে ব্রিটিশ সহায়তায় ১৮৭০-এ সেন্ট্রাল প্রভিন্সেস, ১৮৮০-তে বিহার, এবং ১৯০০-তে নর্থ-ওয়েস্ট প্রভিন্সেসে ফারসি লিপির উর্দুকে প্রতিস্থাপন করে। ১৮৮০-তে ব্রিটিশ সরকার যখন বিহারের বিদ্যালয়গুলিতে পঠনপাঠনের ক্ষেত্রে নাগরী হরফকে বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করে, তখন এই সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে যথেষ্ট সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল। সে-সময়ের সংবাদপত্র ঘাঁটলে আজও সেসব খবরের সন্ধান মিলবে।
বিশ শতকের প্রায় গোড়াতেই হিন্দির পক্ষ নিয়ে মাঠে নামলেন স্বয়ং মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি। ১৯১৭-এ ভারুচে অনুষ্ঠিত গুজরাত শিক্ষা সম্মেলনে তিনি ভারতের জাতীয় সংহতির সহায়ক রাষ্ট্রভাষা রূপে হিন্দির নাম প্রস্তাব করেন। পরের বছর, ১৯১৮-এ, হিন্দি সাহিত্যের বিকাশ ও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তার ভূমিকা আরও জোরদার করার উদ্দেশ্যে তিনি এলাহাবাদে হিন্দি সাহিত্য সম্মেলন প্রতিষ্ঠা করলেন। গান্ধীর পথে চলতে প্রাথমিকভাবে মোটেই রাজি ছিল না কংগ্রেস। ১৯২৫-এর করাচি অধিবেশনে তাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, হিন্দি বা উর্দু কোনওটাই নয়, জাতীয় ঐক্যের কথা মাথায় রেখে বরং গড়ে তোলা হোক হিন্দুস্তানি নামের এমন এক মিশ্রভাষা, যা এই দুইয়ের সমন্বয়ে গঠিত। যদিও শেষপর্যন্ত হিন্দি সাহিত্য সম্মেলনের চাপে এই নীতি থেকে সরতে হয়েছিল কংগ্রেসকে।
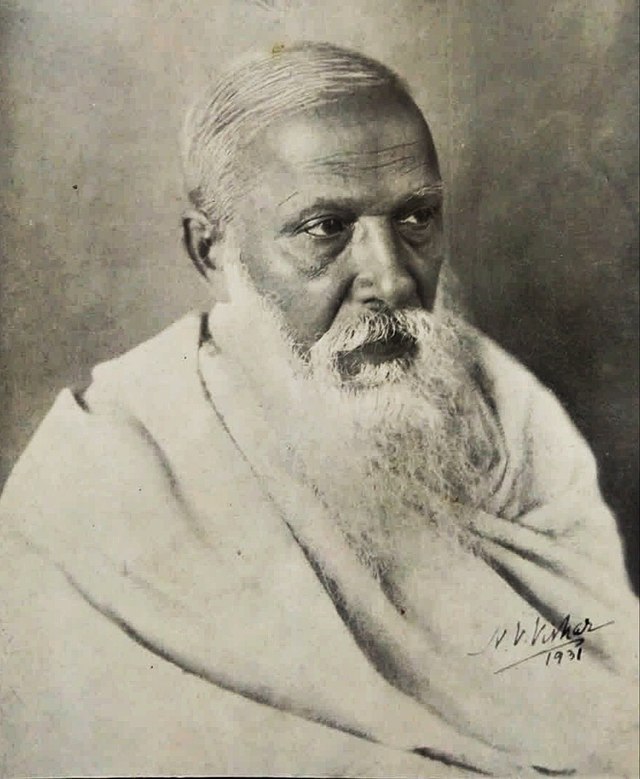
কিন্তু প্রশ্ন হল, এই বিরোধ-প্রতিদ্বন্দ্বিতার আবহে ঠিক কী অবস্থান নিচ্ছিলেন বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা? আসলে এই ভাষা-সংঘর্ষ যতটা-না প্রভাবিত করছিল বঙ্গদেশের বাংলাভাষী সমাজকে, তার থেকে অনেক বেশি আবিষ্ট করছিল প্রবাসী বাঙালিকে, বিশেষত হিন্দিপ্রদেশের প্রবাসী বাঙালিকে। হয়তো সে-কারণেই চল্লিশের দশক থেকে ষাটের দশক পর্যন্ত এ-সম্পর্কিত সবচেয়ে বেশি লেখালিখি প্রকাশিত হয় ‘প্রবাসী’ পত্রিকায়। ‘প্রবাসী’-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন এলাহাবাদ নিবাসী। ফলে হিন্দিপ্রদেশের কেন্দ্রে বসে এই প্রসঙ্গটি এড়িয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। জুলাই ১৯৪১-এর (শ্রাবণ ১৩৪৮) ‘প্রবাসী’-র নিয়মিত সম্পাদকীয় বিভাগ ‘বিবিধ প্রসঙ্গ’-এ সম্পাদক লেখেন, জুন মাসে কলকাতায় ‘পূর্ব ভারত রাষ্ট্রভাষা সম্মেলন’ নামক সভার অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় যার উদ্দেশ্য ছিল হিন্দিকে সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রভাষা বলে ‘স্বীকার করানো ও প্রচার করা’। সম্পাদক সখেদে জানান, হিন্দিভাষীরা হিন্দি ভিন্ন অন্য কোনও ভারতীয় ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার কথা তুললেই সে-প্রয়াসকে প্রাদেশিকতা বলে দেগে দেন, অথচ হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা রূপে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস কেন প্রাদেশিকতা নয় সে-যুক্তি তাঁরা দিতে চান না। এই সম্মেলনের সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদও হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে সওয়াল করেছেন। কংগ্রেসের ঘোষিত মত মিশ্র হিন্দুস্তানির পক্ষে হওয়া সত্ত্বেও রাজেন্দ্রপ্রসাদ বা একাধিক কংগ্রেসি নেতা কেন সভায় হিন্দুস্তানির বদলে হিন্দির কথা বলেছেন তা নিয়ে ‘প্রবাসী’-সম্পাদক বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। কলকাতায় রাজেন্দ্রপ্রসাদের বক্তৃতা সম্পর্কে লক্ষ্ণৌর ‘ন্যাশনাল হেরাল্ড’-ও মন্তব্য করে, ‘যদিও দায়িত্বশীল হিন্দু ও মুসলিম কংগ্রেস নেতারা হিন্দি সাহিত্য সম্মেলন এবং উর্দু প্রচারের জন্য সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলির সভাপতিত্ব করে চলেছেন, অথচ এখনো পর্যন্ত একটি সাধারণ মঞ্চ তৈরির জন্য, প্রয়োজন থাকলেও, তাঁরা কিছুই করছেন না।’ কংগ্রেসের মধ্যে মিশ্রবুলির পক্ষে সওয়াল করলেও কংগ্রেসের বাইরে এটাই ছিল নেতাদের প্রকৃত অবস্থান।
‘প্রবাসী’-সম্পাদকের বক্তব্য— এই হিন্দি-পক্ষ সেন্সাস রিপোর্ট বা ‘স্টেটসম্যান’স ইয়ারবুক’-এর মতো নির্ভরযোগ্য সূত্রগুলির পরোয়া না করে হিন্দিভাষীর সংখ্যা যেমন খুশি বাড়িয়ে বলছে। সমগ্র বিহারকে হিন্দিভাষী অঞ্চল বলে তাঁরা দাবি করছেন, অথচ পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সচ্চিদানন্দ সিংহ পর্যন্ত স্পষ্ট বলছেন, বিহারি হিন্দি নয়, তা মৈথিলী, ভোজপুরি ও মগাহির সমাহার। হিন্দি-প্রচারকরা রাজস্থানি ও পাঞ্জাবিকেও হিন্দি বলে দাবি করছেন, কিন্তু যে-সব ‘ভাষাতত্ত্ববিদদের রাজনৈতিক চরকায় তেল দিতে হয় না’ তাঁরা এ-দু’টিকে স্বতন্ত্র ভাষা বলেই মনে করেন। যে-যুক্তিতে তাঁরা এই সব ভাষাকে হিন্দি বলে দাবি করেন, সেই একই যুক্তিতে বাঙালি ওড়িয়া, অসমিয়া বা মৈথিলীকে বাংলা বলে দাবি করতে পারেন, কিন্তু কোনও বাঙালিই এমন মূর্খতা দেখান না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে-কথাটি সম্পাদক এই নিবন্ধে উত্থাপন করেন, তা হল রাষ্ট্রভাষা ও লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কার পার্থক্যের প্রসঙ্গ। মত তাঁর, বহুভাষিক দেশে ভিন্নভাষীদের মধ্যে সংযোগসূত্র গড়ে তোলার যুক্তি দিয়ে যে সাধারণ ভাষার দাবি করা হচ্ছে, সেই সাধারণ সংযোগের ভাষা আদতে লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা। কিন্তু লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কাকেই যে রাষ্ট্রভাষা হতে হবে, এমন দাবি অর্থহীন এবং ইতিহাস-সমর্থিত নয়।
বাংলা ভাষার প্রতি যে একটা সূক্ষ্ম বৈষম্য নেহরু ব্যতিরেকে প্রায় সিংহভাগ কংগ্রেসি নেতৃবর্গের মধ্যে বিদ্যমান, সে-কথাটাও রামানন্দবাবু একাধিকবার ঠারেঠোরে বলার চেষ্টা করেছেন। ১৯৪২-এ কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের রজতজয়ন্তী উপলক্ষে গান্ধীজির বক্তৃতায় ভারতের চলিত ভাষাগুলোর নাম করতে গিয়ে হিন্দি, উর্দু, হিন্দুস্তানির পরেই মারাঠির নাম করেন, অথচ বাংলাভাষী জনতার সংখ্যা মারাঠির অপেক্ষা তিনগুণ হলেও বাংলার নাম করেননি— সে-প্রসঙ্গে ফাল্গুন ১৩৪৮-এর (ফেব্রুয়ারি ১৯৪২) ‘বিবিধ প্রসঙ্গ’-এ টিপ্পনী করতে ছাড়েননি।
ভাষা কমিশনের মূল সিদ্ধান্তের সঙ্গে তিনজন সদস্য ভিন্নমত পোষণ করে তাঁদের ডিসেন্ট নোট দেন। এই তিনটি ডিসেন্ট নোটের একটির প্রণেতা ছিলেন সুনীতিকুমার। তাঁর নোটে সখেদে জানান তিনি— এতদিন তিনি হিন্দির পক্ষে ওকালতি করে এসেছেন। তাঁর বাঙালি বন্ধুরা এ নিয়ে তাঁকে অনেক ভুলও বুঝেছেন। তিনি নিজে হিন্দিতে চারখানি বইও লিখেছেন। কিন্তু আজ তিনি বলতে বাধ্য হচ্ছেন, তিনি যেন চোখের সামনে এক ‘হিন্দি সাম্রাজ্যবাদের’ সূচনা দেখতে পাচ্ছেন। হিন্দি কোনওভাবেই ভারতের অন্য ভাষাগুলির তুলনায় প্রাধান্য লাভ করতে পারেনি। ফলে এই পরিস্থিতিতে হিন্দিকে অপর ভাষাভাষী ভারতীয় জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে ‘জাতীয় স্বার্থবিরোধী’।
তবে সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্ব ও পরবর্তী সময়পর্বটিতে বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা যে হিন্দিকে সমর্থন করেছিলেন, তার একাধিক নজির রয়েছে। ‘প্রবাসী’-তেই ১৯৪৭-এর মে মাসে প্রকাশিত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ‘বাঙালির হিন্দিশিক্ষা’ নামের নিবন্ধে লেখক হিন্দি কেন শেখা দরকার তার বিবিধ কারণ দর্শিয়েছেন। লেখকের মতে— প্রথমত, হিন্দি ভারতের সংখ্যাগুরু জনগণের ভাষা; দ্বিতীয়ত, ভারতের একটি সংহতির জন্য একটি রাষ্ট্রভাষা প্রয়োজন, যা বিদেশি ইংরেজি মেটাতে অক্ষম; তৃতীয়ত, অতি সহজেই হিন্দি আয়ত্ত করা যায়; চতুর্থত, আধুনিক বাংলার সমকক্ষ সাহিত্যসম্ভার হিন্দির না থাকলেও প্রাক্-ঔপনিবেশিক সাহিত্যের নিরিখে হিন্দি এবং বাংলা সমগোত্রীয় বলা চলে। ১৯৪৬-এ প্রকাশিত বঙ্গীয় রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতির প্রাদেশিক সঞ্চালক রেবতীরঞ্জন সিংহের ‘বাংলায় হিন্দি শেখার বই: রাষ্ট্রভাষার প্রথম সোপান’-এর ভূমিকায় আচার্য সুনীতিকুমার মূলত জাতীয় সংহতির প্রয়োজনেই হিন্দি শিক্ষার প্রতি জোর দেন। তিনি স্মরণ করাতে ভোলেন না যে ‘ভারতের ঐক্যবিধায়িনী ভাষারূপে’ ১৮৭৫-এ কেশবচন্দ্র সেন বা ১৮৮৫-তে ভূদেব মুখোপাধ্যায় হিন্দিরই আবাহন করেছিলেন।
স্বাধীনতার পর ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে হিন্দিকে ভারতীয় ইউনিয়নের সরকারি ভাষারূপে গ্রহণ করা হয়, পাশাপাশি ইংরেজিকেও পূর্ববৎ সরকারি ভাষারূপে বলবৎ রাখা হয়। সরকারি ভাষারূপে সেই সময়ে সংবিধানের অষ্টম তফসিলে যে-চোদ্দোটি ভাষা ছিল, তার মধ্যে থেকে হিন্দিকেই বেছে নেন গণপরিষদের সদস্যরা। ১৯৫৬-এ রাষ্ট্রপতির নির্দেশে যে ভাষা কমিশন গঠিত হয়েছিল, তার অন্যতম সদস্য পি. সুব্বারায়ন কমিশনের রিপোর্টের সঙ্গে প্রদত্ত তাঁর ডিসেন্ট নোটে স্পষ্ট বলেন যে, এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে-সদস্যরা, তাঁরা কেউই জনগণের দ্বারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি নন এবং পরিষদের সদস্যদের মধ্যে হিন্দিভাষীরা ছিলেন সংখ্যাগুরু। মাদ্রাজ, মারাঠা ও বাংলার প্রদেশের সদস্যদের বিরোধিতায় শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা হিন্দির জোটেনি। সিদ্ধান্ত হয়েছিল, পনেরো বছর পর ইংরেজিকে সম্পূর্ণ প্রতিস্থাপন করে হিন্দিকেই একমাত্র সরকারি ভাষা করা হবে। পুরো ব্যাপারটিকে খতিয়ে দেখতে রাষ্ট্রপতি ভাষা কমিশন গঠন করেন। ভাষা কমিশনের মূল সিদ্ধান্তের সঙ্গে তিনজন সদস্য ভিন্নমত পোষণ করে তাঁদের ডিসেন্ট নোট দেন। এই তিনটি ডিসেন্ট নোটের একটির প্রণেতা ছিলেন সুনীতিকুমার। তাঁর নোটে সখেদে জানান তিনি— এতদিন তিনি হিন্দির পক্ষে ওকালতি করে এসেছেন। তাঁর বাঙালি বন্ধুরা এ নিয়ে তাঁকে অনেক ভুলও বুঝেছেন। তিনি নিজে হিন্দিতে চারখানি বইও লিখেছেন। কিন্তু আজ তিনি বলতে বাধ্য হচ্ছেন, তিনি যেন চোখের সামনে এক ‘হিন্দি সাম্রাজ্যবাদের’ সূচনা দেখতে পাচ্ছেন। হিন্দি কোনওভাবেই ভারতের অন্য ভাষাগুলির তুলনায় প্রাধান্য লাভ করতে পারেনি। ফলে এই পরিস্থিতিতে হিন্দিকে অপর ভাষাভাষী ভারতীয় জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে ‘জাতীয় স্বার্থবিরোধী’।
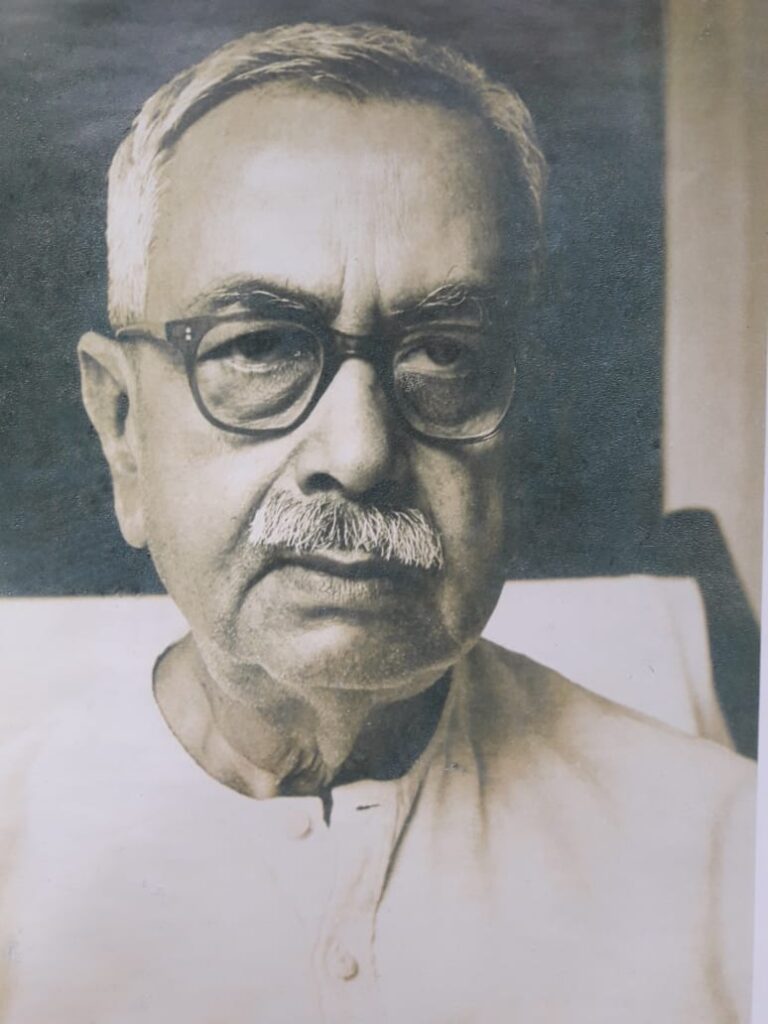

তিনি আরও স্পষ্ট করে বলেন যে, অন্য ভারতীয় ভাষার নাগরিকদের নিজের ভাষার পাশাপাশি যেমন হিন্দি শেখা উচিত, তেমনি হিন্দিভাষীদেরও উচিত হিন্দির পাশাপাশি অন্তত অপর একটি ভারতীয় ভাষা শিক্ষা করা। বর্তমানে ভারতে অষ্টম তফসিলের অন্তর্ভুক্ত ভাষার সংখ্যা চোদ্দো থেকে বেড়ে বাইশ হয়েছে, কিন্তু সে-প্রস্তাব কি অদ্যাবধি কোনও রূপ লাভ করতে সমর্থ হয়েছে?
১৯৫০-এ ভারতীয় সংবিধানে পনেরো বছর পরে হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা করার সংকল্প গৃহীত হলে ১৯৫১-তে রাজশেখর বসু এর প্রতিক্রিয়ায় একটি চমৎকার নিবন্ধ লিখেছিলেন, শিরোনাম ছিল ‘বাঙালির হিন্দিচর্চা’। রাজশেখর সে-প্রবন্ধে জানান, এই সিদ্ধান্তে অনেকে রাগ করেছেন বা ভয় পেয়েছেন, কিন্তু অধিকাংশ বাঙালি ছিলেন উদাসীন। তবে রাগের বশে হিন্দি বয়কট করা বা ভয়ে নিরাশ হওয়া, কিংবা ভেবে নিশ্চেষ্ট থাকা—কোনওটাই বুদ্ধিমানের কাজ নয় বলে তিনি মনে করেন। তাঁর মতে, বাঙালির জন্য বিষয়টি মোটেই কঠিন নয়। বরং দু’টির জায়গায় তিনটি ভাষা শিখলে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে বাঙালির লাভই হবে। হিন্দির আধিপত্যে বাংলা ভাষার ক্ষতিসাধনের ভয়ও অমূলক। ইংরেজির প্রভাবে বাংলা যেমন বিশিষ্টতা না হারিয়ে পুষ্ট হয়েছে, হিন্দির ক্ষেত্রেও তেমনি সে কিঞ্চিৎ প্রভাবিত হলেও অভিভূত হবে না। সর্বোপরি, তাঁর সাংস্কৃতিক পুঁজিকে ব্যবহার করে হিন্দির মাধ্যমে বাঙালির লাভেরও একটি দিক রয়েছে বলে তিনি মনে করেন।
ব্যবসাবুদ্ধির অভাব থাকলেও বাঙালির সাহিত্য যে অতি সমৃদ্ধ, সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু অনুপাতে বাঙালি পাঠকের সংখ্যা তত নয়। তাঁর মতে, ভাষা ভাবের বাহন মাত্র; বাঙালির সাহিত্যপটুতা তাঁর ভাষার জন্য নয়, বরং বাঙালি লেখকের স্বাভাবিক পটুতার জন্য। প্রভাত মুখুজ্জে, শরদিন্দু বা বনফুলের গল্পে যে অসংখ্য অবাঙালি চরিত্র নিপুণভাবে চিত্রিত হয়েছে, সেসব গল্প হিন্দিতে লিখলে ভারতব্যাপী সমাদর পেত। এমনকী যদি কেবল বাঙালি চরিত্রনির্ভর হিন্দি গল্প লেখা হয়, তারও হিন্দির বাজারে অত্যন্ত কাটতি হবে বলে তিনি মনে করেন। তাই নিজের সাংস্কৃতিক পুঁজি ব্যবহার করে হিন্দির সাহিত্যবাজার ধরতে বাঙালিকে পরামর্শ দিয়েছিলেন রাজশেখর। আজ সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যে-পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তার মোকাবিলায় বাঙালি কি তাঁর সাংস্কৃতিক পুঁজিকে সত্যিই হাতিয়ার করতে পারে না? এ-কথা বোধ হয় আজ ভেবে দেখার সময় এসেছে…