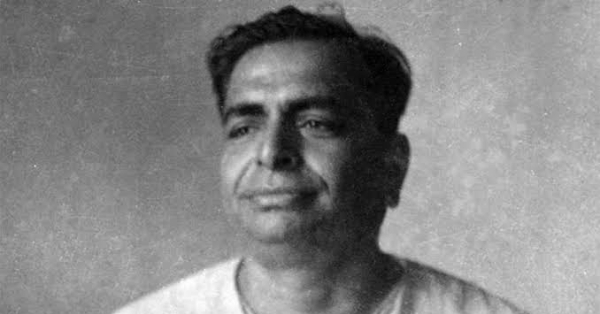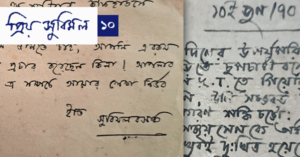ছাত্রবয়সে পাঠক্রমে অনেকরকমের গল্প পড়তে হত। ছোটগল্প, বড়গল্প, অণুগল্প, এইসব নানারকম নাম তাদের। গল্পকে শুধু গল্প বললেই যে চলে, একথাটা জোরগলায় কেউ বলেনি বলে আমরাও দুলে-দুলে সেই নাম পড়েছিলাম। অণুগল্প বা গল্পাণুর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে অবধারিতভাবে যাঁর লেখা গল্পের উদাহরণ টানতে হত, তিনি বনফুল। বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় নামটা আমাদের পছন্দ হয়নি, লেখকের নিজেরও হয়নি অবশ্য। বনফুলের গল্প পড়তে গিয়ে কিন্তু তাকে অণু-পরমাণু কিছুই মনে হয়নি, আস্ত গল্পই মনে হয়েছিল। আকারে বিস্তারে কিছু গল্প বেশ ছোট, সেকথা ঠিক, কিন্তু গল্প হবার যাবতীয় উপাদান সেখানে মজুত। আবার আয়তনে বিপুল গল্পও লিখেছেন তিনি, তাকে খামকা নভলেট বা উপন্যাসিকা বলার দরকার হয় না।
ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য বা গল্প লেখার কৌশল যদি সাহিত্যের রীতিনীতির একটা অক্ষ হয়, তবে এমনিতেও বনফুল সেখানে আলোচ্য হয়ে উঠতে পারেন। বেশ কিছু গল্প আছে, যেখানে গোটা গল্প জুড়ে যেন চলমান ছবির মতো গল্পটা হয়ে উঠতে থাকে। আখ্যান রচনার কক্ষপথ, কথনের মেজাজ, কথকের অবস্থান— সবই তাঁর গল্পে বেশ বৈচিত্র্যময়।
আরও পড়ুন: জীবনের কথা জীবনের ভাষায় বলার দায়বোধ ছিল রবীন্দ্রনাথের! লিখছেন আশিস পাঠক…
গল্প আর বাস্তব, বাস্তব আর কল্পনার ভেদ যেমন ক্ষীণ হয়ে যায়, লৌকিক-অলৌকিকের সীমাও তেমন আবছা হয়ে আসে অনেক ক্ষেত্রে। ‘পূজার গল্প’-এ বিষ্ণুচরণ বর্মা নামে এক ইনশিওরেন্সের দালাল ট্রেনে সহযাত্রী হিসেবে পান এক যুবককে, যিনি সরস পত্রিকায় সিনেনায়িকার ছবি দেখতে ব্যস্ত। তাঁকে বিমা করানোর জন্যে খানিকক্ষণ পীড়াপীড়ি করতেই তিনি দেখিয়ে দেন নিজের মাকে। মা ভারি স্নেহময়ী। উদ্ধত পুত্রের মতো বেচারা এজেন্টের সঙ্গে দুর্ব্যবহার না করে, তিনি ধৈর্য ধরে শোনেন সব কথা। তবে কিনা, তাঁরও তো দরকার হবে না এসবের। না, তাঁর স্বামীরও হবে না। ঘুমে ব্যাঘাত ঘটার জন্যে বাঙ্কের ওপর থেকে ততক্ষণে মুখ বের করে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন আরেক পুত্র, মুখের সঙ্গে দিব্য একটি শুঁড়ও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে! এতক্ষণ স্বয়ং জগজ্জননীকে জীবনবিমা বোঝাচ্ছিলেন শ্রীমান বিষ্ণুচরণ! জননী অবশ্য একেবারে নিরাশ করেন না। নিজেদের জন্যে না হলেও ‘বঙ্গদেশে পূজাটা ইনশিওর’ করে রাখতে চান। দৈবের প্রতি আস্থা বা আধ্যাত্মিক ভাব নয়, বনফুলের গল্পের প্রবণতা স্যাটায়ার। বিশ্বাসের কাঠামোকে বারবার চারপাশের জমিতে ফেলে যাচাই করে নেন তিনি, বিশ্বাস ভাঙা, তাই ব্যঙ্গের স্রোত খুলে যায়। সেই ব্যঙ্গ মাঝেমাঝে বেশ তেঁতো। মহাযুদ্ধোত্তর মানুষ ঈশ্বরকে আর কতটাই বা বিশ্বাস করতে পারে?
‘কার্তিকেয়-কাহিনী’ গল্পে একেবারে রাজশেখরীয় ভঙ্গি ও ভাষায় কার্তিকজন্মের দীর্ঘ আখ্যান লেখেন তিনি। এই আখ্যান পুনঃকথনের কী-ই বা প্রয়োজন ছিল? কৈফিয়ৎ দেন বনফুল— ‘উপরোক্ত গল্পটি মহাভারত হইতে টুকিয়াছি।… অবৈধ প্রণয়-মূলক গল্পও পড়া চলিবে অথচ ধরমও বজায় থাকিবে যদি মহাভারতটা একবার খুলিয়া বসেন। …তরুণ গল্প লেখক-লেখিকাগণও এই মহাভারতে নানারূপ প্লট খুঁজিয়া পাইবেন।… আর একদল পাঠক-পাঠিকা ও সমালোচক আছেন তাঁহাদের মত মাইকেলের পরবর্তী সাহিত্য মাত্রই অশ্লীল ও বাজে। অনেকেই পড়েন নাই কিন্তু তাঁহাদের মনটা সততই রামায়ণ মহাভারতমুখী। উপরোক্ত গল্পে তাঁহারা মহাভারতের নমুনা (অবশ্য সামান্যই) পাইবেন।’ ‘বিধাতা’ গল্পের ঈশ্বর দুনিয়ার সব মানুষের দাবিদাওয়ার ফর্দ দেখেটেখে নাকে-কানে তেল দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। আর গল্পকথক জানিয়েও দেন, সেই ঘুম আজও ভাঙেনি। এই মৃতভক্তিই সেই আমলের পক্ষে স্বাভাবিক। ‘রামায়ণের এক অধ্যায়’ গল্পে রামচরিত্রে অভিনয়কারী নকুড় মাইতে মঞ্চে অভিনয়কালে সীতাবিরহে কাতর হয়ে রাজ্য, ঐশ্বর্য বিসর্জন দিতে চান। মধ্যরাতে মাতাল হয়ে বাড়ির দরজায় ধাক্কা মেরে স্ত্রী হরিমতিকে বলেন, ‘হারামজাদি, আধঘন্টা ধরে দোর ঠেলছি, খেয়াল নেই?’ হরিমতি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু সে যুক্তি মাতাল নকুড় মাইতির মনে ধরবে কেন? তাই প্রহার শুরু হয়। বনফুল লেখেন— ‘… এক লাথি এবং রাম লাথি।’

এই পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাক্ষী নিশ্চয়ই ছিলেন বনফুল। যে-কারণে তাঁর এতগুলি গল্পে হেরে যাওয়া, খসে যাওয়া, ঝরে যাওয়া সব মেয়েদের দেখা যায়। নানা বয়সের মেয়ে। ‘অদ্বিতীয়া’ গল্পে বহুপ্রসবিনী স্ত্রীর মৃত্যুর ভুয়ো খবর পেয়ে স্বামী সামান্য উপরোধেই দ্বিতীয় বিবাহ করে নেন, শ্যালিকার ষড়যন্ত্রমাফিক অবশ্য প্রথম স্ত্রীকেই। ‘অনির্বচনীয়’ গল্পে বিপত্নীক অজয়কুমার বোস স্ত্রীর মৃত্যুর অল্প দিনের মধ্যেই ক্ষণিকা খাস্তগীরকে বিবাহের প্রস্তাব আনেন, ক্ষণিকা রাজি না হলে তারই বান্ধবী সুজাতাকে বিবাহ করেন, আর সেই বিবাহের অল্পদিন পরেই সুজাতার আত্মহত্যার সংবাদ ও অজয়-ক্ষণিকার পরিণয়সংবাদ আসে। ‘সমাধান’ গল্পের বুঁচির মত ছোট্ট মেয়েরা বড়জোর মরে যায়। নীহাররঞ্জনের কন্যা হলেও পুষ্পমঞ্জরীর মতো সুন্দর নাম তাকে মোটেই দেওয়া যায় না, কুচ্ছিত আর বোকা বলে আড়াই বছর বয়সেই তার বিয়ের সম্ভাবনা নিয়ে চণ্ডীমণ্ডপে ঘোর আলোচনা চলে। অবশেষে দুশ্চিন্তার সমাধান মেলে বুঁচির মরে যাবার খবরে। বনফুলের গল্পের মজা তার পরিসমাপ্তিতেই, একথা সমালোচকেরা বলে থাকেন। অদ্ভুত নির্লিপ্ত এক ভঙ্গিতে গল্পের জরুরি তথ্যগুলো সবশেষে দেন তিনি। ‘রাম লাথি’ শব্দবন্ধটির মধ্যেই যে আয়রনি, তা আর কোনও শব্দবিস্তার ঘটলে নষ্ট হত। বুঁচির মৃত্যুর খবর, ক্ষণিকার সঙ্গে অজয়ের বিয়ের খবর, সবই গল্পের উপসংহারে বড়জোর আধ-লাইনে বলে ছেড়ে দিয়েছেন তিনি। বহুপঠিত ‘তিলোত্তমা’, ‘বুধনী’, ‘ছোটলোক’- সব গল্পেই এই প্রবণতা দেখতে পাওয়া যায় সহজেই। যেন আরেকটা গল্প বলার খুব তাড়া এই কথকের, এখনই নতুন কোনও আসর জমিয়ে বসতে হবে, নতুন কোনও গন্তব্যের উদ্দেশ্যে এখনই বেরিয়ে পড়তে হবে।
বিশ্বাসের কাঠামোকে বারবার চারপাশের জমিতে ফেলে যাচাই করে নেন তিনি, বিশ্বাস ভাঙা, তাই ব্যঙ্গের স্রোত খুলে যায়। সেই ব্যঙ্গ মাঝেমাঝে বেশ তেঁতো। মহাযুদ্ধোত্তর মানুষ ঈশ্বরকে আর কতটাই বা বিশ্বাস করতে পারে?
চিকিৎসাবিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন বনফুল, মানুষের শরীর ও শরীরসংশ্লিষ্ট মনকে দেখেছিলেন। সংস্কার, অভ্যাস, জরাগ্রস্ত মানসিকতা তাঁর গল্পের মানুষগুলিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। সেই আচ্ছন্নতার প্রতি শ্লেষ তাই স্বাভাবিকভাবেই এসেছে। ‘বাঘা’ গল্পে তারিণীচরণের পোষ্য কুকুরটি যে আসলে তাঁরই দাদা সরোজ, এমন উদ্ভট বিশ্বাস তাঁর মাথায় ঢোকান জ্যোতিষ শিরোমণি। তারিণীচরণের চাকরি যাবার জন্যেই যে তাঁর ‘কুকুরযোনিপ্রাপ্ত’ দাদা অন্নজল ত্যাগ করেছে, এও বিশ্বাস করেন তাঁরা। রোগগ্রস্ত কুকুর প্রথমে তারিণীচরণকে কামড়ে মারা যায়, পরে তারিণীচরণ শিরোমণিকে কামড়ায়, জলাতঙ্কে দুজনেই মৃত্যুশয্যায়। ‘দিবা দ্বিপ্রহরে’ গল্পে পাগলা গারদ থেকে পালিয়ে আসা ফেরারি পাগলকে মহা গুণী ওঝা বিশ্বাস করে পাড়াসুদ্ধ লোক প্রকাণ্ড বিষধর গোখরো সাপ ধরতে দেয়। বিশু বাগদির ধরে ফেলা গোখরো নতুন করে ছাড়া হয়। সাপ পালায়, পাগলও মরে। কিন্তু শুধু কি এমন শ্লেষ? সঙ্গোপন রহস্যও কি নেই? ‘আত্ম-পর’ গল্পে মুখের ওপর সদ্যোজাত কুশ্রী পাখির ছানা পড়ায় তাকে ছুঁড়ে ফেলে যে যুবক, সে-ই যখন কয়েক বছর পর তার সাপে কাটা, মরাছেলেকে চিরকালের জন্যে চলে যেতে দেখে, তখন চিনতে পারে বিশ্বপ্রকৃতির অশ্রুত অজ্ঞাত অভিসম্পাত। পারুল-প্রসঙ্গ, একফোঁটা জল, খেঁকি— নানারকমভাবে মানবেতর প্রাণীদের সঙ্গে মানুষের সংযোগ ও সম্বন্ধের আখ্যান রচনা করেছেন বনফুল। পড়তে গিয়ে কখনও বিভূতিভূষণের বুধীর গল্প মনে পড়তে পারে, কখনও পরশুরামের লম্বকর্ণের গল্প। পোষ্যের প্রতি মমতা, অপত্যস্নেহ, অতিপ্রশ্রয়, বিচিত্র অধিকারবোধ ও সম্পর্কের কথা যেমন আছে, তেমনই ঠিক বিপরীত প্রবৃত্তির কথা আছে।
খেঁকি গল্পে যে কুকুরটি তার দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনা দেয়, তার অভিজ্ঞতা বিশেষ সুখের ছিল না।
পরস্পরবিরোধিতা, বিপরীতধর্মী দুই প্রকৃতির টানাপোড়েন, সাদা-কালো-ধূসরের খেলা বনফুলের গল্পের ভরকেন্দ্র। একইসঙ্গে তা মানুষের নিষ্ঠুরতা আর মানুষের অসহায়তার গল্প। একদিকে সংসারের ব্যস্ততায় হাবুডুবু খাওয়া, অন্যদিকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যে ছটফট করা; পারিবারিক বাধ্যতা আর সসংকোচ ব্যর্থতার গল্প, আমাদেরই গল্প। ‘হাসির গল্প’, ‘বেচারামবাবু’, ‘মাত্র দশটি টাকা’, ‘অজান্তে’, ‘ক্যানভাসার’, তালিকা দীর্ঘতর হয়। ছোট-ছোট চাকরি, অস্থায়ী কাজ, সামাজিক অসম্মান, ক্রমবর্ধমান পরিবার, অসচেতন অভ্যেস, মানুষগুলির ভেতর থেকে হৃদয় বলে ব্যাপারটাকেই প্রায় বাইরে ফেলে দিয়েছে। তারা ওপরওয়ালার ধমক খায়, সম্পাদকের তাগাদা পায়, ঘরদোর সামলাতে পারে না, সন্তানের কান্না-অসুখ-মৃত্যুতে তিতিবিরক্ত হয়ে পালাতে চায়, ঋণে জর্জরিত হয়ে যায়, আঘাত করে বসে অপরকে, গ্লানিতে দীর্ণ হয়, মধ্যবিত্ততার মুখোশ পরে, সমাজমান্য নিয়মে ‘ভদ্রলোক’ হয়ে জন্মানোর অজস্র অবান্তর ‘মেডেল’ ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়, দর পায় না কিছুই।