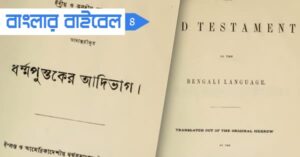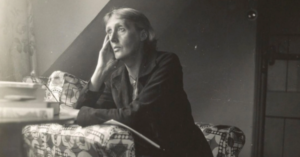আজ শ্রাবণের এই অবিশ্রান্ত জলধারায় আমরা আর বিজন ভট্টাচার্যকে পাব না। যে বিজন ভট্টাচার্য ‘সুবর্ণরেখা’-য় বলেছিলেন, ‘ঈশ্বর, আমারে কইলকাতায় নিয়া যাবা?’ সেই কলকাতায় আমরা আর থাকি না। আমরা যারা কিন্নর ও অপ্সরী, শপিং মলে পরিবৃত— তারা বিজন ভট্টাচার্যকে চিনতে পারব না। ‘নবান্ন’ বলতে আজকের কলকাতায় বোঝায় শুধুই একটি প্রশাসন কেন্দ্র। কেউ-ই জানে না, এই নাটক থেকে ভারতীয় আধুনিকতার সূত্রপাত।
এ-কথা না বলে কোনও উপায় নেই, আমাদের সব ছিল; পারিবারিক নাটক ছিল, ঐতিহাসিক নাটক ছিল, মহাকাব্যও ছিল। কিন্তু বিজনবাবু যেভাবে ‘নবান্ন’ নাটকে আমাদের পথে নামিয়ে আনলেন, নাটককে সরাসরি সড়কে নিয়ে এলেন, তা আমরা অনুমানও করতে পারিনি। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ‘দুর্গেশনন্দিনী’ বাঙালির হৃদয় লুঠ করে নিয়েছিল। উপন্যাসের মতো বিদেশি ফর্ম যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে পড়ে আমাদের চমৎকৃত করেছিল, তেমনই ‘নবান্ন’-ও এক প্রকার নতুন আলোকসম্পাত; একে শুধুমাত্র দুর্ভিক্ষ, অনশনের মঞ্চায়ন বলে পার পাওয়া যায় না।
‘নাট্যদর্শন’ পত্রিকায় ঋত্বিক ঘটক একবার বলেছিলেন, বিজনবাবুই প্রথম দেখালেন, কী করে জনতার প্রতি দায়িত্বশীল হতে হয়, কী করে সম্মিলিত অভিনয়-ধারার প্রবর্তন করতে হয় এবং কী করে বাস্তবের একটা অংশের অখণ্ড রূপ মঞ্চে তুলে ধরা যায়। গিরিশ ঘোষ থেকে শিশিরকুমার ভাদুড়ী পর্যন্ত প্রসারিত যে ব্যক্তিকেন্দ্রিক অভিনয়, তা প্রথম অস্বীকৃত হল ‘নবান্ন’ নাটকে এবং তারপর গণনাট্য সংঘে। এই যে বিজন ইতিহাসের পট পাল্টানোর মুখে বাইরের দ্বন্দ্ব আত্মসাৎ করে নিলেন উচ্চগ্রামী শরীরী অভিনয় দিয়ে, এটা ঋত্বিক ঘটকের কাছে চিরকাল অবিস্মরণীয় মনে হয়েছে।
আরও পড়ুন: বাদল সরকারের হাত ধরে চিনতে শিখেছি কলকাতাকে!
লিখছেন অঞ্জন দত্ত…
কিন্তু এত যুগ পরে আমার কাছে ‘নবান্ন’ সম্পর্কে যে-মত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সেটা এমন একজনেরই, যাঁকে সাধারণত বিজন ভট্টাচার্যর বিপরীত মেরুর বলে ভাবা হয়। অর্থাৎ, অবিস্মরণীয় শম্ভু মিত্র। তিনি বলেছিলেন ‘নবান্ন’-র আগে অবধি আমাদের সব ট্র্যাজেডিই পারিবারিক ট্র্যাজেডি; ‘নবান্ন’ এল এপিকের ব্যপ্তি নিয়ে। কী বলতে চেয়েছিলেন শম্ভুবাবু? যাকে বলা যায় নাট্য সংহতি ও নাট্য প্রবহমানতা, তা পুরোপুরি অস্বীকৃত হয়েছিল প্রবল সাহসী এই নাটকে। এই নাট্য আধুনিকতার মূল ভাষ্যের প্রতি নজর রেখে মুহূর্তনির্ভর। দৃশ্যের পর দৃশ্য জুড়ে আছে কান্নার একটি অদৃশ্য সুতো দিয়ে। তাই শম্ভু মিত্র বলেন— ‘একটা দৃশ্যে কুঞ্জকে কুকুরে কামড়েছে। শোভা কুকুরকে লক্ষ্য করে ওয়াইল্ডলি শাউট করে তারপরই সফটলি বলে: জল খাবে? জল তেষ্টা পেয়েছে?’
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য এই দৃশ্য দেখে বলেছিলেন, এটা শাশ্বত। এই মুহূর্তের জয় আধুনিকতার জরায়ুতে নিহিত। বোদলেয়ার, মার্ক্স ও নিৎসে-তে এই মুহূর্ত-বন্দনা ছত্রে-ছত্রে। বিজনবাবুর প্রথমাঙ্ক আর দ্বিতীয়াঙ্কের মধ্যে যাঁরা মিল খুঁজে পান না, অথবা শেষ অংশটিকে যাঁদের প্রক্ষিপ্ত মনে হয়, তাঁরা বুঝতেই পারেন না, যে তিনি আত্ম-আখ্যান রচনা করেননি, তাঁর মেধা নিবেদিত হয়েছে নাট্যসন্দর্ভ প্রণয়নে। এই সন্দর্ভধর্মিতা উনিশ শতকের শিল্পচর্চার একটি মূল অন্বিষ্ট। ‘নবান্ন’ একটি প্রকল্প, কিন্তু তা বাস্তবের অনুলিখন নয়।

‘নবান্ন’ যখন প্রথমবার পড়া হয়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, ‘আপনি তো জাত চাষা!’ বিজন ভট্টাচার্য তাঁর সারাজীবন যে উদ্দেশ্যে নিবেদন করেছিলেন, খতিয়ে দেখলে তা ইতালীয় শিল্পী পাসোলিনির মতো এক ন্যাশনাল পপুলারের উদ্বোধন।
ঋত্বিক ঘটকের শেষ ছবি ‘যুক্তি তক্কো আর গপ্পো’-তে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর মাস্টার চরিত্রটি ও জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়ের গ্রাম্য মুখোশ শিল্পীটির যে সংঘাত— তার অনুকুল তটরেখা রচনা করার জন্য বিজনবাবু ‘জীয়নকন্যা’ ও ‘দেবীগর্জন’ লেখেন। সেখানে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতিতে ব্রাহ্মণ অতিরিক্ত মনীষা কীভাবে কাজ করতে পারে সেই সন্ধান করেছেন।
আর যদি সিনেমার কথা বলি, তাহলে আজকের প্রজন্মের আমরা জানিই না যে, ‘ধরতি কে লাল’, যা সত্যজিৎ রায়ের মতেও ভারতীয় ছবিতে অন্য ধারার সঞ্চার করেছিল, তা আসলে বিজন ভট্টাচার্যের ‘নবান্ন’ এবং ‘জবানবন্দি’-র অনুসরণে রচিত। আমরা অধিকাংশ মানুষই জানি না, এই যে হিন্দি ছবি ‘নাগিন’ এত জনপ্রিয়, তার গল্প তাঁরই রচনা। বস্তুত ‘জীয়নকন্যা’ নাটকটি থেকে বিজনবাবু নাগিনের বিষয়টিকে জনপ্রিয়তার ছাঁচে ঢালার উপাদান খুঁজে পান। তবু হিন্দি ভাষায় বিজনবাবুর দক্ষতা না থাকায়, বা তত প্রমাণিত না হওয়ায় তিনি অস্বচ্ছন্দ বোধ করতে থাকেন, সঙ্গে-সঙ্গে ‘বোম্বাই’ ছবির বাণিজ্য-বায়ু তার পক্ষে সহনীয় মনে হয় না। তিনি কলকাতায় ফেরেন। এবং আমরা সঙ্গে-সঙ্গে দেখছি এই যে, উত্তমকুমারের অলৌকিক উত্থান ‘বসু পরিবার’ ও ‘সাড়ে ৭৪’-এ, পরপর এই দু’টি ছবিতে নির্মল দে তাঁকে চিত্রনাট্যকার হিসেবে বেছেছিলেন। পাশাপাশি শব্দশিল্পী হিসেবেও যদি বিজন ভট্টাচার্যকে দেখি, তিনিই আমাদের সেই শিল্পী, যিনি বলেন ভাষা তো দু’মাইল অন্তর-অন্তর পালটে যায়। এই যে ভাষার প্রতি প্রণাম, সংলাপ রচনায় তাঁর অনায়াস দক্ষতা এবং একইসঙ্গে ইতিহাসের প্রতি তাঁর যে আনুগত্য, আমাদের কাছে এখন তা বিস্মৃতির বিষয়, অনেক সময়ে হয়তো পরিহাসেরও।

বিজন ভট্টাচার্য শুধু ঋত্বিক ঘটকের অভিনেতা নন, শুধু ঋত্বিকের সমধর্মী এক শিল্পী নন, নিজ-অধিকারী এক চিন্তাবিদ। ‘দেবীগর্জন’ নাটকে মাতৃশক্তির যে উন্মোচন, তাকে ঋত্বিক ‘যুক্তি তক্কো আর গপ্পো’-তে ছৌ নাচের স্তরে-স্তরে খুঁজে পেয়েছেন। ‘দেবীগর্জন’— যা আসলে চাষির যুগ-যুগ সঞ্চিত বাসনা ও ক্রোধের প্রকাশ, তাঁকে ঋত্বিক ইতিহাসের একটি পালাবদলের মুহূর্তে জনসাধারণের সংস্কৃতিতে প্রোথিত দেখেছিলেন। কিন্তু তার আড়ালে বিজন ভট্টাচার্যের প্ররোচনা ছিল। জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক আলোচনা চক্রে, জীবনে মাত্র একবারই ইংরেজিতে বিজন ভট্টাচার্য জানিয়েছিলেন, ‘Drawn to a last ditch they are compelled to revolt. The violence of their revolt I associated with Devi’s Garjan, the roar of the angry goddess as long as my people make the gods and goddess dance, I am prepared to accommodate to belief of my people.’ জনসাধারণের যে অসামান্য প্রজ্ঞান, তাতে বিজন ভট্টাচার্যর বিশ্বাস ছিল; তাই তিনি একা-একা তপস্বীর মতো রাজেন্দ্র রোডে হেঁটে গেছেন, আমাদের চোখের সামনে দিয়ে রাসবিহারীর মোড়ে ফুটপাথে চা খেয়ছেন আর সামান্য একটি পেরেকের খোঁচা সহ্য না করতে পেরে খুব নির্জন মানুষের মতো, পদাতিক মানুষের মতো বিদায় নিয়েছেন। মৃণাল সেনের ‘পদাতিক’ ছবির শেষে, তাঁর সংলাপে একটিমাত্র বাক্য ছিল be brave! আমরা কি অত সাহসী হতে পারব?