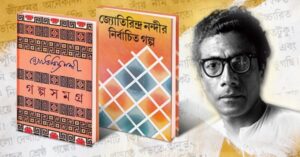ছোট, কালো, বাহারি কাঠের দরজা– দরজার এ-পাশে পড়ন্ত বেলার উঠোন, কয়েকগুচ্ছ লতা আর গাছ। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলে টিমটিমে পৃথিবী। একটেরে মানুষের সৃজনশীল পৃথিবী। ইতিউতি ছড়িয়ে আছে একটা-দুটো আঁকা ছবি, ধুলো পড়ে যাওয়া সম্মাননা-মানপত্র, পেপারকাট পাপেট। রাজস্থান-গুজরাতের কুলুঙ্গি-নকশা বাঁ-হাতের দেওয়াল জুড়ে, সেখানে কোনও খোপে কাঠের পেঁচা, কোনও খোপে টেরাকোটার পুতুল, কোনও খোপে হ্যাজাক, কোনও খোপে কেরোসিনের লণ্ঠন। কুলুঙ্গির সামনে একফালি তক্তাপোশে কয়েকটা পরপর বই— কোনওটার বিষয় ফ্রিদা কাহলো, কোনওটা ভাল রাক্ষস, কোনওটা আবার ভোটের কার্টুন। ছায়াপুতুলের বর্ষীয়ান শিল্পী স্বপ্না সেনের মোকাম। স্বপ্না সেন রঘুনাথ গোস্বামীর পুতুলনাচ ঘরানার মনোযোগী ছাত্রী। আড্ডা শুরু হয় কুলুঙ্গির কথা বলতে বলতে, মরুদেশের সহজ মানুষজনের ঘর-গোছানোর গপ্প দিয়ে। শুনছেন সোহম দাস।
আপনার ছোটবেলা কোথায় কেটেছে?
আমার ছোটবেলা কেটেছিল বার্নপুরে। তবে, আমার বাবা-মা দুজনেই ওপার বাংলার। বাবার বাড়ি ছিল যশোরে, মায়ের বাড়ি একজ্যাক্টলি কোনদিকে ছিল, সেটা ঠিক মনে নেই। হয়তো যশোরেরই আশপাশে কোথাও ছিল। মাঝে মাঝে মনে হয় খুলনা, কিন্তু সেটা সঠিক নয়, সেখানে সম্ভবত দিদিমার বাপের বাড়ি ছিল। আমার বাবা বার্নপুরে ইস্কোতে চাকরি পেয়ে গিয়েছিলেন। এক জ্যাঠার সঙ্গে কলকাতায় চলে আসেন, স্বাস্থ্য ভাল ছিল, ভাল ফুটবল খেলতেন, সেই কারণেই হয়তো চাকরি পেতে অসুবিধা হয়নি। বার্নপুরে প্রথম দিকে কোয়ার্টার এরিয়ার বাইরে আমরা থাকতাম। প্রথমে ভাড়া বাড়ি, তারপরে নিজেদের বাড়ি তৈরি হল। তারপরে, বাবা নিজের কোয়ার্টারও পেয়ে গেলেন। বিদ্যুৎ ছিল না, হ্যারিকেনের আলোতে আমরা পড়াশোনা করেছি। পড়তাম বার্নপুর গার্লস স্কুলে।
আরও পড়ুন : আটের দশকে সারাতে দেওয়া রেডিও জমিয়ে রেখেছেন আজও! রেডিওর ডাক্তার অমিতরঞ্জন কর্মকারের সাক্ষাৎকার…
সাংস্কৃতিক চর্চা কেমন হত?
বার্নপুরে ভারতী ভবন বলে একটা সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ছিল। এই ভারতী ভবন পশ্চিমবঙ্গের আরও অনেক জায়গায় আছে। সেখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হত, পুজো হত, খেলার জায়গা থাকত, এছাড়া, মাঠে যাত্রার আসরও বসত। দুর্গাপুজোটা বেশ হইহই করে কাটত। ওখানে প্রতিমা মানে একদম ডাকের সাজ। আচার-অনুষ্ঠানও খুব নিষ্ঠাভরে পালন করা হত।
আমার যখন এগারো-বারো বছর বয়স, তখন একদিন, বোধহয় এরকম মার্চ মাসই হবে, ফুরফুর করে হাওয়া দিচ্ছে চারিদিকে, ভারতী ভবনে নবনীদাস বাউল— পূর্ণদাস বাউলের বাবা, যিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও কাজ করেছেন– তাঁর গান শুনলাম। তখন তাঁর যথেষ্ট বয়স হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তখনও কী এনার্জি! চেহারাটা এখনও মনে পড়ে, আর ওঁর গলাটা ছিল একটু হাস্কি, পূর্ণদাসের মতো মিষ্টি গলা নয়। কিন্তু কী উদাত্ত আর অদ্ভুত সে কণ্ঠ, কী তার রেন্ডারিং! হাওয়ায় তাঁর পাগড়ি উড়ছে, তার মধ্যে গান গাইছেন, সে এক অপূর্ব ব্যাপার। তখন বাউল গান-টান কিছুই বুঝি না, কিন্তু এখনও মনে আছে।
এমন অনেক শিল্পীকে তখন আমরা বার্নপুরে দেখেছি। সারারাত ধরে আলাউদ্দিন, রবিশংকরদের বাজনা হচ্ছে। কখনও হয়তো আধুনিক গানের শিল্পীরা এলেন। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে দেখেছি, মানবেন্দ্রর (মুখোপাধ্যায়) গানও আমি ওখানেই শুনেছি। এছাড়া, দুর্গাপুজোর সময়ে নাচের অনুষ্ঠান হত। একজন বেশ নামকরা শিল্পী, পদবি সেন, নামটা মনে পড়ছে না, তাঁর নাচ দেখলাম একবার। যদিও আধুনিক গানের অনুষ্ঠানগুলো, বেশিরভাগ সময়ে খোলা মাঠেই হত আর উচ্চাঙ্গ সংগীতের অনুষ্ঠানগুলো ভারতী ভবনে হত।
আরেকটা অনুষ্ঠানের কথা বিশেষভাবে মনে আছে। একটা ম্যামথ রবীন্দ্রসংগীতের অনুষ্ঠান। সেখানে কে না যাননি! দেবব্রত বিশ্বাস থেকে শুরু করে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। এটাও মনে আছে, একজন শিল্পীকে দুটোর বেশি গান গাইতে দেওয়া হয়নি। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় গিয়েছিলেন কি না, মনে নেই। তাঁর গান অবশ্য পরে শান্তিনিকেতনে অনেক ভালোভাবে শুনেছি। শান্তিদেব ঘোষকেও শান্তিনিকেতনেই দেখেছি।
আর, সিনেমা বা থিয়েটার?
আমার একদম ছোটবেলায়, মাঠে পর্দা টাঙিয়ে সিনেমা দেখার একটা হিড়িক ছিল, মনে আছে। সে পর্দা উড়ে যেত, কখনও-কখনও ছিঁড়েও যেত। খুব আবছা মনে আছে, একবার ‘নৌকাডুবি’ (সম্ভবত, ১৯৪৭ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত, নরেশচন্দ্র মিত্র পরিচালিত) দেখানো হচ্ছে। আর, যে সিনেমাটা প্রথম দেখেছিলাম, অর্থাৎ, যেটার কথা এখনও পরিষ্কার মনে আছে, সেটা হল তপন সিংহের ‘কাবুলিওয়ালা’ – এটা ভারতী ভবনে দেখানো হয়েছিল।
কলকাতার সংস্কৃতি জগতের ভাল যা কিছু, তার সবটাই কিন্তু ওখানে আমরা পেতাম। কারণ খুব সহজ। ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, যাঁরা ওখানে চাকরি করেন, তাঁদের ভালোই পয়সাকড়ি ছিল। কলকাতার আর্টিস্টদের আনতে কোনও অসুবিধা হত না। পুরো আয়োজন, অতিথি-আপ্যায়ন বেশ গোছানোই হত। তবে, আমাদের ছোটবেলায় ওখানে নাটকের কম্পিটিশন এসব অত দেখিনি। এখন তো অনেক দল হয়েছে, যারা কলকাতায় এসে নিয়মিত শো করে, কিন্তু তখন এই কালচারটা অত গড়ে ওঠেনি।
তবে, সবচেয়ে ভাল দেখেছি যাত্রা। যাত্রার যত ভাল প্রোডাকশন, সব আমি ওখানেই দেখেছি। ‘রানী লক্ষ্মীবাঈ’ থেকে শুরু করে কোনটা নয়! নট্ট কোম্পানি, আরও অন্যান্য যাত্রার দল ওখানে আসর বসিয়েছে। নট্ট কোম্পানিতে কোনও মেয়ে ছিল না, ওখানে সব ছেলেরাই মেয়ে সেজে অভিনয় করত। বাবলিরানীর (আসল নাম, প্রকৃতীশ ভট্টাচার্য) অভিনয় তো চোখে লেগে রয়েছে। স্বপনকুমারের অভিনয় তো এখনও চোখের সামনে ভাসে। তখন ওঁর বয়সও অল্প, আর অভিনয়টাও যাত্রার চিরাচরিত স্টাইলে নয়, সেজন্য ভীষণভাবে চোখে লাগত। আমার বাবা দানীবাবুকেও দেখেছেন, আমি অত দেখিনি, কিন্তু যা দেখেছি, তাও মনে রাখার মতো। সেখানে, কলকাতায় যাত্রা দেখতে বসে একটুখানি দেখেই কিন্তু আমি অনুভব করেছি, আমার মন ভরছে না। মহাজাতি সদনেই হোক কি খোলা মাঠেই হোক, আমার ভালো লাগেনি। আমার বাড়ির এই সামনের মাঠে, আমি যখন প্রথম আসি, তখন যাত্রা হত, কিন্তু সেই বার্নপুরের যাত্রার কোয়ালিটি এখানে আমি পাইনি। ওখানকার পরিবেশের সঙ্গে যাত্রাটা খুব মানানসই হত।

আচ্ছা, ওই সময়ে ওখানে পুতুলনাচের কোনও পারফরম্যান্স দেখেছেন বলে মনে পড়ে?
পুতুলনাচ সম্ভবত দেখিনি। আসলে, সব অনুষ্ঠানই যে দেখতে যেতাম, তেমনটা তো নয়। আমার বাবা যাত্রার পোকা ছিলেন, তাঁর সঙ্গে প্রায়ই যাত্রা দেখতে যেতাম।
কলকাতায় যাতায়াত কেমন ছিল?
কলকাতায় যাতায়াত ছোটবেলা থেকেই ছিল। আমার জন্মই তো শুনেছি, মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। দিদিমা কলকাতাতেই থাকতেন। মা ছিলেন বাড়ির ছোট মেয়ে, ফলে দিদিমা মেয়ে-অন্ত প্রাণ ছিলেন। বড়মামার পোস্টিং ছিল শিয়ালদায়, মাঝেরহাট রেলস্টেশনের কাছে কোয়ার্টার নিয়েছিলেন। সেই সময়ে, মানে আজ থেকে ষাট-সত্তর বছর আগে, তার ভাড়া ছিল চল্লিশ টাকা। সে যুগে চল্লিশ টাকা মানে অনেক। তবে, সে বাড়িটা ছিল অসাধারণ, কোনও ব্রিটিশ চাকুরে সম্ভবত বানিয়েছিলেন। মাঠের সমান দুটো বিশাল হলঘর ছিল, সেই দুই ঘরে দরজার মাপের বড়ো বড়ো জানলা, সেই জানলা দিয়ে সমানে পাখিরা আসত-যেত। কয়েকটা ছোট ঘরও ছিল। খুব উঁচু সিলিং, সিলিংয়ে কড়ি-বরগা দেওয়া। সিড়িটা ছিল কাঠের, আর পুরনো আমলের আয়রন কাস্টিংয়ের রেলিং। বাড়িটা থেকে কিছু দূরেই টাঁকশালটা, দেখা যেত। টাঁকশালের অন্য পাশে বেহালা, তখনকার বেহালা মানে খানা, খন্দ, পুকুর। মাঝেরহাটের এই বাড়িতে এত গিয়েছি, যে এখনও সব ছবির মতো মনে আছে।
তখন আমাদের কাছে কলকাতা বলতে কিন্তু শিয়ালদা, কলেজ স্ট্রিট এসব। আমার দিদিমার বোনের বাড়ি ছিল আমহার্স্ট স্ট্রিটে। ওখানে এসে আমরা উঠতাম। দিদিমা আমায় নিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতেন। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির সেনেট হল আমি দেখেছি। এছাড়া, গঙ্গার ঘাটে জাহাজ দেখার স্মৃতি আছে। মেজমামা একবার আমায় ২৬ জানুয়ারির কুচকাওয়াজ দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। ৩এ বাসটার কথা মনে আছে। আরেকটু বড়ো হতে কলকাতার যে জায়গাটা খুব টানত, সেটা হল ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম। মিউজিয়ামে গিয়ে অনেকক্ষণ সময় কাটিয়েছি। নানা রকমের কাপড়ের একটা গ্যালারি ছিল, অন্যান্য আর্টওয়ার্কও ঠাসা ছিল, ওই গ্যালারিটা খুব ভাল লাগত। একটা কুমিরের পেটে মেয়েদের গয়না পাওয়া গিয়েছিল, সেটাও খুব আকর্ষণের জায়গা ছিল। আর দেখতাম মিনিয়েচার পেন্টিংয়ের কালেকশনটা।

তাহলে কি এই সময় থেকেই শিল্পের প্রতি একটা সহজাত আকর্ষণ তৈরি হচ্ছে, না কি সেটা আরও ছোট থেকেই তৈরি হয়েছে?
এখানে একটু বিস্তারিতভাবে বলা দরকার। আমাদের বার্নপুরের স্কুলে একজন আঁকার শিক্ষক ছিলেন, তিনি বোধহয় শ্রীনিকেতনে পড়াশোনা করেছিলেন। তিনি যে ধরনের আলপনা দিতেন, সেগুলো আমায় খুব আকর্ষণ করেনি। কারণ, সেখানে টিপিক্যাল শান্তিনিকেতনী স্টাইল ছিল। ওই স্টাইলটার প্রতি কী কারণে জানি না, আমার একটা রেজিস্ট্যান্স তৈরি হয়েছিল। সেই থেকে ‘শান্তিনিকেতন মানেই ওই লতাপাতা’, এরকম একটা ধারণা তৈরি হয়েছিল। তখন নন্দলাল বসুকে জানি না, তার উপর শান্তিনিকেতন সম্পর্কে সকলের মধ্যে একটা নেগেটিভিটি কাজ করত, ‘এই গরু, সর না’ বা ওই চেহারার মধ্যে লতানে ভাব, শান্তিনিকেতনি ঝোলা— এই ব্যাপারগুলো আমাকেও প্রভাবিত করেছে। পরে অবশ্য এই ভুলগুলো ভেঙেছে।
সেই ভদ্রলোক পরে অন্য আরেকটা স্কুলে চলে যান, ফলে দীর্ঘদিন আমাদের স্কুলে কোনও আঁকার টিচার ছিল না। আমার ছবি আঁকার জগতের সঙ্গে জুড়ে ছিল ম্যাগাজিনের ছবি। বিভিন্ন পুজোসংখ্যা আর কাগজের ইলাস্ট্রেশন, এই ছিল আমার আঁকা শেখার সোর্স। দু-একটা বাড়িতে ভাল ভাল ক্যালেন্ডার আসত, সেগুলো দেখে দেখে কিছুটা শিখেছি। রঘুদার করা ক্যালেন্ডার আমি তখনই দেখেছি, কিন্তু তখন তো তাঁকে চেনার প্রশ্নই নেই।
আরেকজন ভদ্রলোক ছিলেন, তাঁর নাম দেবেন দাস, হাওড়ার মানুষ, ইস্কোতেই চাকরি করতেন— তাঁর ছবি আঁকার অভ্যাস ছিল। তবে, প্রথাগত প্রশিক্ষণ ছিল না, দেখে দেখেই ছবি আঁকতেন। এছাড়া, দুর্গাপুজোর ডেকরেশন করতেন। তাঁর কাছেই আমি প্রথম রং-তুলি দেখি। তখন গিটার কোম্পানির ওয়াটারকালার খুব চলত, দেবেনবাবুর কাছে আমি সেই গিটারের রং দেখেছিলাম। আমাকে তখন রং-তুলি কিনে দেওয়ার কথাও নয়, তবে রং পেন্সিল কিনে দেওয়া হত। ছোটোবেলার ছবি আঁকা বলতে এই।
বার্নপুরে বাউরি সম্প্রদায়ের কিছু বাড়ি ছিল, বাবা-মায়ের হাত ধরে একদম ছোটোবেলায় যখন বেড়াতে বেরচ্ছি, সেসব বাড়ির দেওয়ালে নানা জিওমেট্রিক প্যাটার্নের আলপনা, নকশা দেখছি। তবে সেগুলোও যে তেমন আকর্ষণ করছে, তা নয়। দেখছি, ওই পর্যন্তই। আর্ট কলেজের খবর পাওয়ার আগে অবধি আর্ট স্কুল কী, আর্টিস্ট কী, এসব ব্যাপারে কোনও ধারণাই ছিল না।
‘পাপেটের যে টাইনিনেস, তার মধ্যে একটা মজা আছে। হ্যাঁ, যে যার খুশিমতো কাজ করতেই পারে, কুড়ি ফুটের পাপেটও হয়, পাপেট নিয়ে অনেক ধরনের এক্সপেরিমেন্ট চলছেই— সেটা চলাটাই উচিত। কিন্তু, সারা পৃথিবীতে ছোট পাপেট নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ হচ্ছে।’
গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে ভর্তি হওয়া কবে?
১৯৬৭ সালে। আর্ট কলেজের খবরও যে কীভাবে পেয়েছিলাম, সেটাও এখন আর মনে নেই। মিউজিয়াম যেতাম ঠিকই, আর্ট কলেজ তার পাশেই। কিন্তু খবরটা বোধহয় কোনও ম্যাগাজিনেই বেরিয়েছিল। খুব যে বুঝেও গিয়েছিলাম, তেমনটা নয়। আর্ট কলেজ আছে, সেখানে আর্ট শেখা যায়, এইটুকুই জানতে পেরেছিলাম।
নেপথ্যে অবশ্য আরেকটা ঘটনাও ছিল। ভারতী ভবনে লেডি রাণু মুখার্জি একটা আর্ট এক্সিবিশন করেছিলেন। ওই আমার প্রথম এক্সিবিশনে ছবি দেখা। তখন বোধহয় ক্লাস নাইনে পড়ি। কলকাতার বড় আর্টিস্টদের ছবি সেখানে আনা হয়েছিল। ঠিক কারা ছিলেন, মনে নেই, তবে বড় বড় ক্যানভাসে আঁকা ছবি দেখানো হয়েছিল, সেটা মনে আছে। কিন্তু, তখনও অবধি একাডেমি কী, এসব কীভাবে হয়, লেডি রাণুই বা কে, কিচ্ছুটি জানি না। পরে জেনেছি, ইস্কো ওঁরই স্বামী বীরেন মুখার্জির করা, লেডি রাণুর নিজেরও অনেক প্রতিপত্তি, একেবারে ‘সোসাইটি লেডি’ বলতে যা বোঝায়, সেরকম ছিলেন। চৌখস চেহারা, চোখজোড়াও তেমন জ্বলজ্বল করত।
১৯৬৫ সালে স্কুল ফাইনাল পাশ করলাম। ক্লাস নাইনে পড়াকালীনই ইন্টার-স্কুল আর্ট কম্পিটিশনে ফার্স্ট হয়েছিলাম, ছবি আঁকিয়ে বলে মোটামুটি একটা পরিচয় তৈরি হয়েছে। আঁকতেও কেউ বাধা দেননি, আমাকে রং-তুলি কিনে দেওয়া হয়েছে, ড্রাই প্যাস্টেল কিনে দেওয়া হয়েছে, রঙিন কাগজ কিনে দেওয়া হয়েছে। এসব ব্যাপারে সবচেয়ে স্পয়েলিং ছিলেন আমার বাবা। আমার জন্য রঙিন কাগজ চৌরস করে স্কেল দিয়ে তিনি লাইন টেনে দিচ্ছেন। কীরকম অসভ্য মেয়ে আমি, তাহলে ভাবো! (হাসি) ওই লাইন টানার কাজটাও আমি করছি না, কারণ, আমার বক্তব্য, আর্টিস্টরা আবার স্কেল ধরে নাকি!
এই ভুল ধারণাটার জন্য আজও আমায় ভুগতে হয়, সেট-স্কোয়্যার দিয়ে লাইন টানতে গেলেও বেঁকিয়ে ফেলি। রঘুদার মতো লোকের সঙ্গে থেকেও এগুলো আমার ঠিক হল না। আমার এই কতকগুলো ব্যাপার ভীষণ খারাপ। একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে বসে গেলে আর সেটার পরিবর্তন হয় না। আর্টিস্ট হতে গেলে শুধু ছবি আঁকলেই চলে না, কিছু টেকনিক্যাল ব্যাপারও জানতে হয়, সেগুলো আমি আয়ত্ত করতে পারিনি। ওই কারণেই, আর্ট কলেজের সেকেন্ড ইয়ারে লেটারিং, বুক কভারের যে পরীক্ষাটা ছিল, সেটায় আমি ডাহা ফেল করেছিলাম। কিন্তু অন্য সাবজেক্টগুলোয় ভাল করেছিলাম বলে পাশ করেছিলাম। (হাসি)
কলেজজীবন কেমন কাটল?
ফার্স্ট ইয়ারে লাইফ স্টাডি, ফোলিয়েজ আর ডিজাইনিং। তখন এগুলো সবই প্রাথমিক পর্যায়ে, খুব শক্ত ব্যাপার ছিল না। সুশীল সেন, মৃদুল ঘোষ, বরেণ নিয়োগী, ধীরেন ব্রহ্ম, এঁদের কাছে ক্লাস চলছে। সুশীল সেন কিছুদিনের মধ্যে রিটায়ারও করে গেলেন।
প্রথম টার্মের পরীক্ষায় কুড়িটা কি পঁচিশটা স্কেচ জমা করতে হবে। স্কেচ করতে তো জানি না, শিখিনি। একটু-আধটু লাইফ স্টাডি শিখতে চেষ্টা করছি। তবে, খুব ভালো করতে পারছি ফোলিয়েজটা। ফোলিয়েজের ফর্ম, কালারিং, এগুলো খুব ভালো হচ্ছে। মডেলিংটা মোটামুটি স্তরের। একদম খারাপ হচ্ছে ডিজাইনটা। ফোলিয়েজটা এত ভালো করলাম যে তার পুরস্কার হিসেবে আমার ফি হাফ হয়ে গেল।
স্কেচের ব্যাপারটায় আসি। বলে দেওয়া হল, বিভিন্ন জায়গায় যাবে, এভাবে বসে আঁকবে। কিন্তু, আমি তো রাস্তাঘাট কিছুই চিনি না। আমি দিদাকে দেখে স্কেচ করছি, একে ধরছি, তাকে ধরছি। তারপর, গ্লাস-মার্কিং পেনসিল আর কালো রং ব্যবহার করে ড্রয়িংয়ের যা নমুনা জমা দিলাম, সেগুলো দেখে মৃদুলদা বললেন, দু-হাজারটা স্কেচ করলে যদি তোমার হয়!
ড্রয়িংয়ে পাশ করতে পারলাম না। এদিকে অনেকেই ভাল করছে। বিভিন্ন জায়গায় তারা গিয়েছে, শিখেছে। আমি তখন ভাবতে লাগলাম, কীভাবে আয়ত্ত করা যায়। আমাদের ব্যাচে মাধব বলে একজন ছাত্র ছিল। সে থাকত কসবার দিকে। তার নামও মাধব, কাজেও সে বিদ্যাসাগরের সেই ভাল বালক মাধবের মতো। তার বাড়ি থেকে আবার কেবল মান্থলিটাই করে দিত, আর কোনও টাকাপয়সা দিত না। (হাসি) কম্পারেটিভলি, আমার অবস্থা তার চেয়ে একটু ভালো। সে আমায় বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যেত। কলেজ আওয়ারের বাইরে যে ড্রয়িংটা দরকার, সেটার বিষয়ে ওই মাধবই আমায় সাহায্য করেছে। পরের বারে আর স্কেচে ফেল করিনি। শিয়ালদায় বসে স্কেচ, হাওড়ায় বসে স্কেচ, এভাবেই ক্রমশ এগিয়েছে।
সেকেন্ড ইয়ারেও আবার কম্পোজিশনে বেস্ট মার্কস পেলাম, এদিকে লেটারিংয়ে ফেল, যেটা একটু আগেই বললাম। লাইফ স্টাডিতে সেই মধ্যমানেই থেকে যাচ্ছি।
আমার ফাইন আর্টসের দিকেই যাওয়ার কথা। কিন্তু, সেক্ষেত্রে অত ক্যানভাসের খরচ কীভাবে আসবে, বাড়ি থেকে সেটা পারবে কিনা, এতশত ভেবে আমি ইন্ডিয়ান স্টাইল অফ পেইন্টিংটাই নিলাম। তবে আর্ট কলেজে থাকাকালীন আমি প্রায় সব ডিপার্টমেন্টেই কাজ করেছি। পেইন্টিংও করছি, ড্রয়িংও করছি, আমাদের কলেজে নিখিল বিশ্বাসের এক্সিবিশন হল, তখন উনি মারাও গিয়েছেন, সে এক্সিবিশন দেখে এসে ঘোড়ার ড্রয়িং করা শুরু করেছি। ব্যাচের মেয়েরা বলত, এই স্বপ্নার জন্য আমরা সবাই বকুনি খাই।
এমনকী, কলেজে পড়তে পড়তেই আমি বাইরেও কাজ করা শুরু করেছি। মানে, ছবি আঁকা-সংক্রান্ত কাজ।
সেটা কোন সময়ে?
ওই ’৬৯ সালের শেষ কিংবা ’৭০ সালের শুরু, এরকম একটা সময়ে। তখন আমি বুঝতে পারছি, আর্টিস্ট হতে গেলে শুধু আর্ট নিয়ে থাকলেই হবে না। ফলে, ভাল লেকচার, ভাল থিয়েটার, ভাল সিনেমা, যা কিছু ভাল হচ্ছে কলকাতায়, আমি ছুটে যাচ্ছি। মীরা মুখার্জির স্কাল্পচারের এক্সিবিশন সেই কোথায়, সুচিত্রা সেনের বাড়ির ওখানে হচ্ছে, সেখানে খুঁজে খুঁজে চলে গিয়েছি। মীরাদির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতাও তৈরি হয়েছিল।
এইখানে একটা প্রশ্ন করব। তখন আপনি একটা প্রথাগত প্রতিষ্ঠানের ছাত্রী। সেখানে আর্ট নিয়ে সর্বক্ষণের চর্চাটাই দস্তুর। কিন্তু, এই আর্টের বাইরের পৃথিবীটাকেও যে জানা দরকার, এই বোধটা কীভাবে এল?
এই বোধের জায়গাটা কীভাবে এল, বলাটা কঠিন। এরকম বলা যেতে পারে, তখন আমি সব মিলিয়েই আর্টকে বোঝার চেষ্টা করছি। তখনকার সময়টার একটা প্রভাব অবশ্যই ছিল। ওদিকে ভিয়েতনাম যুদ্ধ চলছে, এদিকে নকশাল আন্দোলন। পূর্ব বাংলায় আন্দোলন শুরু হয়েছে। কিছু বছর পরে হেমন্ত বোসকে গলা কেটে খুন করল। ’৬৮ সালে গরমের ছুটিতে ডুয়ার্সের এক চা বাগানে গিয়েছিলাম, আমি আর দিদি। আমার এক দাদা ওখানে ম্যানেজার ছিলেন। ওখানে তখন কানু সান্যালের খুব দাপট। ওই দাদা কিছুতেই আমাদের একা ছাড়ত না। বলত, এখানে নকশালরা খুব স্ট্রং। চা বাগানের ম্যানেজারদের ওরা শত্রু মনে করে।
এবার যে কাজের কথাটা বলছিলেন, সেটা বলুন।
আমি ভীষণ সচেতন ছিলাম বলে বিভিন্ন রকম মানুষের সঙ্গে আমি আলাপ করতাম। ‘নয়ন কবীরের পালা’ লিখেছিলেন যিনি, সেই নভেন্দু সেনের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। একজন আর্টিস্ট, তিনি নাটক লিখছেন, ছবি আঁকছেন, অন্যান্য পরিকল্পনা করছেন, সেই নভেন্দু সেন ভারতের স্বাধীনতার ওপর একটা সিরিজ করলেন, ১৯৭০ সালে লেনিন শতবর্ষ নিয়ে কাজ করলেন। সেই ’৭০ সালে আমি ‘শীতপ্রাসাদ আক্রমণ’-এর উপর একটা বিশাল ছবি আঁকলাম। সেই ছবি সোভিয়েত অবধিও পৌঁছেছিল। নভেন্দু সেনের আর-একজন আর্টিস্ট বন্ধু ছিলেন, বাঁধন দাস। রাজনৈতিকভাবেও খুব সক্রিয়। লেনিন শতবর্ষের সূত্রে বাঁধনদার সঙ্গে আলাপ হল।
নভেন্দুদার সূত্রে বাগবাজারের একটা স্কুলে, নাম ‘চিত্র নিকেতন’— আমার যাতায়াত শুরু হল। একদিন দুপুরবেলা স্কুলে যাচ্ছি, তখনই একটা লাশ পড়েছে। চারদিক শুনশান, থমথম করছে। ওই স্কুলটা আসলে এক ভদ্রমহিলার বাড়ি, সেখানে তাঁর ভাশুরের অংশে তিনি কিছু বাটিকের কাজ করতেন, আর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আঁকা শেখানো হত। ওখানে সবচেয়ে ভাল ব্যাপার ছিল এই যে, শেখার ব্যাপারে ছেলেমেয়েদের খুব স্বাধীনতা দেওয়া হত। অর্থাৎ, বাটিতে রং গুলে দেওয়া হত, বাচ্চারা তুলি ডুবিয়ে ছবি আঁকত।
ওই স্কুলের ছেলেমেয়েরা একবার হাওড়ায় একটা কম্পিটিশনে গেল। সেখানে জাজ হয়ে এসেছিলেন গণেশ হালুই। অন্যান্য জায়গা থেকেও অনেকে এসেছে। এবার, একটি ছেলে, অসম্ভব ভাল আঁকত, প্রাইজ পেল না বলে আঁকাই ছেড়ে দিল। সেই থেকে আমি ঠিক করেছিলাম, কোনও কম্পিটিশনে আমি কোনও ছেলেমেয়েকে পাঠাব না। আরও একটা চেতনা এখানে কাজ করেছিল। আমি দেখছি, আর্ট কলেজ থেকে বেরনো মানেই সবটা খুব একাডেমি-কেন্দ্রিক, অর্থাৎ, ওই চেনা লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই ধরনটাকে ভাঙার প্রয়োজন ছিল। বড়দেরকে পাল্টাতে পারব না, বাচ্চারা নরম মাটি, অতএব, তাদেরকে নিয়ে কাজ করা যেতে পারে। সেই আমার শুরু। আজকেও আমি বাচ্চাদের নিয়েই বেশি কাজ করে যাচ্ছি।

রঘুনাথ গোস্বামীর সঙ্গে আলাপ কি ওই সময়েই?
রঘুদার সঙ্গে আলাপ হল ১৯৭১ সালে। সেটাও একটা ঘটনা। রঘুদা বিবেকানন্দ সেন্টারে একটা এক্সিবিশন করবেন, সেটার জন্য আর্টিস্ট খুঁজছিলেন। অসিত পাল আমায় নিয়ে গেল। অসিত আমার চেয়ে এক বছরের জুনিয়র ছিল। ওই একজিবিশনে আমার সঙ্গে ছিলেন অমল চাকলাদার, অশোক বিশ্বাস, এঁরা।
একজন মানুষ যে এত সুন্দরভাবে কথা বলতে পারেন, সেটা রঘুদার আগে কাউকে দেখিনি। আমি খানিক মুগ্ধই হয়ে গেলাম বলা চলে। আমি তক্কে তক্কে থাকতাম, কীভাবে আরেকটু ওঁর সঙ্গে কথা বলা যায়। ভাল ভাল ছবির একজিবিশন তখনও হচ্ছে, কিন্তু আমি আর বেশি পাত্তা পাইনি। সেটাই খুব স্বাভাবিক, আমি তখনও আর্ট কলেজে পড়ছি। কিন্তু, ভাল ছবি এলে সবসময়েই ওঁর অফিসে সেগুলো দেখতে যেতাম। অফিসটা ছিল কিরণশঙ্কর রায় রোডে।

তারপরে ঘনিষ্ঠতা বাড়ল কীভাবে?
তখনও আমি ঘোড়ার আস্তাবলে বসে ঘোড়ার বড় বড় ছবি আঁকছি। একটা পেইন্টিং করলাম, আকারে এত বড় হল যে, রাখার খুব মুশকিল। ওঁকেই সাহস করে বললাম, আপনার অফিসে একটু রেখে দেবেন? উনি আপত্তি করলেন না, বললেন, কিছুদিনের জন্য রাখতে পারো।
এইভাবে একটু একটু করে ওঁর অফিসে যাতায়াত বাড়ছে। চিত্র নিকেতনের বাচ্চাদের নিয়েও ওঁর সঙ্গে কথা বলছি। সেই সময়ে উনি চাইল্ড সাইকোলজি নিয়েও ভাবনাচিন্তা করছেন। বাহাত্তর কি চুয়াত্তরটা দেশের সঙ্গে যোগাযোগ করে চিলড্রেন্স ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল আয়োজন করছেন, এগুলো আমি দেখিনি, সবটাই শুনেছি। ছোটদের ছবি নিজেও দেখছেন, ছোটদের জন্য ব্যবস্থাও করছেন। চিত্র নিকেতনেও একদিন নিজে এলেন।
এরপর আমার কাছে খবর এল, উনি পাপেট থিয়েটার নিয়ে আবার কাজ করবেন। সেটা শুনে আমি একদিন কোনও একটা গল্পের প্রসঙ্গে ওঁকে একটা প্রস্তাব দিলাম, এই গল্পটা যদি পাপেটের মাধ্যমে করা যায়। তাতে উনি আমার দিকে তাকালেন, কিন্তু কিছু বললেন না। আসলে, উত্তর দেওয়ার প্রয়োজনও মনে করেননি।
এই প্রসঙ্গে আরেকটা কথাও বলা দরকার। আর্ট কলেজে আমাদের বন্ধুবান্ধবদের একটা অ্যাসোসিয়েশন ছিল। কাঞ্চন দাশগুপ্ত, দেবব্রত চক্রবর্তী, এরা যদিও আমার চেয়ে কিছু সিনিয়র, কিন্তু সবাই একসঙ্গেই বসতাম। কে কোথায় ভাল নাটক করছে, বা ভাল সিনেমা করছে, সেটা নিয়ে আমাদের আলোচনা চলত। কাঞ্চন অসম্ভব প্রতিভাবান, আমার সঙ্গে খুব বন্ধুত্বও ছিল, কিন্তু পরে সেটা নষ্ট হয়ে যায়। কাঞ্চন একটা নাটক করে, নাম ‘লঙ্কাদহন পালা’, খুব প্রমিসিং প্রোডাকশন। ওর সঙ্গে রঘুদার যোগাযোগ হয়েছিল অন্যভাবে, আমার সঙ্গে অন্যভাবে। অথচ, ওর নাটকে রঘুদা মেক-আপটা দেখছেন, আমি সেখানে রঘুদাকে সাহায্য করছি। অনেক কিছু শিখছি।
তারপরে, কাঞ্চন দিল্লি চলে গেল। কালীঘাটে প্রান্তিক বাচ্চাদের নিয়ে যে সংস্থাটা করেছিল, সেই ‘দখিন বায়ু’-ও সেভাবে টিকল না। কাঞ্চন নিজেও রঘুদার কাছে টিকল না, কিন্তু আমি টিকে গেলাম। রঘুদার এই শেষের দিকের যে পাপেট থিয়েটারের ব্যাচ, মানে ’৭১ সাল থেকে, সেখানে আমি দিব্যি টিকে গেলাম। রঘুদার আস্থাভাজন হওয়াটা খুব সহজ কাজ ছিল না। আজকে যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, তাতে রঘুদার শিক্ষার অবদান তো আছেই, সঙ্গে আমার নিজেরও জোর নিশ্চয়ই ছিল।
রঘুনাথ গোস্বামীর কাজের পরিসর তো ছিল বিরাট, বিজ্ঞাপনের ছবি বা বইয়ের অলংকরণ থেকে শুরু করে নাটকের সেট, প্রোডাকশন হাউস ‘ভিডিওপ্যান’, এমন অনেক কিছু। সেক্ষেত্রে তাঁর যে পাপেট থিয়েটার, সমসাময়িকদের নিরিখে রঘুনাথ গোস্বামীর পাপেট থিয়েটারের ধারাটা ঠিক কীরকম ছিল?
রঘুনাথ গোস্বামীর ধারাটা একদম অন্যরকম। সেই সময়ে পাপেট থিয়েটারে দু’জন বড় নাম পাশাপাশি শোনা যায়। একজন হীরেন ভট্টাচার্য, অন্যজন সুরেশ দত্ত।
হীরেন ভট্টাচার্যর কাজ একদম শান্তিনিকেতনি ঘরানার। তার সংগত কারণও ছিল। উনি নন্দলাল বসুর ছাত্র ছিলেন। ওঁর স্টাইল অফ প্রেজেন্টেশনটাই আলাদা। তার সঙ্গে আবার পলিটিক্স ভীষণভাবে জড়িয়ে ছিল। এমনকী, ওঁর প্রোমোশনও পলিটিক্সের লোকজনই করতেন। সেই সময়ে বছরে পঞ্চাশটা শো করছেন, তাতে বামফ্রন্ট সরকারের সাপোর্ট থাকছে। রঘুদা গত হওয়ার পর আমি ওঁর সঙ্গে একটা-দুটো শো-তে গিয়ে দেখেছি, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শহরে যে রবীন্দ্র ভবন আছে, সেখানকার স্টেজ মেপে ওঁর প্রোডাকশনটা বানানো। যে বাসে করে উনি নিয়ে যেতেন, সেখানে কোন জিনিস কোথায় রাখা হবে, সবটাই হিসেব করা থাকত। এবং, সবচেয়ে বড় কথা, একসঙ্গে তিন-চারহাজার লোক ওঁর শো দেখবে, সেই ক্যালকুলেশন মেনে ডিজাইন করা হত।
এবার আসি, সুরেশ দত্তর কথায়। খুব গুণী লোক, বড় বড় থিয়েটার স্টেজে উনি যেভাবে পাপেট থিয়েটার ডিজাইন করেছেন, সেভাবে আর কেউ করতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। সঙ্গে, প্রচণ্ড পরিশ্রমও করতে পারতেন, অনেক ক্ষেত্রে খুব ওপেন-মাইন্ডেডও ছিলেন। ওঁর অ্যাপ্রোচটা আবার পুরোপুরিই কমার্শিয়াল। এটা একেবারেই দোষের নয়, এটা একটা ধরন। ওঁর ‘আলাদিন’ দেখতে গিয়েছিলাম অবন মহলে। আমরা ‘দ্য পাপেটস’ থেকে কয়েকজন গিয়েছিলাম, গিয়ে দেখছি, আনন্দশঙ্করের পরিবার, আরও অনেকে। মানে, কলকাতার ক্রিম গ্যালাক্সি। ওদিকে তাপস সেন আলো করছেন, খালেদ চৌধুরী সেট করছেন, আর পুরো ক্রাফটসম্যানশিপটা সুরেশদার। ফলে, স্কিলের দিক থেকে তখনকার ‘আলাদিন’ একেবারে পারফেক্ট। কিন্তু, দেখে মনে হয়েছিল, খুব সিনেম্যাটিক একটা কিছু ঘটছে। পাপেট থিয়েটার দেখতে গিয়ে তাকে আমার অন্য কিছু কেন মনে হবে? তার ওপর, তখন রঘুদার সঙ্গে আমি এমন একটা পিক-আপে রয়েছি, যে-কোনও জিনিসেরই এতটুকু এদিক-ওদিক আমি নিতে পারতাম না। সুরেশ দত্তর অন্য কয়েকটা দিকেও সমস্যা ছিল। পাপেট থিয়েটারের জগতে ভাল মিউজিয়াম করার মতো অনেক কিছু করতে পারতেন, সেই ক্ষমতা, লোকবল তাঁর ছিল, কিন্তু উনি সেগুলো করেননি।
এবার রঘুদার ব্যাপারে আসি। এই লোকটাকে বুঝতে গেলে আরেকটু গভীরে ঢুকতে হবে। ১৯৫২ সাল থেকে উনি পাপেট থিয়েটার নিয়ে কাজ করছেন। আমরা যাওয়ার আগে আরও দুটো ব্যাচ বেরিয়েছে, এবং সেখানে অনেকেই খুব ভাল কাজ করেছেন। যেমন, শান্তিদা (শান্তিরঞ্জন পাল), দিলীপদা (দিলীপ ভৌমিক), রঘুদার স্ত্রী, এঁরা প্রথমদিককার ব্যাচ। তখন পাপেট থিয়েটারকে উনি থিয়েটার হিসেবেই ট্রিট করেছেন। প্রচুর শো করেছেন, রাজস্থানে শো করতে গিয়ে পুরস্কার পেয়েছেন, পাপেট ফিল্ম তৈরি করে বেস্ট চিলড্রেন্স ফিল্মে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার (‘হট্টগোল বিজয়’, ১৯৬১) পেয়েছেন। হরিশ মুখার্জি রোডে রেগুলার শো করার ব্যবস্থা করেছিলেন। চক্রবেড়িয়া রোডে তরুণ রায় আর দীপান্বিতা রায় (সদ্যপ্রয়াত দেবরাজ রায়ের বাবা-মা) ‘থিয়েটার সেন্টার’ করেছিলেন, সেখানে রঘুদার শো হত। তরুণ রায়ের ‘পরাজিত নায়ক’-এর সেটটা রঘুদার করা, আমি দেখতেও গিয়েছিলাম।

পরে সেটা পাল্টাল। রঘুদা অ্যানিমেশন নিয়ে বরাবর খুব ওয়াকিবহাল ছিলেন। অ্যানিমেশনের রস্ট্রাম উনি নিজের মতো করে বানিয়েছিলেন। যদিও, অত অবধি আমার পৌঁছনোর ক্ষমতা ছিল না বলে আমি ওতে খুব ইন্টারেস্ট দেখাইনি। যাই হোক, রঘুদা ওয়াল্ট ডিজনির অ্যানিমেশন স্টাইল দেখেছেন। সেটার কস্টিং বিশাল। সেই কস্টিং যাতে কমানো যায়, সেটা নিয়ে গোটা পৃথিবীতে তখন বিভিন্ন শিল্পীরা কাজ করছেন। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সে চেষ্টা হয়েছে। সেটা অনেক বেশি ডাইরেক্ট, অনেক বেশি পলিটিসাইজড, প্রতিবাদমূলক। রঘুদা নিজে এগুলোর খবর রাখতেন, বিভিন্ন এমব্যাসির সঙ্গে যোগাযোগ করে পোলিশ ছবি, জার্মান ছবি আনতেন, নিজে দেখতেন, আমাদের দেখাতেন। জার্মান (পরবর্তীতে চেক) পাপেটিয়ার জিরি ট্রিঙ্কার কাজ খুব দেখতেন। আর, যদি গভীরে গিয়ে ভাবো, বুঝতে পারবে, পাপেট থিয়েটার ইজ আ কাইন্ড অফ অ্যানিমেশন। ফলে, রঘুদা তখন অ্যানিমেশনের বিকল্প হিসেবে পাপেটকে দেখছেন।
’৭৫ সালে কলকাতায় দূরদর্শন চলে আসার পর থেকে উনি কিন্তু এই মিডিয়ামটাকে পাল্টে ফেললেন। কীভাবে এটাকে মাস মিডিয়ামে নিয়ে যাওয়া যায়, সেটা নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করলেন, সেই কারণেও কাজের ধারাটা আরও পাল্টে গিয়েছিল। কম খরচে অ্যানিমেশনটাই তখন ধ্যান-জ্ঞান।
আপনারা যখন ঢুকলেন, সেই সময়ে কি রঘুনাথ গোস্বামী আর তাহলে সেভাবে থিয়েটার শো করছেন না?
না না, ঠিক তা নয়। আমরা যখন ঢুকেছি, তখনও রেগুলার আমাদের শো হত। লেক টেরেসে গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্কুল ছিল, সুশিক্ষণ বিদ্যালয়, তার ছাদে আমাদের শোয়ের ব্যবস্থা হয়েছিল। সেখানে লোকজন আসত, কখনও কম, কখনও বেশি। শোয়ের জন্য উনি কাজও করেছেন। এই ক্ষেত্রে ওঁর অ্যাপ্রোচটাকে বুঝতে হবে। বাকি যে দু’জনের কথা বললাম, ওঁদের মতো উনি খুব বিরাট ক্যানভাসে পাপেটের শো ভাবেননি।
পাপেটের যে টাইনিনেস, তার মধ্যে একটা মজা আছে। হ্যাঁ, যে যার খুশিমতো কাজ করতেই পারে, কুড়ি ফুটের পাপেটও হয়, পাপেট নিয়ে অনেক ধরনের এক্সপেরিমেন্ট চলছেই— সেটা চলাটাই উচিত। কিন্তু, সারা পৃথিবীতে ছোট পাপেট নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ হচ্ছে। পকেটের মধ্যে পাপেট, ঝোলার মধ্যে পাপেট, এমন নানা রকম। সেরকমই, পাপেটের একটা শো, যেটা বারান্দায় করা যায়, উঠোনে করা যায়, যে-কোনও জায়গায় স্টেজটা বসিয়ে করা যায়, রঘুদার ভাবনায় সবসময়ে এগুলো কাজ করত। মবিলিটি ওঁর পাপেটের একটা বৈশিষ্ট্য। সেই অনুযায়ী মিউজিকের মডিউলেশন। একটা অডিওর জন্য কী যে পরিশ্রম করতে পারতেন! রাতে যখন চারপাশ শান্ত হয়ে এল, তখন কাজ করতে বসলেন। সমস্তটা নিজে হাতে। নিজেই পিয়ানোর কর্ড বাজাচ্ছেন, বা দোতারা বাজিয়ে শুনছেন, যেখানে যেটা লাগবে। আসলে, ওঁর রোজগারের উৎস ছিল ওঁর এজেন্সি, সেখানে ডিজাইনিংয়ের কাজ হত, আর পাপেটটা ছিল ওঁর ভালবাসার জায়গা। এতে মনপ্রাণ ঢেলে এক্সপেরিমেন্ট করতেন।

ভিস্যুয়ালের সঙ্গে মিউজিকের বন্ডিংটা কীরকম হবে, সেটা ওঁর সঙ্গে থেকে যেভাবে বুঝেছি, সেই কারণেই সুরেশদার কাজ হলে দেখতে গিয়ে তার মিউজিক শুনে মনে হয়েছিল, এটা তো পুরো সিনেমা হচ্ছে। এতটুকু আকারের একটা পাপেট, সেখানে মিউজিক কখনওই পাপেটকে ছাপিয়ে যাবে না, এই বোধটা রঘুদার সঙ্গে কাজ করার ফলেই তৈরি হয়েছে।
চিত্তপ্রসাদ যখন বম্বেতে থাকতেন, উনিও সেই সময়ে পাপেট নিয়ে কিছু কাজ শুরু করেছিলেন, না?
হ্যাঁ। চিত্তপ্রসাদ যখন আন্ধেরিতে থাকেন, রঘুদাও তখন কিছুদিন বম্বেতে ছিলেন। রঘুদা চেষ্টা করেছিলেন, যদি ওঁর সঙ্গে মিলে একটা দল করা যায়। আসলে, এটা তো ঠিক একা-একা করা যায় না। দল লাগে। কিন্তু, চিত্তপ্রসাদ একাই কাজ করতে পছন্দ করতেন। ফলে, ব্যাপারটা আর ঘটেনি।
আপনাদের দলে সেই সময়ে কতজন ছিলেন?
কখনও আটজন, কখনও দশজন, কখনও বারোজন। বেশিরভাগ সময়ে দেখা যেত, আমি আর রঘুদাই সবকিছু করছি। আমি তাও চেষ্টা করতাম, সকলে মিলে যদি কাজ করা যায়। কিন্তু রঘুদা নিজেই সেটা পারতেন না। আসলে, চিত্তপ্রসাদের স্বভাবটা রঘুদারও ছিল, একা কাজ করতেই বেশি পছন্দ করতেন। শেষের দিকে একেবারেই কারও সঙ্গে কাজ করতে পারতেন না। ১৯৯৫ সালে তো চলেই গেলেন।
আপনাদের সঙ্গে ওঁর কাজের ধরনটা তাহলে ঠিক কীরকম ছিল? মানে, কীভাবে শেখাতেন উনি?
রঘুদা নিজের কাজ সবসময়ে নিজেই করতেন। মাঝে মাঝে হয়তো বলেছেন, এটা এভাবে করো, বা ওভাবে করো, কিন্তু এমনিতে কিছু বলতেন না। ওঁকে দেখে আমাদের শিখতে হত। আর উনি নিজেও চাইতেন, উনি যে কাজটা করছেন, আমরা তাতে ওঁকে সহায়তা করি। শেষের দিকে হয়তো বলতেন, আমি আর ক’দিন! কিন্তু, তার জন্য নিজের কাজ যে ছেড়ে দিতেন, তা কিন্তু নয়।

আপনার দিকটা আমি যদি দেখি, আপনি নিজে উদ্যমী হয়ে ওঁর সঙ্গে নানা বিষয় আলোচনা করেছেন, অর্থাৎ, অন্যদের তুলনায় বেশি কাছাকাছি যেতে পেরেছিলেন— সেই অবস্থান থেকে আপনি শিক্ষক রঘুনাথ গোস্বামীকে অন্যভাবে কি পেয়েছিলেন?
আমি যে তখন নানা জায়গায় ছুটে বেড়াচ্ছি, নাটক, সিনেমা, একজিবিশন দেখছি। রঘুদার সঙ্গে যখন আমার কাজ শুরু হল, তখন কিন্তু আর বেশি আমায় কোথাও যেতে হল না। তার একটা কারণ হল, আমার সব উত্তরগুলো আমি ওঁর কাছে পেতাম। সে সাহিত্য, শিল্প, ডান্স, আর্কিটেক্ট, যাই বলো, আমার যে কোয়্যারিগুলো ছিল, সেগুলো আমি ওঁর কাছ থেকে জেনে নিতাম। এখন এই প্র্যাক্টিসেরও ভাল আছে, মন্দও আছে। আমি এক জায়গা থেকেই সবটা পেয়ে যাচ্ছি, আমাকে ওই ফিজিক্যাল এফর্টটা অত দিতে হচ্ছে না, অস্থিরতাটা কমে যাচ্ছে। আবার, যেহেতু একজনের কাছ থেকেই সবটা পাচ্ছি, পাঁচজনের কাছ থেকে পাওয়াটা কমে গেল।
একটা সময়ের পরে রঘুদাই আমার কাছে আইকন হয়ে দাঁড়ালেন। উনি ভাল বললে ভাল, উনি খারাপ বললে খারাপ। বিশেষত, আমার আঁকা ছবির ক্ষেত্রে বলি। প্রথম দিকের আঁকা ছবিগুলো দেখলেই উনি বলতেন, হোয়াই আর ইউ সো গ্রোটেস্ক (Grotesque)? যে ছবিই দেখাই, এই একটাই কথা বলেন। তখন আমি কিছুদিনের জন্য ছবি আঁকা বন্ধ করে দিলাম। তারপর, আবার একটু একটু করে, পড়াশোনা করে, অতীতের যা কিছু ছিল, সেসব অল্পস্বল্প রেখে, নতুন ধারণা নিয়ে নিজস্ব একটা ধারা তৈরি করার চেষ্টা করলাম। মূলত ওয়াল পেইন্টিং, ভারতের ফোক আর্ট, এই ফর্মগুলোই আমায় এনগালফ করল। ধীরে ধীরে আবার কাজ শুরু হল। সেটা ’৮৭-’৮৮ সাল।

১৯৮৫ সালে মস্কোতে
রঘুনাথ গোস্বামীর পাপেট্রির প্রসঙ্গেই ফিরব। উনি তো বিজ্ঞাপন জগতের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন, প্রোডাকশন হাউসও করেছেন, সেখানে অনেক দর্শকের সঙ্গে ওঁর কাজের সংযোগ, তাহলে পাপেটের ক্ষেত্রে উনি ছোট স্পেসে কম লোকজনের মাঝে কাজ করার কথা ভাবলেন কেন বলে আপনার মনে হয়?
ওঁর অন্যদিকের কাজগুলো আমি খুব একটা কাছ থেকে দেখিনি। ওই জগতে থাকতে গেলে যা যা দরকার, সবই উনি করেছেন। আমি যখন গিয়েছি, তখন থেকেই কিন্তু ওঁর কাজের ধরনটা পাল্টে যেতে শুরু করেছে। উনি সবসময়ে চাইতেন, ব্যাপারটা ব্যপ্ত হোক, কিন্তু গভীরভাবে ব্যপ্ত হোক। ছোট স্পেস মানে কিন্তু আবদ্ধ নয়। খুব সহজ উদাহরণ দিয়ে যদি বোঝাতে হয়, তাহলে আমি বলব, বাদল সরকার যেভাবে থার্ড থিয়েটারকে ভাবতেন, রঘুদা পাপেট থিয়েটারকে সেভাবে দেখতে চেয়েছেন। একজন লোক যে-কোনও অবস্থায় যে-কোনও ভাবে যাতে পাপেট থিয়েটার করতে পারে, সেটা ছিল ওঁর ভাবনার মূলে।
এই দর্শনের কারণেই আমি আজও কাজটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছি। যদি অন্যান্য বড় রিকোয়্যারমেন্ট থাকত, এটা কিন্তু একটা সময়ে বন্ধ হয়ে যেতেই পারত। হয়নি, তার কারণ, ওই ইন্টিমেট স্পেসে কাজ করার ভাবনা।
এখানেই আরেকটা প্রশ্ন এসে যায়। আপনি একটু আগেই বললেন, আপনি বরাবর ছোটদের নিয়েই কাজ করতে পছন্দ করেছেন। আবার, আপনার কাজে ওই ছোট স্পেস, ছোট পাপেট এগুলোই চলে এসেছে। এই যে আয়তনের দিক দিয়ে ছোট একটা জায়গায় পাপেট নিয়ে কাজ করা, সেখানে কি যারা বয়সে বা অভিজ্ঞতায় খুদে, তাদেরকে নিয়ে কাজ করার বিষয়টা খাপ খেয়ে যাচ্ছে?
অবশ্যই। আমি সবসময়ে চেষ্টা করি, ওরা যাতে নিজের মতো করে ভাবতে পারে, কাজ করতে পারে। সেটা পাপেটের টাইনিনেস ছাড়া সম্ভব ছিল না। এমনকী, এখনও যে আমি কাজ করার কথা ভাবতে পারছি, সেটাও রঘুদার সঙ্গে কাজ করেছি বলেই সম্ভব হচ্ছে।
রঘুনাথবাবু চলে যাওয়ার পরে তো প্রায় ৩০ বছর হয়ে গেল, আপনি এখনও কাজ করে যাচ্ছেন। কখনও সচেতনভাবে তাঁর যে কাজের ধারা বা প্রফেশনাল অ্যাপ্রোচ, সেটাকে সচেতনভাবে ভাঙার চেষ্টা করেছেন?
দেখো, আমি ওঁর সঙ্গে একটা দীর্ঘ সময় কাজ করেছি। ১৯৭১ থেকে ১৯৯৫। অর্থাৎ, আমার কেরিয়ারের যে প্রাইম টাইম, সেটা কিন্তু আমি পুরো ওখানেই দিয়েছি। তার ফলে এই সময়ে আমার অন্যান্য যে কাজগুলো করার প্রয়োজন ছিল, সেগুলো আমি করিনি।
যেমন ধরো, সংগীত নাটক একাডেমিতে গিয়ে কিছু তদ্বির করা, একটা গ্রুপকে কীভাবে কবজায় রাখা যায়, সেটা নিয়ে ভাবা, আরও একটু প্রফেশনাল হওয়া— এগুলো কিন্তু সময়ে করতে হয়, তবেই একটা উদ্যোগ সাস্টেন করে। একটা পারফর্মিং আর্টকে টিকিয়ে রাখতে আরও যেসব কাজগুলো দরকার পড়ে, সেগুলোও আমি করিনি। রঘুদা যখন কাজ করেছেন, তিনি একটা ধরন মেনে কাজ করে গিয়েছেন, আমি সেটাই ফলো করে গিয়েছি। বরং, রঘুদা গত হওয়ার পরে আমি বেশ কিছু পারফরম্যান্স করেছি।
রঘুদার নিজেরও কিছু খামতি ছিল। যেমন, ওঁর একটা স্টেজ-ফ্রাইট ছিল। একজন রেগুলার স্টেজ পারফর্মারের কিন্তু ওই ভীতি বা নার্ভাসনেস থাকা উচিত নয়। রঘুদার যে ছিল, তার একটা বড় কারণ, উনি বেশি শো করতেন না। অসম্ভব পারফেকশনিস্ট ছিলেন, ফলে একটা কাজ পারফেক্ট না হলে সেটা নিয়ে চাপা টেনশন তৈরি হচ্ছে, সেটা গোটা গ্রুপকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। আমাকেও করেছে।
যখন উনি পারফর্ম করতেন, তখন নিশ্চয় এতটা ভীতি ছিল না। কিন্তু পরে স্টেজ শো কমিয়ে দেওয়ার ফলেই ওই ভীতিটা চলে এসেছিল। কারণ, তখন উনি অ্যানিমেশনের দিকটা নিয়েই বেশি ভাবছেন। স্বাভাবিকভাবেই, আমাদের কাজটাও সেই ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। তবু, উনি চলে যাওয়ার পর আমি কিছু শো করেছি। দিল্লিতে ন্যাশনাল পাপেট ফেস্টিভ্যাল হল, সেখানে আমরা ডাক পেয়েছিলাম।
আপনি তো নিজেও একটা দল করলেন পরে।
সেটা খানিক বাধ্য হয়েই করলাম। ‘দ্য পাপেটস’ ছেড়ে যাওয়ার ইচ্ছা আমার ছিল না। কিন্তু, ওঁর পরিবারের ভাবনার সঙ্গে আমার ভাবনার মিল হচ্ছিল না। ফলে, আমি বেরিয়ে এলাম। তাও, যতদিন পেরেছি, আমার সবটা ওখানে দিয়েছি। শেষ পর্যন্ত ২০০২-’০৩ সাল নাগাদ নিজের দল করলাম, ‘সিম্পল পাপেটস’।
এই সময়ের আশপাশে আপনি তো বোধহয় পাপেট্রিতে ফুলব্রাইট ফেলোশিপ নিয়ে আমেরিকাতেও গেলেন, সেখানকার অভিজ্ঞতা কেমন ছিল?
আমি আমেরিকা গেলাম ১৯৯৯ সালে। সিয়াটেলের ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াশিংটনে একটা পাপেট ফেস্টিভ্যাল হচ্ছিল, ওখানে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। অবশ্যই পারফর্মার হিসেবে নয়, অবজার্ভার হিসেবে। সেখানে মোটামুটি এক্সপেরিমেন্টাল ওয়ার্কই বেশি এসেছিল। তবে, আমেরিকায় পাপেট নিয়ে সেভাবে এক্সপেরিমেন্ট হয়নি, যতটা সুইজারল্যান্ড বা নরওয়েতে হয়েছে, বা রাশিয়ায় সের্গেই ওবরাজৎসভ করে গিয়েছেন। ১৯৮৫ সালে যখন মস্কো যাই, তখন ওবরাজৎসভের প্রোডাকশন আমি দেখেছি, আমার সৌভাগ্যও হয়েছিল তাঁকে মিট করার। আমেরিকায় ওই বিল বেয়ার্ড, কোরা বেয়ার্ড, মেল হেলস্টেইন, এঁরাই যা করার করেছেন।
সিয়াটেলের ওই ফেস্টিভ্যালে অবশ্য অনেক কিছুই দেখা হয়েছিল। জানা হয়েছিল। আমেরিকার ভারমন্টে ‘ব্রেড অ্যান্ড পাপেট থিয়েটার’ খুব বিখ্যাত, পিটার শ্যুম্যান তৈরি করেছিলেন। সেখানে সারা সপ্তাহ বা একমাস ধরে অনেক লোক একসঙ্গে কাজ করেন, কিন্তু তাঁরা যে খুব প্রফেশনাল পাপেটিয়ার, তা নয়। ওখানে কিছু ব্রেড মানে পাঁউরুটি রাখা থাকে, কিছু সস রাখা থাকে, আরও এটা-সেটা রাখা থাকে। খিদে পেলে খাও, বাদবাকি সময়ে কাজ করো— এই হল ওখানকার নিয়ম। এই ফেস্টিভ্যালে আমি ওদের কাজের কিছু ভিডিও দেখেছিলাম, সে এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। অত বিশাল আকারের সব পাপেট। মূলত, ওখানকার স্থানীয় মানুষদের যেভাবে ইউরোপীয়রা ডিপ্রাইভ করেছে, সেই গল্পগুলো পাপেটের মাধ্যমে বলে, যে কারণে ওরা সরকারি সাহায্য কোনওদিন পায় না, আবার সরকার ওদের অস্বীকারও করতে পারে না, মুখরক্ষার জন্য ওদের নাম দিতে হয়।
আরেকদিন একটা প্রাইভেট পাপেট মিউজিয়ামে গিয়েছিলাম। সেখানে বিল বেয়ার্ডের করা ‘দ্য সাউন্ড অফ মিউজিক’-এর পুরো পাপেট সেট-আপটা দেখলাম, ১০ ফুট উঁচু স্ট্রিং পাপেট, এমন বেশ কিছু অরিজিনাল পাপেটের কাজ দেখলাম। যেগুলো এতদিন ছবিতে দেখেছি, রেফার করেছি, সেগুলো চোখের সামনে দেখছি।
আপনি নিজে তো শ্যাডো পাপেট্রির কাজ করেন, এছাড়া আর কত ধরনের
পাপেট্রি আছে?
পৃথিবীব্যাপী আমরা চার রকমের পাপেট দেখতে পাই। হাত দিয়ে করা হয়, সেটার নাম ‘গ্লাভ পাপেট’। একটা হয় তিনটে কাঠির উপর ভর দিয়ে, সেটাকে বলে ‘রড পাপেট’। তৃতীয়টা স্ট্রিং পাপেট, সুতোগুলো আঙুলে বেঁধে চালনা করা হয়। চতুর্থটা শ্যাডো পাপেট, একটা সাদা স্ক্রিন রেখে, পিছনে আলো রেখে, পাপেটের ছায়াটা স্ক্রিনে ফেলে পাপেট্রি করা হয়।
এছাড়া, কম পরিচিত বেশ কিছু ফর্ম আছে। যেমন, জাপানের বানরাকু পাপেট। জাপানে আরেক ধরনের ট্র্যাডিশনাল পাপেট হয়, বড় আকারের, তিনজনে মিলে চালাতে হয়। এই ফর্মটা নিয়ে পশ্চিম ইউরোপে আবার খুব কাজ হচ্ছে। এক্সপেরিমেন্ট হওয়াটাই প্রয়োজন।
আর্কিটেকচার নিয়ে আপনার যে একটা স্বাভাবিক ঝোঁক রয়েছে, সেটা বোঝা যায়। আপনি এখনও মামার কোয়ার্টারের নকশাটা মনে রেখেছেন, সেনেট হলের থামগুলোকে মনে রেখেছেন, আপনার ঘরের এই কুলুঙ্গির নকশা। যেহেতু থিয়েটার বা পাপেট থিয়েটার, সবেতেই স্পেস ব্যবহারের একটা ব্যাপার থাকছে, সেটা ইন্টিমেট হোক কি ওপেন, আর্কিটেকচারের প্রতি আপনার ঝোঁক পাপেট থিয়েটারে কি কাজে এসেছে?
ব্যক্তিগতভাবে, আর্কিটেকচার আমার ভীষণ পছন্দের বিষয়। আগেকার বাড়ির ক্ষেত্রে একটা ব্যাপার ভীষণ চোখে পড়ত, আকাশকে বাড়ির মধ্যে কতখানি এনে ফেলা যায়। বড় বড় জানলা, চারিদিক দিয়ে ঘর, মাঝখানটা খোলা আকাশ, স্কাইলাইটটাকে ব্যবহার করা— এই বিষয়গুলো কিন্তু ভীষণ স্বাস্থ্যসম্মত, কারণ এখানে প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় যোগ আছে। পাপেট থিয়েটারে এর সবকিছুই এসে যায়। আর্কিটেকচারের সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে, নেচারের সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে, নাচের সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে— হয়তো এক্সট্রিম ধারণা না থাকলেও হয়, কিন্তু মোটামুটি একটা স্বচ্ছ ধারণার প্রয়োজন।
আপনি শুরুতে ছোটবেলায় যাত্রা দেখার অভিজ্ঞতার কথা বলছিলেন। যাত্রাও খুবই এনগেজিং একটা আর্ট ফর্ম, কিন্তু সেটা হয় ওরকম খোলা জায়গায়, আর অত দর্শকের সামনে। আপনার কাজের ধারা ইন্টিমেট স্পেসে। কিন্তু, সেখানেও অভিনয়ের একটা অংশ থাকছে। যাত্রার মতো একটা ওপেন-স্পেস ফর্মের প্রতি আপনার যে টান, সেটা কখনও এই পাপেট থিয়েটারে প্রয়োগ করেছেন?
এটার উত্তর দেওয়া কঠিন। এই প্রসঙ্গে একটা পার্থক্যের কথা বলতে পারি। একধরনের শ্যাডো পাপেট হয়, যেখানে, আর্টিস্ট এবং পাপেট, দু’জনকেই সমানভাবে দেখা যাচ্ছে। ওটা একটা টেকনিক। আমি একেবারে যে করিনি, তা নয়। তবে, আমি আর্টিস্টকে নেপথ্যে রাখতেই পছন্দ করি।
এখনকার বাচ্চাদের সঙ্গে যে কাজ করেন, তাদের মধ্যে উৎসাহ কেমন দেখছেন?
খুব যে কাজ করি, তা নয়। ‘ছবি ও ঘর’ গ্যালারিতে শ্যাডো পাপেট নিয়ে কিছু ওয়ার্কশপ করিয়েছি। বারাসতে ‘কলতান’-এর একটা স্কুল আছে, ওখানে বাচ্চাদের নিয়ে কাজ হয়। ওদের একটা ভাল ব্যাপার হল, বাচ্চাদের নিজের হাতেই সব করতে দেওয়া হয়। সেখানে স্টিক পাপেট শেখাই, সুকুমার রায়ের ‘আবোল-তাবোল’-এর কবিতার ওপর কাজ করার চেষ্টা করছি। স্কুলটা যারা চালায়, তাদের খুব উৎসাহ, ওইজন্যই সম্ভব হচ্ছে।
আসলে, আমি চেষ্টা করি, সোজাসাপটাভাবে কোনও একটা গল্প মানুষের সামনে তুলে ধরার। ধরো, সুকুমার রায়ের কুমড়োপটাশ, বা কোনও একটা ছড়া, তার যে ইমেজ, সেটাকে তুলে আনার জন্য সবসময়ে যে খুব জটিল পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে, তেমন কোনও মানে নেই। সেজন্য আমি সবসময়ে স্টিক পাপেট, বা কাট-আউট পাপেট, এগুলো বেশি ব্যবহার করে। অনেকগুলো পাখি দিয়ে আমি শিকারীর জাল ছিঁড়ে উড়ে যাওয়ার গল্পও বলতে পারি, আবার অন্য ধরনের হাজারও গল্প বলতে পারি। তার জন্য বিরাট খরচের প্রয়োজন নেই।
অনেক জিনিস, অনেক লোক ব্যবহার করে অনেক গল্প হয়, কিন্তু অনেক জিনিস ছাড়াও যে অনেক গল্প হতে পারে, সেটাই আমার লক্ষ্য।
ছবি সৌজন্য : স্বপ্না সেন, সীমা মুখোপাধ্যায়, কলকাতা দূরদর্শন, সোহম দাস