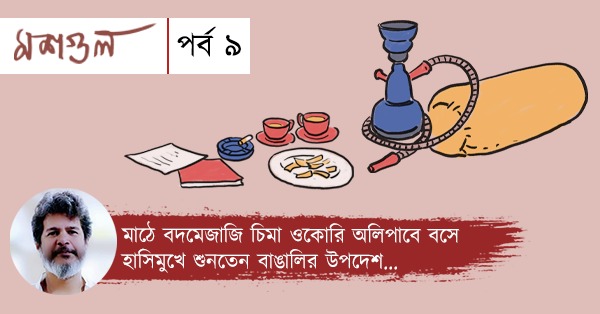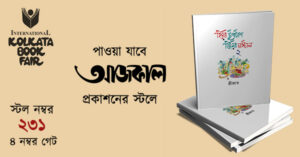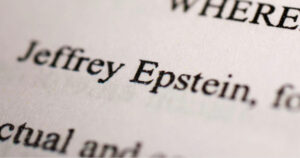কুঞ্জে ‘অলি’
আমার প্রথম অলিপাব যাওয়া ১৯৯২ সালে। তখন আমার উনিশ বছর বয়স। সদ্য উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছি। এই পরীক্ষাটা দেওয়ার পরেই বাঙালি ছেলেপুলের মধ্যে একটা অদ্ভুত আফটারএফেক্ট দেখা যেত। আমার দাদা আর তার বন্ধুরা যেমন এই আফটারএফেক্টে একটা জটিল ছবি দেখতে চলে গেছিল, ‘আঘাত’। সেখানে রানা নামে একটা ছেলে পূজা নামের এক মেয়ের প্রেমে পড়ে। এরপর পূজার সম্মান রক্ষা করতে রানা জেলে চলে যায়। এই আঘাতে পূজা পুলিশ হয়ে যায়। তারপর রানা আর পূজা মিলে ছবিটার সঙ্গে যুক্ত বাকিদের ওপর প্রতিশোধ নেয়। যাই হোক, বিষয় এটা নয়, বিষয় হল— অলিপাব।
আমরা বন্ধুরা সেদিন অলিপাব যেতে চাইনি। আমাদের বাজেট অনুযায়ী আমরা খোঁজখবর করে দেখলাম, আমাদের জন্য সঠিক পানশালা হল শ’জ। ধর্মতলা মেট্রো সিনেমা হলের গায়ের গলি, যা মেট্রো গলি নামেই খ্যাত, সেই গলির জনপ্রিয় ওয়াটারিং হোল শ’জ, যা ‘ছোটা ব্রিস্টল’ নামেও পরিচিত।
কিন্তু কপাল খারাপ! ঢুকে আবিষ্কার করলাম, ছোটা ব্রিস্টলের ম্যানেজার হলেন গৌরকাকু। গৌরকাকু আমার স্কুলের বাইরের এক বন্ধুর বাবা। আমাকে দেখে বিরাট চোটপাট করতে শুরু করলেন গৌরকাকু, ‘আঠারো বছর বয়স হয়নি, এখনই মদ খেতে চলে এসেছিস!’ বোঝানোর চেষ্টা করলাম, ‘উচ্চমাধ্যমিক দিয়েছি, অবশ্যই আঠেরো হয়েছে।’ গৌরকাকু অনড়, ‘রেজাল্ট তো বেরোয়নি! উচ্চমাধ্যমিক পাশ না করলে আঠারো পার হয় না।’
বিফল-মনোরথ হয়ে সেই প্রথম অলিপ্রবেশ।
অলিপাবের সঙ্গে দ্বিতীয় আলাপে সখ্য জমে। ১৯৯৪ সালের ফেব্রুয়ারি। তখন ময়দানে হত কলকাতা বইমেলা। এক সন্ধেবেলা বইমেলার মাঠে খবর পেলাম, সিনিয়র সব কবিদাদারা গেছে অলিপাবে। মূলত তাদের সঙ্গে দেখা করতেই ঢুঁ মারলাম অলি-তে। দোতলায় উঠে দেখি, সব মদ্যপায়ী ধুঁয়াধার ব্যাটিং করছেন। দু-হাত দূরের মানুষ দেখা যাচ্ছে না ধোঁয়ার চোটে। আজ্ঞে হ্যাঁ, তখন কলকাতার রেস্তোরাঁ-পানশালায়, বাসে-ট্রামে-ট্রেনে ধূম্রপান করা যেত।
সে যাই হোক, চোখ সেটল হলে দেখলাম, নক্ষত্র সমাবেশ! টেবিলে টেবিলে বিখ্যাত কবিরা থিকথিক করছেন। এক টেবিলে উৎপলকুমার বসু, জয়দেব বসু, রাহুল পুরকায়স্থ, সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়, চৈতালি চট্টোপাধ্যায়। পাশের টেবিলে কবি তুষার চৌধুরী তাঁর জুনিয়র সঙ্গীদের সঙ্গে আড্ডায় মগ্ন। আমি রাহুলদা, জয়দেবদাদের টেবিলে যোগ দিলাম। মদ অর্ডার দেওয়ার প্রশ্নই নেই, পকেটে একটা পাঁচ টাকার নোট, একটা চারমিনার সিগারেট আর একবাক্স দেশলাই। কিন্তু বরাবরই সঙ্গে রাহুলদা, জয়দেবদারা থাকলে জীবনে মদের অভাব থাকত না। দুই দরাজদিল কবি আমার জন্য দুটো করে মোট চার পেগ রাম বলে দিলেন।

সে অবশ্য সবে শুরু। খানিক বাদে তুষার উঠে এলেন। অননুকরণীয়, গায়ে জ্বালা ধরানো, চিবিয়ে-চিবিয়ে কথা বলার অ্যাকসেন্টে উৎপল বসুকে বললেন, ‘উৎপলদা, আপনার রিসেন্ট একটা কবিতা পড়লাম, আপনি পোকাদের কথা শুনতে ভাল-টালবাসেন, এরকম কিছু একটা লিখেছেন। তা পোকাদের ভাষা শিখলেন কোথায়?’ উৎপল মুচকি হেসে বললেন, ‘বিদেশ থেকে শিখে এসেছি। তোমার তো মনে হয় যাওয়াটাওয়া হয়ে ওঠেনি, গেলে তুমিও বেশ শিখে নিতে।’ তুষার কি এতে দমার পাত্র! ‘বিদেশে শুধু পোকার ভাষাই শিখলেন? আর কিছু?’ উৎপল সঙ্গে সঙ্গে, ‘আর লাতিন আমেরিকান বেলি ডান্স শিখেছি। ওটা অবশ্য তুমি বুঝবে না।’
উৎপলদা মাঝেমধ্যেই মদের আসরে কঠোর অনুশাসন জারি করতেন। একবার বললেন, ‘আজ থেকে আড্ডায় আমরা কেউ কারও সম্পর্কে ভাল কথা বলব না, শুধুমাত্র পরচর্চা আর পরনিন্দা।’ আমি বললাম, ‘আপনিই শুরু করুন, একটা বেঞ্চমার্ক সেট করে দিন।’ উৎপলের হাজির জবাব, ‘শঙ্খবাবুর একটা কথাও বিশ্বাস করি না আমি! উনি যদি বলেন, সূর্য পূর্বদিকে ওঠে, আমি প্রতিবাদে উঠে দাঁড়িয়ে বলব, আপনি মিথ্যে কথা বলছেন স্যর!’
একদিন সন্ধেবেলা অলিপাবে একা-একা বসে আছি। বন্ধুরা তখনও কেউ ঢোকেনি। দেখি, উৎপল ঢুকছেন। আমাকে দেখে মুচকি হেসে আমার সঙ্গেই এসে বসলেন। এবার সেদিন ছিল সরকারি ব্যবস্থাপনায় ওঁর কবিতাপাঠ, রবীন্দ্র সদনে। বললাম, ‘এত তাড়াতাড়ি পড়া হয়ে গেল?’ উৎপলের স্বভাবসিদ্ধ সংক্ষিপ্ত উত্তর, ‘যাইনি।’ ’কেন?’ ‘ধুস! অন্ধকার হলের মধ্যে স্টেজে আমার ওপর গোল স্পটলাইট ফেলবে, টেনশন হয়। মনে হয়, বাঘের খেলা দেখাতে হবে, নয়তো দর্শকের পয়সা উশুল হবে না।’ সেই অনুষ্ঠানেই কবিতা পড়ার কথা ছিল পরিচিত আটের দশকের আরেক তাবড় কবির। তিনি হন্তদন্ত হয়ে অলি-তে ঢুকলেন। আমি তাঁকে বললাম, ‘তুমিও পড়লে না?’ তিনি হাত নেড়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উড়িয়ে দেওয়ার ভঙ্গি করে বললেন, ‘কীসের পড়া! খবর পেলাম তোরা এখানে বসে গেছিস!’
খানিক বাদে তুষার উঠে এলেন। অননুকরণীয়, গায়ে জ্বালা ধরানো, চিবিয়ে-চিবিয়ে কথা বলার অ্যাকসেন্টে উৎপল বসুকে বললেন, ‘উৎপলদা, আপনার রিসেন্ট একটা কবিতা পড়লাম, আপনি পোকাদের কথা শুনতে ভাল-টালবাসেন, এরকম কিছু একটা লিখেছেন। তা পোকাদের ভাষা শিখলেন কোথায়?’ উৎপল মুচকি হেসে বললেন, ‘বিদেশ থেকে শিখে এসেছি। তোমার তো মনে হয় যাওয়াটাওয়া হয়ে ওঠেনি, গেলে তুমিও বেশ শিখে নিতে।’
সেই কবি (নাম অনুল্লিখিত থাক) আমার দেখা এক বিচিত্র সুরারসিক। একসময় তাঁর কিঞ্চিৎ আর্থিক অনটন চলছিল। তখনও তাঁর প্রত্যহের সান্ধ্যকালীন ঠেক ছিল অলিপাব। সঙ্গী এক মাড়োয়ারি কবি। তিনি তাঁর লেখা কবিতা শোনাতেন আর মদ খাওয়াতেন, আর সেই অগ্রজ কবি তাঁর কবিতার ভালমন্দ নিয়ে আলোচনা করতেন। একসময় সেই মাড়োয়ারি কবির কবিতার স্টক শেষ হয়ে গেল। তিনি অলি আসা বন্ধ করলেন। ওদিকে সেই রসিক কবি তখনও আসছেন, আর শুরু করেছেন এক অত্যাশ্চর্য খেলা। তখন অলি-তে পরিবেশকরা টেবিলে একপেগ করে মদ দিতেন আর সেই পেগের বিলটা টেবিলে রাখা একটা গ্লাসে গুঁজে দিতেন। সেই কবি, একা একটা টেবিলে বসে থাকতেন, পেগ অর্ডার দিতেন, চুমুক দিতেন আর বিল জমা হত সামনের গ্লাসে। চেনা-পরিচিত যে কেউ ঢুকলেই তিনি তাকে/তাদের ডেকে বসিয়ে নিত নিজের টেবিলে। সে/তারা নিজের মতো মদের অর্ডার দিত, তার/তাদের বিলও জমা হত ওই গ্লাসে। একসময় সে/তারা উদ্যত হত বিল মিটিয়ে বেরিয়ে যেতে। কবি বলতেন, তার/তাদের বিলের টাকা তাঁকে দিয়ে যেতে। সে/তারা সেটাই করত। সে/তারা চলে গেলে কবি অতি দ্রুত নিজের বিলগুলো খেয়ে নিতেন। ঠিক পড়ছেন। নিজের মদের বিলগুলো গিলে খেয়ে ফেলতেন। তারপর আবার এক দলকে তিনি বসাতেন নিজের টেবিলে। চলত একই অপারেশন। বার বন্ধ হওয়ার সময় তিনি মোটা একটা বিল মিটিয়ে স্থানত্যাগ করতেন। অলিপাব খুশি, তিনিও খুশি, আমরা বিস্মিত। অলি কর্তৃপক্ষ এই কারচুপি ধরতে পারত কি না, (ধরতে পারা স্বাভাবিক), ধরতে পারলে কেন তারা কোনওদিন তাঁকে কিছু বলেনি, আমি জানি না। ওহ হ্যাঁ, তখন তাঁর আর-একটা অভ্যেস ছিল, ট্যাক্সির মিটার দেখার ছোট্ট বাল্বটা হাতানো। তখনও ডিজিটাল মিটার হয়নি। তিনি অলি থেকে বেলঘরিয়ার বাড়ি ফেরার সময় ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে ওই পুঁচকি বাল্বটা হাতসাফাই করে বাড়ি ঢুকে যেত। এক বৃষ্টির রাতে ছোট বাল্বের সঙ্গে দুটো বিরাট বিরাট বাল্বও নিয়ে বাড়ি ঢুকেছিলেন, তাই নিয়ে বিস্তর বাওয়াল, কিন্তু সেই গল্প অন্য কোনওদিন।

অলিপাবে ক্বচিৎ-কদাচিৎ আসতেন চিমা ওকোরি। দুটো পেগ ভদকা বা জিন আর সঙ্গে একটা স্টেক নিতেন। আরাম করে খেতেন। কিন্তু হাতের সামনে কিংবদন্তি ফুটবলারকে পেয়ে বাঙালি কি এত সহজে ছেড়ে দেবে! তারা চিমাকে অনর্গল জ্ঞান দিত, চিমার কীভাবে গোলে শটটা মারা উচিত ছিল, কীভাবে বিপক্ষের ডিফেন্ডারকে কাটানো উচিত ছিল, এমনকী, কোনও একটা ক্রসে কেন হেডের চেষ্টা না করে পা ছোঁয়ানোই জায়েজ ছিল, সেসবও শুনতে হত চিমাকে। আর মাঠের মধ্যে দোর্দণ্ডপ্রতাপ, বদমেজাজি হিসেবে কুখ্যাত চিমা অমায়িক হাসিমুখে শুনতেন সব আর মৃদু স্বরে বলতেন, ‘আই উইল ট্রাই নেক্সট টাইম।’

চিমা প্রসঙ্গে আরও একটা ঘটনা মনে পড়ল। আমাদের বন্ধুদের মধ্যে জয়দীপ (কবি জয়দীপ রাউত) সেসময় একেবারেই মদ খেত না, মানে হাফ গ্লাস বিয়ার খেয়েই আউট হয়ে যাওয়া টাইপ ছিল। ফলে জয়দীপের মনে সুরাপায়ীদের সম্বন্ধে নানা অলীক ধারণা ছিল। যেমন ও মনে করত, সুরাপানের সময় সুরাপায়ীদের হৃদয় প্রসারিত হয়, তাদের অদেয় কিছু থাকে না, গ্লাসের মদটুকু ছাড়া। জয়দীপ তখন হন্যে হয়ে বাংলা পড়ানোর টিউশনি খুঁজছে। যথারীতি কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসে আমরা ওর কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করছি না। তাই ও গান্ধারীর আবেদন নিয়ে হাজির হল অলিপাবের সান্ধ্যকালীন আড্ডায়। মনোযোগ দিয়ে পুরোটা শোনার পর এক বন্ধু গম্ভীর মুখে বলল, ‘আছে, একটা টিউশন আছে, এক বিদেশিকে বাংলা শেখাতে হবে। পার ক্লাস তিন হাজার টাকা, মাসে চারটে ক্লাস।’ এবার মধ্য-নব্বইতে এটা একটা অবিশ্বাস্য টাকার অঙ্ক! এত ভাল তো ভাল নয় নীতি মেনে জয়দীপও খুবই সন্দিগ্ধ। আশা-নিরাশার দোলাচলে দুলতে দুলতে জয়দীপ জানতে চাইল, ‘কে সেই বিদেশি?’ বন্ধুর নির্লিপ্ত উত্তর, ‘চিবুজোর। বাংলা জানে না বলে গ্যালারির খিস্তির মানে বুঝছে না।’
আসতেন বিজ্ঞাপন জগতের মহাগুরু আলেক পদমসি। কলকাতায় এলে উঠতেন পার্ক হোটেলে, আর সন্ধেবেলা অলিপাব মাস্ট। বাংলা কবিতার অসম্ভব ভক্ত আলেক বলতেন, কলকাতা তাঁর নিজের শহর বলে মনে হয়। খ্যাতনামা সাংবাদিক এম জে আকবরও আসতেন অলিপাবে। একটা শোনা গল্প, আকবর তখন স্টেটসম্যানে। স্টেটসম্যানে সেসময় অফিসের ভেতর মদ্যপান নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। আকবর সন্ধেবেলা ঢুকলেন অলিতে। মুখে ভুরভুর করছে মদের গন্ধ। এক বন্ধু জিজ্ঞেস করলেন, ‘কোন বার ঘুরে এলে?’ আকবর ধপাস করে সোফায় বসে পড়ে, ‘স্ট্রেইট ফ্রম অফিস।’ বন্ধু অবাক, ‘তোমাকে এখনও অফিসে ড্রিঙ্ক করতে অ্যালাও করছে?’ আকবর মুচকি হেসে, ‘ইফ আকবর’স এলবো বেন্ডস অ্যান্ড স্টেটসম্যান গেটস রিটার্ন ফ্রম ইট, হোয়াট’স রং ইন ইট?’
একদিন আমি আর সারণ (সারণ নিজে চলচ্চিত্র পরিচালক ও প্রখ্যাত অভিনেতা স্বরূপ দত্তর ছেলে) অলিপাবে বসে যা করা উচিত, তাই করছি। অভিনেতা রাজেশ শর্মা এসে বসল। আরও কিছু বন্ধুবান্ধব যোগ দিল আড্ডায়। কথায় কথায় প্রসঙ্গ এল, স্বরূপকাকু কেন সারণের বিয়ে দিচ্ছেন না? কারণ সারণের দ্বারা যে প্রেম হবে না, এটা তো সর্বজনবিদিত। রাজেশদা জলদগম্ভীর স্বরে বলল, ‘কাকু কোনোরকম উদ্যোগ নেবে না।’ আমরা জানতে চাইলাম, ‘কেন?’ রাজেশদা নির্বিকার মুখে, ‘সারণের বাবা সারণকে একটা ফ্ল্যাট দিয়েছিল, সারণ সেটা ভাড়ায় দিয়েছে, একটা গাড়ি দিয়েছিল, সারণ সেটা ভাড়ায় খাটায়, এরপর সম্ভব বিয়ে দেওয়া?’
বিজ্ঞাপনের কাজ করা শুভ্রকে ডাকা হত মাইকেল নামে। ও একবার লম্বাচওড়া জুলফি রেখেছিল, সেই সূত্রে মাইকেল। সুরারসিক ও সুরসিক, ক্ষুরধার উইট, বিস্তর পড়াশোনা, নো-ননসেন্স শুভ্রর সঙ্গে বসলে অলিপাবের আড্ডা বিস্তৃত হত ওর যাদবপুর থানার বাড়ি পর্যন্ত, কখনও-সখনও প্রায় ভোর পর্যন্ত। প্রথমদিকে, যখন শুভ্রর বাড়িটা একজ্যাক্ট কোথায় আমরা জানি না, সেই সময়ের দুটো ঘটনা। অলিপাবে আকণ্ঠ পানের পর আমার ওপর দায়িত্ব পড়েছে শুভ্রকে বাড়িতে নামিয়ে দেওয়ার। এবার যাদবপুর থানার কাছে এসে আবিষ্কার করা গেল, ১) শুভ্র বাড়ির মেইন গেটের চাবি নিয়ে বেরতে ভুলে গেছে। ২) বাড়ির কেয়ারটেকার মেইন গেট বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়েছেন। ৩) পাশাপাশি তিনটে বাড়ির মধ্যে শুভ্র চিনতে পারছে না, ওর নিজের বাড়ি কোনটা। শুনশান যাদবপুর থানার মোড়। রাস্তাঘাটে জনপ্রাণী নেই। শুধু শুভ্র, আমি আর অদিতি (সাংবাদিক অদিতি রায়)। আমার মাথায় বুদ্ধি এল। শুভ্রর নাম ধরে চিৎকার করা যাক, ওর পরিচিতরা নিশ্চয় ঘুম ভেঙে জানলাটানলা খুলে দেখবেন, কে এসেছে এত রাতে, আর শুভ্রকে বাড়িতে ঢুকিয়ে নেবেন। পরিকল্পনামাফিক আমি চিৎকার করলাম, ‘শুভ্র!’ আমার ঠিক পাশ থেকে নম্র, বিনীত স্বরে শুভ্র বলল, ‘বল।’ আমি আর অদিতি বিস্মিত। আমি বললাম, ‘তুই সাড়া দিচ্ছিস কেন?’ শুভ্র বলল, ‘ও হ্যাঁ হ্যাঁ, ভুল হয়ে গেছে।’ আমি ফের চিৎকার করলাম, ‘শুভ্র!’ ফের শুভ্র মৃদুস্বরে, ‘বল।’ আমি হতবাক! অদিতি হাসতে হাসতে রাস্তায় বসে পড়ার উপক্রম। এরপর বেশ কিছুক্ষণ এই ‘শুভ্র!’ আর ‘হ্যাঁ বল’-এর পালা চলার পর, যাদবপুর থানা থেকে কয়েকজন পুলিশ চলে এলেন এবং দায়িত্ব নিলেন শুভ্রকে বাড়িতে ঢোকানোর। অসহায়ভাবে বললেন, ‘আর দাদা, মাতাল ডিল করার ভাগ্য নিয়ে জন্মেছি, করতেই হবে।’
আর-একবার, অলিপাব থেকে বেরনো হয়েছে। বাবু নামে আমাদের এক বন্ধু গাড়ি ড্রাইভ করছে। তার পাশের সিটে বসে পাপু। পাপুর পেছনের সিটে শুভ্র বসে। শুভ্রকে যাদবপুর থানায় নামিয়ে বাবু আর পাপু গড়িয়া যাবে। তখনও বাবু আর পাপু, শুভ্রর বাড়িটা একজ্যাক্ট কোথায়, জানে না। পার্ক স্ট্রিট থেকে এসে ঢাকুরিয়া ফ্লাইওভার পার করে যাদবপুর থানার মোড়ে ইউ টার্ন করে বাবু গাড়ি দাঁড় করাল দাশগুপ্তদের মদের দোকানের সামনে। বাবু শুভ্রকে জিজ্ঞেস করল, ‘কী রে? তোর বাড়ি এখানেই তো?’ শুভ্র বলল, ‘হ্যাঁ এখানেই। একটু এগো।’ বাবু গাড়িটা খানিকটা এগিয়ে ফের দাঁড় করাল, ‘কী রে? বাড়ি চিনতে পারছিস? এখানেই তো?’ শুভ্রর উত্তর, ‘হ্যাঁ, বললাম তো এখানেই। একটু এগো।’ বাবু গাড়িটা আরও খানিক এগলো। ফের একই কথোপকথন। এইভাবে ‘হ্যাঁ এখানেই, একটু এগো’ করতে করতে গাড়ি যখন ঢাকুরিয়া দক্ষিণাপণের সামনে, বাবু মরিয়া হয়ে শুভ্রকে বলল, ‘কী কেস বল তো? আর কত এগোব? তোর বাড়িটা কোথায়?’ শুভ্র অসম্ভব বিরক্তি নিয়ে বলল, ‘আমার বাড়ি তো অনেক পিছনে! সেই যাদবপুর থানার ওখানে!’ বাবু বিস্ময়ের সপ্তম স্বর্গে, ‘তাহলে বা* তখন থেকে ‘একটু এগো, একটু এগো’ করছিস কেন!’ শুভ্র সেই বিরক্তি নিয়েই বলল, ‘আমি তো তখন থেকে পাপুকে সিটটা এগোতে বলছি! না এগোলে নামতে পারছি না তো!’
অলিপাবে এখন অনেক বদল এসেছে। এখন আর বারে বসে ধূমপান করা যায় না। এখন আর দু-তিনটে টেবিল জড়ো করে বসা যায় না। কিন্তু আড্ডা এখনও বহমান। এখনও নিশ্চয়ই আরও এরকম নতুন, নতুন নানা গল্পের জন্ম হয়। ইদানীং আর অলিপাবে সেভাবে যাই না, শুভ্র অকালে মরে যাওয়ার পর থেকে।
এবার বহুদিন পর, চলচ্চিত্র উৎসবের সময় অলি গেলাম, দেখি প্রখ্যাত ডিরেক্টর অফ ফোটোগ্রাফি সুদীপ চ্যাটার্জি বসে। সুদীপদা দীর্ঘদিনই বাংলা-ছাড়া, মুম্বইনিবাসী। বলল, ‘কলকাতায় এলে অলি না এসে পারি না। আসাটা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।’
এটুকুই। শুভ্রর বাকি গল্প অন্য কোনওদিন। শহরের মায়া, অলির মায়া, সুরার মায়া, আড্ডার মায়া, সব কাটিয়ে যে উড়াল দিয়েছে কোথায়, কে জানে!