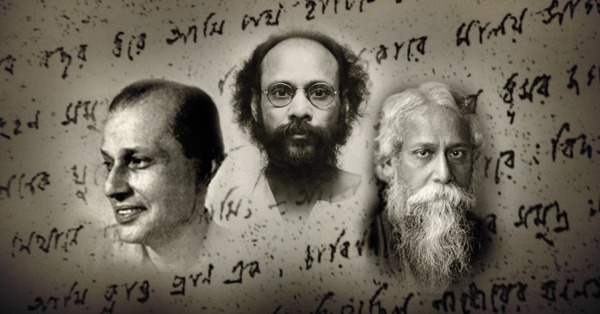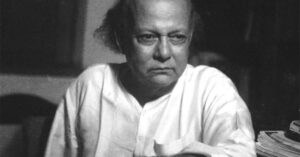সম্প্রতি একটা হিড়িক তৈরি হয়েছে। সমাজমাধ্যমে কবিরা নানা পত্রিকার পাতা থেকে ছবি তুলে জানান দিচ্ছেন, অমুক আমার কবিতা-বই নিয়ে লিখেছিলেন। এই প্রবণতা হয়তো আগেও ছিল, চলতি আড্ডায় উঠে আসত সেসব কথা; এখন ফেসবুক, ফলে দৃশ্যমান। যাঁরা লিখেছিলেন, তাঁরা বয়সে প্রবীণ। কেউ-কেউ এখন আর ইহলোকেও নেই হয়তো-বা। প্রশ্ন হল, এই শংসাপত্র-প্রদর্শন, কোন মনস্তত্ত্বের কথা বলে? যাঁরা এই তথ্য সরবরাহ করছেন জনতার মাঝে, তাঁরা কি এই কথা বলতে চাইছেন না, ওহে, আমাকে যতটা এলেবেলে ভাবো আমি ততটা নই? তাঁরা কি পরোক্ষে খানিক এ-ও বোঝাতে চাইছেন না, আমাকে নিয়ে চর্চাটা শুরু করলেই তো পারো? ইঙ্গিত সুদূরপ্রসারী। আত্মপ্রচারের একটা সূক্ষ্ম পন্থা। অন্যের চিন্তনপ্রক্রিয়াকে কিঞ্চিৎ ঘুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও কি এতে লুকিয়ে নেই? যে-পাঠক মনে করতেন, ক-ব্যক্তির লেখা তাঁর পছন্দ নয়, সেই তিনিই যখন দেখেন ক-ব্যক্তির লেখা নিয়ে একজন বড় কবি দু’কলম খরচ করেছেন, তখন তিনি সন্দেহ করতে থাকেন তাঁর নিজস্ব বিবেচনাকে। সবাই যে করবেন, তা নয়; তবু কেউ-কেউ করে থাকেন। সংশয় জাগে মনে। ভাবতে ইচ্ছে করে, যাঁরা বয়সে তরুণ কবির বই নিয়ে কোনও পত্রিকায় লিখে থাকেন, তাঁরা আসলে কী শর্তে লেখেন!
তাগিদ থেকে যে-লেখা, তা পড়লে টের পাওয়া যায়। কিন্তু সচরাচর এমন ঘটে কি চারপাশে? প্রবীণ কবি, নির্দিষ্ট কোনও ‘অ্যাসাইনমেন্ট’ ছাড়া, তরুণ কবির কবিতা নিয়ে লিখছেন-বলছেন, খুব কি চোখে পড়ে আজকাল? পত্রিকা সম্পাদক হয়তো অনুরোধ করলেন, প্রবীণ কবি লিখলেন। তিনিই যেচে কোনও সম্পাদককে বলছেন, ‘শুনুন ভাই, আমি অমুক তরুণ কবির বই নিয়ে লিখব, আমাকে লিখতেই হবে’— এ-ঘটনা প্রায় বিরল। তাগিদে যত-না লেখা হয়, তাগাদায় লেখা হয় তার চেয়ে বেশি। পত্রিকা সম্পাদক ছাড়া এই ‘তাগাদা’ আসে কোথা থেকে? উদ্যোগ নেয় তরুণ কবি স্বয়ং। একটা করে বই বেরোয়, সে যায় দাদাকবিদের কাছে। বলে, ‘আপনাকে এই বইটা দিতে এলাম। পড়ে মতামত দিলে ভাল লাগবে।’ কিন্তু যতটা আলাগা ঢঙে কথাগুলো বলা হয় বিনয়ের সঙ্গে, কিছুদিন পেরিয়ে গেলে বেরিয়ে আসে আসল রূপ। প্রত্যাশা একটাই, যদি দাদাকবি কিছু লেখেন। ফোন আসে, মেসেজ আসে। বাড়িতে গিয়ে বই দিয়ে আসা যেন দোরগোড়ায় কার্তিক ঠাকুর ফেলে আসার নামান্তর; পুজো করতেই হবে। অবশেষে চাপে পড়ে দাদাকবিকে কিছু-না-কিছু লিখতেই হয়। এবং লেখা মানে ভাল-ভাল লেখা, বিরূপ সমালোচনা নয়। সম্পর্কজনিত সৌজন্যও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে মাঝে মাঝে। কবিতাভাবনায় মিল নেই, তবু হয়তো তরুণ কবির সঙ্গে প্রবীণ কবির দীর্ঘ বন্ধুতা। আপদে-বিপদে তরুণ কবিই ভরসা। প্রতিদানে প্রবীণ কিছুই দিতে পারেন না। অবশেষে প্রতিদানস্বরূপ তিনি লিখে ফেলেন তরুণের কবিতা নিয়ে। আপ্লুত হয়ে যায় তরুণ। আর অচেনা পাঠক? সে কী ভাবল এই পাঠ-প্রতিক্রিয়া পড়ে? এ-নিয়ে আদৌ কি আমরা সচেতন থাকি?
ভুলে গেলে চলবে না, দয়ার দান— সাহিত্যে কখনও চিরস্থায়ী হয় না। বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন, ‘কবিদের যা সবচেয়ে বড় শত্রু, তা দারিদ্র্য নয়, অবহেলা নয়, উৎপীড়নও নয়— তা অত্যধিক সাফল্য, তা বহুবিস্তৃত বিজ্ঞাপন।’ এই ‘বহুবিস্তৃত বিজ্ঞাপন’কে সরিয়ে রেখে, আমরা চাই, এমন কবিতা লিখিত হোক, যা নিয়ে স্ব-দায়বোধ থেকে একজন প্রবীণ কবি লিখতে বাধ্য হবেন। সেইরকম কবিতা লেখার চেষ্টা কি আমরা করতে পারি না?
অনেক দিন আগে কবি জয় গোস্বামী ‘রাণাঘাট লোকাল’ কলামে লিখেছিলেন তাঁর এক আশ্চর্য উপলব্ধির কথা। স্বীকারোক্তিমূলক সে-লেখা পড়ে বিস্মিত হতে হয়। তিনি লিখেছিলেন, ‘আমি কি দুর্নীতি করিনি? হ্যাঁ, জেনে বুঝে? করেছি কি?… একেবারে অচেনা একজন যুবকের কবিতার বই উদ্বোধন করেছি, দশ হাজার টাকা নিয়ে। সেই যুবকের কোনও কবিতা পূর্বে কখনও পড়িনি। মেসেজ আসে, ফোনে। যুবকটি নিজেই জানান, তাঁর কবিতার বই আমি উদ্বোধন করলে, তিনি সম্মানদক্ষিণা হিসেবে আমাকে দশ হাজার টাকা দিতে প্রস্তুত। আমি যাই। প্রেস ক্লাবে। যাঁর কবিতা কোনও দিন একলাইনও পড়ার সুযোগ হয়নি, তাঁর বই হাতে নিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে ক্যামেরার ক্লিক-ক্লিক হতে দিই যতক্ষণ যুবকটি চাইলেন ততক্ষণ। আমার বক্তব্য পেশ করার সময়ে সেই বইয়ের দু’টি কবিতা পাঠ করি। আর যে কয়েকটি কথা বলি, সবই ভাল ভাল কথা…।’ দশ হাজার টাকা এখানে গৌণ। এখানে কবির ভেতরের যে-অনুশোচনা, তা কবিমন-জাত। কবিতা নিয়ে মিথ্যাচার করেছেন বলেই, তা ‘দুর্নীতি’। অকপটে জানিয়েছেন সে-কথা। কিন্তু জয় যেভাবে তাঁর অস্বস্তির কথা, মিথ্যাচারের কথা, প্রতারণার কথা উগড়ে দিচ্ছেন লেখায়— অন্য কবিরা সবাই কি তা করে থাকেন? যদি না করেন, পাঠক বুঝবেন কী উপায়ে, কোনটা নীতিবিরুদ্ধ আলোচনা আর কোনটাই-বা আন্তরিক?
‘দায়’ আর ‘দয়া’— কাছাকাছি দুটো শব্দ। অথচ একটা আ-কারের অদলবদলে কত অর্থবিস্তার! ১৯৩৬ সালের ২৮ জুন, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত রবীন্দ্রনাথকে চিঠিতে লিখেছিলেন, ‘অর্কেষ্ট্রার সমালোচনার কথাও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। সেটা যত তাড়াতাড়ি প্রকাশ হয়, আমার ততই মঙ্গল। উপরন্তু বইখানা আরো পুরানো হলে প্রবাসীর কর্ত্তারা সেটার জন্য জায়গা দিতে আরো ইতস্তত করবেন।’ সুধীন্দ্রনাথ যে-দায় থেকে রবীন্দ্রনাথকে এই কথা ক-টি লিখেছিলেন, রবীন্দ্রনাথও তাঁর তরফে একই দায় অনুভব করেছিলেন কি? বা, আরও বড় করে ভাবতে চাইলে, সবসময়ে যা তাঁকে লিখতে হত, স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে লিখতেন কি? একটা ছোট্ট প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ করে রাখা প্রয়োজন। নিরুপমা দেবী তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘ধূপ’ রবীন্দ্রনাথকে পাঠালে, প্রত্যুত্তরে তিনি লিখেছিলেন (৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭), ‘আমায় প্রবন্ধ লিখতে অনুরোধ করো না। আমার বয়স হয়ে এসেছে এবং আমি ক্লান্ত। সংসারে দয়া নেই বলেই দায় পড়ে মাঝে মাঝে লিখতে হয়। কিন্তু তোমাদের কাছ থেকেও কি দয়া প্রত্যাশা করব না?’
প্রত্যাশা দু’তরফেই থাকে। তরুণ কবি চান তাঁর বই নিয়ে প্রবীণ কবিরা আলোচনা করুক, তাঁকে স্বীকৃতি দিক। অন্যদিকে প্রবীণ কবিরা একটা পর্যায়ে পৌঁছে চান, তাঁকে যেন দায়ে পড়ে লিখতে না হয়। ভুলে গেলে চলবে না, দয়ার দান— সাহিত্যে কখনও চিরস্থায়ী হয় না। বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন, ‘কবিদের যা সবচেয়ে বড় শত্রু, তা দারিদ্র্য নয়, অবহেলা নয়, উৎপীড়নও নয়— তা অত্যধিক সাফল্য, তা বহুবিস্তৃত বিজ্ঞাপন।’ এই ‘বহুবিস্তৃত বিজ্ঞাপন’কে সরিয়ে রেখে, আমরা চাই, এমন কবিতা লিখিত হোক, যা নিয়ে স্ব-দায়বোধ থেকে একজন প্রবীণ কবি লিখতে বাধ্য হবেন। সেইরকম কবিতা লেখার চেষ্টা কি আমরা করতে পারি না?