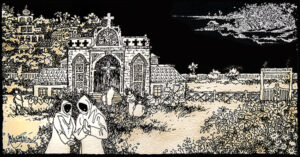বহুবার বলেছি তাঁদের কথা, তবু বার-বার বলতে ইচ্ছে করে। গুরুদের কথা, বিষয়টা লঘু হওয়া উচিত নয়। মনে হয় বার-বার তাঁদের কথা বললে আমি একটু একটু করে সৎ লোক হয়ে উঠি, যেন গ্রীষ্ম-দুপুরে বনের ছায়ার নীচে দিঘির শীতল জলে স্নান করে উঠলাম। আমার মাস্টারমশাইদের কথা। গুরুদের কথা। সব মাস্টারমশাই গুরু হয়ে উঠতে পারেন না এটা যেমন ঠিক, তেমনই সব ‘গুরু’-ও মাস্টারমশাই নন, রাস্তাঘাটে কথার চালাচালিতে সে-শিক্ষাও আমাদের হয়ে যায়। সব মানুষের মতোই আমারও ‘অথিক গুরু, পথিক গুরু, গুরু অগণন’। তবু তাঁদের কয়েকজনের কথা একটু বিশেষভাবে বেছে নিয়ে বলি, কারণ আমার মনে হয় আমার নির্মাণে এঁরা কোনও-না-কোনওভাবে হাত লাগিয়েছিলেন, অন্যদের চেয়ে একটু বেশি করে। এঁরা কি সেটা জানতেন? কে জানে ?
প্রথমে বলি আমার বাড়ির শিক্ষক অমূল্য আচার্য, অমূল্যদার কথা। তিনি পেশায় শিক্ষক ছিলেন না। আমার পালক-পিতা (আমাকে দত্তক নিয়েছিলেন তিনি) ছিলেন পূর্ববঙ্গের ঢাকা জেলার বালিহাটির জমিদারেরের এক আঞ্চলিক নায়েব, অমূল্যদা ছিলেন তাঁর মুহুরি। তিনি এলেন, সম্ভবত আমি তখন গ্রামের পাঠশালায় ক্লাস টু পাশ করেছি, দু-কিলোমিটার দূরে ধামরাইয়ের হার্ডিঞ্জ হাইস্কুলে থ্রি-তে ভর্তি হব, তখন। তিনি সম্ভবত তখনকার এন্ট্রান্স পাশ। আমাকে পড়ানোর দায়িত্ব তাঁর ওপর পড়ল, অনিবার্যভাবেই। সে-দায়িত্ব তিনি খুব আন্তরিক গুরুত্ব সহকারে নিলেন।
তাঁর পড়ানোর প্রাথমিক সূত্র ও প্রকরণ ছিল প্রহার। ছ-ফুটের বেশি লম্বা শক্তিশালী চেহারা তাঁর, পীড়নে বৈচিত্র ছিল প্রচুর। পেটে, হাঁটুতে ও শরীরের অন্যান্য অংশে শক্ত দু-আঙুলের চিমটি, সেরেস্তার খাতায় দাগ কাটার রুলার দিয়ে বাড়ি, পিঠে কিল, মাথায় গাঁট্টা ও চুলের ঝুঁটি ধরে টানাটানি ইত্যাদির পর্যায় চলত, যদি উত্তর দিতে না পারতাম, লেখা করে রাখতে ভুলে যেতাম বা তিনি ‘মহালে’ গেলে মায়েদের প্ররোচনায় বাড়ি ফেরার আগে ঘুমিয়ে পড়তাম। তিনি এসে জাগাতেন পায়ের ডিমে সাঁড়াশির মতো চিমটি দিয়ে, এবং আমাকে হাউমাউ করে উঠে চোখে জল দিয়ে, আবার পড়তে বসতে হত। কাছারি ঘরে বসে আমাদের ‘পড়াশোনা’ চলত। সেখান থেকে আমার কান্নার রোল বন্ধ দরজা দিয়ে অন্দর মহলে পৌঁছলে মায়েরা (আমার পালয়িত্রী দুই পিসিমা) যখন দরজা খুলে দেখতে আসতেন, কিন্তু অমূল্যদা তাঁদের বিশাল ধমক দিয়ে তাড়াতেন। বলতেন, ‘অর আত-পাগুলান যাতে ঠিক থাকে তা আমি দেখুম, আপনেরা যান।’ অমূল্যদার এই আদিম পাঠদানের ফর্মুলা আমার ছ-বছরের বড় আপন দাদা সহ্য করতে না পেরে প্রায়ই জঙ্গলে পালিয়ে গিয়ে গাছের ডালে বা কোনও মাঝির নৌকায় গিয়ে রাত কাটাতেন। তিনি ক্লাস ফোরের পর পড়াশোনাকে সসম্মানে বিদায় জানিয়েছিলেন।
কিন্তু আমার বেলায় সেই সুখান্তিক পরিণাম হল না, মেরে-মেরে পড়াশোনাটাকে কীভাবে ভাল লাগিয়ে দিলেন অমূল্যদা। বোঝালেন যে, পড়াশোনার মধ্যে একটা ‘মজা’ আছে। আমি বসে আছি সেই ঢাকা জেলার এক দূর গ্রামে, আর আমার বইয়ের মধ্যে পড়ছি ইহুদিদের নেতা মোজেসের, গ্রিক দেবতা অ্যপোলোর, পেরুর ইন্কাদের সভ্যতার, গ্রিনল্যান্ডে এস্কিমোদের কথা— পৃথিবীর ছ-টা মহাদেশ— সময় আর স্থানের দিক থেকে যেন একটা বড় জায়গার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে। পড়ার মধ্যে ওই বেরিয়ে পড়ার একটা সুযোগ আছে, অনেক দূরে, অনেক কাল আগে। রেজাল্ট বেরোনোর দিন অমূল্যদা বলতেন, ‘রেজাল্ট ‘এই’ না অইলে আর বাড়ির পথ ধরবা না।’ তাঁর কথা বিশ্বাস করে আমি কাঁদতে-কাঁদতে স্কুলে যেতাম। তিনি হয়তো জানতেন কী হবে, তাই বাড়ি ফিরে তাঁর হাতে কাগজটা দিলে তিনি কোমল গলায় মায়েদের বলতেন, ‘দ্যান, অরে বাটি ভইরা গরম দুধ খাইতে দ্যান, বেশি কইরা চিনি দিয়া।’
২
উদ্বাস্তু হয়ে খড়্গপুর শহরে এসে ক্লাস ফাইভে ভর্তি হলাম উদ্বাস্তুদের জন্য তৈরি এক স্কুলে, অতুলমণি স্কুল। অমূল্যদার নাগাল এড়িয়ে। এই আনকোরা স্কুলের মেঝেতে তখনও কাঁকরের গুঁড়ো। এমন সময় পড়েছিলাম হিতেনবাবু, হিতেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বর্মনের হাতে। মুখস্থ বিদ্যায় তাঁকে তাক লাগিয়ে দিয়েছি পরীক্ষায়, আবার ক্লাসে বসে বন্ধু হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে গলাগলি করে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের ‘যকের ধন’ পড়তে-পড়তে খুক-খুক করে হাসছি সুন্দরবাবুর ডবল ডিমের ওমলেট খাওয়ার নির্দেশে, সেই মুহূর্তে ‘এই তোরা দুটোতে কী করছিস রে’ বলে ধরে ফেলে দু-জনকেই বেঞ্চে কান ধরে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। ক্লাসে মেয়েরাও ছিল, সে এক লজ্জা। ক্লাস সেভেনের হাফ ইয়ারলি অংক পরীক্ষায় একটু দেরি করে গেছি, হিতেনবাবুর হাত থেকে প্রশ্ন নিয়ে দেখি, একেবারে জলের মতো। তাই আধ ঘণ্টাতেই ঘস-ঘস করে উত্তর করে হিতেনবাবুর হাতে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি। হিতেনবাবু একটু ভ্রূ কুঁচকে বললেন, ‘হয়ে গেল?’ আমি বললাম, ‘হ্যঁ স্যার।’ বলে লাফাতে-লাফাতে স্কুলের হাতার বাইরে বেরিযে যাচ্ছি, এমন সময়ে স্কুলের দপ্তরি ছুটে এসে ধরলেন, ‘তোমারে হিতেনবাবু ডাকতেয়াসেন।’ গেলাম। তিনি কখনওই বেশি কথা বলতেন না। যাওয়া মাত্র খাতাটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, ‘আর একবার দ্যাখ্।’ আমি ভাবলাম, এত সোজা প্রশ্ন, ছাঁকা উত্তর, এ আবার দেখার কী আছে? জায়গায় বসে দৌড়ে দেখে নিয়ে আবার তাঁর হাতে দিয়ে বললাম, ‘হয়ে গেছে স্যার, সবই ঠিক আছে ?’ তিনি বললেন, ‘তাই ?’ বলে আর কিছু বললেন না, কিন্তু আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। আমি চলে গেলাম এবং সেই খাতায় পরে একশোর মধ্যে চার নম্বর পেলাম। কিন্তু তিনি আমার আত্মবিশ্বাসের বেলুন ফুটো করে দিয়ে চিরকালের মতো আমাকে বাঁচিয়েছিলেন, তাই অ্যানুয়ালে আর সেই বিপর্যয় পুনরাবৃত্ত হয়নি।
মনে হয়, ভাল ছেলের স্টিরিয়োটাইপে যাতে না পড়ি, তার একটা চেষ্টা ছিল। সর্বস্তরেই ইউনিয়নের পান্ডাগিরি করেছি, নানারকম বাহাদুরি দেখানোর চেষ্টা করেছি, কিন্তু অজস্র শিক্ষকের স্নেহ পেয়েছি, মূলত তাঁদের স্নেহ অজস্র এবং নিঃশর্ত ছিল বলেই। মনে আছে খড়্গপুর কলেজের ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসের ইংরেজির প্রবীণ অধ্যাপক সরোজ ভট্টাচার্য মশায়ের কথা। ধুতি-পাঞ্জাবি পরা অতিশয় ভালমানুষ, সন্ধেবেলার কমার্স ক্লাসের বিশাল-বিশাল দাদারা তাঁকে নানাভাবে হেনস্থা করত। একবার তো তিনি কেঁদে তাঁদের ক্লাস থেকে বেরিয়ে এলেন, তাঁর প্রাক্তন ছাত্র প্রিন্সিপাল হিমাংশুভূষণ সরকারকে জানিয়ে দিলেন তিনি আর ওই ক্লাসে যাবেন না। প্রিন্সিপাল বিপন্ন হয়ে আমাদের ড়াকলেন। তখন ঠিক হল। অর্থাৎ আমরাই দাদাদের বোঝালাম যে, ব্যাপারটি ঠিক হয়নি। দাদাদের বললাম, সরোজবাবুর বাসায় গিয়ে ক্ষমা চাইতে হবে। সুখের বিষয়, তাঁরা রাজি হলেন। আমাদের মিছিল সরোজবাবুর বাসায় পৌঁছোল এক সন্ধ্যায়। দাদারা গিয়ে সরোজবাবুকে প্রণাম করে বললেন, ‘Sir, let us forgive and forget!’ কথাটার মধ্যে যে একটা কূটনীতি আছে, অর্থাৎ ‘আমরা ক্ষমা চাইছি’ বললেন না, সেটা সরোজবাবু উপেক্ষা করলেন। সকলের সামনে আর একবার কাঁদলেন, এবং মিষ্টি-টিষ্টি এনে খাওয়ালেন, এবং সকালের সামনেই আমাকে বললেন, ‘I can see that you are the mediator, and mediators are blessed by God.’
‘গড’ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস না থাকলেও, সেটা ছিল আমার জীবনের এক মস্ত তৃপ্তির মুহূর্ত।
৩
সব গুরুর কথা, বিশেষত স্কুল-কলেজের বাইরের অজস্র গুরুর কথা বলা সম্ভব নয়, তা আমি ‘আমার শিক্ষকেরা’ নামে একটি প্রবন্ধে বলেছি, আমার ‘অল্প পুঁজির জীবন’-এও কিছু আছে। বঙ্গবাসী কলেজের অনার্স ক্লাসে অধ্যাপক অরুণকুমার বসুর কথা বলি একটু। কলেজ জীবনের শেষদিকে এসে সাহিত্য আর রবীন্দ্রনাথ পড়ার ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গিই আমূল পালটে দিয়েছিলেন তিনি। এমএ পাশ করার পর ওই কলেজে আমার চাকরি পাওয়া নিয়ে তাঁর যে কী অসীম ব্যাকুলতা। শেষে আর-এক প্রিয় অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য আর প্রিন্সিপাল প্রশান্তকুমার বসুর আগ্রহে যখন সেই চাকরি হল, প্রথম দিন অরুণদা আমার প্রথম ক্লাসের বাইরে সারাক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন, আমি ক্লাস শাসন করতে পারি কি না দেখার জন্য। বিজ্ঞানের প্রাথমিক শ্রেণির সাহিত্যে উদাসীন ছাত্ররা চুপচাপ সে ক্লাস শুনেছিল। বেরিয়ে আসতেই অরুণদা আমার করমর্দন করে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।
এবারে বলি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের দু-একজন শিক্ষকের কথা। একজন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। যে-কারণেই হোক, তিনি কাছে ডেকে নিয়েছিলেন, তাঁর পটলডাঙার বাড়িতে প্রায়ই হানা দিয়েছি। প্রচুর গল্প করতেন নিজের ছেলেবেলার, নিজের গল্প লেখার। বাড়িতে প্রোজেক্টর এনে আইজেনস্টাইনের ব্যাট্লশিপ পোটেমকিন দেখানো হবে; বললেন, সন্ধেবেলায় চলে এসো। যখন ক্লাসে নাম ধরে ডাকতেন, তখন অহংকারে বুক দশ হাত হত। হয়তো সহশিক্ষার ক্লাসে এ-রকম হওয়াই নিয়ম।
এমএ পরীক্ষার পরে ফল বেরিয়েছে, স্যারকে প্রণাম করতে গেছি। স্যার বাড়িতে যেমন থাকতেন, লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরা, আশাদি (স্ত্রী লেখিকা আশা দেবী)-কে ডেকে বললেন, ‘আশা, পবিত্র এসেছে, ওর সঙ্গে একটু কথা বলো’, বলে ওই পোশাকেই দোতলা থেকে নেমে গেট খুলে কোথায় বেরিয়ে গেলেন। মিনিট পাঁচেক পরে এলেন, ডান হাতে গলায় দড়ি বেঁধে ঝোলানো এক নতুন হাঁড়ি। বললেন, ‘এ সময় পাড়ার দোকানে নতুন রসগোল্লা হয়, তোমার জন্যে গরম রসগোল্লা নিয়ে এলাম। আশা ওকে ক-টা দাও, আর বাকিটা তুমি তোমার মেসে নিয়ে যাবে।’ বোঝো কাণ্ড !
প্রমথনাথ বিশিও স্নেহ করতেন, কিন্তু সেটা সহজে বুঝতে দিতেন না। কিন্তু এমএ-র চূড়ান্ত পরীক্ষায় (১৯৬১) এই ছাত্রকে শতকরা নব্বই নম্বর দিয়ে বসলেন, পঞ্চাশে পঁয়তাল্লিশ। তখন এটা ছিল অবিশ্বাস্য ও বৈপ্লবিক ব্যাপার, এখন যতই সহজ হোক। পরের বছরের ক্লাসে ছেলেমেয়েরা জিজ্ঞেস করল, ‘স্যার, এত নম্বর দিলেন কী করে !’ প্রমথবাবু উত্তর দিতে গিয়ে এমন ভান করলেন যেন খুব রেগে গেছেন। চোখেমুখে ছদ্ম রাগ এনে বললেন, হুমকির মতো করে— ‘আর, পাঁচটা নম্বর তো তবু আমি হাতে রেখে দিয়েছি!’ ব্যাস্, ছেলেমেয়েরা চুপ!
৪
শেষ করি এক গুরুর কথা বলে, যাঁর কাছে আমি অপরাধ করেছিলাম, কিন্তু শিশুবুদ্ধিবশত ক্ষমা চাওয়ার কথা ভাবতে পারিনি। সেই অপরাধবোধ এখনও জেগে আছে।
তিনি অনেক আগেকার, সেই ধামরাই স্কুলের গুরু। রবীন্দ্রনাথের মতো দাড়িওয়ালা, কিন্ত ফেজ টুপি-পরা, এক মৌলবিসাহেব, আমরা বলতাম মৌলবিছাব। তিনি আমাদের বাংলা পড়াতেন ক্লাস থ্রি আর ফোরে। দেশভাগ ঘোষিত হয়েছে, নানা জায়গায় দাঙ্গা-হাঙ্গামার খবর আসছে, গ্রামের হিন্দুরা উদ্বিগ্ন, অনেকেই দেশ ছাড়ার পরিকল্পনা করছে। এমন সময় একদিন ক্লাসে, সম্ভবত পুজোর আগে মৌলবিসাব তাঁর খুলনার গ্রামের বাড়ির গল্প করছিলেন। সেখানে কত কত মাছ পাওয়া যায়, টাটকা খেজুরের গুড়, হঠাৎ আমার দিকে তকিয়ে বললেন, ‘জাইবা না কি সরকারমশয়, পুজরা ছুটিতে আমাগ দ্যাশে আমার লগে। মাছ আর খাজুর গুড়ের পায়েস খাইয়া মোটা অইয়া আসবা।’
হয়তো আমি না, ওই সময় আমাকে দিয়ে বলিয়ে নিল, ‘না মৌলবিছাব, আপনের লগে গেলে মুসলমানেরা আমারে কাইট্যা ফালাইব।’ মৌলবিসাব স্তব্ধ, সমস্ত ক্লাসও স্তব্ধ। কয়েক সেকেন্ড পরে মৌলবিসাব দু-চোখ বিস্ফারিত করে বললেন, ‘তুই আমারে এত বড় একটা কথা কইলি বাবা! আমার লগে থাকলে মুসলমানরা তরে কাইট্যা ফালাইব !’ তাঁর চোখ দিয়ে টপ-টপ করে জল পড়তে লাগল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ‘হায় আল্লা, তুমি দ্যাশটারে কে কইরা ফালাইলা !’ তখন বুঝিইনি যে, তাঁর কাছে এই কথাটার জন্যে ক্ষমা চাওয়ার দরকার ছিল। এখন আর চাইবার কোনও রাস্তাই তো নেই।
আমার অজস্র গুরু, আমার চিরপ্রণম্যরা, আপনাদের কাজ বেঁচে আছে কারও কারও, কিন্তু এই পৃথিবীর ধূলিকণায় আর আপনাদের চিহ্ন নেই। তবু হয়তো আমার মধ্যে আপনারা আছেন, কারণ আমি আপনাদের নির্মাণ। আমি জানি না আমি এভাবে কারও মধ্যে বেঁচে থাকব কি না।