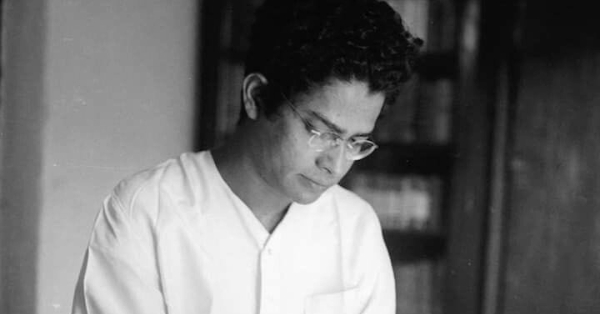সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে নিম্নবিত্ত শ্রেণি— প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পে অনায়াসে স্থান পেয়েছে। সমাজ-সচেতন বিষয় যেমন সেখানে স্থান পেয়েছে, পাশাপাশি শুধু গল্প লেখার জন্যও গল্প লিখেছেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণিই বেশির ভাগ সময়ে তাঁর গল্পের পাত্র-পাত্রী হয়ে উঠেছে। মধ্যবিত্তের স্বর ও সংকটকে এত নিখুঁতভাবে তিনি গল্পে স্থান দিয়েছিলেন, যা বাংলা সাহিত্যের অদ্বিতীয় নিদর্শন। হ্যাঁ, এক-একজন লেখক জীবনকে দেখেন এক-একরকমভাবে। জীবনকে দেখার ধরন থেকে একই বিষয় নিয়ে লিখেও, বক্তব্য সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যায়। পাঠকের হৃদয়তন্ত্রীতে তা ঝংকার তোলে ভিন্ন মাত্রায়। প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছেন প্রচুর। উপন্যাস, নাটক, গল্প, গোয়েন্দা গল্প, অনুবাদ সাহিত্য ইত্যাদি অজস্র সৃষ্টি তাঁর কলম দিয়ে বেরিয়েছে। কিন্তু এখনও তিনি পাঠকের কাছে জীবিত আছেন ছোটগল্প, ঘনাদা ও পরাশর চরিত্রের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে।
শিশু-কিশোর, গোয়েন্দা গল্প বাদ দিলে, প্রায় ১৪০টি গল্প লিখেছেন। গল্পগ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ২৮টি। সুতরাং লেখার সংখ্যা যথেষ্ট। প্রেমেন্দ্র মিত্র ‘কল্লোল’-গোষ্ঠীর লেখক হিসেবেই চিহ্নিত এবং স্বীকৃত। ‘কল্লোল’ পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৯২৩ সালে। যদিও তাঁর প্রথম সাড়া জাগানো গল্প ‘শুধু কেরাণী’ প্রকাশিত হয়েছিল ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় ১৯২৪ সালে। এই গল্প লেখার প্রেক্ষাপট হিসেবে তিনি ‘গল্প লেখার গল্প’-তে জানিয়েছেন, ‘কিছু যাদের নেই, যারা কেউ নয়, তাদের সেই শূন্য একরঙা ফ্যাকাশে জীবনের কোন গল্প কি হতে পারে না? হোক্ বা না হোক্ তাদের কথা লিখব বলেই কাগজ কলম নিয়ে বসলাম। লিখলাম শুধু এক কেরানীর গল্প।’ এ-প্রসঙ্গে মনে পড়ে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সংসারে, যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই— তাদের নিয়ে সাহিত্য রচনার কথা। কিন্তু শরৎচন্দ্রের লেখায় ছিল তীব্র আবেগ, প্রেমেন্দ্র মিত্র সেক্ষেত্রে ছিলেন আশ্চর্য সংযত। তিনি নিম্নমধ্যবিত্তের জীবনকে নির্মোহ দৃষ্টিতে নিজের কলমে তুলে ধরেছিলেন। ‘গল্প লেখার গল্প’তে তিনি আরও স্পষ্ট করে বলেছেন, ‘যাদের কথা কেউ লেখে না, যাদের জীবনে চোখ ধাঁধানোর ছড়াছড়ি নেই, তাদের কথা লেখার একটা তাগিদ’ অনুভব করেছিলেন। তাই তাঁর কলমে আমরা পাই— ‘সাগরসঙ্গম’, ‘কুয়াশায়’, ‘তেলেনাপোতা আবিষ্কার’, ‘কালো মেয়ে’, ‘পঞ্চশর’ ইত্যাদি গল্প।
এখানে একটি তথ্য বলে রাখা ভাল। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ‘কালি-কলম’ পত্রিকায় প্রকাশিত ‘পোনাঘাট পেরিয়ে’ গল্পটি পড়েই ভবিষ্যতের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় গল্প লেখায় নতুন করে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। লিখেছিলেন প্রথম গল্প ‘রসকলি’। ‘কল্লোল’-এ প্রকাশিত হয় ১৯২৭ (১৩৩৪ বঙ্গাব্দ) সালে। তারপরে এই পত্রিকাতেই লেখেন দ্বিতীয় গল্প ‘হারানো সুর’ ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে। সেদিন পুরনো ‘কালি-কলম’-এর সংখ্যাটি হাতে না পেলে, হয়তো সাহিত্যিক হবার বাসনাই ত্যাগ করতেন তারাশঙ্কর। তবে তারাশঙ্কর কল্লোলের লেখক দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েও মনন ও মেজাজে আর ‘কল্লোল’-গোষ্ঠীর থাকেননি, প্রেমেন্দ্র মিত্র ‘কল্লোল’-এরই লেখক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রইলেন।
নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষ প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পে স্থান পেয়েছে মাথা নত করে। পরিস্থিতির বিরুদ্ধে জোর করে লড়াই করেনি তারা। একজন নিম্নমধ্যবিত্ত শিরদাঁড়ার মানুষ ঠিক যতটা লড়াই দিতে পারে, তাঁর চরিত্ররা ঠিক ততটাই লড়াই দেয়। না হলে অসহায় হয়ে, পরাজয় স্বীকার করে নেয়। বাস্তবে ক’জনই-বা লড়াই দিতে পারে। তাই তাঁর চরিত্ররা অনেক বেশি বাস্তব হয়ে ওঠে। ‘শুধু কেরাণী’ গল্পে স্বামী-স্ত্রী দু’জনেই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে লড়তে চেয়েছে, কিন্তু লড়াইয়ের ময়দানে তারা নামতেই পারেনি। তাই গল্পের একেবারে শেষে মেয়েটি বলে, ‘আমি মরতে চাইনি— ভগবানের কাছে রাতদিন কেঁদে জীবন ভিক্ষা চেয়েছি, কিন্তু—’। আর তার স্বামী কেবল উপায় সন্ধান করেছে, পায়ে হেঁটে গাড়ি ভাড়া বাঁচিয়ে লড়াই করতে চেয়েছে; তার বেশি কিছু পারেনি। বাস্তবের নিম্নমধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষ তো এরকমই হয়। লেখক প্রেমেন্দ্র অযথা কোনও চরিত্রকে ‘হিরো’ করতে চাননি, ওই যে বলে না, ‘লার্জার দ্যান লাইফ’! অহেতুক এসব করেননি। তাঁর প্রতিটি গল্পেই এ-সত্য ধরা পড়ে।
ধরা যাক, ‘তেলেনাপোতা আবিষ্কার’ গল্পটির কথা। কীরকম একটা অলৌকিকতা দিয়ে বা একটা মায়ার জগৎ রচনা করে লেখক পাঠককে তেলেনাপোতায় নিয়ে যান। কিন্তু শেষপর্যন্ত গল্পে তিনি যা বলেন, কোথাও এতটুকু অবাস্তব বলে মনে হয় না। আমাদের জীবনে এরকম ঘটনা ঘটেই থাকে। নিজেকে মহৎ করে দেখানোর দুদর্মনীয় সত্তা যামিনীর মতো মেয়েকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেলে। কিন্তু নিজের পারিপার্শ্বিকে এসে সম্বিত ফিরে এলে মনে হয়, এভাবে নিজের জীবনটা ধ্বংস করা ঠিক হবে না। এই দোটানাই তো মধ্যবিত্তকে মধ্যবিত্ত করেছে। তাই কল্পনার তেলেনাপোতা অত্যন্ত বাস্তব হয়ে ওঠে আমাদের কাছে। আমরা এই আলোচনার শুরুতেই বলেছি প্রেমেন্দ্র মিত্র যে-কোনও অবস্থায় যে-কোনও বিষয় নিয়েই গল্প সৃষ্টি করতে পারতেন। কিন্তু জীবনের ধর্মকে, বাস্তবতার ধর্মকে তিনি কখনও লঙ্ঘন করেননি। হ্যাঁ, পত্রিকা-সম্পাদকদের তাগাদায় বা অর্থের কারণে একই গল্পকে একাধিকবার ভিন্ন নামে, কখনও বা গল্পের সূচনা বা চরিত্রের নামটুকু কেবল বদলে দিয়ে চালিয়েছেন। কিন্তু তাঁর গল্প, পাঠ করা শুরু করলে শেষ করে থামতে হয় এবং গল্প শেষে পাঠক বলতে পারবে না, একটা ফালতু গল্প পড়ে সময় নষ্ট করলাম বা বলতে পারবে না, কোনও গল্পে গল্পের গোরু গাছে তুলে দিয়েছেন।
কিন্তু নিজের পারিপার্শ্বিকে এসে সম্বিত ফিরে এলে মনে হয়, এভাবে নিজের জীবনটা ধ্বংস করা ঠিক হবে না। এই দোটানাই তো মধ্যবিত্তকে মধ্যবিত্ত করেছে। তাই কল্পনার তেলেনাপোতা অত্যন্ত বাস্তব হয়ে ওঠে আমাদের কাছে।
আবার, ‘হয়তো’-র মতো গল্পে, লেখাটাই শুরু করেছেন নাটকীয়ভাবে। গল্পকার বা কথক নিজের ব্যক্তিজীবনে একটি ঘটনার সাক্ষী ছিলেন। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই গল্প ফেঁদে বসলেন। একদম অকপট স্বীকারোক্তি— ‘সেই অসাধারণ ঘটনা ও সেই অস্পষ্ট দেখা দুইটি মূর্তিকে কেন্দ্র করিয়া একটি কাহিনী মনের ভিতর আপনা হইতেই গড়িয়া ওঠে।’ এই বলে আসল গল্প শুরু করলেন। কিন্তু গল্পটা পড়ে কিছু-কিছু জায়গা সামান্য অবাস্তব বলে মনে হলেও, শেষ পর্যন্ত বলতেই হবে— বাস্তব জীবনে তো এরকমই হয়। প্রেমেন্দ্র মিত্র একটু রহস্য করে জীবনের ওই সত্যে পাঠককে নিয়ে গেছেন। স্ত্রীকে সন্দেহের বশে অনেক স্বামীই মারার চেষ্টা করে। কিন্তু এমনভাবে মারে, যাতে প্রমাণ হয় ওটা ছিল দুর্ঘটনা। এই গল্পে মহিমও তাই করতে চেয়েছে। কিন্তু তার স্ত্রী লাবণ্যকে গল্পকার ব্রীজ থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করে বাঁচিয়ে দেন। আর গল্প শেষ করেন এই ব’লে— ‘হয়তো আর কোথাও জীবনের সেতু হইতে মহিম লাবণ্যকে কবে ঠেলিয়া দিয়াছে!’
‘জনৈক কাপুরুষের কাহিনী’ গল্পে, কথকের সঙ্গে করুণা নামের একটি মেয়ের প্রেমের সম্পর্ক হয়। কিন্তু করুণার বিয়ে হয় অন্যত্র। পরে আবার করুণার সঙ্গে কথকের দেখা হয়। দু’জনেরই দু’জনকে মনে পড়ে। তাদের প্রেমের স্মৃতি আবার সজীব হয়ে ওঠে। কথক যেন সুযোগ পেয়েও করুণাকে গ্রহণ করতে পারে না। তাই যেন একপ্রকার পালিয়ে যাওয়ার জন্যই, করুণার স্বামীর বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতে চায়। করুণা বাধা দেয় না। বরং নিজের হাতে সব কিছু গুছিয়ে তাড়াতাড়ি রওনা করিয়ে দেয় যাতে ট্রেন চলে না যায়। কিন্তু স্টেশনে গিয়ে সে করুণার দেখা পায়। কথক বিস্মিত হয়ে করুণার স্টেশনে আসার কথা জিজ্ঞাসা করলে উত্তর পায়, ‘দলিল পুড়িয়ে দিয়ে এলাম।… খুব অসম্ভব কি কিছু বলছি? সব নোঙর ভাসিয়ে নিয়ে যাবার মত ঢেউ কি আসে না কখনো?… তুমি আমায় নিয়ে যেতে পার না?’ বিবাহিত করুণা যখন এই কাতর আর্তি জানাচ্ছে তার প্রাক্তন প্রেমিককে, তখন কথক করুণাকে গ্রহণ করতে চায় না নানা অজুহাত দেখিয়ে। মধ্যবিত্ত জীবনের নিয়মই তো এটা। বলা ভাল নিয়তি। যাকে একদিন প্রবলভাবে চেয়েছি, সে-ই একদিন সব বাধা অতিক্রম করে ধরা দিতে আসলেও ধরতে পারা যায় না। করুণাও সব বুঝে শেষে বলে, সে স্টেশনে এসেছিল পিসিমাদের স্টেশন থেকে বাড়ি নিয়ে যাবার জন্য। অর্গলমুক্ত দু’টি হৃদয় আবার হৃদয়ের সব কপাট বন্ধ করে নেয়। খুবই সাধারণ একটি বিষয়, কিন্তু তা নিয়ে অসাধারণ গল্প লেখায় প্রেমেন্দ্র মিত্র ছিলেন সিদ্ধহস্ত। যে-কোনও সময়, যেকোনও বিষয় নিয়ে একটা কাগজ আর পেন দিলেই, তিনি অসাধারণ কিছু সৃষ্টি করে ফেলতে পারতেন।
‘পঞ্চশর’ গল্পগ্রন্থের গল্পগুলো যেন কত অনায়াসেই লিখে ফেলেছেন। আড্ডা দিতে বসে কয়েকজন বন্ধু নিজের-নিজের গল্প বলে গেল। প্রত্যেকটাই অসাধারণ গল্প। আসলে বলতে ইচ্ছে করছে, গল্প লেখা ছিল প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাছে একটা মামুলি ব্যাপার। পরিচালক তরুণ মজুমদার তাঁর ‘স্মৃতিটুকু থাক’ চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য লিখতে অনুরোধ করেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্রকে। এক মাসের মধ্যে মাত্র কয়েকটি কাগজে চিত্রনাট্য লিখে দেন। পরিচালক দেখলেন সংলাপহীন, সাংকেতিক ভাষায় লেখা একটা কিছু। পরে বুঝেছিলেন, সাংকেতিক ভাষায় লেখা সেই চিত্রনাট্যে সবই ছিল। এবং সেই সিনেমা হিট-ও করে। যদিও তরুণ মজুমদারের আগের একটি চিত্রনাট্য লিখতে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মাসের পর মাস এবং মুড আনার জন্য বায়ু পরিবর্তন পর্যন্ত করেছিলেন। বুদ্ধদেব বসু কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পর্কে বলেছিলেন, কবিতা লেখার মতো এরকম একটা আপাত নিরীহ কাজে তিনি মনোনিবেশ করেছিলেন। আমাদের মতে গল্প লেখাটাও প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাছে ছিল নিরীহ, অনায়াসলভ্য একটি কাজ।