বাবা দেবেন্দ্রনাথের প্রতি রবীন্দ্রনাথের মনোভাবে মিশে ছিল সম্ভ্রম, শ্রদ্ধা। কিন্তু সে দু’য়ের অতিরিক্ত আর-একটা কথাও কি ছিল না? যাকে বলা যায় ভীতি? রবীন্দ্রনাথের নিজের কথাতেই তার আভাস মেলে; ‘জীবনস্মৃতি’তে কখনও তিনি লিখেছেন [প্রবাস থেকে বাবা বাড়ি এলে] ‘আমরা ধীরে ধীরে চলি, ধীরে ধীরে বলি, উঁকি মারিতে সাহস হয় না।’ কখনও বলেছেন, কীভাবে পিতার আদেশে হিমালয়ে গিয়েও ‘বরফগলা ঠাণ্ডাজলে স্নান’ করা ছিল বাধ্যতামূলক, ‘ইহা হইতে কোনোমতেই অব্যাহতি ছিল না।’ কিংবা আর-একটু বড় হয়ে প্রতি মাসের দুই আর তিন তারিখে বাবাকে হিসেব বুঝিয়ে দেওয়ার দিনগুলোর কথা, ‘ওই দুটা দিন বিশেষ উদ্বেগের দিন ছিল।’ রথীন্দ্রনাথ অবশ্য আর-একটু স্পষ্ট করে দিনদুটোর বর্ণনা করেছিলেন তাঁর এক স্মৃতিকথায়, ‘স্কুলের ছেলেরা যেমন করে পরীক্ষা দিতে যায়, বাবা [রবীন্দ্রনাথ] যেন তেমন করে যেতেন মহর্ষির কাছে হিসাব দাখিল করতে। আমরা সব ছেলেমানুষেরা অবাক হয়ে ভাবতাম, আমাদের বাবা তাঁর বাবাকে এত ভয় পান কেন?’
রবীন্দ্রনাথ যেমন করে তাঁর বাবাকে পেয়েছিলেন, তার থেকে রথীন্দ্রনাথ আর তাঁর বিশ্ববিখ্যাত পিতার সম্পর্ক ঠিক কোথায় কতদূর আলাদা হয়ে গেল?

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ‘বাল্যকালে তিনি [দেবেন্দ্রনাথ] আমার অপরিচিত ছিলেন বলিলেই হয়।’ হিমালয়-সংলগ্ন অঞ্চল ও ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে দেবেন্দ্রনাথ সেসময়ে প্রায় সারা বছরই কাটাতেন। কলকাতায় এলেও জোড়াসাঁকোয় না-থেকে পার্ক স্ট্রিটে বাড়ি ভাড়া করে থেকেছেন। পত্নী সারদাসুন্দরীর অসুস্থতার খবর জানিয়ে তাঁকে টেলিগ্রাম করায় তিনি আসার ব্যাপারে খুবই গড়িমসি করেছেন। এমনকী আসার পথে সরাসরি কলকাতায় না-এসে শান্তিনিকেতনে নেমে কিছুদিন কাটিয়ে তবে এসেছেন বাড়িতে।
রথীন্দ্রনাথ কিন্তু ছোটবেলায় তাঁর বাবাকে পেয়েছেন নিঃসন্দেহে এর চেয়ে অনেক নিবিড়ভাবে। বাধ্যত দূরে থাকতে হলে বারবার রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন তাঁর ‘খোকা’র কথা; স্ত্রীকে লিখেছেন, ‘বেলি [=মাধুরীলতা] খোকার জন্যে এক একবার মনটা ভারি অস্থির বোধ হয়।’ কাছে থাকলে বাবা-ছেলে ঘুরে বেড়িয়েছেন নানা জায়গায়, কখনও শান্তিনিকেতনে কখনও-বা উত্তরবঙ্গের জমিদারিতে। তবু, বাবা নন, তাঁদের ছেলেবেলা জুড়ে ছিলেন মা, একথা রথীন্দ্রনাথই বলে গেছেন। ‘বাবা ছিলেন তাঁর নিজের ঘরে লেখাপড়া নিয়ে মা ছিলেন তাঁর ছেলেমেয়েদের নিয়ে সংসারের কাজে। সেইজন্য ছেলেবেলার কথা মনে করতে গেলে মায়ের কথাই বেশি মনে পড়ে।’ ১৮৯৮ থেকে রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে শিলাইদহে গিয়ে বাস করতে আরম্ভ করেন। তখন রথীন্দ্রনাথের বয়স দশ। নিজের বিদ্যালয় জীবনের ভয়াবহ অভিজ্ঞতাকে মনে রেখে ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করেননি রবীন্দ্রনাথ। শিলাইদহে নিজের তত্ত্বাবধানে পুত্রের লেখাপড়া শুরু হল। প্রকৃতির মধ্যে স্বাধীনভাবে বিচরণের শিক্ষাও এখানেই পেলেন রথীন্দ্রনাথ। যেখানে খুশি ঘুরে বেড়ানো, ঘোড়ায় চড়া, মাছ ধরা, নৌকো বাওয়া, লাঠিসড়কি খেলা ইত্যাদি সবরকমের কাজে পিতার উৎসাহ পেয়েছেন ভরপুর। এমনকী জমানো-টাকা দিয়ে ছোট ডিঙি কিনে তাতে দাঁড় টেনে, পাল তুলে সমস্ত দিন নদীর এপার-ওপার করার দুষ্টুমিকেও শাসন করে দমিয়ে রাখেননি কবি। খুব অল্প বয়সেই প্রায়-অচেনা বা অল্প-চেনা লোকদলের সঙ্গে ছেলেকে পাঠিয়ে দিয়েছেন কেদার-বদরী। অবশ্য অল্প দূর থেকে নজর রেখে গেছেন বাবা যে, এই স্বাধীনতা যেন স্বেচ্ছাচারে বদলে না-যায়।
বাবার সঙ্গে কিছু-বা দূরত্বময় কিছু-বা নিবিড় এক ছোটবেলা কাটানোর পর বাবা যেন অনেকখানি বন্ধু হয়ে এলেন একটু বড় বয়সে। ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষিবিদ্যায় ডিগ্রি লাভ করে, ইউরোপ ঘুরে রথীন্দ্রনাথ ভারতে এসে পৌঁছোলেন ১৯০৯-এর সেপ্টেম্বরে। তখন শমীন্দ্রনাথ-সহ দুই পুত্রকন্যাকে হারিয়ে স্ত্রীকে হারিয়ে মানসিকভাবে অনেকখানি বিপর্যস্ত কবি। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ‘হাউসবটে কেবল বাবা আর আমি। বারবার মৃত্যুশোকের আঘাতে, বিশেষ করে অকালে শমী চলে যাওয়ায়, তাঁর মনে তখন গভীর বেদনা, তিনি নিতান্ত একাকী। দীর্ঘকাল প্রবাসের পর আমি ফিরে এসেছি, সুতরাং তাঁর হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ-ভালোবাসা তিনি যেন উজাড় করে ঢেলে দিলেন।’

ছেলের প্রতি একান্ত নির্ভরতার এই হল সূচনা। রথীন্দ্রনাথ তাঁর সমস্ত জীবন দিয়ে এই নির্ভরতার মূল্য চুকিয়েছেন। ছেলেকে লেখা কবির চিঠিপত্রগুলো মন দিয়ে পড়লে বোঝা যায়, সেই চিঠির মধ্যে এমন এক বিশ্বস্ত নিবিড়তার সুর আছে যা অন্য কারও উদ্দেশে লেখা চিঠিতে পাওয়া সম্ভব নয়। নিজেরই গড়া আশ্রম সম্পর্কে তাঁর হতাশার বোধ অকপটে ব্যক্ত করেছেন ছেলের কাছে। ১৯৩৫-এর এক চিঠিতে যেমন লিখবেন, ‘আশ্রমে এখন অধ্যাপকেরা সকলেই অক্রণ, এবং কারো মধ্যেই আদর্শে বিশ্বাসের গভীরতা নেই…। তাই এরা আশ্রমকে কোনোদিক থেকে গড়তে পারছে না।’ কখনও বিশ্বভারতীর প্রকাশন বিভাগের উপর রাগ করে ছেলেকেই বলতে পারছেন, ‘বিশ্বভারতীর হাতে স্বাধীনতা খুইয়েছি, নইলে আগেকার মতো ইন্ডিয়ন প্রেসের হাতে বই ছাপার ভার দিতুম।’ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বইতে বলশেভিক বিপ্লবের সমর্থনে কথা আছে দেখে কিছু-বা আশঙ্কিত কবি ছেলেকেই জানাচ্ছেন, ‘এই বই বিশ্বভারতীর নামে বাজারে চালিয়ে দেওয়া কোনো মতেই হতে পারে না।’
চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে তাঁর বিরোধ সর্বজনবিদিত। তা সত্ত্বেও চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর শোকসভায় তাঁর যাওয়া উচিত কিনা সে-বিষয়ে ছেলেকে প্রায় অভিভাবক মেনে কবি পরামর্শ চাইছেন। এবং অবশ্যই, ছেলেকেই লিখতে পারছেন তাঁর গোটা জীবনের সম্ভবত সবচেয়ে মর্মান্তিক দুটো বাক্য। প্রথমটা, ১৯১৪ সালে, নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পরের বছর, অমরত্বের পাকা-আসন যখন তাঁর জন্য বরাদ্দ হয়ে গিয়েছে, ছেলেকে লিখছেন, ‘দিনরাত্রি মরবার কথা এবং মরবার ইচ্ছা আমাকে তাড়না করেছে। মনে হয়েছে আমার দ্বারা কিছুই হয়নি এবং হবে না, আমার জীবনটা যেন আগাগোড়া ব্যর্থ।’ এ স্বীকারোক্তি কি আর কারও কাছে করা সম্ভব ছিল কবির পক্ষে? আর দ্বিতীয়, নিজের মেয়ের মৃত্যুকামনা, ‘বিয়ের রাত্রে মীরা যখন নাবার ঘরে ঢুকছিল তখন একটা গোস্ রো সাপ ফস্ করে ফনা ধরে উঠেছিল আজ আমার মনে হয় সে সাপ যদি তখনি ওকে কাট্ তাহলে ও পরিত্রাণ পেত।’ রবীন্দ্রনাথকে অন্তরঙ্গভাবে চিনতে হলে আমাদের তাই রথীন্দ্রনাথের মাধ্যমেই অনেকখানি চিনতে হয়।
রথীন্দ্রনাথ তাঁর সমস্ত জীবন দিয়ে এই নির্ভরতার মূল্য চুকিয়েছেন। ছেলেকে লেখা কবির চিঠিপত্রগুলো মন দিয়ে পড়লে বোঝা যায়, সেই চিঠির মধ্যে এমন এক বিশ্বস্ত নিবিড়তার সুর আছে যা অন্য কারও উদ্দেশে লেখা চিঠিতে পাওয়া
সম্ভব নয়।
অমিতা ঠাকুর একবার একটা আশ্চর্য কথা লিখেছিলেন। ‘রথীন্দ্র-স্মৃতি’ শিরোনামের এক লেখায় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তিনি লিখলেন, ‘একটা কথা মনে হয় ঠিক, স্বাধীনতা বলতে যা বোঝায় তা তিনি ছেলে-বউকে দেন নি।’ রবীন্দ্রনাথ দেননি, এই কথাটা কতদূর সত্য তা বলা আজকে বেশ মুশকিল, তবে রথীন্দ্রনাথ নিজেই অনেকটা স্বেচ্ছাবৃত দায়ের মতো করে তাঁর জীবনের অনেক ‘স্বাধীনতা’ স্ব-ইচ্ছা, সাধ-আহ্লাদ বাবার স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে বিসর্জন দিয়েছিলেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই।
চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক যখন ভাল ছিল, চিত্তরঞ্জন প্রস্তাব নিয়ে এলেন যে, তিনি রথীন্দ্রনাথকে রাজশাহী থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিতে নিয়ে যেতে চান। রবীন্দ্রনাথ রাজিও ছিলেন তাতে। রথীন্দ্রনাথ যাননি। বিশ্বভারতীর কাজ ছেড়ে তিনি কোত্থাও যেতে চান না। স্বাধীন ভারতবর্ষে জওহরলাল নেহেরু তাঁকে ডাক দিয়েছিলেন রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়ত্ব গ্রহণের, সে প্রস্তাবও সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেন তিনি। ১৯২৪ সালে এক চিঠিতে রথীন্দ্রনাথ লিখছেন, ‘শান্তিনিকেতনে যখন থাকি, আমি তখন সম্পূর্ণভাবে আমার অফিসের নিয়ন্ত্রণে কাজের এত চাপ যে ন্যূনতম সাধ-আহ্লাদের অবসরটুকুও মেলে না।’ এই সব সত্ত্বেও নিজেকে চাপমুক্ত করার কোনও চেষ্টা কখনও তিনি করেননি, এই ঋণ রবীন্দ্র-অনুরাগীদের কখনও ভোলা উচিত নয়।
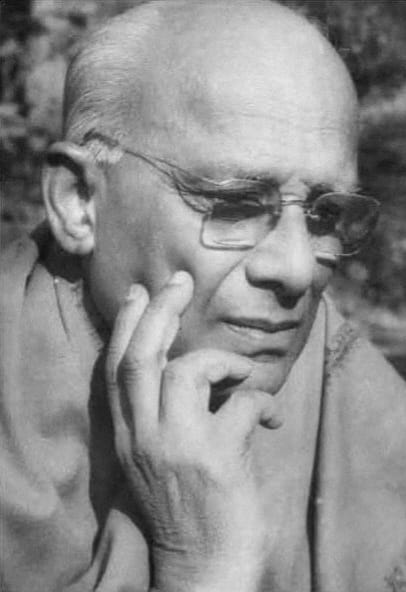

আরও একটা কথা নিশ্চয়ই খেয়াল রাখবার। বিশ্বভারতী গড়ে ওঠবার পেছনে রথীন্দ্রনাথের নীরব অবদান। রবীন্দ্রভবনের মতো অনন্য সংগ্রহশালার পরিকল্পনা ও রূপদানের পেছনে তাঁর প্রায় একেক প্রচেষ্টা তো বিশেষভাবে মনে করবার বটেই, সেই সঙ্গে এ-কথাও ভুললে চলে না যে, তাঁর অসামান্য খামখেয়লি এবং বিশ্ববিখ্যাত পিতাকেও আগাগোড়া সামলাতে হয়েছে তাঁকেই। সে বড় কম কথা নয়। যেমন ধরা যাক, রবীন্দ্রনাথের বাসস্থান পরিবর্তনের এক বাতিক ছিল। জোড়াসাঁকোর দিনগুলোতেও নিজের ঘর পরিবর্তন করতেন যখন তখন। মৃণালিনী দেবী তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠতে পারেননি সবসময়। মা অকালে চলে যাওয়ার পর থেকে, বাবার এই খামখেয়াল প্রায় সারাজীবন রথীন্দ্রনাথকেই সামলাতে হয়েছে। দ্বারকানাথ ঠাকুর সম্বন্ধে একটা কথা রসিকতার ঢঙেই হাওয়ায় ভাসত, “Babu often changes his mind”। দ্বারকানাথের বিখ্যাততম পৌত্রটি এ বাবদে একেবারে তাঁরই অনুরূপ ছিলেন। রথীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছেন, ‘এজন্য আমাদের কম ভুগতে হয় নি। এ নিয়ে অনেক মনকষাকষি হয়েছে এমন-কি মাঝে মাঝে তো রীতিমতো বিপদে পড়তে হয়েছে বাবার এই খেয়ালিপনার দরুন।’ কিন্তু এইসব ‘বিপদ’ও হাসিমুখে সামলেছেন, প্রায় একারই হাতে, রথীন্দ্রনাথ।
পুত্রের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে পিতা যে কবিতাখানি লিখেছিলেন, তাতে ছিল এই লাইনগুলো— ‘কর্মের যেখানে উচ্চদাম/সেখানে কর্মীর নাম/নেপথ্যেই থাকে একপাশে।’ রবীন্দ্রনাথ জানতেন তাঁর পুত্রের এইটাই জীবনব্যাপী কাজ। পুত্রও জানতেন এইটাই তাঁর সর্বোচ্চ গর্ব, তিনি একজন কর্মী।






