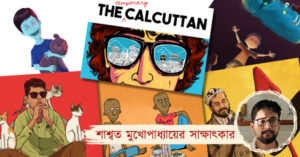‘শ্মশানের মাঝখানে বসে কাপালিক ঋত্বিককে কি আমরা আবিষ্কার করতে পেরেছি?’— বিজন ভট্টাচার্য
আজ থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার কথা। ১৯৯১ সালের ১১ মে নন্দন প্রেক্ষাগৃহে দেখানো হল ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ সিনেমার একটি সুসম্পাদিত বয়ান। পশ্চিমবঙ্গে প্রথমবার। আমরা সবাই জানি, পূর্ণদৈর্ঘ্যের এই ছবিটি তৈরি হয়েছিল সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশে, ১৯৭৩ সালে। সে-দেশে এই ছবির প্রযোজক ছিল ‘পূর্ব প্রাণ কথা চিত্র’। বাংলাদেশে ছবিটি মুক্তি পায় ১৯৭৩ সালের ২৭ জুলাই। তবে ছবির অবয়ব পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের আদৌ মনঃপূত হয়নি। ছবির এডিটিং বিষয়ে নানান সাক্ষাৎকারে ঋত্বিক তাঁর অসন্তোষের কথা জানাতে শুরু করেন। মাঝখানে কেটে গেছে প্রায় ২০ বছর। ভারতবর্ষে সেই নবায়িত চলচ্চিত্রের প্রথম প্রদর্শনের দিন আমিও উপস্থিত ছিলাম নন্দনে।
তখন আমি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। দিনটা, বলা ভাল সন্ধেটা এখনও আমার কাছে স্পষ্ট। তৎকালীন মহারথীরা প্রায় সকলেই সেদিন উপস্থিত ছিলেন। সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং সমাজবিজ্ঞানের অগ্রগণ্য ব্যক্তিত্বদের এমন সমারোহ আগে আমি অন্তত কখনও আগে দেখিনি। ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ দেখার পর সেসব কিছু মনে ছিল না। একটা ঘোরের মধ্যে একদম একা হেঁটে বেড়িয়েছিলাম পার্ক স্ট্রিট-ধর্মতলা-কলেজ স্ট্রিট-বিবেকানন্দ রোডের অলিতে-গলিতে। একটা বিস্ময়, একটা অস্থিরতা, একটা মুগ্ধতা। ১৯৯১ সালের জুন সংখ্যা ‘প্রতিক্ষণ’-এ সেই অভিভূত মনের প্রকাশ ঘটেছিল এক অকিঞ্চিৎকর লেখায়।
আরও পড়ুন: ক্যামেরার চলনে ‘সুবর্ণরেখা’ ছাপিয়ে যায় সংকীর্ণ বাস্তবকে! লিখছেন প্রদীপ্ত ভট্টাচার্য…
উল্লেখযোগ্য কথাটা হল, তার পর থেকে আজ পর্যন্ত অসংখ্যবার ছবিটি দেখেও, সেই উত্তেজনা এবং মুগ্ধতার শেষ হল না। বরং মনে হয়, প্রতিটা দেখায়, ছবির নতুন-নতুন ‘পাঠ’ এবং তাৎপর্য যেন খুলে যায়। ১৫৯ মিনিটের ছবিটি এক বহুস্তরিক, বহুব্যাপ্ত অতিকায় চেহারা নিয়ে মনে প্রবল অভিঘাত তৈরি করে। বিশেষজ্ঞতার দাবি আমার একেবারেই নেই। ব্যক্তিগতভাবে মনে হয়, এত বড়মাপের ইতিহাস-ভূগোল-বিশ্ববীক্ষণের চলচ্চিত্র আমাদের দেশে অন্তত আমার চোখে পড়েনি। পরিকল্পনা-প্রয়োগ, প্রতিটি শট এবং সামগ্রিক রূপায়নের পারস্পরিকতা, সিনেমার ভাষা এবং সংগীত-প্রয়োগ, সমাজসময়ের সঙ্গে মহাসময়ের সংলাপ— সবই অনন্য দক্ষতায় নির্মিত হয়েছে। অদ্বৈত মল্লবর্মণের উপন্যাসের যেন এক নতুন ‘পাঠ’, এক নতুন আয়তন, এক নতুন আবিষ্ক্রিয়া উপস্থাপন করলেন ঋত্বিক। একটি সাক্ষাৎকারে জানালেন, ‘…উপন্যাসটা আমার নিজের ধারণায় এপিকধর্মী, এ ছবিতে আমি প্রথম এই ঢঙটা ধরার চেষ্টা করেছি…।’
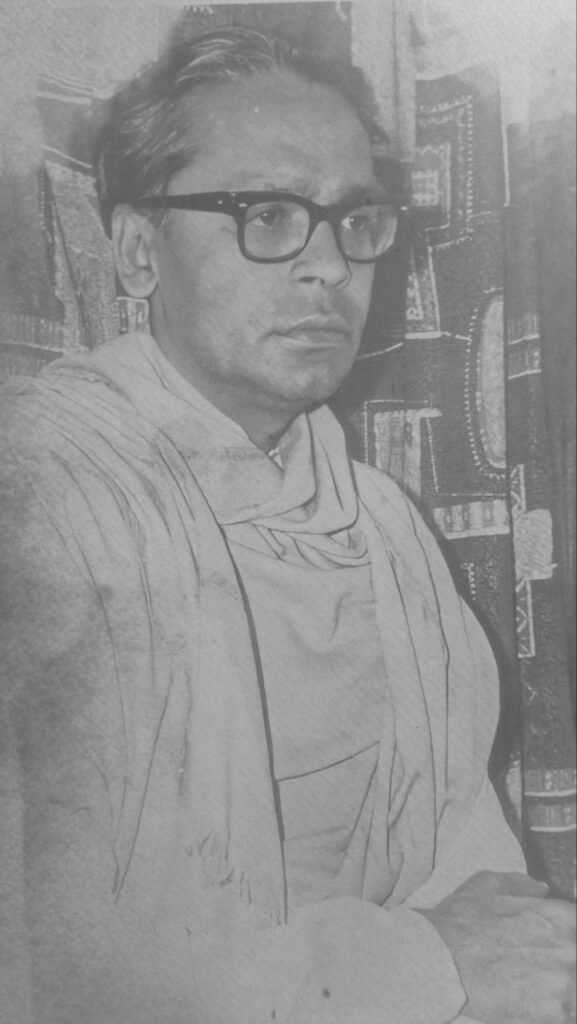
২
এখন প্রশ্ন হল, কী সেই ঢং? যে-কোনও মহাকাব্যের থাকে অপরিসীম বিস্তার, থাকে উপকাহিনি-শাখাকাহিনি থেকে কিংবদন্তি, গালগল্প, ইতিহাসপুরাণ, স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গ, দাস্তান-কাহ্ন-বাতেল্লার অযুত প্রবাহ। ‘আধুনিক’ সময়ের শুরু-মধ্য-অন্ত নির্দিষ্ট খোপকাটা চকচকে নির্মাণ এখানে পাওয়া যাবে না। কথা-উপকথা-ইতিকথা-বৃত্তান্ত মিলেমিশে সেখানে সমানে ‘কেন্দ্রীয়’ ঘটনাকে সংযোজন-সংরচনে বহুমুখী করে তোলে। ‘তিতাস’ নদীর মুখ্য উপস্থিতির সঙ্গে এই চলনের জোয়ার-ভাঁটা-সহস্রধারার কাহিনি বেশ মিলে যায়। ‘শিথিল’, ‘ঢেউ-স্রোত-তরঙ্গ’ বিশিষ্ট মহাআখ্যানের একটা বহুস্বর সেখানে ফুটে ওঠে। চরিত্রেরা আসে-যায়, নিজস্ব ‘পরস্তাব’ নিয়ে এক-একটি বিন্দু তৈরি করে। আরও মন দিয়ে লক্ষ করলে বোঝা যায়, কাহিনি গ্রন্থনার ফাঁকে-ফাঁকে ঋত্বিক একই অনুসন্ধিৎসায় ঢুকিয়ে যেতে থাকেন ব্রত, কথকতা, গান, পার্বণ, সমবায়িক জীবনের পরব-ছড়া-নাচ-উল্লাস-বেদনা। সেখানে বাস্তব থেকে অতিবাস্তব, সমকাল থেকে অতীত, জনপদের সমবেত নির্জ্ঞান (Collective Unconscious) সবই স্পর্শগোচর থাকে। লক্ষ করা যাবে, ‘তিতাস…’ ছবিটি শুরু হয় মাঘমণ্ডলের ব্রত দিয়ে, তারপর আসে দোল উৎসব, তারপর পৌষ সংক্রান্তি। ঢুকে পড়ে বিয়ের গান, নৌবাইচের হুল্লোড়, মেয়েদের নিজেদের ছড়া-হেঁয়ালি-মজামস্করার জগৎ। এইভাবে পার্বণ, লোকপুরাণ, গান, শরীর, জল আর সম্প্রীতি মিলেমিশে যেতে থাকে। রামপ্রসাদ কাকা হয়ে যান কাদের মিঞা। পোড়াকপাল মা স্বপ্নে দেখা দেয় ভগবতী রূপে। বাস্তব থেকে তার যাত্রা অলৌকিকে। মহাজনপদের সমবেত মননে। ‘উপন্যাসটা আমার নিজের ধারণায় এপিকধর্মী’— কথাটায় আছে সেই জনগোষ্ঠীর মহাকাব্যিক কালাতীত ইতিহাস-শরীরের ইঙ্গিত। নদী, অববাহিকা, মালোজীবন, অজস্র চরিত্র, যৌথকামনা মৌখিক সংস্কৃতি আর জননিরীক্ষা— সেই ইতিহাসের অপ্রতিরোধ্য উপাদান। আমরা জানি, মহাকাব্য নির্মিত হয় জনপরিসরে, জনসৃষ্টির বহমানতায়। আলগা তার গঠন, বহুমুখী তার বিস্তার, নদীর মতোই বহুস্বর-বহুবিচিত্র তার কলধ্বনি, অগণ্য তার শরিক। এই পরিবর্তমান, আয়তনবান, তরঙ্গয়িত ইতিহাসের তথা আত্মপরিচয়ের সন্ধান ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ চলচ্চিত্র।

৩
শুধু এপিকের নির্মাণই নয়, ঋত্বিক নজর করতে চাইছেন নিজেকে, নিজের সময়কে। নজর করছেন আমাদের। ‘আমাদের আধুনিকতা’ নিয়ে বড়াই আর দম্ভকে। খুঁজছেন বিকল্প। সেই বিকল্পসন্ধানী মনটিই, আমার কাছে এই ২০২৫ সালে আদ্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এখানেই তার কালোত্তীর্ন সমকালীনতা।
ঐতিহাসিক গৌতম ভদ্র জানাচ্ছেন— “কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রিক কাঠামোর বাইরে যে-সব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নিম্নবর্গের স্বচ্ছন্দ বিচরণ, সেইসব ক্ষেত্রে যে সংঘর্ষ ও সমঝোতার ইতিহাস আছে, তার প্রকাশ রয়েছে সম্প্রদায়ের চৈতন্যে, সমূহের (Community) ধারণায়, গোষ্ঠী আর কৌমের (Clan) নানা ধর্মীয় বিশ্বাস আর আচারে। ধর্মভিত্তিক চৈতন্যের মাধ্যমেই মার্গ বারবার আত্মসাৎ করেছে জন-কে, জন্ম দিয়েছে দেশজ সংস্কৃতির। প্রতীচ্য ‘যুক্তিবাদ’ ও সংস্কৃতি এখানে বড় ছেদ এনেছে, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও দুর্বলতা এই ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে মোচড় দিয়েছে অন্যভাবে, জন্ম দিয়েছে ‘ছক কাটা শতরঞ্জের মতো’ খোপে ভরা ইতিহাসবিদ্যার।” এই ‘ইতিহাস বিদ্যা’-কেই রবীন্দ্রনাথ দেউলিয়া বলেছিলেন। কেননা, আত্মআবিষ্কারের বদলে সে অনুকরণ আর ইয়োরোকেন্দ্রিক ভাবালুতায় অন্ধ। এই ‘ইতিহাসবিদ্যা’-র বদ্ধ, সাদা, পাশ্চাত্যপ্রযোজিত খাঁচা থেকেই আমাদের আধুনিকতার জন্ম। শহুরে, আত্মবিস্তৃত, হীনমন্য, উপনিবেশের মেরুদণ্ডহীন প্রজার ‘পরমুখাপেক্ষী’ আধুনিকতা। ঋত্বিক সেই আধুনিকতাকে প্রত্যাখ্যান করেন, তাকে সম্পূর্ণ বিচূর্ণ করেন।
‘উপন্যাসটা আমার নিজের ধারণায় এপিকধর্মী’— কথাটায় আছে সেই জনগোষ্ঠীর মহাকাব্যিক কালাতীত ইতিহাস-শরীরের ইঙ্গিত। নদী, অববাহিকা, মালোজীবন, অজস্র চরিত্র, যৌথকামনা মৌখিক সংস্কৃতি আর জননিরীক্ষা— সেই ইতিহাসের অপ্রতিরোধ্য উপাদান।
বারংবার তিনি সেজন্য এক আদিম প্রত্ন-প্রতিমা (Archetype) খোঁজেন; জল, মাতৃত্ব, গর্ভস্থ জলের স্মৃতি আর কৌমসমাজের যৌথচেতনার অবচেতনকে মোচড় দিয়ে নতুন অর্থে সঞ্জীবিত করতে চান। দেশমৃত্তিকালগ্ন জনজীবনের নিজস্ব যাপনে খোঁজেন দেশমাতৃকার অপার্থিব অতিবাস্তব অবয়ব। ‘Cinema and I’ গ্রন্থে একটি প্রবন্ধে সেজন্য বারংবার মনে করান ‘চলচ্চিত্র’কে ‘কবিতা’ করে তোলাই পরিচালকের কাজ। যেখানে আভাসে-ইঙ্গিতে-প্রতীকে-সুরে-গানে-নাচে-উল্লাসে ধরা যাবে, কোনও মহাকায় দোত্যনা। আমাদের মনে পড়তে পারে, অধ্যাপক বিনয় চৌধুরী আদিবাসী সমাজের অস্তিত্ব আর উপলব্ধি প্রসঙ্গে বলেছেন, ‘অব্যাহত’ স্মৃতি’ নামক ইতিহাসের উপাদানের কথা। সেই ‘স্মৃতি’কে এপিক ফর্মের মাধ্যমে ছুঁতে চান ঋত্বিক। আমাদের মনে করাতে চান বিকল্প এক ‘আধুনিকতা’-র অবয়ব। মৃত্তিকালগ্ন অবয়ব। আত্মবীক্ষা আর আত্মশক্তির ‘আধুনিকতা’। দুই বাংলা জুড়ে তার দুই ডানা। ধর্ম-বর্ণ-জাতি-লিঙ্গ-বিশ্বাস জড়িয়ে-জাপতে তার বহুস্বরিক আধুনিকতা।

৪
এক কথায় বলা যেতে পারে, ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ সেই অর্থে ঋত্বিক ঘটকের বৃহত্তম এবং মহত্তম প্রকল্প। ব্যক্তিঅনুভব, ব্যক্তিস্মৃতি থেকে জনযাপন আর জনশ্রুতির উদ্ঘাটন তার লক্ষ্য। সে-কাজে দেশমৃত্তিকা থেকেই উদ্গত দেশমাতৃকার গগনচুম্বী অবয়ব। হয়তো সে-জন্যই প্রধান চরিত্রের নাম হয়ে ওঠে ‘অনন্ত’।
আত্মপরিচয় আবিষ্কারের এই অভিযানে তার প্রকল্প সে-জন্য খুঁজে দেখা মানুষের রুক্ষ, প্রসাধনবিহীন, আঁকাড়া, এবড়োখেবড়ো জীবন। আরও গভীর সমস্যা ছিল এই জীবনযাপনকে চলচ্চিত্রের ভাষায় তর্জমা করা। প্রকৃতি আর মানবজন্মের সমন্বয়ী এক অনুভব, জনজীবন আর জনমানুষের অবিরাম কর্মমুখর অভিযাত্রা— তার চিত্রভাষ। এ প্রায় অসম্ভবের সাধনা। কতটা সচেতন ছিলেন ঋত্বিক, সে তো স্পষ্ট তাঁর জবানবন্দিতে— ‘একটি ভাষা, যাহা কম বলিবে, যাহা স্বয়ং দ্যোতনাময়। যাহার allusion-এর ভার নাই, পরিপূর্ণ ধরে আছে। যাহা Reference-এ ভারাক্রান্ত করে না, অথচ মনে পড়াইয়া দেয়— কারণ ছোঁয়ায় ছোঁয়ায় যে অনুভূতি, আর যে চিত্রকল্প, তাহা Archetypal!… তেমন ভাষাটি কিন্তু আছে। খুঁজিয়া পাইতেছি না, কি সব আজেবাজে করিতেছি।… বায়োস্কোপে ঐ ভাষায় কথা বলা প্রয়োজন। য়ুরোপ পারিবে না, এ যুগে। আমরা পারিব যদি খুঁজি।… খুব খানিকটা না রাগিলে, খুব ভাল না বাসিলে, খুব খুসী না হইলে, খুব না কাঁদিলে এ আদিম ভাষা কোথা হইতে উঠিবে?…আমি সেই একটা দুরাশা করিয়াছি। সেই ভাষাটিকে ধরিবার জন্য প্রাণপাত করিয়া যাইব, এ দেহ দিব।…কারণ আমাকে যে ফিরিয়া যাইতে হইবে আমার মায়ের গর্ভে, এ ভাষার উৎস সন্ধানে।’
মাতৃগর্ভ এবং তার এবং তার জন্মকালীন জলে যেমন মিশে থাকে ভ্রূণের স্মৃতি। ব্যক্তি থেকে কৌমে। এই পুরো স্মৃতিলোকটিকেই টান দিতে চেয়েছেন ঋত্বিক। মাতৃমূর্তি আর নারীচরিত্রের সেজন্যই ‘তিতাস’ চলচ্চিত্রে এত প্রভাবশালী উপস্থিতি।
৫
‘তিতাস একটি নদীর নাম’ ছবির অন্তর্লীন নানা স্তরকে উপলব্ধি করতে গেলে, দেখতে হবে এরই সমান্তরাল একটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের চিত্র। ১৯৭১ সালে নির্মিত। নাম হল ‘দুর্বার গতি পদ্মা’। নদী, জনপদ, মাতৃমূর্তি আর আত্মপরিচয়ের সেই সন্ধানে অবশ্য ফিরে-ফিরে আসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ। কালসীমা নির্দিষ্ট সেই ছবির আবহে ব্যবহৃত হয়েছিল, ‘আমি টাকডুম টাকডুম বাজাই/ বাংলাদেশের ঢোল’ গানটি। কণ্ঠ: শচীনদেব বর্মন।

বাংলা মায়ের কোল আর ‘মা-পুতের এই বাঁধন ছেঁড়ার সাধ্য কারো নাই’— উচ্চারণ চিরায়ত মাতৃত্বের ব্যক্তি থেকে জনঈপ্সার ক্ষেত্রটিকে স্পষ্ট করে। ‘তিতাস’ ছবিতে এত স্পষ্ট ইঙ্গিত নেই। কালচিহ্নও নেই। বাসন্তীর অবসানের দৃশ্যে, ভেপু বাজানো বালকের দিকে তোলা হাতটিই আমাদের সম্বল। অতীতকে ছোঁয়ার ঈপ্সা। আত্মআবিষ্কারের ঈপ্সা। কাপালিকের সাধনাই তো দেহ ছুঁয়ে দেহাতীতের দিকে সন্ধানকে নিয়ে যাওয়া। নদী শুকিয়ে যায়, সাধনায় বিরতি নেই। সে চলে, চলে, চলে। নিজস্ব আধুনিকতাকে খোঁজে। শতবর্ষে ঋত্বিক আমাদের নাচতে বলেন। নিজস্ব নাচ। — অপার্থিব। বিমূর্ত।