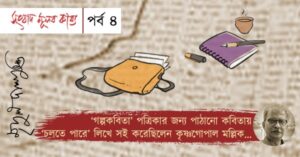নাসা, রকেট, লংহর্ন,
‘ভ্রমি বিস্ময়ে!’ মহাকাশের অপার রহস্যময়তা নিয়ে সেই যে লিখে গেছেন রবি ঠাকুর, হিউস্টনে নাসার দপ্তরে পা রেখে, সেটাই মনে পড়ল। টানা সপ্তাহখানেক ঘুরলেও দেখা ফুরোবে না, আর আমরা কিনা এসেছি একবেলার ঝটিকা সফরে! এমনিতেই টিকিট কেটে যেটুকু দেখা যায় লিন্ডন বি জনসন (প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট) স্পেস সেন্টারে, তা এখানকার বিপুল কর্মযজ্ঞের একশো ভাগের একভাগও না, আর সেটুকু বুঝে ওঠাই আমাদের মতো আনাড়িদের পক্ষে মুশকিল।
কাঠফাটা রোদে, টুপি দিয়ে মাথা বাঁচিয়ে, ওই বিশাল চত্বরে ঢুকেই, প্রথম নজর কাড়ল গুটিকয়েক অভিজাত চেহারার বিশাল শিংওয়ালা গরু, মনে হল জার্সি গরু। কিন্তু না, ওদের কাউ বললে রীতিমত ক্ষুণ্ণ হন হিউস্টনের লোকেরা। ওরা টেক্সাস লংহর্ন। এই রাজ্যের প্রতীক পশু বলা যায়। কিন্তু এরা কেন স্পেস সেন্টারে? আসলে একসময়ে যখন মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র গড়ে ওঠেনি, এই মাঠে আনন্দে চরে বেড়াত ওরা। তারপর নাসা তৈরি হল, শুরু করল লংহর্ন প্রজেক্ট। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের কৃষি ও পশুপালনের প্রশিক্ষণ। এখন এই শিংওয়ালার দল পরমানন্দে থাকে নাসার আদরে। শুনলাম, বিজ্ঞানীদের সংস্কারের মান রাখতে, নতুন মহাকাশযানের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময়ে এদের হাজির রাখতেই হয় আশেপাশে। এরা নাকি শুভ।

এই মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রের এক-একটি বাড়িতে ঢুকে, আমার তো নিজেকেই গরু বলে মনে হচ্ছিল, অবশ্য যদি সত্যিই গরু নির্বোধ প্রাণী এমন কোনও প্রমাণ থেকে থাকে। ১,৬২০একর জায়গায় ছড়ানো শ’খানেক বাড়ি, সবক’টি নম্বর দেওয়া, তার এক-একটিতে অজস্র ঘর। মেশিনপত্র, কম্পিউটার, এল.ই.ডি স্ক্রিনের ছড়াছড়ি। গ্যালারির চেয়ারে বসে, মনযোগী ছাত্রের মতো নোটও নিতে পারেন। এর সবগুলোতে অবশ্য ঢোকার অনুমতি নেই ট্যুরিস্টদের। গোটা তিনেক বিল্ডিং সফরের পরই মাথা ভোঁ-ভোঁ করছিল। যদিও গাইড যথাসম্ভব সোজা করে বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু সেটাই আমার বা আমার আশেপাশের লোকেদের কাছে গুরুপাক মনে হচ্ছিল।
বিশ্বের এনার্জি করিডর হিউস্টনে চমকে দিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের মূর্তি! পড়ুন: ডেটলাইন পর্ব ৩৪
যেটুকু বুঝলাম, মহাকাশযানে নভোশ্চর পাঠানো, যাকে বলে হিউম্যান স্পেসফ্লাইট, তাই নিয়ে এঁদের এই রাজসূয় যজ্ঞ। গবেষণা আর প্রশিক্ষণ তো বটেই, এখানকার বিজ্ঞানীদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল মিশন কন্ট্রোল। নাসা যে-ক’টি মহাকাশযান পাঠিয়েছে, সবগুলো নিয়ন্ত্রিত এই হিউস্টন থেকে। উৎক্ষেপণের পর থেকে, পৃথিবীতে ফিরে আসা পর্যন্ত পুরোটা। জেমিনি, অ্যাপোলো থেকে হালের স্টারলাইনার, সব।
তাছাড়া, মহাকাশ কেন্দ্রের খুঁটিনাটি কন্ট্রোল করেন, এখানকার বিজ্ঞানীরা। গাইড বললেন, যখন কোনও মিশন চলে, চব্বিশ ঘণ্টা শিফটে কাজ করেন নাসার বিশেষজ্ঞরা। ‘ছুঁয়ে দেখতে পারি যন্ত্রপাতি?’ আমার সঙ্কোচ হেসেই উড়িয়ে দিলেন গাইড ভদ্রলোক, ‘হোয়াই নট?’ যদিও এগুলো নিশ্চয়ই বাতিল বলেই ভিজিটরদের দ্রষ্টব্য হিসেবে সাজানো, তবু গায়ে কাঁটা দিল। একদিন হয়তো বিজ্ঞানের সূক্ষাতিসূক্ষ্ম হিসেব-নিকেশে, এগুলো থেকেই নির্ধারিত হয়েছিল সেই অমোঘ মুহূর্ত— ‘মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্যসীমা।’


১৯৬৯ সালে অ্যাপোলো ইলেভেনের যাত্রী হয়ে, চাঁদের মাটিতে পা রাখা প্রথম মানব নীল আর্মস্ট্রং-এর ভাষায়, ‘দ্যাটস ওয়ান স্মল স্টেপ ফর ম্যান, ওয়ান জায়ান্ট লিপ ফর ম্যানকাইন্ড।’ শিহরিত হলাম শুনে, চাঁদ থেকে ফিরে নীল আর্মস্ট্রংরা এখানেই কোয়ারেনটাইনড ছিলেন। চাঁদের বুক থেকে কুড়িয়ে আনা পাথরের (না কি পাথরের মতো কিছু?) টুকরো এখানেই রাখা আছে। তখন এই জনসন স্পেস সেন্টারে ছিল, লুনার রিসিভিং ল্যাবরেটরি।
এই তো সেদিন খবরে জানলাম, সুনীতা উইলিয়ামসরা দীর্ঘদিন মহাকাশে কাটিয়ে, নানা বাধাবিপত্তি পেরিয়ে, মর্ত্যে ফিরে কোয়ারেনটাইনড হয়েছিলেন জনসন স্পেস সেন্টারে। এর মধ্যেই হাসির রোল পড়ে গেল, নীল আর্মস্ট্রং-এর মাইনে শুনে; বছরে ২৭,৪০১ ডলার। অসামরিক ব্যক্তি বলে সেটা অনেকটাই বেশি, ওঁর বাকি দুই সঙ্গী প্রতিরক্ষা বাহিনীর মাইনেটাই পেয়েছিলেন, চাঁদে যাওয়ার জন্য কোনও বোনাস ছিল না। হিসেব করে দেখতে গেলে, চাঁদের বুকে প্রায় আড়াই ঘণ্টা হাঁটার জন্য, আর্মস্ট্রং-এর পারিশ্রমিক ৩৩ ডলার!
নাসা চত্বরে আরও দুর্ধর্ষ সব দেখার জিনিস রয়েছে। এয়ারপোর্টে যেমন প্লেনের হ্যাঙার থাকে, এখানেও তেমন আছে। সেখানে স্পেস শাটল থেকে রকেট সব দেখতে পাবেন। যত ইচ্ছে ছবি তুলুন, নিজেকে মহাকাশচারী কল্পনা করে পোজ দিন। এমনকী একসময়ে সত্যি মহাকাশযাত্রা করেছে, ‘অ্যাপোলো’ ১৭-র মতো যানও রাখা আছে। স্পেস স্টেশনের মডেল আছে, নিজের চোখেই দেখে নিন কোথায় ঘুমোন, কীভাবে ব্যায়াম করেন, কেমন টয়লেট ব্যবহার করেন মহাকাশচারীরা।
কয়েকঘণ্টা ধরে এতসব দেখেশুনে, উত্তেজনা যখন তুঙ্গে, অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্স হয়ে দেখা দিল স্পেস ফুড। ফুড ল্যাব থেকে অত্যাশ্চর্য কিছু খাবার (খাদ্যবস্তু কি আদৌ বলা যায় তাকে?) কিনল আমাদের দলের এক কিশোর। আমরাও খুব উৎসাহ দেখালাম, মহাকাশের খাবার-দাবার এই মাটির পৃথিবীতে বসে কি আর পাব কখনও? রং-বেরঙের তাক লাগানো চেহারা আর নামগুলোও অদ্ভুত। কোনওটা মুখে দিয়ে মনে হল থার্মোকলের টুকরো তো কোনওটা স্পঞ্জ। কিন্তু মহাকাশচারীরা কি সত্যিই এরকম সব বিস্বাদ খাবার খান? ওঁদের ইন্টারভিউতে পড়েছি, বিশেষভাবে প্যাক করা স্যুপ, ম্যাকারনি, শ্রিম্প ককটেল, ফল, সব্জি, অনেক সুখাদ্যই খান।
সে যাই হোক, নাসার অফিশিয়াল স্যুভেনির শপে গিয়ে আরেকবার আশ্চর্য হলাম। সব আইটেমই মেড ইন চায়না। এমনকী নাসার লোগো ফ্রিজ ম্যাগনেট পর্যন্ত। অগত্যা বিশ্বব্যপী চাইনিজ আগ্রাসনের কথা ভাবতে-ভাবতে, কিনেই ফেললাম গোটাকতক স্মারক। নাসা দেখেছি বলে কথা, দেশে ফিরে জানাতে হবে না!
টেক্সাস কেন মাদক পাচারের জন্য এত দুর্নাম কিনেছে জানেন? এখানকার লোক একবাক্যে বলেন, মেক্সিকোর জন্য। বড়লোক আমেরিকার গরিব লাতিন আমেরিকান প্রতিবেশী। গালফ অফ মেক্সিকো দিয়ে জোড়া। ট্রাম্প তাঁর আগের বারের শাসনকালে মাঝেমাঝেই হুমকি দিতেন, সীমান্তে পাঁচিল তুলে বন্ধ করে দেব অনুপ্রবেশ। তাহলেই আর ড্রাগ ঢুকবে না।
শুধু হিউস্টন বা অস্টিনের মত টেক্সাসের বড় শহরে নয়, এখান থেকে অনেকটাই দূরে নিউ জার্সিতেও দেখেছি ছোটখাটো চাকরি বা বাড়ির কাজের জন্য, মেক্সিকো বা গুয়াতেমালা থেকে আসা সস্তার শ্রমিকদের। মার্কিন মুলুকে বাড়ির কাজ মানে রান্নাবান্না, ঘর পরিষ্কার, বাগান করা, এসবের জন্য কাজের লোক রাখার মতো আর্থিক অবস্থা যে বিরল বাঙালিদের আছে, সৌভাগ্যক্রমে তাঁদের একজন আমার দিদি ডাঃ নূপুর লাহিড়ি। নিউ জার্সিতে তাঁর বাড়িতে, আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল মেরি আর তার বরের। সপ্তাহে দু’দিন তারা আসত, ঘণ্টা ধরে, ডলারের পারিশ্রমিকে ঘরের যাবতীয় কাজকর্ম করতে। তাঁদের কাছে শোনা, সীমান্ত পেরোনোর রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা অন্য কখনও শোনাব।
ভাবাই যায় না, প্রাচীন মায়া সভ্যতার আলো, কীভাবে নিভে গিয়ে দারিদ্রের অন্ধকার নেমে এল, কীভাবে অপরাধের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠল মেক্সিকো। হিউস্টনে অবশ্য দুর্ধর্ষ মেক্সিক্যান ফুড পাওয়া যায়। রেস্তোরাঁয় খেতে বসলে, প্রথমেই টেবিলে দিয়ে যাবে, ইয়া বড় একবাটি টরটিলা চিপস, সঙ্গে ডিপ। অথেন্টিক ট্যাকো বা ফাহিতা অর্ডার করতে পারেন তারপর। ভেতো বাঙালির জন্য পট রাইসও মন্দ নয়, সব্জি আর মাংস মেশানো আঠালো ভাত।
মেক্সিকো যাওয়ার সৌভাগ্য এখনও পর্যন্ত না হলেও, আপাতত গালফ অফ মেক্সিকোর ধারে, অসাধারণ গ্যালভেস্টন বিচ বেড়ানোর গল্প বলতেই পারি। আটলান্টিক মহাসাগরের একফালি, যার একদিকে আমেরিকা, অন্যদিকে মেক্সিকো। হিউস্টন থেকে ঘণ্টাখানেক লাগে যেতে। একবাস বাঙালি পা রাখলাম, দুপুর গড়িয়ে যাওয়া নরম রোদে গা এলিয়ে থাকা এক আলসে দ্বীপে। যার একদিকে আঠারো শতকের বিশাল সব ভিক্টোরীয় স্থাপত্যের বাড়ি, সামনে পাথরের রাস্তা দিয়ে ট্রাম চলে। একঝটকায় মনে হবে, পৌঁছে গিয়েছেন দু’শো বছর আগের লন্ডনে।
অন্যদিকে আধুনিক বিচ টাউনের সব বিনোদনের আয়োজন, বড়-বড় হোটেল, রেস্তোরাঁ। অথচ শুনলাম, মাত্র বছর কুড়ি আগেও নাকি গ্যালভেস্টনকে বলা হত, ‘সিন সিটি অফ দ্য গালফ।’ নেশা আর জুয়ার আড্ডা ছিল গোটা দ্বীপে। এখন আমূল বদলে গেছে ছবিটা। ফ্যামিলি ভ্যাকেশন বলতে যা বোঝায়, তার আদর্শ স্পট।
আরও শুনলাম, সেই ১৯০০ সালে বিশাল ঝড়ের তান্ডবে, এখানে কয়েক হাজার লোকের মৃত্যু হয়েছিল। তাদের অতৃপ্ত আত্মা নাকি আজও কেঁদে ফেরে, সাগরের নোনা বাতাস ভারি হয়ে ওঠে তাদের দীর্ঘশ্বাসে। অশরীরির কান্না না শুনলেও, সিগালদের কোরাস কান্নায় কান পাতা দায় সৈকতে। ঠিক মনে হয়, অনেক বাচ্চার সমবেত চিল চিৎকার। কেন যে ওদের লাফিং গাল বলে কে জানে!
তবে পাখি তো দূর, হাসি-কান্নার তফাৎ কি সবসময় মানুষও বোঝে? বালিতে হাঁটার সময়ে আর-একটা ব্যাপার খেয়াল রাখবেন, নীল কাঁকড়া। আমাদের তালসারি বা বকখালির সৈকতে যেমন লাল কাঁকড়ার দল ঘুরে বেড়ায়, জবার কুঁড়ির মত লাগে দূর থেকে, কাছে গেলেই কম্পন টের পেয়ে ঢুকে যায় গর্তে, এখানেও তাই। তবে অত পরিমাণে দেখলাম না। বেশি নীল কাঁকড়া দেখতে গেলে, যেতে হবে জলের একেবারে কাছাকাছি।
মানুষ ভয় পেতে ভালবাসে। তাই ভূতের বই, হরর ফিল্ম সুপারহিট। প্রায় সব শহরেই ঘোস্ট ওয়াকের ব্যবসা ভাল চলে। গ্যালভেস্টনেও ট্যুরিস্টরা বেশ পছন্দ করেন এই ভুতুড়ে সফর। সন্ধে নামার পর, দু’চারটে পুরনো বাড়ির সামনে, গা-ছমছমে আবহ তৈরি করে আসলে যা বলেন গাইড, তা হল এই প্রাচীন সৈকত শহরের ইতিহাস। সেটা খুবই আগ্রহব্যঞ্জক। তবে তার থেকেও বেশি চমকদার, ট্রি স্কালপচার ট্যুর। ২০০৮ সালে হারিকেন ঝড়ে প্রচুর গাছ উপড়ে গেছিল গ্যালভেস্টনে। এর মধ্যে খান তিরিশেক নিয়ে অসাধারণ ভাস্কর্য তৈরি করেছেন স্থানীয় শিল্পীরা।
হিউস্টন ফেরার পথে, অন্ধকার মাইক্রো বাস ছুটে চলেছে হাইওয়ে দিয়ে। বঙ্গ সম্মেলনের পর দুটো দিন, একদম খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে ঘোরাঘুরি হল। কাল ঘরে ফেরার প্লেন ধরবে সবাই। এক শিল্পী গান ধরলেন— ‘মন চল নিজ নিকেতনে/সংসার বিদেশে বিদেশির বেশে/ভ্রম কেন অকারণে।’ চারপাশে হঠাৎ নৈঃশব্দের তর্জনী।