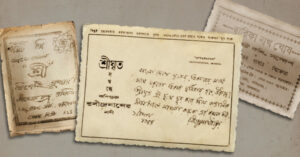শতবর্ষ পেরিয়ে এসে ফিরে দেখা সলিল চৌধুরীর সংগীত, রাজনীতি, সুরের দর্শন। আইপিটিএ থেকে সলিলের মূল্যায়ন নিয়ে কথা বলছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের চলচ্চিত্রবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক মৈনাক বিশ্বাস। কথোপকথনে প্রিয়ক মিত্র…
‘গণসংগীত’-এর ধারায় সলিল চৌধুরী কী একটি স্বতন্ত্র অবস্থান তৈরি করেছিলেন বলে মনে হয়?
‘গণসংগীত’ শব্দটা আইপিটিএ বা ভারতীয় গণনাট্য সংঘ-র আন্দোলনের আগে খুব একটা উচ্চারিত হয়নি। দেশাত্মবোধক গান ইত্যাদি ছিল। সলিল চৌধুরী যখন প্রথম দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কোদালিয়া বা তার আশপাশের গ্রামগুলিতে (এখন যা সুভাষগ্রাম অঞ্চল) কৃষক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ছেন, তখন ওঁর বয়স, ওঁরই বয়ানমাফিক (‘জীবন উজ্জীবন’ বই অনুসারে) ১৭। সালটা ১৯৪১। সেই নিরিখে দেখলে এটাকে ঠিক সলিল চৌধুরীর শতবর্ষ বলা যায় না যদিও। সেইসময় যে গানগুলি রচনা করছিলেন সলিল, সেগুলি কৃষক আন্দোলনের জন্যই রচনা করা। সলিল নিজেই বলছেন, সেই গানগুলিকে গণসংগীত বলে তখনও অভিহিত করা হত না। একথা বলতেই হবে, গণসংগীতে সলিল চৌধুরীর সিদ্ধি, সফলতা ও প্রভাব সেই সময়ের অন্য যে-কোনও সংগীতকারের থেকেই অনেকটা বেশি। ওঁর গান জনপ্রিয় হয়েছে তুমুলভাবে, স্থায়ীও হয়েছে। আজও যখন পথে নেমে আন্দোলন হয়, বিশেষ করে একটু বামঘেঁষা যে আন্দোলনগুলি, দলীয় রাজনীতির ছত্রছায়ায় না থাকলেও— সেখানে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে সলিল চৌধুরীর গান। চারের দশকের শেষে যে গান লিখেছেন সলিল চৌধুরী, ‘হেই সামালো ধান হে’ বা ‘ও আলোর পথযাত্রী’— তা এখনও গাওয়া হয়।
এখানে কি গান রচনার পাশাপাশি নতুন সুরের কাঠামোও জরুরি হয়ে থাকছে?
সলিল চৌধুরীর সুরের যে নতুন গঠন, তার মূলত দুটো সূত্র তিনি উল্লেখ করেছেন ‘জীবন উজ্জীবন’-এ। সলিল ওঁর বাবার কর্মক্ষেত্র অসমের চা বাগান, কোদালিয়ার মামার বাড়ি ও কলকাতা— বিভিন্ন জায়গায় থেকেছেন ওঁর কৈশোর-যৌবন জুড়ে। ওঁর লেখা থেকেই জানা যায়, গ্রামে ওঁর মামার বাড়িতে থাকাকালীন পাশ্চাত্য সিমফনি সংগীতের সঙ্গে ওঁর পরিচয় হয় রেকর্ড মারফত। এর প্রভাব ওঁর ওপর ছিল। ওঁর স্কুল ফাইনাল তখনও শেষ হয়নি, কলকাতায় পড়তে এসেছিলেন। অর্থাভাবের মধ্যেই পড়াশোনা চলছিল। তখন একটা অদ্ভুত কাণ্ড হয়। সেসময় রামবাগানের দেহোপজীবিনীদের নাচের দল ছিল। এঁদের মধ্যে রাজকুমারী বলে এক নৃত্যশিল্পী খুব বিখ্যাত ছিলেন। এঁদের দলে উনি বাঁশি বাজিয়ে হিসেবে যোগ দেন। সলিল ছ’-সাত বছর বয়স থেকেই অপূর্ব বাঁশি বাজাতেন। কলকাতায় সুকিয়া স্ট্রিটে থাকতে এসে ‘মিলন পরিষদ’ বলে একটি অর্কেস্ট্রার দলের সঙ্গে ওঁর পরিচয় হয়। সেখানে নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র শিখতে শুরু করেন। বাঁশি বাজানোয় ওঁর পারদর্শিতার কথা সহজেই ছড়িয়ে পড়ে। পরে ছাত্র জীবনে রাজকুমারীর মতো নৃত্যশিল্পীদের দলের সঙ্গে বাঁশি বাজাতে শুরু করেন সলিল। তিন বছর বাজিয়েছিলেন, তাতে ওঁর কিছুটা অর্থের সুরাহাও হয়। কিন্তু সেখানে যেভাবে অর্কেস্ট্রেশন হচ্ছিল, তার সঙ্গে সলিল তাঁর রেকর্ডে শোনা পাশ্চাত্য সংগীতের অর্কেস্ট্রেশনের খুব একটা মিল পাচ্ছিলেন না। বিশেষত লক্ষ করেছিলেন হারমনির অভাব। ঐসব অর্কেস্ট্রাকে ওঁর মনে হচ্ছিল, ‘টু ডাইমেনশনাল’। একটা তৃতীয় মাত্রার অভাব বোধ করছিলেন। সেই শুরু হল সলিলের এক নিজস্ব সাংগীতিক স্ট্রাকচার সন্ধান, যা অনেকটা পূর্ণতা পেল চারের দশকের শেষে গিয়ে। তিনটি নৃত্যশিল্পীদের দলের সঙ্গে তিনি বাজিয়েছিলেন। শেষ যে দলটিতে বাজিয়েছেন, সেখানে বেশ কিছু প্রতিভাবান সংগীতকার ছিলেন। কিন্তু সেখানেও হারমনির ব্যবহার, এবং হারমনিকে স্ট্রাকচারাল এলিমেন্ট হিসেবে অর্কেস্ট্রেশনের মধ্যে নিয়ে আসার অভাব লক্ষ করছিলেন। সিমফনিতে যে সাংগীতিক সমাহার খুঁজে পেয়েছিলেন সলিল, তা এখানে ছিল না। তবে নাচের সঙ্গে বাজাতে গিয়ে সলিল পরীক্ষা নিরীক্ষার একটা সুযোগ পেলেন। সেখানে তাল আর লয় দিয়ে দেওয়া হত, সেই অনুযায়ী তাঁকে যন্ত্রবাদন সাজাতে হত। শীলা হালদারের মতো শিল্পীদের জন্য গোটা অর্কেস্ট্রা তিনি তৈরি করছেন, তাতে সেই তৃতীয় মাত্রাকে সলিল একটু হলেও খুঁজে পাচ্ছিলেন।
গীতিকার হিসেবে সলিলের প্রতিভার বিকাশ ঘটছিলই। বহু ক্ষেত্রেই কৃষক আন্দোলনের বিভিন্ন মিটিং বা কনফারেন্সে গিয়ে কয়েক ঘণ্টায় গান লিখে ফেলছেন। ফলে, গান উঠে আসছে আন্দোলনের ভেতর থেকে। শুধু সুরের দিকটা দেখলেও বলতে হয়, রবীন্দ্রনাথ থেকে লোকসংগীত, দেশজ রাগসংগীত— সবকিছুর প্রভাবই ছিল তাঁর ওপর, কিন্তু কোথাও ওই তৃতীয় মাত্রার সন্ধান সলিল করছিলেন হারমনি খোঁজার মধ্য দিয়েই।
আরও পড়ুন: গানে নারীকণ্ঠের নির্বাচন চিনিয়ে দেয় সলিল চৌধুরীর সাংগীতিক দৃষ্টিভঙ্গি! লিখছেন অর্ক মুখার্জি…

আইপিটিএ-র ভূমিকা এখানে কতটা জরুরি ছিল?
এমনিতে গণনাট্য সংঘ, বিশেষত, কমিউনিস্ট পার্টি-র বিরুদ্ধে ওঁর প্রচুর অভিযোগ ছিল। সেটা ওই সময়ের অনেকেরই রয়েছে। ওঁকে তো একরকম তাড়িয়েই দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু যেকথা উনি নিজেও স্বীকার করেছেন, তা হল গণনাট্য সংঘের বিবিধ কনফারেন্সের ভূমিকা। একথা আমি বাবাকেও (হেমাঙ্গ বিশ্বাস) বলতে শুনেছি। বম্বে কনফারেন্স থেকে তো আইপিটিএ-র শুরু। এছাড়াও লখনউ, এলাহাবাদ প্রভৃতি জায়গায় এই কনফারেন্সগুলো হত। সেখানে সারা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংগীতকাররা, গায়করা আসতেন। বিভিন্ন অঞ্চলের গান, খাঁটি লোকসংগীতও সেখানে পরিবেশন করা হত। সেসব তো রেকর্ডে শোনার কোনও সুযোগ তখন ছিল না। ক্যাসেটও আসেনি তখন। কিন্তু এই কনফারেন্সগুলোতে সেই সুযোগ ঘটত। গণনাট্য এই পরিসরটা তৈরি করে রেখেছিল ১৯৪৩ থেকে ’৫৩-’৫৪ পর্যন্ত। বাবা থেকে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, বিনয় রায় হয়ে মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ— বিবিধ জায়গার শিল্পীরা সেখানে গান গেয়েছেন। সলিল চৌধুরীর ওপর তার প্রভাবটা খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ধরা যাক, ‘গাঁয়ের বধূ’-র কথা, সেখানে খুব পরিষ্কার রবীন্দ্রনাথের ‘প্রাঙ্গণে মোর শিরীষশাখায়’-এর প্রভাব রয়েছে, শুরু থেকে। তারপরে সেখানে ঢুকছে অহমিয়া গানের সুর । কনফারেন্স থেকে এমন অনেককিছুই আহরণ করেছিলেন সলিল। কাজেই, সবটাই পশ্চিমি প্রভাব নয়, নানা কিছুর সিন্থেসিস হচ্ছিল গণনাট্যর মাধ্যমেই। অনেক প্রতিভাবান সংগীতশিল্পীই তখন উঠে এসেছেন, কিন্তু ওঁর মতো প্রতিভাবান আর কেউ-ই ছিলেন না।
আপনি লোকসংগীতের কথা উল্লেখ করলেন। অসমের চা বাগানের গান তো উনি শৈশবে শুনেইছেন। আরও বিবিধ লোকসংগীতের প্রভাব ওঁর গানে আছে। কিন্তু গণসংগীতে লোকসংগীতের ব্যবহার নিয়ে ওঁর সঙ্গে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের একটি বিখ্যাত তর্কও রয়েছে…
লোকগান ওঁর সুরে বারবার, অহরহ ঢুকেছে। বাউল, কীর্তন থেকে ভাটিয়ালি এসেছে, আর অসমের সুর তো এসেইছে। কিন্তু লোকগানকে মাধ্যম করে গণসংগীত তৈরির ইচ্ছে ওঁর খুব একটা ছিল না। ১৯৫৩ সালে গণনাট্যর বম্বে সম্মেলনে বাবার সঙ্গে এই নিয়ে ওঁর তর্কটা হয়। বাবার বক্তব্য ছিল, এই দেশের লোকের কাছে পৌঁছতে হলে লোকজ সুরকে মাধ্যম করা উচিত। এক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্কেস্ট্রেশনের বিপদ আছে। সলিলের তর্ক ছিল, তবে কি লোকোমোটিভের যুগে লোকে গরুর গাড়ি চড়বে? পরে ‘উজান গাঙ বাইয়া’ বইয়ে সংকলিত একটি লেখায় বাবা বলেছিলেন, এক্ষেত্রে দু’পক্ষেরই একটু গোঁড়ামি ছিল। এইরকম মেরুকরণ করে সংগীতসৃষ্টি হয় না। এটা খানিক বাবার আত্মসমালোচনাও ছিল, সলিল চৌধুরীকে সমর্থন করেই।

১৯৫৩ সালে গণনাট্যর বম্বে সম্মেলনে বাবার সঙ্গে এই নিয়ে ওঁর তর্কটা হয়। বাবার বক্তব্য ছিল, এই দেশের লোকের কাছে পৌঁছতে হলে লোকজ সুরকে মাধ্যম করা উচিত। এক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্কেস্ট্রেশনের বিপদ আছে। সলিলের তর্ক ছিল, তবে কি লোকোমোটিভের যুগে লোকে গরুর গাড়ি চড়বে?
সংগীতের বাইরে থেকেও যদি ভাবা যায়, সলিলের গান নিয়ে, সে ‘আয় বৃষ্টি ঝেঁপে’ হোক বা ‘গাঁয়ের বধূ’— পার্টির ভেতরে নানা আপত্তি উঠেছিল। কিন্তু সলিল তাঁর নিজস্ব অবস্থান কি তৈরি করেছিলেন এক্ষেত্রে?
পার্টিলাইন মেনেই শিল্পীদের চলতে হবে, এজাতীয় একটি ধারণা সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি থেকে শিখেছিলেন পার্টি নেতারা। এটা যে কত বড় ভুল বা অন্যায় ছিল, সেটা তখনকার নেতারা বোঝেননি। কাজেই সেই সময়ের বহু শিল্পীই এই অভিযোগ করেছেন বারবার। মৃণাল সেন যেদিন প্রথম ৪৬ ধর্মতলায়, অর্থাৎ গণনাট্য সংঘর দপ্তরে যান, সেদিন ওঁর হাতে জঁ পল সার্ত্রে-র একটি বই ছিল। সেটা দেখে পার্টির অনেকেই আপত্তি করে ওঠেন, যে এরকম প্রতিক্রিয়াশীল বুদ্ধিজীবীদের লেখা কেন পড়ছেন? মৃণাল পরে লিখেছেন, সেদিনই তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে, এঁদের সহযাত্রী হয়ে থাকবেন, কিন্তু সরাসরি সংঘ বা পার্টির সদস্য হবেন না, যা তিনি হনওনি কখনও। সলিল কেন ‘আয় বৃষ্টি ঝেঁপে’-তে ‘বিধি’-র উল্লেখ করেছেন, তাই নিয়ে আপত্তি তোলা হল। সলিল পরে খানিক বিরক্তি সহকারেই ‘জীবন উজ্জীবন’-এ লিখেছেন, আমরা যখন হায় বিধি বা হায় আল্লা বলি, তখন কেন বলি, তাও এরা বোঝে না।
সলিল তো মার্কসীয় তাত্ত্বিক ছিলেন না, তাই ওঁর পক্ষে নতুন কোনও ভাষ্য তৈরি করা খুব একটা সম্ভব ছিল না। কিন্তু ১৯৫১ সাল নাগাদ, তখন ওঁর বাবারও মৃত্যু হয়েছে, সেসময়েই উনি অনেকটা ডিসিলিউশনড হয়ে পড়ছেন, সেকথা উনি লিখেছেন। গণনাট্য সংঘ ছেড়ে সেসময় উনি বেরিয়ে আসছেন। গণনাট্যর সবচেয়ে সৃজনশীল পর্বটাও সেই ১৯৪৩ সাল থেকে এক দশক পর্যন্ত। পৃথিবী জুড়েই এই ধরনের বড় সাংস্কৃতিক আন্দোলনগুলো ওর বেশি টেকেনি। কিন্তু সেই আন্দোলনগুলো মানুষের নতুন সৃষ্টিশীলতায় অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে।

সলিল আইপিটিএ ছেড়ে বম্বে গেলেন, তারপর মূলধারায় সংগীত করলেন এত বছর। কিন্তু সলিল কখনওই আইপিটিএ-র রাজনৈতিক অবস্থান থেকে সরে যাননি। ওঁর বিভিন্ন গানে সেটা দেখা যায়। এই বিষয়টা নিয়ে যদি কিছু বলেন…
রাজনৈতিকতা, রাজনৈতিক বোধ বা নীতি তো আর পার্টি থেকে বেরিয়ে গেলেই চলে যায় না। পাঁচের দশকে সলিল যেমন গণনাট্য ছেড়েছেন, ঋত্বিকও বহিষ্কৃত হয়েছেন পার্টি থেকে। তাতে তো ঋত্বিকের রাজনীতি বদলে যায়নি কখনও। তবে একটা কথা সলিল বলছেন, বম্বের সংগীতকে চটুল, তরল বলেই তখনকার সংগীতবোদ্ধারা মনে করেছেন। কিন্তু সর্বভারতীয় আধুনিক গান তৈরি হচ্ছে বম্বের সংগীতশিল্পীদের হাত ধরেই। সংগীত-তাত্ত্বিকরা তা হয়তো সিরিয়াসলি নিচ্ছেন না। কিন্তু তাই বলে তাকে অশ্রদ্ধা করার কারণ নেই। এমনকী, লতা মঙ্গেশকরের জন্য যখন পরপর আধুনিক গান সলিল তৈরি করছেন, সেখানে কোনও বিচ্যুতি হচ্ছে বলে তিনি কখনওই মনে করেননি।
শতবর্ষ পেরিয়ে এসে সলিলের মূল্যায়ন নিয়ে কী মনে হয়?
সলিল চৌধুরীর সেই অর্থে সাংগীতিক মূল্যায়ন তো দেখিনি। কবীর সুমন করেছেন কিছু, সেটা করার মতো ট্রেনিং ওঁর রয়েছে। আর দেবু, মানে দেবজ্যোতি মিশ্র ওঁর সংগীত বিষয়ে কিছু মূল্যায়ন করেছে। এখন, বম্বের অধ্যায়টাই তো একেবারে আলাদা। গণসংগীতের অধ্যায়টা তো কলকাতা, চব্বিশ পরগণাতে অতিবাহিত মূলত। ড. সমীর গুপ্তরা সলিলের প্রথমদিকের কিছু গান, যেগুলো সলিল নিজেও ভুলে গিয়েছিলেন, সেগুলো উদ্ধার করেছিলেন। গৌতম চৌধুরীরা salilda.com -এ কিছু গান প্রকাশ করেছিলেন। সেই ১৯৪৬-এ ‘ঢেউ উঠছে কারা টুটছে’ বা ‘বিচারপতি তোমার বিচার’ থেকে শুরু হয়ে ‘দো বিঘা জমিন’, ‘মধুমতী’ হয়ে হৃষিকেশ মুখার্জির ‘আনন্দ’ ইত্যাদি ছবি হোক, বা লতা মঙ্গেশকরের পুজোর গান— এই গানগুলো নিয়ে একটা ইন্টারেস্টিং কথা অনেকেই বলেন যে, এই গানগুলোর দুটো চরণ শুনলেই চিনে নেওয়া যায় সলিল চৌধুরীর গান বলে। অন্য কোনও সংগীতকারের ক্ষেত্রে এমনটা ঘটে কি? গণনাট্যের কিছু গান শুনে একজন সুরকারের বদলে অন্যজনের কথা হয়তো ভাবা সম্ভব। কিন্তু সলিল চৌধুরীর এমন একটিও গান নেই।
(কথোপকথন থেকে অনুলিখিত)