সোমবারের সকালগুলোয় কিছুতেই আর চোখ খুলতে ইচ্ছে করত না স্বামীনাথনের। শনি আর রবিবারের আয়েশি স্বাধীনতার পর, কাজ আর শৃঙ্খলার চক্রে নিজেকে আরও একবার সঁপে দেওয়ার আগে মনটা তার বিদ্রোহ করে বসত। আর স্কুলের নাম শুনলেই তো তার অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে— সেই হলুদ রংচটা স্কুলবাড়ি, আগুনচোখো ক্লাসটিচার ভেদানয়নাগম আর সরু বেত হাতে হেডমাস্টার। জীবনের প্রথম উপন্যাস ‘স্বামী অ্যান্ড ফ্রেন্ডস’-এ (১৯৩৫) এমনই লিখেছিলেন রসিপুরম কৃষ্ণস্বামী আইয়ার নারায়ণস্বামী বা আরকে নারায়ণ। একইরকম অকারণ শাসনে ভরসাহারা অবস্থা হয়েছিল রাজুরও, ‘দ্য গাইড’ (১৯৫৮) উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র, যার বাবা আস্থা রেখেছিলেন এক পুরনো প্রবাদে— ‘না মারলে ছেলেপুলে মানুষ হয় না’— ‘আকাশ ফরসা হয়ে আসত যেই, বাবা আমার জন্য একেবারে তৈরি হয়ে বাড়ির সদরে রকের ওপর বসে থাকতেন হাতে একটা সরু কঞ্চি নিয়ে। আধুনিক শিশু মনস্তত্ত্বের ধার কেউ ধারত না সে-যুগে, লাঠি ছিল শিক্ষকের অপরিহার্য সরঞ্জাম।’ ফলে শেষপর্যন্ত স্কুলছুট হয়ে পড়ল রাজু। স্বামীনাথনই হোক বা রাজু, এদের জীবন একঘেয়েমি আর অবসাদে পূর্ণ, আর তার গোটাটা নেমে এসেছিল স্কুলশিক্ষার গতানুগতিকতার হাত ধরে।
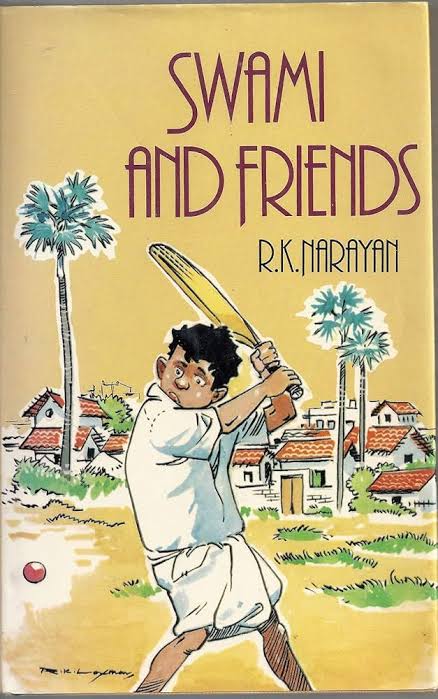
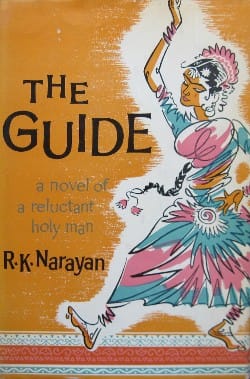
আর কে নারায়ণ নিজে যে কড়া ভিক্টোরীয় রীতিতে বাঁধা মিশিনারি স্কুলে পড়াশোনা করেছেন, সেখানে তাঁর অভিজ্ঞতা সুখের হয়নি কখনও। যে সর্বগ্রাসী পাঠপিপাসা তাঁর মধ্যে ছিল, গতে-বাঁধা পাঠ্যক্রমে পড়াশোনার প্রতি আকর্ষণ সেখানে এতটাই ফিকে হয়ে গিয়েছিল যে, পাঠ্যতালিকা উলটেও দেখতেন না তিনি। ফল যা হওয়ার তাই হল। উচ্চশিক্ষার একেবারে দোরগোড়ায় এসে প্রথম হোঁচটটা তিনি খেলেন। পাশ-ই করতে পারলেন না কলেজের প্রবেশিকা পরীক্ষায়। একবছর পর সে ক্ষতি পূরণ করে, ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে পড়তে কলেজে ভরতি হলেন বটে, কিন্তু স্নাতক স্তরের পরীক্ষা পাশ করতে গিয়ে আরও একটা বাড়তি বছর খুইয়ে বসলেন তিনি। বিরক্তি আর বিবমিষা এতদূর গিয়েছিল যে, স্নাতকোত্তর স্তরের জন্য তিনি নামই লেখালেন না, পাছে এই যান্ত্রিক শিক্ষাপদ্ধতির পেষণে সাহিত্যের প্রতি তাঁর যেটুকু আগ্রহ অবশিষ্ট আছে সেটুকুও নষ্ট হয়ে যায়!
১৯৭৪ সালে লেখা স্মৃতিকথা ‘মাই ডেইজ’ বইয়ে এর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আছে। লুথেরান মিশন স্কুলে যখন তিনি পড়তেন, সহপাঠী গুটিকয় অখ্রিস্টানদের মধ্যে একমাত্র তিনিই ছিলেন ব্রাহ্মণসন্তান। নারায়ণ লিখছেন, ‘ধর্মশিক্ষার ক্লাসে হিন্দু দেবতাদের জঘন্য আক্রমণ আর পৌত্তলিকতার প্রতি ঘৃণা ভরা হিংসা ছড়ানো ছাড়া আর কিছুই হত না, আর এই সবই ছিল যিশুকে মহিমান্বিত করে উপস্থাপন করার একটা কদর্য রাস্তা।’ এসময় থেকেই বিদেশি ভাবনাজারিত শিক্ষার প্রতি তাঁর একটা প্রগাঢ় বিকর্ষণ লক্ষ করা যায়। অকারণ অপ্রাসঙ্গিক বিষয়কে জোর করে পাঠ্যবস্তুর মধ্যে ঢোকানোর বিষয়টিও এখানে তিনি বারবার তুলে ধরেছেন। লিখছেন, স্কুলে গিয়ে শেখানো হল ‘এ ফর অ্যাপল’। অথচ দেশের যে প্রান্তে তাঁর বেড়ে ওঠা সেখানে তখনও কেউ আপেল কাকে বলে জানেই না। খুব ছোটবেলাতেই এই অদ্ভুত দিশাহীন শিক্ষাপদ্ধতি তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করে গিয়েছিল, যেখানে গোটা ক্লাস তো বটেই, এমনকী শিক্ষক নিজেও পর্যন্ত বুঝিয়ে উঠতেই পারছেন না যে, একটা আপেল ঠিক কেমন দেখতে হয়। নারায়ণ বলছেন, ‘ক্লাস বইয়ে গুঁজে দেওয়া এই পাশ্চাত্য সভ্যতার আমদানিকৃত অনুষঙ্গগুলোকে শিক্ষকের বোঝানোর সাধ্য অনুযায়ী আমরা যে যার মতো কল্পনা করে নিতাম।’ এই একটা জায়গায় নারায়ণ বারবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন ঠাকুমার কাছে, যিনি না থাকলে তাঁর এই অসম্পূর্ণ এবং অপর্যাপ্ত স্কুলশিক্ষার ফাঁকগুলো কোনওদিনই ভরাট করা সম্ভব হত না।’ স্কুলে নিয়মশৃঙ্খলার নামে অযথা কড়াকড়ির দিকটাকেও বারবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন তিনি, বলেছেন— ‘কোনও এক অজানা, অনামা, প্রাণহীন সংস্থা যেভাবে টেক্সটবুকগুলো চাপিয়ে দেয়, সম্বাৎসরিক পড়াশোনার বিন্দুমাত্র বিচার না করে, একটিমাত্র মেধানির্ণায়ক মূল্যায়নের ভিত্তিতে যেভাবে ছাত্রদের ভাল বা খারাপ বলে দাগিয়ে দেয় এর বিরুদ্ধতা আমি চিরকাল করেছি।’
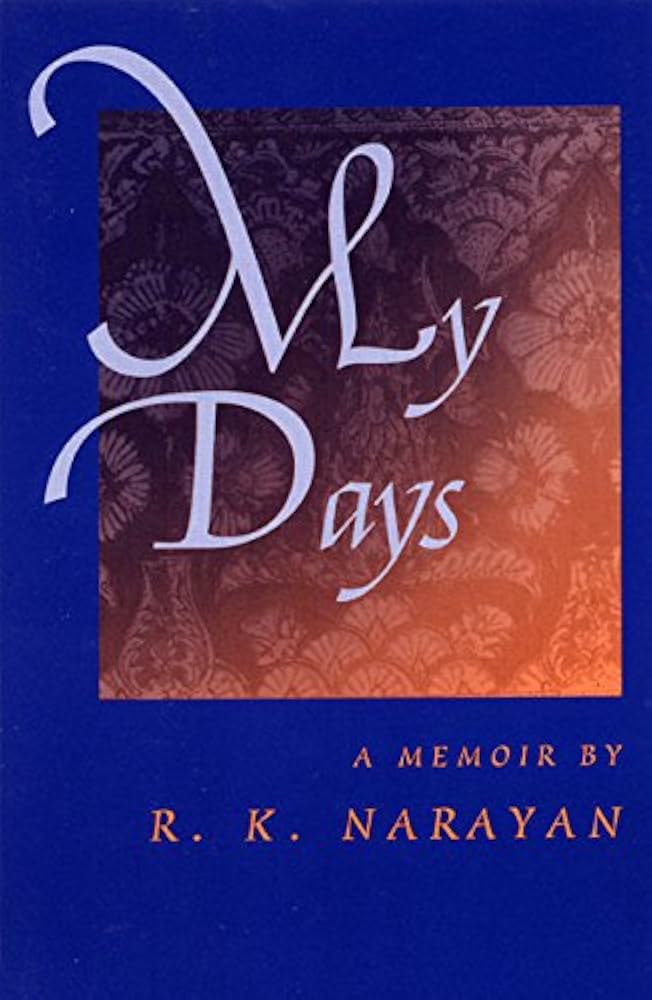
এই পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি তাঁর বিরক্তি আর অবিশ্বাসই ফুটে উঠেছে ‘স্বামী অ্যান্ড ফ্রেন্ডস’-এ। এক দশ বছরের বালকের চোখ দিয়ে নারায়ণ এখানে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার অসারতার দিকটিকে বারবার খুঁচিয়ে তুলেছেন। কিছু না বুঝে পড়া মুখস্থ করা আর উগরে দেওয়া কিছুতেই ভাল লাগত না স্বামীর, একমাত্র মনে ধরত ইতিহাসের ক্লাস, কারণ সেখানে কোনও চাপিয়ে দেওয়া বানানো কথা বলত না কেউ। পড়াশোনার ক্ষেত্রে স্বামীর ভাগ্যও নারায়ণের মতোই; খারাপ রেজাল্ট, শাস্তি, বকা খাওয়া আর অপমান হয়ে উঠল যার অ্যালবার্ট মিশন স্কুলের নিত্যসঙ্গী। নারায়ণের মতোই স্বামীকেও ধর্মশিক্ষার ক্লাসে হিন্দু বনাম খ্রিস্টান বিতর্কের মুখোমুখি হতে হয়। তবে যে প্রশ্ন নারায়ণ নিজে তাঁর শিক্ষকদের করে উঠতে পারেননি, এখন স্বামীর মুখে সেই কথাগুলোই হুবহু বসিয়ে দেন তিনি। ভারতের তৎকালীন ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলোতে, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান শিক্ষকবেষ্টিত পরিমণ্ডলে, সম্পূর্ণ অচেনা এবং জীবনের সঙ্গে সংযোগ-সম্পর্কহীন এক বিশ্রী পাঠক্রমের পাল্লায় পড়ে এক সাধারণ ভারতীয় ছাত্রের মনের যে কী দুরবস্থা হতে পারে, স্বামী নিজেই তার মূর্ত প্রমাণ। প্রতিবাদ মিছিলে পা মিলিয়ে স্বামীর কপালে জোটে শিক্ষকদের নির্দয় মার। স্কুলের ড্রিলে না গিয়ে ক্রিকেট খেলতে চাওয়ার অপরাধে শাস্তি পেতে হয় তাকে। এই বেতের শাসন থেকে পালাতে চেয়ে, এই শাস্তির ফাঁস থেকে বাঁচতে চেয়ে স্বামী একদিন মরিয়া ঔদ্ধত্যে তার প্রধানশিক্ষকের উদ্যত হাত থেকে বেত কেড়ে নেয়, শেষপর্যন্ত স্কুল যাওয়াই বন্ধ করে দেয় কিশোর ছেলেটি। স্বামীর এই বিদ্রোহ তৎকালীন স্কুলশিক্ষার মুখ থুবড়ে-পড়া ব্যর্থতারই প্রতিচ্ছবি।
স্বামীরই আর-এক অবিকল প্রতিরূপ হয়ে ওঠে তাঁর ‘ব্যাচেলর অফ আর্টস’ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র চন্দ্রন। অ্যালবার্ট মিশন কলেজের শেষদিনে এসে যার মনে হয়, এমন স্বাধীনতার স্বাদ সে আগে কখনও পায়নি, কয়েদ থেকে যেন মুক্তি ঘটল তার। জীবনের ষোলোটা বছর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভে ব্যয় করার পরেও চন্দ্রন বুঝে উঠতেই পারে না যে, জীবনে তার ঠিক কী করা উচিত। আত্মীয়স্বজন আর বন্ধুবান্ধবের হাজার রকম উপদেশ বাতলে দেওয়ার ফাঁদে পড়ে বিভ্রান্ত হয়, হাঁসফাঁস করতে থাকে জালে ধরা মাছের মতো। নিজের আত্মজীবনীতেও তিনি বলেছেন, ‘১৯৩০ সালে স্নাতক পাস করে শেষপর্যন্ত বিলম্বিত ডিগ্রিটা যখন আদায় করলাম সে-বছরটা ভরে রইল অনিশ্চয়তার ধোঁয়াশায়।
শুধু ছাত্র হিসেবে নয়, শিক্ষক হিসেবেও তাঁর ব্যর্থ প্রচেষ্টার কথা রয়ে গেছে ১৯৪৫ সালে প্রকাশিত তাঁর উপন্যাস ‘দ্য ইংলিশ টিচার’-এ। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র কৃষ্ণ ইংরেজি পড়ায় মালগুড়ির অ্যালবার্ট মিশন কলেজে। এককালে এখান থেকেই পড়াশোনা করে বেরিয়েছিল সে, আজ শিক্ষক হয়ে ফিরে এসেও দেখে, কিছুই বদলায়নি। তার মনে হয় এই বদ্ধ পাঁকের মতো জায়গায় পচতে থাকলে তার ব্যক্তিগত বা পেশাগত কোনও উত্তরণই কোনওদিন সম্ভব নয়। সে যন্ত্রের মতো ক্লাসে যায়, বিন্দুমাত্র কোনও আনন্দ বা তৃপ্তি ছাড়াই ক্লাসে গড়গড় করে পুতুলের মতো পড়াতে থাকে প্রতিদিন সকালে উঠে ক্লাসে যা পড়াতে হবে তাতে চোখ বোলায় বটে, কিন্তু পরীক্ষায় পাস করাবার জন্য তাকে যে পরিমাণ শক্তিক্ষয় করতে হয় অনিচ্ছুক ছাত্রদের জন্য, তাতে তার নিজেরই যাবতীয় আশা, আকাঙ্ক্ষা এবং স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যায়। নারায়ণ এখানে কড়া সমালোচক— ‘I am up against the system, the whole method and the approach of a system of education which makes us morons, cultural morons, but efficient clerks for your entire business and administration of office source.”
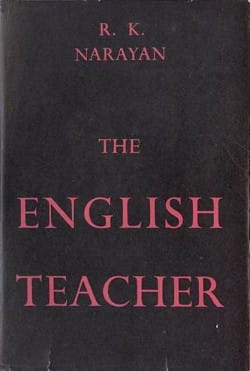
প্রায় এই একই রকমের ঘটনা নিয়েই তিনি লেখেন ‘দ্য ওয়ার্ল্ড অফ নাগরাজ’ উপন্যাসটি। স্বামী বা চন্দ্রন যদি হয়ে থাকে পাশ্চাত্য শিক্ষাপদ্ধতি ঘৃণাভরে দূরে সরিয়ে দিয়ে বিদ্রোহ-করা সব চরিত্র, তবে নাগরাজ হল পাশ্চাত্য শিক্ষাপদ্ধতি আত্তীকরণ করে সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত আর অর্ধজারিত হয়ে গড়ে-ওঠার এক বিপরীতমুখী নমুনা। কোনও বিষয় সম্পর্কেই পূর্ণ দক্ষতা তার তৈরি হয়নি। যন্ত্রের মতো খবরের কাগজ পড়ে সে, পড়ে কিন্তু কিছুই বোঝে না। ইংরেজি ভাষার প্রতি প্রচ্ছন্ন শ্রদ্ধা আর গর্ববোধ তার আছে বটে, কিন্তু সে শিক্ষা দিয়ে পরীক্ষায় পাস করা ছাড়া আর কিছুই করে উঠতে পারে না সে। সারাজীবন সংস্কৃতকে ঘেন্না করে বড়ো হয়ে ওঠা নাগরাজ পরবর্তীকালে নিজের স্বপ্নের উপন্যাসের বিষয় হিসেবে বেছে নেয় নারদের কাহিনি, কিন্তু পড়াশোনায় কোনওদিনই গভীরতা না থাকায়, উপন্যাসটি লিখতে গিয়েও পদে-পদে আটকে যায়। তার শেকসপিয়র পড়া যেন শুধুই কয়েকটা উদ্ধৃতি মুখস্থ করে বাঁধা বুলি আওড়ানোতেই শেষ। ক্রমশ তার প্রতিস্পর্ধী চরিত্র হয়ে ওঠে তার ভাই গোপু। নাগরাজের থেকে পড়াশোনায় হাজার গুণে বেশি ভাল হয়েও এই গোলকধাঁধার শিক্ষাকে জীবন থেকে অস্বীকার করতে চেয়ে গোপু বেছে নেয় তার বংশানুক্রমিক পরম্পরা মেনে কৃষিকাজ আর মাটির কাছাকাছি থাকার অবকাশ। আধুনিক ভারতের এক আদর্শ শিক্ষিত যুবকের প্রতিনিধি হয়ে ওঠে গোপু।
এই পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি তাঁর বিরক্তি আর অবিশ্বাসই ফুটে উঠেছে ‘স্বামী অ্যান্ড ফ্রেন্ডস’-এ। এক দশ বছরের বালকের চোখ দিয়ে নারায়ণ এখানে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার অসারতার দিকটিকে বারবার খুঁচিয়ে তুলেছেন। কিছু না বুঝে পড়া মুখস্থ করা আর উগরে দেওয়া কিছুতেই ভাল লাগত না স্বামীর, একমাত্র মনে ধরত ইতিহাসের ক্লাস, কারণ সেখানে কোনও চাপিয়ে দেওয়া বানানো কথা বলত না কেউ।
‘দ্য ওয়ার্ল্ড অফ নাগরাজ’ উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৯০ সালে। ঠিক তার আগের বছরে আর কে নারায়ণের লেখকজীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আর-একটি দায়িত্বভার। ১৯৮৯ সালে তিরাশি বছর বয়সে ‘নমিনেটেড মেম্বার’ হিসেবে আর কে নারায়ণ হাজির হলেন রাজ্যসভায়। ২৭ ফেব্রুয়ারি রাজ্যসভার দেড়শোতম অধিবেশনে, নাজমা হেপতুল্লা-র সভাপতিত্বে, রাজ্যসভায় নিজের প্রথম বক্তৃতা দিতে উঠলেন তিনি। সেদিন নারায়ণ যেন হয়ে উঠলেন এতদিনের মুখ লুকিয়ে-বেড়ানো সমস্ত স্বামীনাথন আর রাজুদের প্রতিনিধি। প্রথমেই আক্রমণ করলেন পাঠক্রমের অহেতুক চাপকে, বললেন, ব্যাগের বীভৎস ভারে বেঁকে যাচ্ছে শিক্ষার্থীদের মেরুদণ্ড— তাদের দেখলে মনে হয় যেন ঝুঁকে পড়া এক শিম্পাঞ্জি হেঁটে চলেছে। প্রশ্ন তুললেন আমাদের পরিবেশ ও আবহাওয়ার কথা না ভেবে চাপিয়ে দেওয়া পাশ্চাত্য কায়দার ইউনিফর্মের উপযোগিতা নিয়ে। প্রশ্ন তুললেন পরীক্ষাব্যবস্থা এবং শুধু পরীক্ষা পাশের জন্য যান্ত্রিক কোচিং-ক্লাস আর তার হোমওয়ার্কের চাপ নিয়েও। শেষে রাজ্যসভার সদস্যদের উদ্দেশ্যে বললেন, ‘Members to think over and device a remedy by changing the whole educational system and outlook so that childhood had a chance to bloom rather than wilt in the dreadful process of learning.’
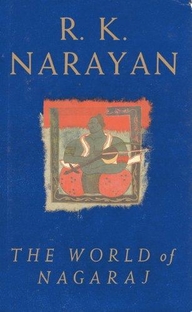
এই বক্তৃতা আলোড়ন তুলল রাজ্যসভার অন্যান্য সদস্যদের মধ্যেও, যাঁদের মধ্যে ছিলেন আর-এক বিখ্যাত লেখক অমৃতা প্রীতম। তিনিও সোচ্চার হলেন পার্লামেন্টে আর কে নারায়ণকে সমর্থন করে। তিনি বললেন, ‘এই কথা ছাড়াও আমি একটি বিশেষ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। একটিমাত্র বার্ষিক পরীক্ষা দিয়ে ছাত্রদের ভাগ্য নির্ধারণের এই যে প্রথা, তা ক্রমশ অন্য দেশে বন্ধ হয়ে গেছে, অচিরেই আমাদের দেশেও তা বন্ধ হওয়া উচিত। সারা বছর পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে একজন শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হবে কিনা সে বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত। বাচ্চোঁ কী সাইকী কো হর তহরা কী জবরদস্তী সে, ইম্তহানোঁ কে খউফ সে অউর চান্স কী গেম সে বচানা হোগা এক সেহতযোগ্য কৌম কী তৈয়ারী কে লিয়ে।’
এই বক্তৃতার অভিঘাতের ফলেই ১৯৯২ সালের মার্চ মাসে তৈরি হল ন্যাশনাল অ্যাডভাইসরি কমিটি, ভারত সরকারের মানবসম্পদ দপ্তরের অধীনে। কমিটির চেয়ারম্যান হলেন পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক যশ পাল। ১৯৯৩ সালে এই যশ পাল কমিটি এক যুগান্তকারী রিপোর্ট পেশ করে, যার নাম ‘ভারমুক্ত শিখন’ (Learning Without Burden)। ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার ধারায় এই রিপোর্টটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই রিপোর্ট নারায়ণের কথাকেই স্বীকৃতি দিল, কিন্তু একেবারে ভোল বদলে দিতে পারল না। তারপর কেটে গেছে আরও তিরিশ বছর। একটু একটু করে আমরা এগিয়েছি আর কে নারায়ণের পথে।
আগেই বলেছি তাঁর আস্থা ছিল শিক্ষার ক্ষেত্রে দেশীয় শিক্ষার পরম্পরার ওপর, তাই তাঁর শিক্ষার যাবতীয় কৃতিত্ব যেন তিনি দিতে চান তাঁর ঠাকুমাকে। ঠাকুমার মুখে শোনা নানা অভিজ্ঞতাই ছিল তাঁর বুনিয়াদি শিক্ষার প্রধান ভিত্তি। কোনও বই বা ব্যাগের ভার ছিল না সেখানে, ছিল না কোনোও ইউ ফর্মের বালাই। জীবনের একেবারে শেষপ্রান্তে এসে ঠাকুমাকে নিয়ে লিখলেন “গ্র্যান্ডমাদার’স টেল”। উপন্যাসটি প্রকাশিত হওয়ার পর তাঁর পরিকল্পনা ছিল দাদু-নাতনির সম্পর্ক নিয়ে লিখবেন আরও-একটি উপন্যাস। হয়তো নিজের জীবনে তাঁর ঠাকুমার যা ভূমিকা, তাকেই আর-একবার ফিরে দেখতে চেয়েছিলেন নাতনি ভুবনেশ্বরীর সঙ্গে তাঁর আশ্চর্য অন্তরের টান দিয়ে। এ-উপন্যাস যদিও আর লেখার সুযোগ মেলেনি। তার আগেই তিনি চলে গেলেন পৃথিবী থেকে। পরিকল্পনাটুকু পড়ে রইল শুধু, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে শিক্ষা আর ঐতিহ্য পরিবহনের ধারায় যে বৃত্তটি নিটোল হয়ে উঠতে পারত, তা শেষ হল না আর।




