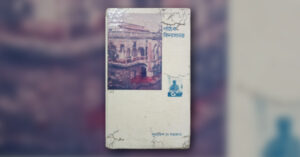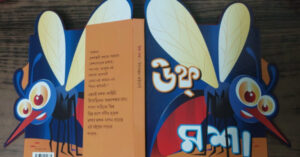প্রতারক রক্স
যে লোকটা ক্রিমিনাল, তার কিছুটা সাহিত্যপ্রতিভা থাকতেই হয়। খুনের পর যদি সে ধরা পড়ে, আর পুলিশ জিজ্ঞেস করে ‘কাল সন্ধে ছটার সময় তুমি কী করছিলে’, সে তো আর বলবে না, ‘অঃ, ওই সময় চাঁদনি চকের গলিতে অম্লান লাহিড়ীর গলার নলি কাটছিলাম’, বরং বলবে ‘মনটা দুঃখু করছিল, আলিপুরে ভাটিখানায় একলা বসে মদ খাচ্ছিলাম’। মানে, তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনে একটা গল্প বানাতেই হবে। এবং সেটা খুব ছোট গল্পও নয়, কারণ প্রশ্নের পর প্রশ্নে এদিক-ওদিক প্রচুর মিথ্যে বুনতে হবে, যা প্রথম মিথ্যেটার সঙ্গে সংলগ্ন ও সমঞ্জস। এটাই গল্পকার বা ঔপন্যাসিকের কাজ। অপু বলে কেউ নেই, তবু তাকে গড়ে, তাকে কেন্দ্র করে আখ্যান লিখতে হবে, দুর্গা বলে কেউ নেই, তবু তাকে অসুখে মেরে ফেলতে হবে। সে-সব মিথ্যে যত বিশ্বাসযোগ্য হবে, বিভূতিভূষণের পসার তত বাড়বে। ক্রিমিনাল মিথ্যে বানিয়ে সাধারণত পার পায় না, কিন্তু অপরাধের দক্ষতার সঙ্গে তাকে যে গল্প তৈরির অনুশীলনও করতে হয়, এবং অনেক ক্ষেত্রেই সেই গল্পটা আগে ভেবে তবেই ঘুঁটি সাজাতে হয়— তাতে বোঝা যায়, বড় অপরাধীর মধ্যে কাহিনি-সৃষ্টির প্রতিভা আবশ্যক।
গাজিয়াবাদে গত ন’বছর ধরে একটা লোক সকলকে বোকা বানিয়ে নিজেকে বিভিন্ন দেশের দূতাবাস-প্রধান বলে পরিচয় দিচ্ছিল, সে ধরা পড়েছে। কিন্তু চতুর্দিকে তার কল্পনাশক্তির প্রশস্তি চলেছে। সে নিজেকে বাতলে নিয়েছিল ‘ওয়েস্টার্কটিকা’-র ব্যারন, আবার ‘সিবর্গা’-র কী যেন একটা বিশাল মাতব্বর, ‘লাডোনিয়া’ আর ‘পলোভিয়া’-রও কীসব! ওয়েস্টার্কটিকা বা লাডোনিয়া বা সিবর্গা-র অস্তিত্ব সত্যিই আছে, এগুলোকে বলে মাইক্রো-নেশন, মানে কেউ না কেউ আচমকা একটা জায়গায় ‘এই রাষ্ট্রটা বানালাম’ ঘোষণা ক’রে, তার প্রধান হওয়ার দাবি করেন, কিন্তু অন্য কোনও রাষ্ট্রই এই দেশটাকে স্বীকার করে না। ইচ্ছে করলে সেই নতুন দেশের পতাকা বা সিলমোহর, এমনকী, সংবিধানও বানানো যায়, কাউকে রাজা বা রানি নির্বাচন করাও যেতে পারে, এমনকী, উৎসাহী লোককে নাগরিকত্বও দেওয়া যায়। কিন্তু যেহেতু এর কোনও স্বীকৃতি নেই, শুধু কয়েকটা লোকের খেয়ালখুশির মজা আছে, তাই ওটা খেলার স্তরেই থাকে। কতকটা যেন, আমি আমার বাগানের পশ্চিম-কোণটার নাম দিলাম হালুমগঞ্জ আর জবাগাছকে ঠাউরে নিলাম তার প্রহরী। সে রোজ মাথা ঝুঁকিয়ে আমার কাছে রিপোর্ট করে, কাল কাঠবেড়ালি বহুত হুজ্জুত করেছে স্যার, কিংবা পরশু অঝোর বৃষ্টি কী দুর্দশা করেছে দেখে যান হুজৌর! আমি ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী বা চিরকালের শাহেনশা হিসেবে যথাযথ মাথা নাড়ি।
গাজিয়াবাদের এই অপরাধীর (নাম, হর্ষবর্ধন জৈন) অভিনবত্ব হল, প্রথমত সে জানত মাইক্রো-নেশন কাকে বলে (যা আমাদের মধ্যে ঝানু কুইজ-মাস্টার ছাড়া কেউ জানে না) এবং খুঁটে খুঁটে তাদের কয়েকটার নাম বের করেছিল। আবার ভেবেচিন্তে একটা নতুন দেশের নাম বানিয়েওছিল (পলোভিয়া), মানে তার মগজের ইঞ্জিন ভালই হর্সপাওয়ারে চলে। তার পেল্লায় বাড়ির সামনে চারটে গাড়ি দাঁড়িয়ে, তাদের কয়েকটার গায়ে রাষ্ট্রদূতের গাড়ির মতোই নীল রঙের প্লেট (মার্সিডিসের নম্বর প্লেটের ওপরদিকে লেখা: ‘অনরারি কনসাল ব্যারন ওয়েস্টার্কটিকা’), সব মিলিয়ে সে গড়ে তুলেছিল এক জলদগম্ভীর সাম্রাজ্য, যেখানে হোমরাচোমরা জ্যোতি তার মাথার পিছনে অন্যরাই ফোটোশপ করে নেয়। তার বাড়িময় অনেক দেশের পতাকা লাগানো। এখন তল্লাশি চালিয়ে প্রচুর জাল স্ট্যাম্প, পাসপোর্ট উদ্ধার হয়েছে, অনেক বিদেশি মুদ্রাও, আবার সঙ্গে জাল প্রেস কার্ডও পাওয়া গেছে, মানে সাংবাদিক সাজতেও লোকটার অনীহা ছিল না। আসলে এসবের আড়ালে সে চালাত টাকা লেনদেনের একটা বেআইনি কাণ্ড, আবার চাকরি দেওয়ার জাল একটা চক্রও। কিন্তু সেসব তথ্যে না গিয়ে আমরা তার পরিকল্পনার কদর করব।
যে কোনও লোককেই জোচ্চুরি চালাতে গেলে গল্প তৈরি করতে হয়, ছোট্ট বাচ্চাও বলে, মা আমি জানলার কাচ ভাঙিনি, ম্যাওপুষি ভেঙেছে, আমি তখন বারান্দায় বসে স্কেচপেনে নারকোল গাছ আঁকছিলাম, এই দেখো। কিন্তু হর্ষবর্ধনের তৈরি কাহিনিটা দুরন্ত, কারণ তা ‘মারি তো গন্ডার’ গোত্রীয়। একটা লোক খুব বড় আমলা, বা পুলিশের কর্তা, কিংবা মন্ত্রীর সেক্রেটারি সাজলেই তার প্রভূত ছলাকলা ও আত্মবিশ্বাস দরকার, তাকেও কাগজ সই সিলমোহর জাল করতে হয়, কিন্তু হর্ষমশাই ভেবে পেয়েছে, এসব চুনোপুঁটিত্ব সবিশেষ বিসর্জন দিয়ে, একেবারে একটা গোটা দেশের ব্যারন হয়ে ওঠা যাক। আরও একটা দেশের তমুক হয়েছি বলে গাড়িতে লিখে ফেলতেই বা আটকাচ্ছে কে। আমরা ফট করে ভাবব, ধাপ্পাটা যত প্রকাণ্ড হবে, অবাস্তব হবে, সেটা ধরা তত সহজ। কিন্তু ব্যাপারটা উল্টো। হর্ষবর্ধন বুঝেছে, মানুষ যখন নিজের লকেটে দুর্দান্ত অভিজাত কোনও তকমা লাগায়, তখন অন্য লোকেরা তাকে সন্দেহ করার বদলে, সত্য যাচাই করার বদলে, ঝুঁকে সেলাম জানাতে অধিক ব্যস্ত হয়ে পড়ে। লোক-ঠকানোটা যত ডাকাবুকো স্তরে হবে, মিথ্যেটাকে যত ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে মেগা-জবরদস্ত অবয়ব দেওয়া হবে, ততই ধরা পড়ার সম্ভাবনা কমবে, কারণ সকলেই ভাববে, ধুর, অ্যাদ্দূর বাড়িয়ে বলার আস্পদ্দা আবার কারও হতে পারে? তাই ঠকাবেই যদি, একেবারে উদ্দাম স্তরে গুলবাজিটা নিয়ে যাও, ‘আমি বজবজের স্টেশন মাস্টার’ না বলে, ‘আমি কোস্টা রিকা-র ভাইস প্রেসিডেন্ট’ বলাটা সবসময় বেশি নিরাপদ।
যে কোনও লোককেই জোচ্চুরি চালাতে গেলে গল্প তৈরি করতে হয়, ছোট্ট বাচ্চাও বলে, মা আমি জানলার কাচ ভাঙিনি, ম্যাওপুষি ভেঙেছে, আমি তখন বারান্দায় বসে স্কেচপেনে নারকোল গাছ আঁকছিলাম, এই দেখো। কিন্তু হর্ষবর্ধনের তৈরি কাহিনিটা দুরন্ত, কারণ তা ‘মারি তো গন্ডার’ গোত্রীয়। একটা লোক খুব বড় আমলা, বা পুলিশের কর্তা, কিংবা মন্ত্রীর সেক্রেটারি সাজলেই তার প্রভূত ছলাকলা ও আত্মবিশ্বাস দরকার, তাকেও কাগজ সই সিলমোহর জাল করতে হয়, কিন্তু হর্ষমশাই ভেবে পেয়েছে, এসব চুনোপুঁটিত্ব সবিশেষ বিসর্জন দিয়ে, একেবারে একটা গোটা দেশের ব্যারন হয়ে ওঠা যাক।
সে আরও একটা ব্যাপার বুঝেছে। এই দেশের লোকের, কর্তৃপক্ষের সাড়া পাওয়ামাত্র পেট-গুড়গুড় শুরু হয়ে যায়। বস লিফ্টে উঠেছেন শুনেই সবাই সিকনির রুমাল পকেটে ঢুকিয়ে, তাসখেলা মিনিমাইজ ক’রে, গলা-খাঁকারি দিয়ে সিধে-পিঠে বসে, যৌবনবতী কলিগের পানে পারতপক্ষে তাকায় না। আমরা থাকি গণতন্ত্রে, কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই প্রজা-প্রজা নতমাথা আত্মা পোঁতা রয়েছে। রাজামশাইও নয়, তাঁর খাস খানসামার সামনে পড়লেই আমরা কুঁকড়ে দাসানুদাস। যে কোনও লোক যদি বিশাল একটা গাড়ি থেকে নামে, যে-গাড়ির সামনে আবার একটা রংচঙে পতাকা উড়ছে, আর তারপরেই তেড়ে দাবড়ানি দেয় (অ্যাই, পার্কিং-এ নাকি পরশু কীসব গন্ডগোল হয়েছিল!) আমাদের মেরুদণ্ডে ৮৮০ ভোল্ট। নিতম্ব থরথরিয়ে কাঁদে, এই বুঝি সুলতান ৭০ ঘা জুতো লাগালেন। সমগ্র জীবন ধরেই হেডমাস্টার, বাড়িওলা, বড়লোক মেজোজ্যাঠা, সরকারি দফতরের দু্র্মুখ কেরানি, বেসরকারি অফিসের উচ্চ-পান্ডা, থানার পুলিশ, ইনকাম-ট্যাক্সের অফিসার ইয়াব্বড় লাল-লাল চোখে যেই না আমাদের দিকে তাকিয়েছেন, আমাদের প্যান্টে হিসি হয়ে গেছে। এঁরা আমাদের যথেচ্ছ হ্যারাস করেছেন, ব়্যাগ করেছেন, আর আমরা হাতজোড় করে ভেবেছি, আর তো কদিন, মাত্তর ক’বছর, তারপরেই শান্তি-পারাবার, আমার শৃঙ্খলও নেই হারাবার, লে বাবা, সয়ে যা, নইলে আমারই ক্ষতি।
অবশ্য অফিসার অবধি যাওয়ার দরকার নেই, বহু নামীদামি সংস্থার দারোয়ান বা রিসেপশনিস্টও ভয়ানক দুর্ব্যবহার করেছে, ডাহা মিথ্যে কারণ দেখিয়ে ফেরত পাঠিয়েছে, ওপরে যেতে দেয়নি। আসলে প্রত্যেকেই নিজের লাথ-খাওয়া কালশিটেটার জ্বলুনি উশুল করে নিতে অন্যের গায়ে ক্ষমতার পাঁচনবাড়ি হানে, আমরাও হয়তো রোগা রিকশাওলাকে গাল দিয়ে ঝাল মেটাই। তাই চিত্রনাট্য খুব স্পষ্ট: কর্তা বা কর্ত্রী, স্যুট বা বুট, গট বা মট, লাখ টাকার ঘড়ি বা তেল মাখার কড়ি, রাঙা চোখ বা চাঙা ধমক দেখলেই আমাদের সত্তা আড়ষ্ট জড়োসড়ো আঁক্স, আমরা হাত কচলে দাঁত বের করে চকিত-চাটুকার। ওটা আমাদের ইতিহাসগত ট্রেনিং, আমাদের সামাজিক অভ্যাস। চালবাজ বা হামবড়া, উদ্ধত বা খেঁকুরে, সিধে কথায় ওই মুহূর্তে ক্ষমতাবান— উঁচু চেয়ারে বসা অন্যায়কারীকে যে চ্যালেঞ্জ করা যায়, তার অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়, একথা আমাদের মাথায় ভুলেও চিড়িক মারে না। যে লোকটা বুক ফুলিয়ে হাত দুলিয়ে ‘এ আমার জমি, এখানে আমার চোদ্দো-পুরুষ বিড়ি খেয়েছেন ও পা দিয়ে মাটিতে ঘষে নিভিয়েছেন’ ভঙ্গিমায় হাঁটে তার গলায় যথাযথ আই-ডি কার্ড ঝুলছে কি না যাচাই করার সাহস দারোয়ানের হয় না, যে লোকটা প্রথমেই গলা চড়িয়ে টেবিলে চাপড় দিয়ে বলে ‘বাতিল!’ তাকে ভুল ধরিয়ে দেওয়ার ধক কনিষ্ঠ কেরানির গজায় না, আইসিইউ-এর রূঢ় ডাক্তার হনহনিয়ে লিফ্টে ওঠার সময় রোগীর পরিজনের জিভ সুড়সুড়োয় তবু কিছুতে উচ্চারণ করতে পারে না: ওর কন্ডিশন এখন কী, তা আমাকে বিশদ বোঝাতে আপনি বাধ্য। আমরা চরণ-চাটা লেংচে-হাঁটা পিত্ত-চাটার দল, সিগ্রেট খেলে নিচে চল।
আমাদের এই জন্মগত কেন্নোবাজিটা হর্ষবর্ধন এমন নাড়ি টিপে বুঝে ফেলেছে, সে অ্যাক্কেরে টপ-লেভেল কর্তা সেজে ন’বচ্ছর কাটিয়ে দিল। আরও হয়তো কত্ত পাবলিক ঘুরে বেড়াচ্ছে এদিক-সেদিক, ‘আমি মস্তান তুই সস্তা’ বডি-ল্যাঙ্গোয়েজ আছড়ে হুমহাম, আর আমাদের ঈর্ষা থেকে সড়সড়ে স্যালুট কত্তই বাজে খরচ হয়ে চলেছে, কে-ই বা জানে। যাক, কারও না কারও হর্ষ বর্ধন হচ্ছে, এ-ই কি কল্যাণবিশ্বে যথেষ্ট নহে?