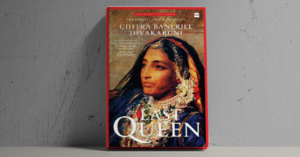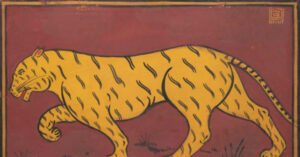১৯৬০-এ পৃথিবী জুড়ে এক অত্যাশ্চর্য জোয়ার আসে, সে-জোয়ার প্রাতিষ্ঠানিক ধ্যানধারণা, চর্চার উল্টোদিক থেকে আসা অন্য-ভাবনা, ভিন্ন-চর্চার। এই সময়, ১৯৬০, কাউন্টার-কালচারের সময় হিসেবে চিহ্নিত। এখনই শুরু হচ্ছে সিভিল রাইটস মুভমেন্ট, একটি-একটি করে আফ্রিকার ঔপনিবেশিক দেশগুলি নিজেদের স্বাতন্ত্র্য পাচ্ছে। ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রতিবাদে ‘বিগ ব্রাদার’-এর বিরুদ্ধে পথে নামছে ছেলেমেয়েরা। পশ্চিমবাংলার হাওয়ায় তখন রক্ত চলকানো সব স্লোগান— ‘আমার নাম/ তোমার নাম/ ভিয়েতনাম/ ভিয়েতনাম’, ‘ভুলতে পারি বাপের নাম/ ভুলব না কো ভিয়েতনাম’। শুরু হচ্ছে হিপি মুভমেন্ট এবং উডস্টক। আবিষ্কার হচ্ছে বৈপ্লবিক জন্মপ্রতিরোধক পিল— সন্তান ধারণ করার সিদ্ধান্ত এখন শুধু যিনি সন্তান ধারন করবেন, তার হাতে, লিঙ্গ-বৈষম্যের লড়াইয়ের এক দারুণ মাইলস্টোন।
এর মধ্যেই ভারতের প্রথম মহিলা প্রধান মন্ত্রী, ইন্দিরা গান্ধী প্রতিষ্ঠা করলেন ‘ফিল্ম এন্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া’ (এফটিআইআই)। সিনেমা, যাকে কি না কোনও গুরুত্ব বা সম্মান দেওয়া হয়নি সাধারণ এবং শিক্ষিত সমাজে, যাকে নাকি আজও সিনেমা ‘লাইন’-এ ‘নেমেছে’ বলা হয় মাঝেমধ্যেই, সেই সিনেমার পঠনপাঠন, চর্চা ও কারিগরি শিক্ষার পুরোদস্তুর একটি ইনস্টিটিউশন। সবে স্বাধীন দেশের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক তো বটেই, একটি অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ, দূরদর্শী পদক্ষেপ। সময়টা তখন আলাদা ছিল। রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরা শুধুই নিজেদের আখের গোছানোর জন্য আর ‘ডেমোক্রেসির এইসি-তেইসি’ করার জন্য রাজনীতি করত না বোধহয় সবসময়, হয়তো কোথাও তাদের একটা দায় ছিল দেশটার প্রতি, ভোটের আগে যাদের কাছে হাত কচলে ভোট ভিক্ষে করতে যায় তাদের প্রতি— এভাবে দেশের ছালচামড়া উঠিয়ে তা দিয়ে ডুগডুগি বাজানর কালচার তখনও শুরু হয়নি, চূড়ান্ত শাসকের পদলেহনের কালচারও আরও একটু পরের গল্প।
আরও পড়়ুন : কাশ্মীর হামলার পর যারা ‘যুদ্ধ চাই’ বলে চিৎকার করছে, তারা কি আদৌ দেশপ্রেমিক? লিখছেন চন্দ্রিল ভট্টাচার্য…

সে-সময় একজন ঋত্বিককুমার ঘটক ছিলেন, কোনও নেতা মন্ত্রীকে রেয়াত করা যাঁর ধাতে ছিল না, আর এই পাঁড় মার্কসবাদী, পাঁড় মাতাল, জিনিয়াস ফিল্মমেকার লোকটিকে সম্মান করার এক কংগ্রেসি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন— মিসেস গান্ধী। ঋত্বিককে এফটিআইআই–এ নিয়ে এলেন ইন্দিরা, সবচেয়ে প্রতিষ্ঠান-বিরোধী শিল্পীকে সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি দিতে তিনি ভয় পেলেন না, কারণ তিনি জানতেন, এ-লোকটি সিনেমা বানানোর শিল্পে বিপ্লব আনতে পারেন আর সত্যিকারের শিল্প বা শিল্পী, আর যাই হোক, কোনওদিন তাঁবেদার হতে পারেন না। ঋত্বিক ঝড়ের মতো এফটিআইআই-এ ঢুকলেন। আজও এফটিআইআই-এ গেলে সেই ঝড়ের দাপট টের পাওয়া যায়। আজও সুভাষ ঘাই, এত কিছু করার পরেও, কলারটা তোলেন ঋত্বিক-এর ছাত্র হিসেবে। আজও উইজডম ট্রি-তে দুলতে থাকে প্ল্যাকার্ড— ঋত্বিক ওয়াজ হিয়ার— ঋত্বিক এখানে ছিলেন।
ইদানীং পুনে ইনস্টিটিউটের ছবিগুলি রেস্টোর করছে সরকার। এত বছরের খনি— অসামান্য সব কাজ; আর তাছাড়া যাঁদের আমরা পরে কৃতী হিসেবে দেখছি, স্টার বা লেজেন্ড হিসেবে চিনেছি— তাঁদের প্রথম কাজ, ছাত্রাবস্থার কাজ দেখার মজাই আলাদা। এই খনির ভেতর থেকেই উঠে এসেছে মণির মতো ঘটকের সেই সময়ের তৈরি একটি ছোট ছবি। ১৯৬৫-র ছবি, স্টুডেন্ট প্রোজেক্ট, নাম ‘ফিয়ার’, বা ‘ভয়’। এফটিআইআই-এর অভিনয় শিক্ষা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে তৈরি এই ছবি। সাদা-কালো মুখগুলি দেখতে দেখতে মনে হয়, সিনেমা সেই মাধ্যম, যা মানুষকে বুড়ো হতে দেয় না, মরে যেতে দেয় না। জীবন ফুরিয়ে যায়, কিন্তু সিনেমার পর্দা জলজ্যান্ত রয়ে যায় যতদিন, ততদিন।
ছবিটিতে বেশ কিছু মানুষ, নানারকম মানুষ, মাটির নিচে একটি শেলটারে লুকিয়ে রয়েছেন। খবর এসেছে, যে কোনও মুহূর্তে হাইড্রোজেন বোমা এসে ধ্বংস করে দিতে পারে তাদের দেশ। ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ভয়ে, শেষ হয়ে যাওয়ার ভয়ে তারা মাটির তলার একটি সুরক্ষিত চেম্বারে এসে জড়ো হয়েছেন। সুরক্ষিত হলেও এখানে আলো ঢোকে না, হাওয়া খেলে না; এখানে একসঙ্গে অনেকগুলি মানুষ আসলে একা একা ভয়ে ভয়ে মরে মরে বাঁচে, প্রাণরক্ষাই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু কেমন এই বেঁচে থাকা, কেমন এই জীবনযাপন, যেখানে ভয় তাদের ঘিরে রেখেছে সারাক্ষণ? কী-ই বা মানে ভয়ে ভয়ে এই বেঁচে থাকার? ছবিটিতে এক গর্ভিনী নারী ও তার স্বামী অপেক্ষা করছে তাদের সন্তানের ভূমিষ্ঠ হওয়ার। আছে এক মা, যে ঢুকে পড়েছে এই সুরক্ষাগহ্বরে, কিন্তু তার ছোট ছেলেটি রয়ে গেছে মাটির ওপর। মা পাগলের মতো বেরিয়ে যেতে চায় এই চেম্বার থেকে, তার ছেলেটিকে খুঁজে বের করতে আর তাকে প্রত্যেকবার আঁটকায় এক শক্ত চোয়ালের যুবক, যে কথা বলে না, হাসে না, কাঁদে না। তবু কান্নায় ভেঙে পড়া এই তরুণী মা-র মাথা কোলে নিয়ে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দেয় তার মাথায়। এই নির্বাক চরিত্রে অভিনয় করেছেন পরবর্তীকালের কিংবদন্তি কৌতুকাভিনেতা আসরানি। অথচ ঋত্বিক তাঁকে ব্যবহার করেছেন সবচেয়ে গম্ভীর, সবচেয়ে তীব্র একটি চরিত্রে।
কেন কিছু কিছু চিত্র-নির্মাতা ‘মাস্টার’ বা ‘অত্যুর’? কেন অনেক সময়েই রমরমে হিট দেওয়া, বাজার-কাঁপানো চিত্র-নির্মাতার থাকা বা না-থাকায় কিছু যায় আসে না ‘সিনেমা’-র? একটি মোক্ষম কারণ বোধহয়, একজন মায়েস্ত্রো কোনওদিন সিনেমায় জ্ঞান দেওয়ার চেষ্টা করেন না, কিন্তু তিনি এমন কিছু দৃশ্যকল্প তৈরি করেন, যা বুনে দেয় আরও অন্য অনেক দৃশ্য-শব্দ-ভাবনার পরত। এই বাচ্চাকে হারিয়ে ফেলা মা যেন সেইসব মায়ের প্রতিভূ হয়ে যায়, যারা সমগ্র যুদ্ধের ইতিহাসে— দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দেশভাগ, সিরিয়া, গাজা— ছুটতে ছুটতে, গরুর পালের মতো তাড়া খেয়ে পালাতে পালাতে হারিয়ে ফেলেছে তাদের ছোট্ট শিশুকে।

দৃশ্য মনে পড়ায় আরও দৃ্শ্য। ‘হীরক রাজার দেশে’-র পা ছড়িয়ে বসে কাঁদতে থাকা বাচ্চাটির শট মনে পড়ে, পেয়াদাদের খেঁদানি খেয়ে যার বাপ-মা তাকে হারিয়ে ফেলেছে। এই গহ্বরে আছে একটি মানুষ, যে শুধুই ঘুমোয়— ভয়, সংকট, অসহায়তা বা যুদ্ধবিধ্বস্ততা তাকে ভাবায় না, যুদ্ধবাজদের চাল তাকে রাগায় না— সে শুধু ঘুমিয়ে থাকে। এভাবেই চলতে চলতে হঠাৎ ঘোষণা হয়, জানা গেছে হাইড্রোজেন বোমা এগিয়ে আসছে তাদের লুকোনো ঘাঁটির ওপর, নিশ্চিত মৃত্যুর ভয়ে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে মানুষগুলি। কিছুক্ষণ পর আবার ঘোষণা হয়, সামান্য ভুল হয়েছিল, বোমা নয়, আসলে যা এগিয়ে আসছিল তীব্র গতিতে, তা ছিল একটা পাখির ঝাঁক। সিনেমার শেষ হয় যখন সেই ঘোষণার পর, গর্ভবতী মেয়েটি ঠিক করে, তার সন্তান জন্মাবে ভয়হীন, বদ্ধতাহীন, স্বাধীন এক মাটিতে, সে ওপরে উঠে আসতে থাকে, আর দেখা যায় আলোঝলমলে আকাশ জুড়ে কিচিরমিচির করতে করতে এগিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে পাখির ঝাঁক। বাঁচার মানে পালটে যায়, ভয়ে লুকিয়ে, গুটিয়ে থাকা মানুষগুলোর। তাদের মুখে হাসি ফুটে ওঠে এই প্রথম, ভয়ের কবল থেকে বেরিয়ে পড়ার হাসি।
ছবিটি দেখতে দেখতে মনে হতে পারে যেন নাটকের মতো এই ছবি। কার্ডবোর্ড আর প্লাই-এর সেট, আলো-আঁধারি লাইট ডিজাইন, একটিই স্পেস-এই পুরো সিনেমাটি তৈরি— চেম্বার-ড্রামা। সংলাপ বলাও একটু নাটকীয়, চরিত্রদের চলন-বলনও তাই। বিশষত সেট-টি বেশ অবিশ্বাস্য, আর সেটাই স্বাভাবিক, ফিল্ম ইনস্টিটিউটের বাজেটে, স্টুডেন্ট প্রজেক্ট-এ এমন সেটই তৈরি করা যায়। দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল, আহা, যদি বেশ খানিকটা টাকা পেতেন ঋত্বিক, তাহলে একটি দারুণ সাই-ফাই, ফিউচারিস্টিক মাস্টারপিস তৈরি করতেন সেই ১৯৬৫-তেই। তারকোভস্কির ‘সোলারিস’ বা গদার-এর ‘আলফা ভিলে’-র থেকে তা কিছু কম হত না।
‘ফিয়ার’ ছবিটির ভাবনা ও বিন্যাস, সময়ের থেকে অনেক এগিয়ে, কিন্তু বিষয়টি চিরকালীন। ভয় দেখিয়ে আর ভয় পেয়ে বেঁচে থাকার ইতিহাস তো চিরন্তন। গুটিকয় মানুষের তৈরি করা ভয়ে, ভয়ে ভয়ে মাথা নামিয়ে, শিরদাঁড়া ঝুঁকিয়ে, হাত কচলে, ‘স্যর, স্যর’ করে বেঁচে থাকার গল্পের কোনও শেষ নেই। বাঁচতে ভুলে যাওয়া, স্বাধিকার আর স্বাধীনতার সঙ্গে ঘরে-বাইরে আপস করে শেকল পরে একটা জীবন কাটিয়ে দেওয়ার কাহিনি লুপের মতো ঘুরে চলেছে। সিনেমায় আকাশ জুড়ে পাখিরা উড়ে বেড়ায়, বন্ধ ভীতু মানুষগুলি তা দেখে উঠে দাঁড়ায়, আবার মাথা তুলে তাকায়। জীবনে রোজ রোজ নতুন যুদ্ধপরিস্থিতি তৈরি হয়, রোজ একটি নতুন ভয় নিয়ে সকালে জেগে ওঠে মানুষ আর একটা অন্য ভয়ের গলা জড়িয়ে রাতে ঘুমিয়ে পড়ে। আর তাই শিল্পী ও শিল্প জিতে যায় রাজনীতিবাজদের কাঁচকলা দেখিয়ে।