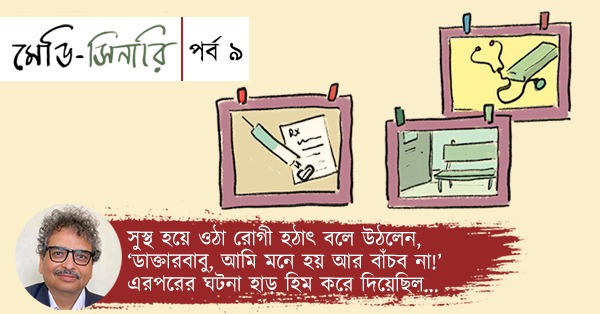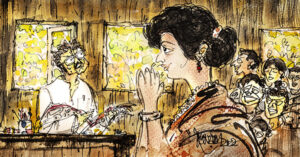কিছু বিজ্ঞান, কিছু জীবন
একজন ডাক্তার, ও একজন ডাক ও তার বিভাগের কর্মীর তফাত কী?
আমাদের মেডিসিনের একজন শিক্ষক এই প্রশ্নটা আমায় করেছিলেন। তখন মাত্র তিন বছর হয়েছে মেডিকেল কলেজের চৌহদ্দিতে পা দিয়েছি, এবং এক বছর আগে গলায় স্টেথো ঝুলিয়ে ঘোরার অধিকারটা অর্জন করেছি। কিছুক্ষণ মাথা চুলকে বললাম, ‘ডাক ও তার বিভাগের কর্মীদের একটা প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে, তাঁরা পোস্টকার্ড হোক, ইনল্যান্ড হোক বা টেলিগ্রাম সংগ্রহ করে, তা সঠিকভাবে পৌঁছে দেন তার প্রাপককে। আমাদের কাজ হচ্ছে, একজন মানুষ যখন তাঁর কষ্ট আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করেন, তখন আমাদের সিনিয়রকে, বা আরেকটু বয়স বাড়লে নিজের কাছেই সেই বার্তা প্রেরণ করে তার থেকে আমরা সমাধান বের করার চেষ্টা করি।’
কিছুক্ষণ ভ্রু কুঁচকে থেকে তিনি বললেন, ‘কিচ্ছু হল না। ডাক্তারির আসল চাবিকাঠি হল ধৈর্য। যেজন্য রোগীকে আমরা ‘পেশেন্ট’ বলি। এই পেশায় চোখ বন্ধ করে কাজ করার কোনও সুযোগ নেই।’
কতটা কী বুঝেছিলাম, তা জানি না। তবে সেদিন এটুকু উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম, যে, অন্যান্য পেশার সঙ্গে ডাক্তারির পার্থক্যটা এই, অন্য কাজগুলি জীবনের সঙ্গে সংলগ্ন নয়। আমরা যে যন্ত্রটিকে মেরামত করার চেষ্টা করি, তাকে কিন্তু বন্ধ করে মেরামত করা যায় না।
২
হাতে-কলমে ডাক্তারি আমরা মূলত শিখতে শুরু করি থার্ড ইয়ার থেকে। তার আগে যখন বিভিন্ন ক্লাস হয়, তখন নিজেকে ডাক্তার বলে তো মনেই হয় না, বরং মনে হয়, কেন এত তথ্য শেখার জন্য এত কষ্ট করে ডাক্তারিতে ভর্তি হলাম। শরীরের নানাবিধ তথ্য— হাড়, কঙ্কাল নিয়ে বোঝাপড়া, কোন পেশি কোথা থেকে শুরু হয়ে কোথায় গিয়ে যুক্ত হয়, তার কাজ কী, ছোট ছোট গহ্বরের মধ্য দিয়ে, কোন ধমনি, কোন শিরা, কোন নার্ভ যায়। সেইসব নাম বেশিরভাগই বিদেশিদের দেওয়া, তাদেরই গবেষণার ফসল হিসেবে পাওয়া। আমাদের সেগুলিই পড়ে যেতে হয়। মজার বিষয়, বঙ্গসন্তানের নাম দিয়ে অ্যানাটমিকাল ল্যান্ডমার্ক বা যন্ত্র কমই আছে, নেই তা অবিশ্যি নয়। আবার কিছু সাহেব কলকাতায় বসেই সেসব আবিষ্কার করেছেন।
যাক গে, থার্ড ইয়ারে যে অবিস্মরণীয় ঘটনাটি ঘটে, যে, প্রথমবারের মতো গলায় একটি ঝকঝকে স্টেথোস্কোপ ঝুলিয়ে ওয়ার্ডে বা আউটডোরে গিয়ে রোগী বা রোগিনী, বা তাদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলার অধিকারটা পাওয়া যায়। ব্যাপারটা কেমন হয়? ধরা যাক, সার্জারি ওপিডি। প্রফেসর একটি ঘরে বসে। পাশের একটি ঘরে রয়েছেন জুনিয়র ডাক্তার বলে যাঁদের আমরা চিনি, অর্থাৎ, ইনটার্ন বা গবেষক ও পোস্ট গ্র্যাজুয়েট স্তরের কেউ কেউ। সেই ঘরে কোনও রোগীর স্বাস্থ্যের বিষয়ে কোনও প্রশ্নের উত্তর যদি না মেলে, তখন পাঠানো হয় অধ্যাপক বা বরিষ্ঠ চিকিৎসকের কাছে। তিনি আবার কোনও কোনও রোগীকে পাঠান জুনিয়রদের কাছে, চিকিৎসার জন্য। তাঁদের আমরা সচরাচর ‘কেস’ বলে সম্বোধন করে থাকি। সেইসব কেসদের কী অবস্থা হয়, তা আমাকে বলেছিলেন এক মহিলা। ‘আপনারা ঝাঁকে ঝাঁকে এসে প্রশ্ন করেন, নানাবিধ পরীক্ষা করেন। তখন মনে হয়, ডাক্তারবাবুরা এত মন দিয়ে দেখছেন! কিন্তু তারপর যখন একই প্রশ্ন করতে থাকে সকলে, এবং একইরকম পরীক্ষানিরীক্ষা চালায়, তখন মনে হয়, কতক্ষণে এখান থেকে পালানো যাবে!’
আজকের দিনে যাঁরা নিজেরাই যখনতখন সিটি স্ক্যান বা আলট্রাসাউন্ড করে ডাক্তারবাবুকে রিপোর্ট দেখাতে চলে আসেন, তাঁরা ভাবতেই পারবেন না, একটা সময় আমাদের অধ্যাপকরা চিকিৎসা করতেন, এই ধরনের ‘ইমেজিং’ ছাড়াই। আমরা তখন সবে আলট্রাসাউন্ড শিখছি, সিটি স্ক্যান মেশিন যেখানে বসানো হচ্ছে, সেই বসানোর জায়গাটা হাসপাতালে সবচেয়ে অভিজাত, সেখানে সবসময়ই হয়তো শীতাতপনিয়ন্ত্রণ চলছে।
এখানে একটা মজা আছে। ধরুন, দু’জন চিকিৎসকের মধ্যে মতানৈক্য চলছে এই নিয়ে যে, রোগীর হার্টে বা হৃদয়ে সমস্যাটা ঠিক কী ঘটেছে। একজন বলছেন, ‘আমার মনে হচ্ছে এই জায়গায় একটি ফুটো আছে।’ অন্যজন বলছেন, ‘মোটেই না, ভালভের এইখান থেকে রক্ত লিক করছে।’ এই বিবাদের মধ্যে কোনও সমাধাই সম্ভব হত না, যদি ইকোকার্ডিওগ্রাফি না থাকত। এমনই একটি তর্কের মীমাংসা ঘটেছিল ইকোকার্ডিওগ্রাফির মাধ্যমেই, আমাদের সময় সেই প্রযুক্তি এসে গিয়েছে। দুই ডাক্তার দুই মত নিয়ে গিয়েছিলেন, ইকোকার্ডিওগ্রাফি বা ইকো করাতে। যেহেতু নতুন প্রযুক্তি, তাই একজন অপেক্ষাকৃত তরুণ চিকিৎসক বা আরএমও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ইকো করে দেখা গেল, দুই ডাক্তারই ভুল। কিন্তু এই কথা একজন আরএমও কী করে দুই সিনিয়রকে বলেন? ‘ইগো’ ব্যাপারটা তো নেহাত ফেলনা নয়। তাই এরপর তিনি যা বললেন, তা অনেকটা নাটকের চিত্রনাট্য যেন। তিনি জানালেন ওই দুই চিকিৎসককে, ‘আসলে স্যর, আপনারা দু’জনেই ঠিক বলছেন। এখানে একটা ফুটো আছে, আবার অন্য একটি জায়গায় আরেকটা গণ্ডগোল আছে। সেজন্যই ডানদিকের রক্ত আর বাঁদিকের রক্ত মিশে যাচ্ছে। আপনারা যদি মনে করেন, তবে হার্টের মধ্যে ভালভ বা ক্যাথিটার ঢুকিয়ে আরও বিশদে পরীক্ষা করে দেখতে পারি!’
যাঁরা বলেন, ডাক্তারি বিজ্ঞান, তাঁরা আসলে ডাক্তারিটাকে গোটাটা বোঝেননি। ডাক্তারি বিজ্ঞান তো বটেই, কিন্তু তাও পুরোপুরি বিজ্ঞান নয়। ভাবলে অবাক হতে হয়, পদার্থবিজ্ঞান বা অঙ্কের মতো ডাক্তারিতে কোনও ‘ল’ বা নীতি তৈরি হয়নি। কারণ, তার জন্য যে কাঠামো প্রয়োজন, তাই তো নেই। আজ এক আর একে দুই হলে, কাল তা না-ও হতে পারে। কাজেই, ডাক্তারিশাস্ত্রের প্রায়োগিক দিকের পু্রোটা আমাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে ‘প্রসেস’ করে ওঠাই মুশকিল।
একজন রোগী এসেছিলেন, একজন মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি, যিনি মদ্যপান করে লিভারের বারোটা বাজিয়েছেন। এই ধরনের রোগী আমাদের জন্য খুবই উপযোগী ছিলেন, কারণ, এঁদের দেহে যেসব সিম্পটম থাকত, তার ভিত্তিতে পরীক্ষায় পাশ করা আমাদের পক্ষে সুবিধাজনক হত। যাই হোক, এঁকে যতবার বলা হয়েছে, আর মদ খাবেন না, ততবারই তিনি সে আদেশ অমান্য করেছেন, এবং আবার এসে ভর্তি হয়েছেন।
একটি ঘটনা মনে পড়ে। একদিন দেখলাম, এক মধ্যবয়স্ক লোক অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে। হাত-পা কিছুই নড়ছে না। শুনলাম, তার মাথায় আঘাত লেগেছে। তিনি এমার্জেন্সি থেকে একটি স্কাল এক্স রে করে এনেছেন। সেই এক্স রে প্লেট দেখে বোঝা মুশকিল, তা শরীরের কোন অংশের, এবং সেখানে ঠিক কী ঘটেছে, এতটাই কালো, ঝাপসা ও ধোঁয়াটে। অথচ, নিউরোসার্জারির অধ্যাপক ছাদের ওটি-র অল্প আলোয় আমাকে বোঝালেন, সেই রোগীর ব্রেনের কোথায় রক্ত জমে আছে। আমি তো বিস্মিত!
কিন্তু চমক এখানেই শেষ নয়। রোগীর সার্জারি হবে ঠিক হল। খু্লির ঠিক কোথায় বারহোল বা ফুটোটা তিনি করবেন, সেই সিদ্ধান্তটাও কিন্তু ওই অস্পষ্ট এক্স রে প্লেট দেখেই নিলেন সেই অধ্যাপক-চিকিৎসক। এবং সেই অপারেশন সফলভাবে হল। মাথা থেকে বেরিয়ে এল জেলির মতো কিছু পদার্থ, চিকিৎসক আমাকে দেখালেন, কোথায় রক্ত জমে ছিল। এবং কিছুক্ষণ পরে সেই রোগী সুস্থ হয়ে উঠে বসে জিজ্ঞেস করলেন, ‘কী হয়েছিল বলুন তো আমার?’
এর মধ্যে কতটা বিজ্ঞান, আর কতটা মস্তিষ্কের মানচিত্রের ওপর নির্ভরশীল, তা বুঝতে আমার বোধহয় সারাজীবন লেগে যাবে। এই তথাকথিত চিকিৎসাবিজ্ঞানের বাইরেও একটা জগৎ আছে, তার নাগাল পাওয়া হয়তো সম্ভবই নয়।
৩
আমি তখন মেডিসিনের হাউজ স্টাফ। হাউজ স্টাফ সেই রাজত্বের রাজা। সব রোগীর খবরাখবর তাঁর কাছেই থাকে। তিনিই সমস্তটা নির্ধারণ করেন রোগীর বিষয়ে। কখনও কখনও অধ্যাপকদের সাহায্য নিয়ে। তখন একজন রোগী এসেছিলেন, একজন মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি, যিনি মদ্যপান করে লিভারের বারোটা বাজিয়েছেন। এই ধরনের রোগী আমাদের জন্য খুবই উপযোগী ছিলেন, কারণ, এঁদের দেহে যেসব সিম্পটম থাকত, তার ভিত্তিতে পরীক্ষায় পাশ করা আমাদের পক্ষে সুবিধাজনক হত। যাই হোক, এঁকে যতবার বলা হয়েছে, আর মদ খাবেন না, ততবারই তিনি সে আদেশ অমান্য করেছেন, এবং আবার এসে ভর্তি হয়েছেন।
সন্ধ্যার দিকে আমরা লিখতাম ছুটির কাগজগুলো, যাকে বলে ‘ডিসচার্জ পেপার’। সেদিন যখন এই ভদ্রলোকের ডিসচার্জ পেপার লিখতে লিখতে ওঁকে বললাম, ‘আপনার এবার ছুটি হবে, আপনি বাড়ি যাবেন’, তখন তিনি হঠাৎই বলে বসলেন, ‘না ডাক্তারবাবু, ওটি আর হচ্ছে না।’
আমি অবাক হয়ে বললাম, ‘কেন?’
তিনি বললেন, ‘আমি মনে হয় আর বাঁচব না।’
আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, ‘সে কী! আপনার সব টেস্টের রিপোর্ট ভাল। এরকম কেন ভাবছেন?’
যাই হোক, ইভনিং রাউন্ড সেরে হস্টেলে ফিরে এলাম। রাত তিনটের সময় হঠাৎ কলবুক। কলবুক ব্যাপারটা যাঁরা জানেন না, তাঁদের জন্য বলি, কলবুক হল ডাক্তারদের জন্য ডাক ও তার বিভাগের প্রাচীনতম মাধ্যম। একটি খাতা, যেখানে সিস্টার-নার্সরা অন-কল চিকিৎসকদের জানান দেন, অমুক রোগীর অবস্থা সঙ্গিন। আপনি সত্বর এসে দেখে যান। তারপর সেই খাতা দেখে একজন আসেন হস্টেলের দরজায় কড়া নাড়তে। পেজার, মোবাইল পেরিয়েও কিন্তু এই ব্যবস্থা বহাল তবিয়তে আছে।
যাই হোক, কলবুকের তলব এল। সেই রোগী। গিয়ে দেখলাম, তাঁকে সত্যিই আর বাঁচানো যাবে না।
এই ঘটনাকে বিজ্ঞান দিয়ে কীভাবে, কতটা ব্যাখ্যা করা সম্ভব, তা বলতে পারব না। মৃত্যুকে এত কাছ থেকে দেখতে দেখতে উপলব্ধি করেছি, জীবনমৃত্যুর সূক্ষ্ম ফারাকটা কখন বিলীন হয়ে যায়, তা হয়তো কয়েক জন্ম চিকিৎসক হয়ে থেকেও বোঝা হয়ে উঠবে না।
অনেক বছর আগে প্রফেসর রুডলফ ভির্চো বলেছিলেন, ‘মেডিসিন ইজ আ সোশ্যাল সায়েন্স।’ এই যে সামাজিক দিকটা, তা রোগ ও চিকিৎসার ওপর কীরকম প্রভাব ফেলে, তা চিকিৎসকরা ভালই বোঝেন।
৪
এরপর যখন রক্তবিজ্ঞান নিয়ে কাজ শুরু করি, তখন আরেকটি বিভীষিকার মুখোমুখি হলাম, তা হল ক্যানসার। রক্তের ক্যানসার শিশু থেকে বৃদ্ধ, কাউকেই ছাড় দেয় না। মাঝেমধ্যে চিকিৎসক হিসেবে অসহায় লাগে। মনে হয়, কী লাভ হল ডাক্তারি পড়ে?
আরেকটি ঘটনা বলে শেষ করি। একজন ৩১ বছর বয়সি রোগীর হয়েছিল সিএমএল, বা ক্রনিক মাইলয়েড লিউকেমিয়া। আজকের দিনে সিএমএল প্রায় ডায়াবেটিস বা থাইরয়েডের মতো রোগে পর্যবসিত। একটি করে ওষুধ খেলে সেই রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। আজ থেকে প্রায় ১২ বছর আগের ঘটনা বলছি। তখন সেই ওষুধ এসে গেছে। কিন্তু সকলের ক্ষেত্রে তা অত ভাল কাজ করত না। ফলে, সেই রোগীকে আমরা হারাই। তারপর স্বভাবতই রোগীর বাড়িতে খবর দেওয়া হয়। ছিলেন একমাত্র সেই রোগীর বৃদ্ধা মা। তিনি হাপুস নয়নে কাঁদতে কাঁদতে আমাদের জানালেন, এই মরদেহ তিনি নিয়ে যেতে পারবেন না। আমরা জানতাম, অনেক রোগীরই আর্থিক সংস্থান থাকে না। তাই আমরাই সৎকারের ব্যবস্থা করব, এই আশ্বাস দিলাম। কিন্তু তারপর তাঁর মায়ের থেকে যা শুনলাম, তাতে বুঝলাম, আমরা প্রায় দু’হাজার বছর পিছিয়ে আছি। জানা গেল, গ্রামের লোকের প্রবল আপত্তি, কারণ এই মরদেহ গিয়ে পৌঁছলে নাকি গোটা গ্রামের ক্যানসার হয়ে যেতে পারে। তারা প্রায় সশস্ত্র হয়ে অপেক্ষায়।
কেউ ভাবতেই পারেন, এটা তো পশ্চিমবঙ্গের সূদুর গ্রামের ঘটনা। কিন্তু জানিয়ে রাখা প্রয়োজন, লিউকেমিয়া আক্রান্ত শিশু, যাদের চিকিৎসা চলে সরকারি হাসপাতালে, তাদের জন্য একটি ‘হোম অ্যাওয়ে হোম’ আমরা তৈরি করার উদ্যোগ নিয়েছিলাম, এক সংস্থার সাহায্যে। দক্ষিণ কলকাতার, বাইপাসের ধারে, একটি বেশ সম্ভ্রান্ত পাড়ায় তা তৈরি হয়। সংস্থাটি হঠাৎই আমাকে জানায়, পাড়ার লোকজনের নাকি প্রবল আপত্তি আছে, ওই হোম থাকার বিষয়ে। আমি নিজে গেলাম বিষয়টা পর্যবেক্ষণ করতে। গিয়ে দেখলাম, সমাজের শিক্ষিত, মান্যিগন্যি লোক, আইটি কর্মী থেকে শুরু করে প্রবাসী, তারা দাবি করছে, এই শিশুরা পাড়ায় থাকলে তাদেরও ক্যানসার হবে। তাদের বোঝানো হল, এই শিশুরা গ্রাম থেকে এসেছেন, কলকাতায় তাদের থাকার জায়গা নেই। অনেক সময় শেয়ালদা স্টেশনের মতো খোলা চত্বরে থাকতে গিয়ে নানাবিধ সংক্রমণের শিকার হয়ে অনেকে জীবনও হারান। তাই তাদের এই আশ্রয়টুকু দিতেই হবে। তাতেও তাদের মনস্থির হচ্ছিল না, তখন প্রায় ধমকে বোঝাতে হয়েছিল, ক্যানসার এভাবে হয় না। এবং যারা এত আপত্তি করছে, তাদের শরীরেও কখনও কখনও ক্যানসার দানা বাঁধতে পারে। অবশেষে এইভাবে বাচ্চাগুলিকে রাখা গিয়েছিল।
অসুখ নিয়ে যদি মানুষ নিজে সচেতন না হয়, চিকিৎসকদের পক্ষে কোনও বদল কি আনা সম্ভব হবে?