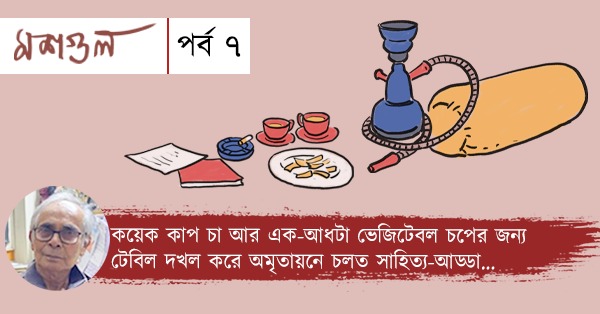অমৃতায়ণের আড্ডা
অমৃতায়ণ-এর আড্ডাটি ছিল পুরোপুরি সাহিত্যকেন্দ্রিক— আরও খোলাখুলি বললে বলব— গদ্যসাহিত্য-কেন্দ্রিক। অবশ্য বেশ কিছু উঠতি কবিও ছিলেন। কিন্তু তাঁরা এতটা উদ্দীপিত ছিলেন না। যেমন কবি পরেশ মণ্ডল, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, পুষ্কর দাশগুপ্ত, অশোক চট্টোপাধ্যায় (হাওড়া থেকে আসতেন, একটু রাত করে, কোনওদিন সকালে তাঁকে দেখিনি)। আমাদের এই আড্ডাটি ছিল সন্ধের পর প্রতিদিন, আর রবিবার দু’বেলা। এই সকালের সমাবেশটি ছিল অনেকটা আঞ্চলিক, অর্থাৎ, যারা এই রাসবিহারীর মোড়ের কাছাকাছি থাকতেন, যেমন সুনীল জানা, অমৃতায়ণের খুবই কাছে, কালীঘাট পার্কের গা ঘেঁষে, সতীশ মুখার্জি রোডের একটি মেসে, সপরিবারে। আর যজ্ঞেশ্বর রায়, কালীঘাটের কাছে আর-একটি বাড়িতে, এই যজ্ঞেশ্বর রায় ‘নরনারী’ পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। তাঁর বিষয় ছিল বিদেশি সাহিত্য এবং দস্তয়েভস্কি। এই দস্তয়েভস্কি নিয়ে তিনি একটি বেশ স্বাস্থ্যবান বই লিখেছিলেন। এবং তারই সুবাদে রাশিয়ায় আমন্ত্রণ, এবং গ্রহণ। পরে তা উদযাপন করা হয়েছিল, একটি কনিয়াক দিয়ে।
এখানে আমি ছিলাম শ্রোতামাত্র। তখন লেখালিখির সঙ্গে কোনও সম্পর্কই আমার ছিল না। এই আড্ডা থেকে জন্ম নিল ‘এই দশক’ পত্রিকাটি। খুব অনিয়মিত ছিল এর প্রকাশনা। তবে প্রস্তুতি ছিল বেশ কিছু দিন ধরে। প্রচ্ছদের জন্য ব্লক করা ছিল খরচসাপেক্ষ। অবশ্য সকলেই একটা না-একটা চাকরি করত, কিন্তু সকলের কাছ থেকে কিছু-কিছু নিয়েও কোনওমতে ছাপানোর খরচের বেশি কিছু হত না।
এই সময়ে আমি শ্রোতা থেকে উত্তীর্ণ হলাম কভার ডিজাইনারে। তাও খুবই সীমিতভাবে। কোনওরকমে একটি শিরোভূষণ তৈরি করা, এবং তা জিঙ্ক ব্লকে। তখনই আমি লিনোপ্রিন্টের কথা ভাবি। এই লিনোর কাটিং করে একটি কাঠের ওপর যদি সেঁটে দেওয়া যায় তাহলে ট্রেডল মেশিনে তো ছাপা যেতে পারে। কিন্তু কোনও প্রেস রাজি হয় না! তাঁদের কথা, একটু চাপেই তো লিনোটি ফেটে যেতে পারে। হ্যাঁ, তা অস্বীকার করা যায় না।
আরও পড়ুন : আকাশবাণীর আড্ডা যেভাবে ঠাঁই নিয়েছে ইতিহাসে! স্বপ্নময় চক্রবর্তীর কলমে ‘মশগুল’ পর্ব ৬…
যাই হোক, এক সময় সাফল্য আমরা পাই— ভবানীপুর অঞ্চলে একটি প্রেস— শ্রীধর প্রেস, মালিকের নামটি এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না, তিনি আমাদের এই পাগলামিতে রাজি হয়ে গেলেন। যে-আশঙ্কা আমরা করেছিলাম, তাও হল। এক সময়ে চাপে লিনো ব্লকটি ফেটেও গেল। আবার নতুন করে লিনো কেটে ব্লক তৈরি করে ছাপার সময়ে একটু কম চাপ দিয়ে খুব সুন্দর ছাপা হল!
আমাদের অন্যতম সদস্য বলরাম বসাক, তাঁর ছোটদের জন্য লেখা ‘পিঁপড়ে হাতি’ বইয়ে ছবির পরিকল্পনা করেছিলেন। সাত-আটটা ফুল পেজ ছবি করেছিলাম, সবার খুব ভালও লেগেছিল। যদিও সবগুলি ছিল একটি রঙে, আর প্রচ্ছদটি করা হয়েছিল অবশ্য লেটার প্রেসে। এক সময়ে এই বই পূর্ণেন্দু পত্রীর হাতে এসে পড়ে। সে এক অন্য কথা।
এই লিনোর সাফল্যে অন্যান্য লিটল ম্যাগাজিনগুলিও তাদের প্রচ্ছদে ছবি ও রঙের ব্যবহার শুরু করে।
অমৃতায়ণের ভেতরে তখন আশীষ ঘোষ, কল্যাণ সেন, সুনীল জানা, সুনীল মিশ্র, রমানাথ রায়, বলরাম বসাক, শেখর বসু, সুব্রত সেনগুপ্ত! নতুন করে গদ্য লিখতে হবে। এই সময়ে কতবার যে ৬ নং সুতারকিন স্ট্রিট ভেঙে পড়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। এক-একদিন নতুন গল্প পড়া হত কেবিনে বসে, আবার একসময় তা বন্ধও হয়ে যায়। কারণটা অবশ্য সুখকর নয়।
ফিরে আসি আড্ডার কথায়। এখান থেকে প্রথম প্রকাশিত হল ‘এই দশক’ পত্রিকা। তার আগে এই গল্প-লেখকদের নতুন ভাবনাচিন্তা, অজস্র কথার ছড়াছড়ি— নতুনভাবে গল্প লিখতে হবে। তৈরি হল এক ম্যানিফেস্টো। তৈরি করলেন রমানাথ রায়, এবং অন্যান্য সদস্যরা। আমার সব মনে নেই, তবে মনে আছে— গল্প থেকে ‘গল্প’ বাদ দেওয়া। কীরকম যেন এক গোলমেলে ব্যাপার। আমার বোঝার কথাও নয়, আর বুঝিনিও। অবশ্য উঠতি সাহিত্যিক মহলে এক নতুন উদ্দীপনা লক্ষ করা গিয়েছিল— তা অস্বীকার করা যায় না। বেশ কিছু তরুণ উঠতি গল্পকার অমৃতায়ণে জায়গা না পেয়ে সামনের ফুটপাথ দখল করেছিল। আর অমৃতায়ণের ভেতরে তখন আশিস ঘোষ, কল্যাণ সেন, সুনীল জানা, সুনীল মিশ্র, রমানাথ রায়, বলরাম বসাক, শেখর বসু, সুব্রত সেনগুপ্ত! নতুন করে গদ্য লিখতে হবে। এই সময়ে কতবার যে ৬ নং সুতারকিন স্ট্রিট ভেঙে পড়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। এক-একদিন নতুন গল্প পড়া হত কেবিনে বসে, আবার এক সময়ে তা বন্ধও হয়ে যায়। কারণটা অবশ্য সুখকর নয়। দেখা গেল কেবিনে পঠিত কিছু গল্পের ভাবভঙ্গি অন্যের গল্পে এসে ঢুকে পড়েছে।
এরই মধ্যে ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’-র শারদীয়া সংখ্যায় শেখর বসুর উপন্যাস ‘অন্যরকম’ প্রকাশিত হল। এ-ঘটনা খুবই স্বাভাবিক, কারণ শেখর বসু ছিলেন ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’-র কর্মী। আস্তে-আস্তে, এবং আমার মনে হয়, স্বাভাবিকভাবেই, ওদের ম্যানিফেস্টো ক্রমশ ধূসর হতে থাকে। এই প্রসঙ্গে আমার প্রশ্নের উত্তরে এক সদস্য জানিয়েছিলেন, ‘যৌবনে আমারা অনেক কিছু দেখি। তার মধ্যে থাকে অ্যাঙ্গার। এই অ্যঙ্গার থেকে আমরা অনেক কিছু অস্বীকার করি। ভুল করি। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, আমাদের সঙ্গে অনেক দায়দায়িত্ব এসে পড়ে, তখন ‘সত্য’ সামনে এসে দাঁড়ায়।’
হয়তো সেই নিয়মে ‘এই দশক’-এর অমৃতায়ণের আড্ডা অন্য পথে চলে যায়। সমস্ত কিছু আবছা হতে থাকে। অমৃতায়ণের আড্ডা ক্রমশ ছোট হতে থাকে। প্রথমত, অমৃতায়ণের মালিক তো অবশ্যই আমাদের পছন্দ করতেন না। কয়েক কাপ চা আর এক-আধটা ভেজিটেবল চপের জন্য টেবিল অধিকার কারই বা পছন্দ হয়। সামনের ফুটপাথে রমাদার কাগজের স্টল, তাও একদিন চলে গেল মেট্রোরেলের স্টেশনের জন্য। আমরা চলে গেলাম বিপরীত দিকের একটি রেস্তোরাঁয়। সবার পছন্দ হল না। দীপ জ্বালিয়ে বসে থাকলেন সুনীল জানা আর যজ্ঞেশ্বর রায়। তাও একদিন ওখান থেকে উঠে দেশপ্রিয় পার্কের উল্টোদিকে ‘সুতৃপ্তি’, সেই ঠেক আবার আগেই অধিকার করে ফেলেছে বেশ কিছু নামী-দামি শিল্পীর দল। অগত্যা আমরা উদ্বাস্তু। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আর কত দিন চলে। তবুও সুনীল জানা আর কয়েকজন ফুটপাথের চা আর কিছু বিস্কুট নিয়ে রবিবার সকালটা কাটিয়ে দেয়।
ইতিমধ্যে কল্যাণ সেন একদিন চলে গেলেন বাস দুর্ঘটনায়। চলে গেলেন অমল চন্দ, একদিন সুব্রত সেনগুপ্ত, আস্তে-আস্তে সুনীল জানা আর আমরা মাত্র কয়েকজন পড়ে রইলাম। আমাদের একজন সদস্য সুকোমল রায়চৌধুরী আত্মহত্যা করলেন, অনেকটা জাপানি কায়দায়। আর-এক দম্পতি চলে গেলেন দক্ষিণেশ্বর। এই কিছুদিন, না কি এক বছর হয়ে গেল— সুনীল জানা, তার আগে রমানাথ রায়, যজ্ঞেশ্বরবাবু তো অনেকদিন আগেই। একটা সময় চলে গেল, স্মৃতিগুলো রয়ে গেল খণ্ড খণ্ড হয়ে।