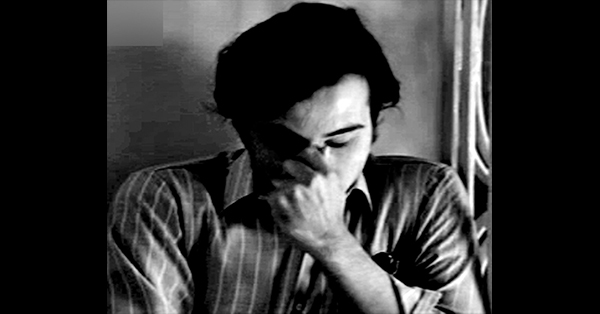ছবিটার শুরুই হয় নেগেটিভ হয়ে যাওয়া দৃশ্য দিয়ে। নেগেটিভ কেন? একটা লোক মারা গেছে, তার বাড়িতে কান্নাকাটি হচ্ছে, এটা স্বাভাবিক ভাবে দেখালে কী ক্ষতি হত? সত্যজিৎ বলেছেন, যে মারা গেছে, তাকে দর্শক চেনে না, তার ওপর গোটা ছবিতে সে নেইও, তাই ছবিটা স্পষ্ট করে দেখাননি। কিন্তু ব্যাপার এত সহজ নয়। নেগেটিভ হওয়ায়, দৃশ্যটা প্রায় অবাস্তব মনে হয়। তার ওপর পিছনে আবহসঙ্গীত সেটাকে আরও অবাস্তব করে। যেন একটা দুঃস্বপ্ন। তারপরেই নায়কের মুখ নেগেটিভ থেকে পজিটিভ হয়ে যায়। তারপর ক্যামেরা তাকে ছেড়ে আকাশে যায়, সেখানে ‘প্রতিদ্বন্দ্বী’ শব্দটাকে দুই-দুই অক্ষরে ভাগ করে যেন পরস্পরের বিরোধিতায় দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়, তারপরেই প্রবল ট্র্যাফিকের গর্জন এবং একটা সাংঘাতিক ভিড়বাসের কিছু দৃশ্য দেখানো হয়, ছবির কলাকুশলীদের নাম ফুটে উঠতে থাকে, দেখা যায় আমাদের নায়ক সিদ্ধার্থও বাসের ফুটবোর্ডে কোনওক্রমে সেঁটে আছে। এরপর সে রাস্তা দিয়ে হাঁটে, পিছনে বাজে যুদ্ধের বা প্যারেডের ড্রামের আওয়াজ (এই আওয়াজ ছবির নাম দেখানোর সময় শোনা গেছে, পরে বহুবার শোনা যাবে), তারপর ঢোকে একটা অফিসে, সেখানে লেখা ‘বোটানিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া’। লিফট থেকে বেরিয়ে একজনকে একটা স্লিপ দেয়, সে ভেতরে বসতে বলে। পাশের ছেলেটি সিদ্ধার্থকে জিজ্ঞেস করে, আপনার কি এটা ফার্স্ট ইন্টারভিউ? এও জিজ্ঞেস করে, প্রশ্নের ধরন সম্পর্কে সে কিছু জানে কি না, এবং ইন্টারভিউটা ইংরেজিতে হবে কি না। সিদ্ধার্থ তার দিকে একবারও না তাকিয়ে খটাস খটাস করে উত্তর দেয়। তারপর পায়ের ওপর পা তুলে আবিষ্কার করে প্যান্টটা একটু ছেঁড়া। একটা দোকানে যায়, তারপর আরেকটা দোকানে। সেখানে আমরা দেখি তার প্যান্ট সেলাই চলছে, সে লুঙ্গি পরে বসে আছে। হঠাৎ তার মুখের ক্লোজ-আপের পরেই আমরা দেখতে পাই পরপর তিনটে স্টিল ছবি, সে কোটপ্যান্ট পরে গাছপালা ভর্তি একটা নার্সারিতে দাঁড়িয়ে, আমরা অনুমান করি জায়গাটা বোটানিকাল গার্ডেনে, অর্থাৎ এটা তার চাকরি পেয়ে যাওয়ার দিবাস্বপ্নের দৃশ্য। তারপরেই দর্জির ডাকে তার ও আমাদের চটকা ভাঙে এবং সে ইন্টারভিউ দেওয়ার ঘরে ঢোকে। এরপর ইংরিজিতে গোটা ইন্টারভিউ। ১৯৭০-এর বাংলা ছবির দর্শকের কাছে ছবিটা ইতিমধ্যেই (মিনিট সাতেকের মধ্যেই) অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছে। সত্যজিতের কাজের মধ্যে একটা নিটোল ব্যাপার থাকে, দর্শককে ঝাঁকুনি দেওয়া উনি পছন্দ করেন না। দর্শকও সেই মসৃণতার প্রত্যাশা নিয়েই তাঁর ছবি দেখতে যায়। যা হবে, তার স্পষ্ট শুরু-মধ্যে-শেষ থাকবে, এবং খুব খানিক অভিনব চিত্রভাষা যদি প্রয়োগ করাও হয়, তা ধরিয়ে দেওয়ার জন্য পরিচালক যথেষ্ট সহায়তা করবেন— এই বিশ্বাস দর্শকের থাকে। কিন্তু এখানে যেন উনি থোড়াই-কেয়ার ভঙ্গিতে, দর্শকের আরামের তোয়াক্কা না করেই, ফিল্মটা বানাতে শুরু করলেন। একটু পরেই বোঝা যাবে, সিনেমা জুড়ে আমরা প্রায়ই নায়কের মাথার মধ্যে তৈরি হওয়া ছবি দেখতে পাব, তা আরও মোক্ষমভাবে প্রযুক্ত হবে সিদ্ধার্থ ডাক্তারি পড়েছিল বলে, রাস্তা-পেরোনো উদ্ধত-বুকের মেয়ে দেখে তার মনে পড়বে ডাক্তারি ক্লাসে স্তন সম্পর্কে লেকচার (এবং আমরা রাস্তার দৃশ্য থেকে চকিতে ক্লাসরুমের দৃশ্যে চলে যাব), কাউকে ট্যাবলেট গিলতে দেখলে তার মনে পড়বে ডাক্তারি ক্লাসে গিলে ফেলার প্রক্রিয়া পড়ার কথা (এবং আমরা এক লহমায় চলে যাব বসার ঘর থেকে ক্লাসে)। বোন মডেল হবে বলতেই তার মাথায় পরপর বোনের বিভিন্ন পোশাক পরা ছবি ভেসে ওঠে, বোন ইংরেজি-মার্কা নাচ শিখছে শুনেই তার মনে পার্টিতে বোনের নাচের এবং সিগারেট খাওয়ার কাল্পনিক দৃশ্য ভেসে ওঠে। একটা দৃশ্যে বোন কথা বলতে বলতে তিরস্কারের সুরে বলে ওঠে ‘দাদা!’ এবং সঙ্গে সঙ্গে ফ্ল্যাশব্যাক শুরু হয়ে যায়, যেখানে বোন ছোট-বয়সে তার দাদাকে ডেকে বলছে, ‘এই দাদা!’ অর্থাৎ শুধু একটা শব্দে ভর করে (যদিও দুই পরিস্থিতিতে তা উচ্চারণের উদ্দেশ্য ও ধরন সম্পূর্ণ ভিন্ন) ফ্ল্যাশব্যাক শুরু হয়, এবং তা কয়েক সেকেন্ড পরেই আবার থেমে যায়। ছবি জুড়ে এতগুলো এত কম সময়ের শট বা সিকোয়েন্স আমরা দেখতে অভ্যস্তই নই, অন্তত ১৯৭০-এর সাধারণ বাঙালি দর্শক (যাঁরা ফরাসি নবতরঙ্গের ছবি দেখেননি) তাঁদের পক্ষে এ রীতিমতো হকচকানো কাণ্ড, তার ওপর এই ফ্ল্যাশব্যাকটার একটা কয়েক সেকেন্ডের অংশ আমরা দেখেছিলাম আগে এক দৃশ্যে, সিদ্ধার্থ যখন ঝিলের জলের দিকে তাকিয়েছিল, যে ঘোর তার ভেঙে যায় কয়েকজন হিপির আগমনে।

এ যেন, সিদ্ধার্থের (বা যে কোনও মানুষের) মনে যেমন কোনও যুক্তি না মেনে কীসব চিন্তা উড়ে এসে পড়ে আবার মিলিয়ে যায়, একটা সিনেমা মাঝেমাঝেই সেই চলনটাকে পাকড়ে ধরতে চাইছে। সত্যজিৎ রায়ের কাছে এমন উদ্ভট চেষ্টা আশা করা যায় না। তাই এই ছবি শুধু প্রায়ই হাতে-ধরা ক্যামেরায় ঝাঁকুনি দিতে দিতে চলে না, তার শট-বিন্যাসের স্টাইলেও গুচ্ছের ঝাঁকুনি সাজানো থাকে। একটা ছবি দেখতে বসে কর্তিত ছেঁড়া-ছেঁড়া সংক্ষিপ্ত কিছু দৃশ্য মাঝেমাঝেই দেখব, তার কয়েকটার মানে তক্ষুনি বুঝব (যখন নায়ক যা দেখছে তার সঙ্গে ক্লাসে পড়ানো বিষয়ের সাদৃশ্য থাকবে) আবার কিছু এমন অপ্রত্যাশিত যে চমকে উঠব (যেমন চে গুয়েভারার বইয়ের প্রসঙ্গ ওঠার একটু পরেই নায়কের মুখ ডিজলভ করে যায় তার আরেকটা মুখে যেখানে চে-র মতোই দাড়ি গজিয়ে গেছে), এত হ্যাপা সামলানো মুশকিল। এবং এই প্যাটার্ন গোটা ফিল্মটা জুড়ে প্রতিষ্ঠা করার ফলেই সত্যজিৎ সেই তাক-লাগানো প্রয়োগ করতে পারেন, যখন বোনের বসের বাড়িতে সোফায়-বসা সিদ্ধার্থ বসের হেঁটে আসার পায়ের শব্দ শুনতে পায়, আর এক হাতে রুমাল আঁকড়ে, অন্য হাতটাও সে-হাতে চেপে কিছু একটা করার জন্যে প্রস্তুত হয়, আর দর্শকেরা অসম্ভব চমকে গিয়ে ব্যাঁকানো ফ্রেমে দেখতে পায়, সিদ্ধার্থ বসকে গুলি করছে, একটা দুটো তিনটে, বস রক্তাক্ত, তারপরেই দেখা যায় পাখা ঘুরছে (মানে বস সেটা চালিয়েছেন) এবং ধীরেসুস্থে বলছেন, ‘দাঁড়িয়ে কেন, বোসো’। অর্থাৎ তাঁকে দেখে উঠে দাঁড়িয়েছিল সিদ্ধার্থ, এবং হত্যাটা পুরোটাই তার মনোজগতে ঘটেছে। এই কোনও ওয়ার্নিং না দিয়ে নায়কের চিন্তাকে যখন-তখন সিনেমার পর্দায় আনার কায়দাকে আরও আশ্চর্য, বেপরোয়া ও অপ্রত্যাশিত রূপ দেওয়া হয় শেষদিকের দৃশ্যে, যখন ইন্টারভিউতে ডাকের জন্যে অপেক্ষারত ক্লান্ত সিদ্ধার্থ দেওয়ালে মাথা হেলিয়ে চোখ বুজে আছে। পর্দায় ভেসে ওঠে: একটা বাড়িতে বসে থাকা কয়েকজন হিপি যুবক-যুবতীর ছবি (তাদের একজন আবার স্টেথোস্কোপ দিয়ে একটা খঞ্জনির আওয়াজ শুনছে, যে স্টেথোস্কোপ নিজের বুকে লাগিয়ে স্পন্দন শুনেছিল একটা দৃশ্যে সিদ্ধার্থ স্বয়ং), তারপর ফুটপাথে শুয়ে থাকা এক ভিখিরি, তারপরে একটি বস্তি— উনুনের ধোঁয়াভরা, এবং তারপরে একটি সুসজ্জিত বাড়ির অভ্যন্তর, কয়েকজন বোধহয় একটু দূরে একটা ঘরে বসে খাচ্ছে, তারপর লেকের ধারে একটা রাস্তা। কোনওরকম সংলগ্নতা নেই শটগুলোর, কোনও পারম্পর্য নেই, এবং সিদ্ধার্থ কেন এগুলো ভাবছে তার ন্যূনতম ইঙ্গিতও আমাদের দেওয়া হয় না। এর সামান্য পরেই আমরা শুনতে পাব ফের ডাক্তারি ক্লাসের প্রফেসরের লেকচার এবং সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ইন্টারভিউ-প্রার্থীর চেহারা কঙ্কালে রূপান্তরিত হবে, তারপর গোটা বারান্দা জুড়েই বিভিন্ন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে-বসে থাকবে কঙ্কালেরা। তাতেও আমরা ধাক্কা খাব, এবং তারপর তো আসবে ছবির ক্লাইম্যাক্স, যেখানে সিদ্ধার্থ ক্রোধে উল্টে দেবে টেবিল, এবং এইসবের অভিঘাতে আমরা বেমালুম ভুলে যাব আগের ওই অ-যুক্তি দিয়ে বাঁধা পাঁচটি শটকে, কিন্তু সত্যজিৎ মুচকি হেসে ভাববেন, তিনি যে এতক্ষণ ধরে নায়কের মনের ছবি আচমকা ফুটে ওঠাগুলিকে যুক্তি দিয়ে বুনেছিলেন, আর একটা সময়ে সেই যুক্তির পাটাতনটাও সরিয়ে নিয়েছিলেন, তা এই ছবির স্বেচ্ছা-ঝাঁকুনির ম্যাপে একটা আশ্চর্য দ্বীপ হয়ে থাকবে। তবে দুরূহতার ফার্স্ট প্রাইজ এটা মোটে পাবে না। শৈশবে শোনা যে অচিন পাখির অকলুষ ডাকটিকে নায়ক সারা ছবি জুড়ে খুঁজে যায়, যা তার কাছে সর্বাধিক সারল্যময় ও জীবনবাচক, তা যখন ছবির শেষ দৃশ্যে সে শুনতে পায়, কেন যে তার সঙ্গে শবযাত্রার মুহুর্মুহু ভক্তিধ্বনি জুড়ে দেওয়া হয় (হয়তো জীবন ও মৃত্যু মিলে এক রহস্যময় পূর্ণবৃত্তের মধ্যেই অর্থ খুঁজে যেতে হবে— ইহাই নীতিকথা), তা কে-সি-নাগাতীত।

ছবিটা কর্কশ। শুধু সংলাপে প্রচুর ‘শালা’, ‘শুয়োরের বাচ্চা’ ছড়ানো আছে বলে নয়, যেখানেই সিদ্ধার্থ যাক হাঁটুক দাঁড়াক তার পিছনে পাশে প্রতিবাদী পোস্টার বা রাজনৈতিক দেওয়াল-লিখন থাকে বলে নয়, সিদ্ধার্থর বাড়িতে সবসময় চাপ-চাপ অন্ধকার থাকে বলে নয়, ছবিটার পাত্রপাত্রীদের অ্যাটিটুড আমাদের প্রকৃত ইট-পাটকেলগুলো মারে। সিদ্ধার্থ বন্ধুদের সঙ্গে নরম দিলখোলা গোছের, কিন্তু অন্যদের সঙ্গে আচরণে আড়ষ্ট, অসহিষ্ণু। যেন সে সর্বক্ষণ ভেতর-ভেতর গজরাচ্ছে, এই সময় ও সমাজের সঙ্গে তার একটা শত্রুতা চলেছে এবং সে ক্রোধে ও অভিমানে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে, একটা বর্ম পরে আছে। নরেশদা নামে একজন যখন তার ভাল চেয়ে কিছু কথা বলতে আসেন, সিদ্ধার্থের ভয়েস-ওভার আমরা শুনতে পাই, ‘আর জ্ঞান দেবেন না নরেশদা, জ্ঞান দেবেন না, এত লোক এত জ্ঞান দিয়েছে যে জ্ঞানের ঠেলায় একেবারে choked হয়ে গেছি। আপনি ভাল লোক, আপনাকে অ্যাডমায়ার করি, কিন্তু তাও বলছি, হয় কথা বন্ধ করুন, নয় কেটে পড়ুন— আর বকবক ভাল্লাগে না।’ এমনকী সিনেমা হল-এ বোম পড়লে যখন সব দর্শকেরা ছুটে পালাচ্ছে, সিদ্ধার্থের বিশেষ ভাবান্তর দেখা যায় না, বেশ নিরাসক্ত ভঙ্গিতে হেঁটে বেরোয়। সিদ্ধার্থের এক বোন আছে, সুতপা। সে চটকদার, তার বসের সঙ্গে তার প্রেম-সম্পর্কের কানাঘুষো উড়ছে, বসের বউ এসে বাড়িতে ঝামেলা করে গেছেন। তাকে এসব নিয়ে সিদ্ধার্থ বকতে ও কৈফয়ৎ চাইতে এলে দেখা যায়, বোন নিতান্ত নির্বিকার। সে কাঁদেকাটে তো না-ই, কোনও ঝগড়া অবধি করে না, ঠান্ডা ও ক্যাজুয়াল গলায় যা বলে, তার মোদ্দা মানে: সে বেশ করছে। আরও একটা অনুরূপ দৃশ্য মিলিয়ে তার বক্তব্য, বস সত্যি সত্যি এখনও কোনো কু-ইঙ্গিত করেননি (যদিও তিনি সুতপাকে তাঁর নরেন্দ্রপুরের নতুন বাড়ি দেখাতে নিয়ে যান, ২০০ টাকা ইনক্রিমেন্ট দিয়ে তাকে তাঁর পিএ করেও নিচ্ছেন), পরে কিছু করতে এলে, তখন দেখা যাবে’খন। আর মা যে মেয়ের নামে অপবাদ নিয়ে এত ভাবছেন, ‘ও সয়ে যাবে’। সে মডেলিং করার কথা অবধি ভাবছে। তখনকার দিনে এক নিম্নমধ্যিত্ত বাঙালি পরিবারের মেয়ে মডেলিং-কে সম্মানজনক পেশা হিসেবে ধরতই না। কিন্তু সুতপার ছোট পোশাক পরতে কোনও দ্বিধা নেই। সিদ্ধার্থ বলে, ’আর তোকে যদি একটা জঘন্য পোশাক পরে পোজ করতে বলে?’ সুতপা: ‘জঘন্য মানে?’ সিদ্ধার্থ: ‘মানে, ধর তোর পোশাক-টোশাক কিছু নেই বললেই চলে।’ সুতপা: ‘তাতে কী হয়েছে! আমার ফিগারটা তো খুব খারাপ নয়।’ একজন সাধারণ গেরস্থ-ঘরের মেয়ে প্রায়-নগ্নছবির পোজ দেওয়ার ব্যাপারে বলছে ‘তাতে কী হয়েছে’, কারণ তার ফিগার এত সুন্দর যে দিব্যি মানিয়ে যাবে, এ এখনও বাঙালি-সমাজে ভাবা যায় না, ১৯৭০-এ তো যেতই না। একজন যুবতীর মধ্যে এরকম নিতান্ত আটপৌরে ভঙ্গিতে মধ্যবিত্তের মূল মূল্যবোধগুলোকে অস্বীকার করার ঢল দেখে দর্শকের প্রকাণ্ড শক লাগে।

অতটা অবশ্য লাগে না যখন পর্দায় আসে সিদ্ধার্থের ভাই টুনু, কারণ নকশাল আন্দোলন ওই সময়ে মধ্যবিত্তের সবচেয়ে চেনা ও সবচেয়ে স্তম্ভিত করে দেওয়া ঘটনা। কিন্তু তা বলে সে চরিত্রও সহজে গেলা যায় না। টুনু বিপ্লব করবে। চাকরি খোঁজাকে সে ঘেন্না করে। সমাজটাকে বদলানোর চেষ্টা ছাড়া আর যে কোনও চেষ্টাই যেখানে অপরাধ, সেখানে যে-দাদা তাকে চে গুয়েভারার বই উপহার দিয়েছিল সে কিনা সারাদিন চাকরির সন্ধানে টো-টো ঘুরছে, জীবনের কোন রাস্তাটায় ঢুকবে কিছুতেই বুঝতে না পেরে ‘স্রেফ ওই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গেঁজে’ যাচ্ছে— এই ঘটনার প্রতি তার তীব্র ঘেন্না ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট নেই। সে অবজ্ঞার চোটে দাদার আদ্ধেক প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন অবধি বোধ করে না। দিলেও খুব অনিচ্ছুক অনাগ্রহী ভাবে দেয়। দাদা তাকে ব্যাগ গোছাতে দেখে জিজ্ঞেস করে, ‘তুই যাচ্ছিস কোথাও? হুঁ?’ টুনু: ‘ইচ্ছে আছে।’ সিদ্ধার্থ: ‘কোথায়?’ টুনু: ‘বাইরে।’ সিদ্ধার্থ: ‘বাইরে মানে?’ টুনু: ‘বাইরে।’ সিদ্ধার্থ: ‘বাইরে!’ টুনু: ‘বাইরে।’ পরে যখন সিদ্ধার্থ তাকে বলে, ‘তুই রেভোলিউশন করবি?’ টুনু উত্তর দেয়, ‘যা-ই করি সেটা তোকে অ্যানাউন্স করে করব না নিশ্চয়ই।’ সিদ্ধার্থর ‘আফটার অল তুমি তো আমার ভাই’-এর উত্তরে টুনু শুধু বলে ‘টাকাটা পেলে সুবিধে হত’ (সে দশটা টাকা চেয়েছিল আগে)।
সিদ্ধার্থের প্রতিদ্বন্দ্বী কি সে নিজেই? সে দিশা খুঁজে পাচ্ছে না, তা তার অক্ষমতা, না সমাজের সীমাবদ্ধতা? সে যে কোনও পক্ষই নেয় না, প্রধানত পর্যবেক্ষণ করে যায়, তা কি তার দুর্বলতা, না জোরের জায়গা? তার ক্রমাগত দ্বিধা তার সম্পদ না বিপদ? রাস্তায় আঁকা এদিকের তিরচিহ্ন আর ওদিকের তিরচিহ্নের বিপরীতমুখী সারির মধ্যে দাঁড়িয়ে সে কোনদিকে চালিত করবে তার ঘুঁটি-জীবন? সত্যজিতের কাজ হল এই প্রশ্নগুলো তুলে ছুড়ে দেওয়া।
ভাই আর বোনের এই দুই সম্পূর্ণ বিপরীত চলন— একজন নীতি-টিতি চুলোর দোরে দিয়ে পুঁজিবাদের কাছে প্রণত, আরেকজন যে কোনও মূল্যে পুঁজিবাদকে আঘাত হানবে বলে অন্য সবকিছুর প্রতি উদাসীন— এর মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে আছে সিদ্ধার্থ। একবার তার মনে হয়, টুনুর কথাই ঠিক, রেভোলিউশন ছাড়া রাস্তা নেই, একবার সে ফ্যান্টাসি দ্যাখে তারও কোটপ্যান্ট হবে, সম্পন্ন সমৃদ্ধ জীবন হবে। সত্যজিৎ এইজন্যই সিদ্ধার্থকে নিয়েই ছবি করেন। টুনুর চরিত্র হয়তো খুব গ্ল্যামারাস, সে মারে ও মরতে রাজি থাকে, আগুন নিয়ে খ্যালে, কিন্তু সে একবগ্গা। সে একটাই রাস্তা দেখতে পেয়েছে, আর কোনওকিছুই তার চোখে পড়ে না, এইজন্যেই সে অনাকর্ষণীয়। আর সুতপার চরিত্রও নিতান্ত একমেটে। লোভ যা বলবে, সে তা-ই করবে। সিদ্ধার্থের সংশয়, তাকধাঁধা লেগে যাওয়া, বাবা মারা যাওয়ার পর বড়ছেলে হিসেবে সংসারের দায়িত্ব ফেলে দিতে না পারা, আবার চাকরির ইন্টারভিউতে চূড়ান্ত অন্যায় দেখে হুড়মুড়িয়ে রেগে ওঠা, নিজের চাকরিটা নিশ্চিত হাতছাড়া হচ্ছে বুঝেও প্রতিবাদ করা— সব মিলিয়ে সে এক এমন যুবসমাজের প্রতিনিধি, যারা কী করবে কোথায় যাবে কিচ্ছু বুঝতে পারছে না, যাদের বহু রং, বহু ছায়া। সিদ্ধার্থর প্রতিদ্বন্দ্বী কে? সমাজের ক্ষমতাধারীরা? নিজের ভাইবোন? একদা-সহপাঠী বন্ধুরা? একজন বন্ধু মোক্ষম হাই-ভোল্টেজ: বড় বংশের ছেলে, ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র, নিয়মিত মদ খায়, বেশ্যাসঙ্গ করে, এমনকী রেডক্রসের জন্যে চাঁদা তুলে সেই কৌটো থেকে পয়সা চুরি করে। সিদ্ধার্থ তাকে যখন বলে ‘তুই কোত্থেকে কোথায় নেমেছিস’, সে তুরন্ত ও অনুতাপহীন বলে, ‘The whole country is going down brother, আমি নিচে না নামলে কি শূন্যে suspended হয়ে থাকব?’ এই বন্ধুই তাকে এক (নার্সের পোশাক পরা) বেশ্যার কাছে নিয়ে যায়, বলে ‘…She is all yours brother’, বলে ‘প্রথমটা অবিশ্যি একটু তেতো লাগবে, ঝাঁঝ লাগবে, তারপর…’। সিদ্ধার্থ রাগে-বিরক্তিতে-ঘেন্নায় সেখান থেকে প্রায় দৌড়ে পালায়। (সাধারণ বাঙালি দর্শকেরও এসব খুবই তেতো ও ঝাঁঝালো লাগতে থাকে। এক বন্ধু কার প্রেমে পড়েছে, সে আন্দাজ করতে গিয়ে সিদ্ধার্থ একসময় বলে, ‘ওঃ, মাস্ট বি গায়ত্রী, অন্যটার তো কিসু নেই, শি হ্যাজ নাথিং!’)। অন্য বন্ধু ফিল্ম-ক্লাবের সিনেমা দ্যাখে, কারণ সেখানে ‘নো কাঁচি’, নির্বিঘ্নে সেক্স দেখা যাবে। না কি সিদ্ধার্থর প্রতিদ্বন্দ্বী পুঁজিবাদ? বোনের বসের বাড়ি থেকে অক্ষম আক্রোশে (আবারও ব্যাঁকা ফ্রেমে) বেরিয়ে আসার পর কিছুদূর হেঁটে, খুব চেঁচামেচি শুনে সিদ্ধার্থ দেখতে পায়, একটি পথের বালিকাকে ধাক্কা দিয়েছে একটি গাড়ি এবং গাড়ির ওপরের চিহ্ন দেখে বোঝা যায় তা বিদেশি বহুজাতিক সংস্থার। সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধার্থ ভিড়ের মধ্যে ড্রাইভারকে মারবে বলে নিষ্ঠুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ে (কারণ এর মধ্যে বহুজাতিক সংস্থার মুখে থাবড়া মারা নিহিত), কিন্তু না পেরে একটু সরে আসতেই দ্যাখে গাড়ির মধ্যে একটি স্কুলবালিকা ভয়ে থরথরিয়ে কাঁপছে, সিদ্ধার্থের মাথা নিচু হয়ে যায়। গ্রেনেড ছোড়ার ক্যারিশমার উল্টোদিকে যে গ্রেনেড খাওয়া ছিন্নভিন্ন শরীরও থাকে, সেটা বহু সিনেমাই বিপ্লবের উত্তেজনায় ভুলে যায়, কিন্তু সত্যজিৎ ভোলেন না। পড়াশোনা জানা, রাজনীতি করা, অন্যরকম বই পড়া মানুষ (সিদ্ধার্থ তার ইন্টারভিউয়ের কাগজপত্র নেয় বার্ট্রান্ড রাসেলের ‘ আ হিস্ট্রি অফ ওয়েস্টার্ন ফিলজফি’ বইয়ের ওপর থেকে) ফাঁদে-পড়া-ছটফটানি এবং চেপে-থাকা-খার বের করে দিতে দৌড়ে গণধোলাইয়ে অংশ নিতে যায়, তাও তিনি অক্লেশে দেখান। সিদ্ধার্থ সিনেমা দেখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর গুণকীর্তন করা প্রচারছবির সময় সিটে মাথা হেলিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে, ‘স্বাধীনতার সময় ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?’ প্রশ্ন শুনে জিজ্ঞেস করে ‘কার স্বাধীনতা, স্যার?’, চাঁদে যাওয়ার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা মনে করে ভিয়েতনামের যুদ্ধকে, কিন্তু নরেশদা যখন রাজনীতির কাজকর্ম করতে যেতে বলেন, বিন্দুমাত্র উৎসাহ দেখায় না। বন্ধুর পাল্লায় পড়ে সে মদ টেস্ট করে, কিন্তু বেশ্যার স্বাদ নেয় না। সিদ্ধার্থকে ব্যঙ্গ করে ভাই বলে, ‘তুই কীরকম ম্যাদা হয়ে গেছিস।’ সিদ্ধার্থকে ব্যঙ্গ করে বোন বলে, ‘তোর ধোলাই দেবার কথা শুনলে হাসি পায়’। সিদ্ধার্থকে ব্যঙ্গ করে বন্ধু বলে, ‘…ওসব ভাবা-টাবার মধ্যে নেই, যা করবার তাই করব। আর তুই, যা করবি না, তা-ই ভাববি।’ এই সিদ্ধার্থই ইন্টারভিউয়াররা প্রখর গরমে প্রার্থীদের জন্য কয়েকটা চেয়ারের ব্যবস্থা অবধি করছেন না দেখে শেষমেশ এতটা রেগে যায় যে ঘরে ঢুকে ভাঙচুর করে, চেয়ার ছুড়ে জানলা ভাঙে, তার প্রেমটাও যে বিপর্যস্ত হচ্ছে এ-কথা মনেই রাখে না। তাহলে সিদ্ধার্থের প্রতিদ্বন্দ্বী কি সে নিজেই? সে দিশা খুঁজে পাচ্ছে না, তা তার অক্ষমতা, না সমাজের সীমাবদ্ধতা? সে যে কোনও পক্ষই নেয় না, প্রধানত পর্যবেক্ষণ করে যায়, তা কি তার দুর্বলতা, না জোরের জায়গা? তার ক্রমাগত দ্বিধা তার সম্পদ না বিপদ? রাস্তায় আঁকা এদিকের তিরচিহ্ন আর ওদিকের তিরচিহ্নের বিপরীতমুখী সারির মধ্যে দাঁড়িয়ে সে কোনদিকে চালিত করবে তার ঘুঁটি-জীবন? সত্যজিতের কাজ হল এই প্রশ্নগুলো তুলে ছুড়ে দেওয়া। এমনিতেই যে কোনও ব্যাপারে খুব নিশ্চিত হয়ে একটা কিছুকে বেধড়ক দণ্ডিত করা তাঁর ভাল ছবিগুলোর স্বভাবের বিরুদ্ধে। ‘প্রতিদ্বন্দ্বী’তে তিনি চারপাশের অবস্থায় রেগে ওঠেন, আগের দুটো ছবি কলকাতার টালমাটালের ভেতর করবেন না বলে অন্যত্র (এবং স্টুডিওর মধ্যে) শুটিং করেন যিনি (‘গুপী গাইন বাঘা বাইন’, ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’), তিনি একেবারে ক্যামেরা নিয়ে কলকাতার পথেঘাটে নেমে পড়েন, কিন্তু তা বলে কারও গায়ে ঢ্যাঁড়া দিয়ে ‘ভাল’ বা ‘খারাপ’ লিখে দেন না। অবশ্য একেবারে প্রতিটি ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয়।
তবে হরেদরে এই ছবি বলে, স্পষ্ট উত্তর দেওয়া যায় না, স্পষ্ট প্রশ্ন করা যায় কি না তাও বোঝা কঠিন, সমাধান অত সহজ নয়, হয়তো সম্ভবও না। ছবিটা এইজন্যেই রূঢ়, সে কোনও আশা দেখতে পাচ্ছে না, আশার কথা শোনাতেও আসেনি, চারপাশটা দেখে ঘেন্নায় নাকমুখ কুঁচকে আছে এবং রাগ উগরে দিতে চাইছে।
সিদ্ধার্থের প্রেমিকার বাবা তাঁর ছোটশালিকে বিয়ে করছেন, এটাকে এ ছবিতে প্রখর অন্যায় হিসেবে দেখা হয়। অথচ প্রেমিকা তার মা’কে হারিয়েছে সাত বছর বয়সে, কিছু না হোক তার বয়স এখন ২০-২১। ১৩-১৪ বছর বিপত্নীক থাকার পর, এখন মেয়ে প্রাপ্তবয়স্কা হয়ে যাওয়ার পর, একটা লোক কেন তার ছোটশালিকে বিয়ে করতে পারে না, বোঝা শক্ত। মেয়েটি বলে, ‘এক এক সময় মনে হয়, আমার হয়তো মেনে নেওয়া উচিত, এমন আর কী? আগে মাসিমা বলতাম, এখন সিমা-টা বাদ দিলেই হবে, কিন্তু তক্ষুনি মায়ের মুখটা ভেসে ওঠে।’ (লক্ষণীয়, সে বলতে পারত, ‘মাসি’টা বাদ দিলেই হবে, কিন্তু কথাটার মধ্যে সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার দ্যোতনাটা যোগ করে দেওয়া হয় সত্যজিতের অনবদ্য সংলাপ-রচনায়)। শেষ দৃশ্যে, কলকাতা থেকে নির্বাসিত সিদ্ধার্থ চিঠিতেও তাকে লেখে, ‘এখানে খুব যে আরামে থাকব তা মনে হয় না, তবে তোমার কষ্টর চেয়ে এ কষ্ট অনেক কম।’ সিগারেটখোর, অন্য লোকের সামনে অনায়াসে কাপড় ছেড়ে ফেলা নির্লজ্জা বেশ্যার বিপরীতে পবিত্র ও অপাপবিদ্ধা রমণী হিসেবে সিনেমায় যাকে গড়ে তোলা হয়েছে (ওই মহিলার বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার পরেই, রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে এই মেয়েটির ডাকে সাড়া দিয়ে অচেনা বাড়িতে ফিউজ সারাতে ঢুকে পড়ে সিদ্ধার্থ, ক্রমে সম্পর্ক গড়ে ওঠে— মনে রাখতে হবে, ওই মহিলাকেও সিদ্ধার্থ দেশলাই জ্বালিয়ে দিয়েছিল সিগারেট ধরাতে, এখানেও দেশলাইয়ের আলোতেই বারবার উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে অন্য নারীর অমলিন মুখ), সে এই কষ্ট ভুলতে দিল্লি চলে যাবে ঠিক করেছে, বান্ধবীর বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করবে। ঠিকই, বাবা যদি অন্য নারীকে বিয়ে করতেন তা তবু লোকের কাছে এবং মেয়ের কাছে কিছুটা গ্রহণযোগ্য হত, শালি ও জামাইবাবুর বিয়ের মধ্যে দিদির প্রতি ও বউয়ের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা পড়ে নেবেই রক্ষণশীল সমাজ, তবু এতে তার বাবাকে যে অবিমিশ্র ভিলেন বানানো হল, তা একটু বাড়াবাড়ি সরল-সিদ্ধান্ত মনে হয়। তবে হরেদরে এই ছবি বলে, স্পষ্ট উত্তর দেওয়া যায় না, স্পষ্ট প্রশ্ন করা যায় কি না তাও বোঝা কঠিন, সমাধান অত সহজ নয়, হয়তো সম্ভবও না। ছবিটা এইজন্যেই রূঢ়, সে কোনও আশা দেখতে পাচ্ছে না, আশার কথা শোনাতেও আসেনি, চারপাশটা দেখে ঘেন্নায় নাকমুখ কুঁচকে আছে এবং রাগ উগরে দিতে চাইছে।
এমনকী সত্যজিতের সর্বব্যাপী হিউমারের নিদর্শনও এ ছবিতে বেশ কম, এবং যেটুকু আছে তার অনেকটাই একটু আড়ে। যেমন ইন্টারভিউতে একজন জিজ্ঞেস করেন, ‘What made you give up Medicine? Did you suddenly lose interest in Medicine?’ আর উত্তরে সিদ্ধার্থ বলে, ‘No Sir, I lost my father.’
সিদ্ধার্থ ছবির গোড়ায় কত যে হাঁটে, তার ইয়ত্তা নেই। সারাদিন শুধু হেঁটে বেড়ায়। ছবির নাম দেখানোর পর থেকে আমরা বহুক্ষণ তাকে তার বাড়িতে ফিরতেই দেখি না। সে বাসে চড়ে, ইন্টারভিউ দেয়, দোকানে যায়, কফি হাউসে যায়, সিনেমা দেখতে যায়, ঘড়ি সারাতে দেয়, এসপ্ল্যানেডের একটা ছাউনিতে বসে সিগারেট ধরায়, বন্ধুদের হোস্টেলে যায়, আবার ফিল্ম ক্লাবের ছবি দেখতে যায়, আরও রাস্তায় হাঁটে, একেবারে সন্ধেবেলা বাড়ি ফেরে। (যে কোনও এমনি-দর্শক ভাববে, এ কী রে, একটা লোক হাঁটছে বসছে ঘুরছে আর আমি হাঁ করে তা-ই দেখছি? এ তো গল্প গড়ে তোলার কোনও চেষ্টা অবধি নেই!) ছবির ২৮ মিনিটের মাথায়, অর্থাৎ প্রায় আধঘণ্টা পরে, সিদ্ধার্থকে আমরা তার বাড়িতে দেখি। কারণটা খুব সহজ, এভাবেই এখানকার যৌবন কাটে, অন্তত বেকার যুবকদের যৌবন, তাদের করার কিছু নেই, যাওয়ারও বিশেষ জায়গা নেই। নিজের স্মৃতি, দিবাস্বপ্ন, হাবিজাবি চিন্তাস্রোত ছাড়া সঙ্গীও নেই। তাই ক্যামেরাও নায়ককে অনুসরণ করে চলে, কখনও তার চিন্তাদেরও, আর তার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে শহরটাকে দ্যাখে। গরগর করা ট্র্যাফিক তাকে ঘিরে ছুটে যায়, চারিদিকে দোকানপাট, নিয়ন সাইন, ফুটপাথের গ্লসি ম্যাগাজিন, অট্টালিকা, পানশালা অনেক কিছুর ওপরেই তার চোখ পড়ে, বা তাকে দেখতে গিয়ে আমাদের চোখ পড়ে যায়। কলকাতার রাস্তায় শুটিং করা ভয়ঙ্কর শক্ত, ক্যামেরা দেখলে মুহূর্তে লোক জমে যায়, তাই কখনও সত্যজিৎ কালো কাপড়ে ক্যামেরা মুড়ে ধৃতিমানকে অনুসরণ করতেন, কখনও আবার গাড়ির মধ্যে থেকে শট নেওয়া হত, কখনও পাঁউরুটি দেওয়ার ভ্যানগাড়িতে ক্যামেরাম্যান গুটিসুটি মেরে ক্যামেরা নিয়ে বসে থাকতেন— ধৃতিমানকে অ্যাকশনটা বুঝিয়ে দেওয়া হত, তিনি সেইমতো হাঁটতেন-চলতেন আর ভ্যান-চালককে একজন নির্দেশ দিতেন। অর্থাৎ, প্রায় দায়ে পড়েই এই ছবি কিছুটা গেরিলা-কায়দায় শুটিং হয়েছে, ফলে সত্যজিতের অন্যান্য ছবির যে লাবণ্যময় পরিপূর্ণতা, প্রতিটি কম্পোজিশনের গাণিতিক নির্ভুলতা, তা এখানে মানা হয়নি। না-হওয়াটাকে সত্যজিৎ তাঁর স্টাইলের অন্তর্গত করে নিয়েছেন। এই অপরিচ্ছন্ন সমাজের দলিল কেনই বা তকতকে পরিচ্ছন্ন হবে— এই তাঁর প্রশ্ন। এবং প্রকরণে রুক্ষতা এনে, বিষয়ের কর্কশতার সঙ্গে তা নিপুণ মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। ছবির চলন তেমন গল্পের ধার ধারে না, একটু খাপছাড়া। কখনও ক্যামেরা ট্রাইপডে চড়ে পুরোপুরি সুচিক্কণ, কখনও হাতে চড়ে কিছু-বেসামাল। ছবিতে অধিকাংশ সময়েই কাট হয় খুব দ্রুত, হুটহুট করে দৃশ্য শেষ হয়ে যায়, নায়িকা ‘চা খাবেন তো?’ বলতে না বলতেই আমরা দেখি নায়ক চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে, একটি দৃশ্যে নায়ক-নায়িকা পরস্পরকে ‘আপনি’ বলছে পরেরটাতেই ‘তুমি’, অর্থাৎ এর মধ্যে তাদের সম্পর্ক অনেকটা এগিয়ে গেছে। এমনকী সত্যজিতের সর্বব্যাপী হিউমারের নিদর্শনও এ ছবিতে বেশ কম, এবং যেটুকু আছে তার অনেকটাই একটু আড়ে। যেমন ইন্টারভিউতে একজন জিজ্ঞেস করেন, ‘What made you give up Medicine? Did you suddenly lose interest in Medicine?’ আর উত্তরে সিদ্ধার্থ বলে, ‘No Sir, I lost my father.’ অথবা সিদ্ধার্থের বন্ধু চাইনিজ রেস্তরাঁয় গিয়ে প্রথমেই প্রশ্ন করে, ‘Do you serve monkey’s brain here?’ কিংবা সুইডিশ ছবিতে যৌনতা না দেখতে পেয়ে সিদ্ধার্থ ও তার বন্ধুর মুখ বাংলার পাঁচ হয়ে যায়। এর অনেকগুলোরই ঘাড়ে ঘাড়ে এমনভাবে পরের সংলাপ বা ঘটনা এসে পড়ে, হাসব কি না বুঝতে বুঝতেই আমরা অন্যদিকে ঝুঁকে যাই। সমস্ত মিলিয়ে, একটা ডোন্ট-কেয়ার এবড়োখেবড়ো ভাব ছবিতে ছড়িয়ে থাকে। কলকাতা শহরটার মতো, এই শহরে ওই সময়টার মতো, এবং ওই সময়ে বেঁচে থাকা এক যুবকের মতোই, ছবিটা এক-গড়ানে নয়, বরং কিছু জায়গায় খোঁচ-ওঠা ও পালিশহীন, কিছু জায়গায় বার্নিশ করা। একদম টাটকা সমকাল ও নিজের শহর নিয়ে ছবি করতে গিয়ে সত্যজিৎ চাবুক-স্মার্ট, অভিনব এবং বেশ দর্শক-উদাসীন। এমনিতে তিনি বরাবর বলেন ভারতে ছবি করতে গেলে গল্পের আশ্রয় নিতেই হবে, কাহিনির কাঠামো তিনি গ্রহণ করেনও, কিন্তু তা বলে সত্যি সত্যি ‘তারপর অমুক হইল’-খচিত গল্প বলার দায় তাঁর কোনওদিনই নেই। অপরাজিত জলসাঘর কাঞ্চনজঙ্ঘা মহানগর নায়ক অরণ্যের দিনরাত্রি ছবিতে কতটুকুই বা প্লটের টান আছে? কিছুটা আঁকবাঁক চড়াই-উতরাই থাকলেও, বেশিরভাগ সময়েই জরুরি হয়ে উঠেছে মানুষ, তার মনের সহস্র স্তর। তাঁর ছবিতে ক্রাইসিস ঘনায় অবশ্যই, কিন্তু তা প্রায়ই সাধারণ দর্শকের কাছে বিরাট সঙ্কট বলে মনে হয় না। ‘প্রতিদ্বন্দ্বী’তেও ক্রাইসিস আছে, সিদ্ধার্থ চাকরি পাবে কি না— এটাকে যদি দর্শকের কাছে একটা বাপরেবাপ সাসপেন্স বলে ধরা যায়। কিন্তু চাকরি না পেলে তার বিয়ে হবে না, অমনি নায়িকার বাবা তাকে অন্যের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেবে, যার সঙ্গে নায়কের তীব্র ঢিশুম-ঢিশুম বহমান, এ ছবি তো সে মেজাজে চলছে না। তাই সিদ্ধার্থ চাকরি না পেলে দর্শক ললাটে করাঘাত করে বসে পড়বে না। যতই সত্যজিৎ বলুন, বাণিজ্যিক ব্যাপারস্যাপার মেনে, দর্শকের মন বুঝেই এ-সমাজে ছবি করতে হবে, আসলে তিনি প্রায় কক্ষনও বাণিজ্যিক শর্তকে পাত্তাই দেননি। এই ছবিতেও তিনি দর্শককে ডিসটার্ব করতে এতটুকু পিছপা হন না। যেমন টাটা সেন্টারের ছাদে বেড়ালেও সিদ্ধার্থ ও প্রেমিকার ঝুঁটি আঁকড়ে ধরে ময়দানের রাজনৈতিক সমাবেশের ক্ষুব্ধ গর্জন, যেমন কোনও দৃশ্যে সিদ্ধার্থ একটা দেওয়াল-টেওয়াল দেখে হেলান দিলেই ক্যামেরা স্বল্প এগিয়ে গিয়ে তাকে কোণঠাসা করে ফ্যালে এবং ঠায় তাকিয়ে থাকে, ওইভাবেই সমকালকে পলকহীন দেখেশুনে খেপে গিয়ে আড়মোড়া-পাকানো দর্শকের মুখে অনেকটা উগ্র আরক ছুড়ে মারতে এ-ছবিতে সত্যজিৎ দিব্যি স্বচ্ছন্দ।
তবে যতই ঝাঁকুনি ভালবাসুন, প্রথম দৃশ্যটায় ছবি যে নেগেটিভ হয়ে গিয়েছিল, সেটুকু রেখে ছেড়ে দেওয়ার বান্দা সত্যজিৎ নন, কারণ তিনি পুরনো স্কুলের ছাত্র, যা মনে করে: চমকে দেওয়া কাণ্ড একবার করলে, অন্তত তিনবার করো, তবেই দর্শক সেটাকে স্টাইল বলে গ্রহণ করবে। নইলে ভাববে খাপছাড়া, প্রক্ষিপ্ত। পরেরবার ছবি সহসা নেগেটিভ হয়ে যায়, যখন নার্স-কাম-দেহোপজীবিনী ব্রেসিয়ার ও শায়া পরনে সিদ্ধার্থের হস্তধৃত দেশলাইয়ে সিগারেট ধরাতে নিচু হয়। অবশ্য সমালোচকের মনে কু থাকলে অন্য ভাবনাও আসতে পারে। এ শটটাকে নেগেটিভ না করলে সত্যজিৎ সেন্সরের কোপে পড়তে পারতেন। অথচ এটা জরুরি, কারণ সিদ্ধার্থ মহিলার উপচে-ওঠা স্বাস্থ্যের লোভ পেরিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে তার মূল্যবোধের জোর বোঝানো যাবে। এবার, সারা ছবিতে শুধু একটা শটকে নেগেটিভ করলে তো মুশকিল। এটাকে জাস্টিফাই করা যায়, যদি আরও অন্তত দুটো জায়গায় শট বা সিন নেগেটিভ করে দেওয়া যায়, আর ভাব দেখানো যায়, ছবি জুড়ে স্টাইল করেছি। হতেই পারে, এই স্ট্র্যাটেজিতে পিছু-ফিরে একদম গোড়ার সিকোয়েন্সটাকে নেগেটিভ করা হয়েছে, আর স্বপ্নদৃশ্যের কিছু শটকে— যেখানে সমুদ্রসৈকতে ইন্টারভিউ বোর্ড বসে আছে, বা টুনুর দিকে ফায়ারিং স্কোয়াড রাইফেল তাক করছে, টুনু গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়ছে। তাহলে বাবার মৃত্যুকে দুঃস্বপ্নের মতো দেখাল, তারপর দুঃস্বপ্নোচিত এক নৈতিক ঝঞ্ঝাটে পরেরবার ছবি নেগেটিভ হল, তারপর সত্যিকারের দুঃস্বপ্নে এটা প্রয়োগ করা হল। একটা প্যাটার্ন তৈরি হল, দুঃখ পাপ অন্যায়কে চিহ্নিত করে। তবে পিছন ফিরে কী কারণে কী প্রয়োগ করা হয়েছে তা দেখাটা আসলে সমালোচকের কাজ না, শুধু এন্ড-প্রোডাক্টটা দেখেই বিচার করতে হবে (এবং তা অনুযায়ী বলতেই হবে, এ ‘নেগেটিভতা’ ছবিকে বিরাট কিছু ধারালো করেনি), তাই এটা নেহাৎ ফক্কুড়ি মারলাম।