ছোট্ট জোনাকি
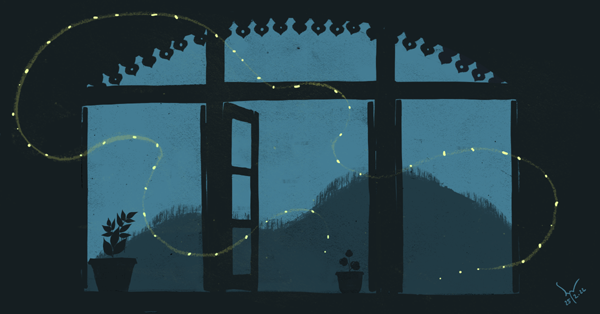
 রাস্কিন বন্ড (Ruskin Bond) (February 26, 2022)
রাস্কিন বন্ড (Ruskin Bond) (February 26, 2022)জঙ্গলের কথা মনে হলেই আমরা শান্ত, নিশ্চুপ একাকিত্বের কথা ভাবি— অবশ্য যখন বাঘের হুংকার বা হাতির ডাক শোনা যায় না। জঙ্গলে কিন্তু সবসময়েই এর চেয়ে অনেক সূক্ষ্ম কিছু শব্দ শোনা যায়, যদি জঙ্গল-ভবঘুরে একটু সংবেদনশীল মানুষ হন।
বহু বছর আগে, মুসৌরি শহরের প্রান্তে, জঙ্গলের কিনারায় একটা ছোট্ট কটেজে থাকতাম আমি। ওক আর মেপ্ল গাছে ছাওয়া একটা সরু, খাড়াই ফুটপাথ ধরে আমার লাল-টালির বাড়িতে নেমে যেত হত, যে-বাড়িতে আমি বেশ কিছু বছর কাটাই।
গ্রীষ্মকালের গোড়ার দিকের কথা। জানালা খুলতেই শয়ে-শয়ে ঘুর্ঘুরে পোকার কর্কশ কোরাস আমাকে জানিয়ে যেত যে আর কিছুক্ষণ পরেই বৃষ্টি নামবে। পা দিয়ে তাদের কাঁপতে-থাকা শরীর ঘষে-ঘষে এই শব্দ তৈরি করে ঘুর্ঘুরে পোকারা। গাছের গায়ে এমনভাবে লেগে থাকে যে তাদের দেখা পাওয়া দায়, কিন্তু গোটা গরমকাল জুড়ে ওই অবিরত, সমবেত সঙ্গীতে তাদের উপস্থিতি বেশ বোঝা যায়।
যে-সময়ের কথা বলছি, তখনকার দিনে আমি প্রচুর হাঁটতে পারতাম, এবং হেঁটে-হেঁটে পাহাড়ের একদম নিচে নালাটা অবধি নেমে যেতাম। কয়েক শতকের বহমান ধারায় মসৃণ হয়ে ওঠা নুড়ি আর পাথরের উপর দিয়ে চলা এই নালাটার নিজস্ব কিছু শব্দ ছিল। কখনও, এক পাথর থেকে অন্য পাথরে লাফিয়ে বেড়ানো ফর্কটেল দেখতে পেতাম; সূর্যস্নাত নালাটার উপর উড়ে বেড়ানো গঙ্গাফড়িংগুলোকে নিঃশব্দে ধাওয়া করে যেত পাখিটা। ম্যাগপাইগুলো কিন্তু মোটেই নির্বাক ছিল না; মহা আড্ডাবাজ ওই পাখির দল উইলো, ওয়াটার-উড আর আখরোট গাছের নুয়ে পড়া ডালে বসে বেজায় চিল্লামিল্লি করত। আর নালার পাড়ের কাঁটাঝোপে, জংলি র্যাস্পবেরি আর ব্ল্যাকবেরির ঝাড়ে খেলে বেড়াত ছোট পাখিরা—ওয়্যাগটেল (দোয়েল) আর ফিঞ্চ।
নালার ধারে একটা ছোট্ট টিলায় একা দাঁড়িয়ে থাকত একটা পাইন গাছ, আর আমি মাঝে-মাঝে, নোটবুক আর বল-পয়েন্ট পেন হাতে, তার তলায় শুয়ে-বসে সময় কাটাতাম, কখনও কবিতা লিখতাম, কখনও কোনও গল্পের অংশ, আর কখনও শুধুই বা ‘রিমেমব্রেন্স অফ থিংস পাস্ট’। কিন্তু আমি প্রুস্ত নই। আমার গুরু ছিলেন থরো এবং রিচার্ড জেফরিস। ‘ওয়ালডেন’ এবং ‘দ্য স্টোরি অফ মাই হার্ট’ প্রায়শই আমার সঙ্গী হত।
পাহাড়ি ঘাসের ঢালে বসে, পাইন গাছের ডালে খেলে বেড়ানো মৃদুমন্দ বাতাসের আমেজে একটা কবিতা লেখা– এ যেন শুধু লেখা নয়, কবিতাটার মধ্যে বাঁচা। আজকে, এত বছর পরে ফিরে দেখলেও আমি যেন ওই বাতাসের ছোঁয়া অনুভব করতে পারি, আর গোটা জঙ্গলের গানটা যেন শুনতে পাই, আর সেটাই আমার প্রতিদিনের, আমার জীবনের কবিতা।
আমার বারান্দার আলো জ্বলছে। জানলা থেকে আমি কটেজের পেছনদিকের বাগানটা দেখতে পাচ্ছি। আমার ডালিয়া মূলগুলোকে পিষে ফেলার মতো কোনও শজারু নেই, কিন্তু তীরবেগে বাগানে ঢুকে পড়ল সেই ভীতসন্ত্রস্ত বার্কিং ডিয়ার। লুকিয়ে থাকার জায়গা খুঁজতে সে একবার এদিকে ছোটে, আর একবার ওদিকে। শেষে আমার কাঠের শেডে ঢুকে পড়ে একরাশ জ্বালানি কাঠের গাদার পেছনে গিয়ে দাঁড়ায়; কাঁপে। কিন্তু সেখানেও কি ও নিরাপদ?
সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে, পূর্ণিমার চাঁদ যখন ল্যান্ডর-এর চুড়োর ওপর উঠত আর দেওদার গাছগুলোকে আরও ছায়া-ছায়া দেখাত, আমি মাঝে-মাঝে আমার নৈশভ্রমণে বেড়িয়ে পড়তাম, আর তখন শব্দগুলো হয়ে উঠত আরো একটু চাপা, আরো একটু রহস্যময়। বুড়ো ওকের গভীর কোটরে নিজের সঙ্গে কথোপকথনে ব্যস্ত একটা প্যাঁচা। নিশাচর নাইটজারের আলগা বক্তব্য, যেন টেবিলে টোকা মারা… একটা বার্কিং ডিয়ার। আজ রাতে এর ডাক যেন একটা জরুরি, দিশেহারা আর্তনাদ। শিকারির হাত থেকে পালাতে ব্যস্ত এই ভীত হরিণ।
আর কয়েক মুহূর্তেই শুনতে পেলাম একটা লেপার্ডের খসখসে কাশি। ভয় দেখাতে হুংকার করে না লেপার্ড। বেশির ভাগ বেড়ালের মতই, তা সে ছোট হোক বা বড়, লেপার্ড নিঃশব্দে শিকারকে ধাওয়া করে। তবুও, ওই বিশেষ কাশি আমি খুব চিনি।
আমার বারান্দার আলো জ্বলছে। জানলা থেকে আমি কটেজের পেছনদিকের বাগানটা দেখতে পাচ্ছি। আমার ডালিয়া মূলগুলোকে পিষে ফেলার মতো কোনও শজারু নেই, কিন্তু তীরবেগে বাগানে ঢুকে পড়ল সেই ভীতসন্ত্রস্ত বার্কিং ডিয়ার। লুকিয়ে থাকার জায়গা খুঁজতে সে একবার এদিকে ছোটে, আর একবার ওদিকে। শেষে আমার কাঠের শেডে ঢুকে পড়ে একরাশ জ্বালানি কাঠের গাদার পেছনে গিয়ে দাঁড়ায়; কাঁপে। কিন্তু সেখানেও কি ও নিরাপদ?
শিকার করে শিকারকে খাওয়াই লেপার্ডের ধর্ম, কিন্তু আজ রাতে আমি অসহায় হরিণের পক্ষে। আমার কোনও বন্দুক নেই; ওই জঘন্যতা সহ্য করতে পারি না। কিন্তু যথেষ্ট শব্দ করে লেপার্ডটাকে ঘাবড়ে দিতে পারি। দেরাজে কিছু শব্দবাজি আছে। আমি একটা গোটা সুতো ধরে বাজি জ্বালিয়ে বাগানে ছুড়ে দিলাম। গোটা জঙ্গলের নিঃশব্দতা ভেঙ্গে খানখান করে, মেশিনগানের মতো শব্দ করে বাজি ফাটল।
লেপার্ডটা কি চলে গেছে? জানি না। কিন্তু আর কিছুক্ষণেই, বার্কিং ডিয়ার তার নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে একছুটে একটা ডগ-রোজের ঝোপে ঢুকে গেল। কোনও লড়াইয়ের শব্দ নেই। বোধহয় আজ রাতের জন্য হরিণটা বেঁচে গেল; আজ একটা রাতের জন্যেই সই।
প্রায় বছর তিন-চারেক এই কটেজে থাকার পর, লেপার্ডের চেয়ে বহুগুণে ভয়াবহ এক শিকারি হঠাৎ একদিন সেখানে এসে হাজির হয়। তারা পি ডব্লিউ ডি-র সড়ক-তৈরি সংস্থা, এবং আমার কটেজের সামনের বাগানের একদম উপর দিয়ে রাস্তা তৈরি করতে এসেছে তারা, যে রাস্তা পাহাড়ের অন্য প্রান্তে আরো গুরুত্বপূর্ণ কিছু রাস্তায় গিয়ে মিলবে। তারা নিয়ে এসেছে বিস্ফোরক, বুলডোজার এবং রাস্তা-কর্মীদের একটা গোটা সৈন্যদল। আমাকে সরে যেতেই হবে। সরে যেতে হবে জঙ্গলের কিছু অংশকেও। ওক, আখরোট, পাইন, মেপ্ল, সব গাছ নুয়ে পড়ে কুড়ুল আর ইলেক্ট্রিক করাতের আঘাতে। পাখিরা উড়ে চলে যায় অন্য জায়গায়। ছোট জানোয়ারেরা পরিযায়ী হয়ে ওঠে। এমন কি শজারুরাও বাগান ছেড়ে চলে যায়, কেননা ডালিয়া আর গ্ল্যাডিওলি সাফ করে দেওয়া হয়েছে।
আমি পাহাড়ের আরও উপরের দিকে উঠে আসি। আরও রাস্তা। নিস্তার নেই। লাল টিব্বা নামের পাহাড়চুড়োয় ওঠার বড়রাস্তার ধারে একটা বড় বাড়ির এক অংশে একটা ছোট অ্যাপার্টমেন্ট খুঁজে নিই। পাহাড়ের মাথায় অনেক জঙ্গল রয়ে গেছে, কিন্তু এখানে শুধু রাস্তা আর রাস্তা; দিল্লি, হরিয়ানা, পাঞ্জাব থেকে আসা টুরিস্টে বোঝাই শয়ে-শয়ে গাড়ি ধুঁকতে-ধুঁকতে, হর্ন বাজাতে-বাজাতে, তড়িঘড়ি চুড়োয় উঠতে চলেছে, শুধু চিরন্তন শুভ্র বরফকে এক ঝলক দেখার জন্যে। খুব ভোরে না উঠলে তার কিছুই প্রায় দেখা যাবে না। দুপুরের মধ্যে মেঘ আর কুয়াশায় উঁচু রেঞ্জের পর্বতমালা ঢেকে যায়। পাঞ্জাব থেকে আসা এক টুরিস্টকে শুনি তাঁর গাইডকে তিরস্কার করে বলতে— ‘তুমি আমাদের এত অবধি নিয়ে যে এলে, আমরা কী দেখতে পেলাম? একটা কবরখানা!’ পাহাড়ের উত্তরদিকের ঢালে পুরানো ল্যান্ডর সেমেটরির কথা বলছিলেন উনি; শ্বেতশুভ্র পাহাড়চূড়া দেখার জন্য যা এখানে শ্রেষ্ঠ স্থান। কিন্তু বুড়ো কেয়ারটেকার ছাড়া আর কে-ই বা দেখে সে দৃশ্য; কবর-অধিবাসীরা যে সবাই এখনও ঘুমোচ্ছেন।
রাতে ভ্রমণবিলাসী এবং গাড়িরা সব চলে যায়, চাঁদের দিকে তাকিয়ে চেঁচাতে থাকা একটা কুকুর ছাড়া নিচের রাস্তা হয়ে ওঠে সুনসান। আজ রাতটা বেশ গরম, আমার জানলা খোলা। ঘরের সব বাতি নেভানো। রাতের বাতাসে ভেসে আসে একটা জোনাকি, ঘরের আনাচে-কানাচে ছোট-ছোট জায়গাগুলো সে আলোকিত করে তোলে। পুরনো কটেজ ছেড়ে বেরিয়ে আসার পর থেকে আমি জোনাকি দেখিনি। এ যেন পুরনো বন্ধুর আসা; নিশ্চুপ রাতের আঁধারে এক ক্ষুদ্র তারা নেমে এসেছে আমাকে দেখতে।
কেন জানি আমার মনে হয়ে এই জোনাকি আমাকে আমার পুরনো আস্তানায় ফিরে যাওয়ার কথা বলছে।
গানে ভরা জঙ্গলটায় হাঁটার পক্ষে এখন আমি বড্ড বুড়ো হয়ে গেছি, কিন্তু জঙ্গলকে আমি সম্মান জানিয়ে যাব আমার মতো করে, আমার লেখা এই শব্দগুলোর মাধ্যমে। ততদিন, আসতে থাকো, ছোট্ট জোনাকি!
ছবি এঁকেছেন সায়ন চক্রবর্তী
পূর্ববর্তী লেখা পরবর্তী লেখা
Rate us on Google Rate us on FaceBook





