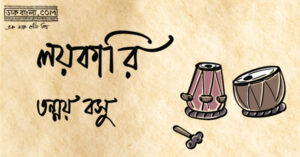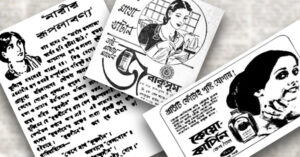শ্রী শিক্ষায়তন কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে যোগ দিয়ে একদিকে যেমন একটা পাকা চাকরি হল, তার সঙ্গে উপরি উপার্জনে এল কিছু বিরল সম্পর্কের উপহার। এমনই এক যোগাযোগে এলেন উমাদি, উমা সিদ্ধান্ত। বিএড ডিপার্টমেন্টের ঘরে আলো করে বসে থাকতেন এবং সকলের থেকে আলাদা। শুধু সাজেই নয়, আচরণ এবং কাজেও। ১৯৮৩ থেকে ১৯৯৫— এই বছর বারো, এমন এক সম্পর্কে তাঁকে নিকটে পেলাম, যার পোশাকি নাম ‘সহকর্মী’। বয়সে প্রায় পঁচিশ বছরের বড় অথচ একেবারে সমকালীন! বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য পাশ করা, পড়ুয়ার গন্ধমাখা হিলহিলে শরীরে তাঁর কাছটিতে গিয়ে বসতাম, সময় পেলেই। আদতে মানুষটা আমি কিছু উদাসীন। নিজের তালেই থাকি, কিন্তু কাউকে মনে ধরলে আর রক্ষা নেই! খানিকটা ওই পাগলের সাঁকো নাড়ানোর মতো। আমার টনক নড়ে ওঠে এক অবিমিশ্র কৌতূহলে; কী খায়, কেমন করে ঘুমায়, ঝগড়া করবার সময়ে কী ভাষা বের হয়, কখন রাগ করে বা বন্ধুবৃত্তে কারা— এমন সব অকারী প্রশ্নে! আমার নিজস্ব স্কেলে চলতেই থাকে মাপ নেওয়া। ফলে উমাদিকে ঘিরে আমার যে নিবিড় ঔৎসুক্য গড়ে উঠল, তার কারণ তিনি নিজেই; মানে ওই চলে-ফিরে বেড়ানো এবং কথা-কওয়া মানুষটি। প্রতিদিন চোখের ওপর দেখা উমাদি এবং নানা সূত্রে শোনা গল্পের উমাদিকে নিয়ে বেশ একটা রসায়ন তৈরি হতে লাগল মনের মধ্যে।
২
যা সকলের চোখে পড়ত, তা তো আমার চোখও এড়াত না; যেমন গুঁড়ো রঙের টিপ আর ডান হাতের কবজিতে চেন আঁটা সোনা-বাঁধানো পাথরের গয়নাটি। পাশে বসার সুযোগে নজর করলাম তাঁর নিজের বানানো ব্রোঞ্জের পানের ডিবেটিও। কুট্টি-কুট্টি করে সাজা পানের পাশে নিপুণ যত্নে রাখা হালকা গোলাপি-রঙা পাউডারের মতো কেয়া-খয়ের, কমলালেবুর খোসার ঝুরি এবং চিলতে করে কাটা জাহাজি সুপারি। ভাবতাম, অমন পানখানি মুখে চেপে কথা বলেন বলেই বোধহয় হাসিটিও এত মধুর হয়ে ঠোঁটে লেগে থাকে। হাতের গয়নার পাথরগুলো যে নবরত্ন, তাও জানতে পারলাম যখন বললেন, সোনা গলিয়ে নিজেই সেটি বানিয়েছেন। গলায় পরা নানা মাপের দু’তিনটে মালার মধ্যে একটা সরু চেনে ছোট্ট লকেট, অন্যটি হালকা বাদামি রঙের বৈজয়ন্তী বীজের মধ্যে-মধ্যে সোনার পুঁতি দিয়ে গাঁথা একটু বড় মালা এবং আরও একটু বড়টিও নিজে বানানো রুপোর পুঁতি দিয়ে গাঁথা। সেগুলি এত সরু যে, তিনখানি মালা জড়াজড়ি করে গলায় ঝুললেও তা বাড়াবাড়ি মনে হত না কক্ষনো।
কপালের ফোঁটায় হালকা হলুদ রঙটার কথা জিজ্ঞেস করে জেনেছিলাম যে, চিত্রী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় তাঁকে যে কয়েক বাক্স গুঁড়ো রং উপহার দিয়েছিলেন, সেই আর্থ কালারগুলি থেকে এই রংটি উনি সরিয়ে রেখেছেন প্রতিদিন কপালে পরবার জন্য। সারাদিনের দৌড়ঝাঁপেও একটুও যা ঘেঁটে যেতে দেখিনি কোনওদিন। ছোট্ট একটা বেতের ঝুড়িতে করে যে-টিফিন আনতেন, সেটিও দেখবার মতো। আর খাবারগুলোও তেমন অভিনব এবং সুস্বাদু। নিজের দেহরেখা নিয়ে শুধু যে সচেতন ছিলেন তাই নয়, ভীষণ ভালও বাসতেন নিজের প্রতিটি অঙ্গের যত্ন নিতে এবং তা সাজিয়ে তুলতে।

বরাবর দেখেছি, হালকা রঙের তসরের শাড়ি পরতে। খুব বর্ষায় যে সিন্থেটিক শাড়ি পরতেন, সেটাও যে কী অপূর্ব ফুলছাপে ভরা! বলতেন, আমার শ্যামলা রঙে এইসব শাড়িই ঔজ্জ্বল্য আনে। কৌতূহল চাপতে না পেরে, একদিন জিজ্ঞেসই করে ফেললাম যে, আপনি তো স্লিভলেস ব্লাউজ পরেন, কিন্তু শাড়ির কুঁচির ওপর ওই ট্যাসেলটা কোথা থেকে আসে! ওটা কী ব্যাপার! মিষ্টি হেসে বলেছিলেন, কাল বলব। পরদিন ওঁদের স্টাফরুমে ঢুকতেই পাশে বসিয়ে, ব্যাগ থেকে বের করে একটি ব্লাউজ দেখালেন। এমনভাবে বানানো যে, আলাদা করে আর অন্তর্বাস পরতে হবে না। সেটি গায়ে গলিয়ে বক্ষবন্ধনীটি টাইট করা হবে ওই ট্যাসেল দেওয়া সুদৃশ্য দড়ি দিয়ে। নমুনাটি হাতে দিয়ে বলেছিলেন, সকলের গায়ে মানাবে না, ‘সুঠাম-স্তনী’ হতে হবে। এই ব্লাউজের নক্সাটিও আমার কাছে উমাদির এক বিশেষ সিগনেচার। এখনও বিস্মিত হয়ে ভাবি, নিজের দেহকেও যে কতটা বুঝে নিয়ে ভালবাসতে হয়, তারও উদাহরণস্বরূপ ছিলেন উমাদি। আর সবটাই করতেন অবলীলায় এবং অনায়াসে। প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য, দু’ক্ষেত্রেই সমানভাবে চলত তাঁর শিল্পনির্মাণ। মননে এবং যাপনে, নিপুণতার এমন এক উপাসক ছিলেন বলেই এত সুদৃঢ় ছিল তাঁর আত্মবিশ্বাস। আমরা যে কত সাধারণ এবং নাগালে পাওয়া গড়পড়তা ধাঁচাটা নিয়েই কীভাবে অন্ধ হয়ে বাঁচি, সেটা বার বার বুঝেছি উমাদির সঙ্গ করে।
নিপুণতার উপাসক বলছি এই কারণে যে, এই যাপন তাঁর কাছে ঠিক আয়োজন করে বাঁচা বা লোক দেখিয়ে বিশিষ্ট হবার আয়াস ছিল না। তাঁর স্বামী, অধ্যাপক শ্রী সুনীল সিদ্ধান্ত চলে যেতেই আর কোথাও কিছুই বদলাল না; কিন্তু আর্থ কালারের সেই টিপটি বদলে হয়ে গেল চন্দনের ফোঁটা। আর এক রকম বদল দেখেছিলাম, পায়ে চোট লাগাতে। লাঠি নিয়ে বেশ কিছুদিন চলতে হয়েছিল। কিন্তু লাঠিটিও হয়ে উঠল কারুকাজময়; মুঠোয় ধরা লাঠির মাথাটিতে সেঁটে বসল কাঠ কুঁদে বানানো এক ময়ূর। ঠিক এমনই ম্যাজিক ঘটেছিল টলিক্লাবে তাঁর নাতির বউভাতে। নাতবউ এবং নিজের গহনাগুলিও সব নিজে হাতে বানিয়ে ছিলেন তিনি। সাদা কড়িয়াল বেনারসির সঙ্গে অমূল্য নকশার সেই সব গহনায় সাজা উমাদিকে দেখা সত্যিই এক অভিজ্ঞতা। সেই সঙ্গে গামছা এবং কলাপাতা দিয়ে টেবিল সাজিয়েছিলেন; লালপেড়ে শাড়ি, সোলার কদম আর টাটকা জুঁইয়ের মালা দিয়ে সাজানো নানারকম মণ্ডপে অতিথি আপ্যায়ন করেছিলেন তিনি। ধনসম্পদের আধিক্য কখনওই তাঁর প্রখর সম্মানবোধ এবং রুচির পোক্ত বেড়াটিকে লঙ্ঘন করতে পারেনি কোথাও।


সম-মান শব্দটিকে অন্যভাবে দেখেছিলেন উমাদি। তাই সকলের সঙ্গে মিশে গিয়েও তিনি ছিলেন একেবারেই ব্যতিক্রমী। আমি যে তাঁর গা ঘেঁষে থাকতাম, সে কি শুধুমাত্র ব্লাউজের নকশা আর স্নানের আগে সাবানের বদলে মাড-প্যাক মাখার তরিকা শিখতে! সেটাও যেমন ছিল, তার সঙ্গেই ছিল, ক্রমে তাঁর ভাস্কর হয়ে ওঠার গল্পগুলিও। গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে পড়া আমার চিত্রী বাবা অশোক মুখোপাধ্যায়ের সতীর্থ ছিলেন তাঁর মাস্টারমশাইরা। বালিকা বয়সে বাবাকে হারালেও গল্পগুলোয় আসা-যাওয়া করা বাবার বন্ধুদের নাম— রথীন মৈত্র, গোপাল ঘোষ, প্রদোষ দাশগুপ্ত— উমাদির মুখে প্রায়ই আনাগোনা করত। উমাদিকে ঘিরে কথায়-কথায় আমিও যেন ঘুরে বেড়াতাম ওই সময়ের আশে-পাশে এক অদেখা শিল্পচত্বরে।
তাঁর সহপাঠী শর্বরী রায়চৌধুরী, বিপিন গোস্বামীদের মতো উমাদিও তখন প্রথিতযশা। অনেকগুলি পুরস্কার পেয়েছেন; ভিসুয়াল লিটারেসি নিয়ে অসাধারণ এক কাজ করে শিক্ষাবিদ হিসেবেও NCERT থেকে পেয়েছেন স্বীকৃতি। দূরদর্শনের নানা অনুষ্ঠানেও ভেসে উঠত তাঁর আলাপচারিতা। বছরের-পর-বছর তাঁর ডাকেই এক্সটারনাল শিক্ষক হয়ে পরীক্ষা নিতে এসেছেন প্রখ্যাত কোলাজ শিল্পী বি আর পানেসর। সত্যি কথা বলতে, কলকাতার বৌদ্ধিক মহলে যে শ্রী শিক্ষায়তন কলেজের নামটিও ছড়িয়ে পড়ে, তার অনেকটাই কিন্তু উমাদির খ্যাতিতেই। আর এই সুনাম এবং খ্যাতি উমাদি পেয়েছিলেন তাঁর নিজের ক্রমাগত অভিনিবেশ এবং উৎকর্ষর জোরে। রিফ্লেক্টেড গ্লোরিতে আভাসিত হয়নি তাঁর অস্তিত্ব। অত্যন্ত শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর অগ্রজ মীরা মুখোপাধ্যায়কেও দেগে দেওয়া হত ‘মহিলা’ ভাস্কর বলে। মীরা মুখোপাধ্যায়ের তীব্র শক্তি এবং ব্যক্তিগত জীবনের ভাঙন— দুটিকেই যেন সবলে এড়িয়ে ছিলেন উমাদি। এই মর্মে সমালোচনাও হত তাঁর ছোট মাপের কাজ নিয়ে যে, ওগুলি ‘মনুমেন্টাল’ নয় ‘মিনিয়েচার’ মাত্র। একটি আন্ডার গ্র্যাজুয়েট কলেজের বিএড বিভাগের আর্ট টিচার হওয়ায় তাঁকে বলা হত ‘ক্র্যাফট’ শেখান। উমাদির কানে এসবের কিছুটাও কি যায়নি! কিন্তু উনি ছিলেন একেবারেই ওঁর মতো; নিজস্ব বিশ্বাসে অনড়।

যতীন দাস পার্কে তাঁর কাজের প্রদর্শনী দেখে অভিভূত হয়ে যান রামকিঙ্কর; সরকারি উদ্যোগে রাস্তার ওপর রাখাও হয় তাঁর একটি কাজ। আবার মেট্রো স্টেশন তৈরির সময়ে সরকারি উদ্যোগেই সরিয়েও দেওয়া হয় সেই কাজটি। তখনও কোনও সোচ্চার প্রতিবাদ বা লবিবাজি করেননি তিনি। বকুলবাগানের সর্বজনীন দুর্গাপুজোয় প্রথম যে-শিল্পী এগিয়ে এসে প্রতিমা গড়েন, তিনিও তো উমাদি! চিত্রী করুণা সাহার উদ্যোগে যখন একটি মহিলা চিত্রী-ভাস্কর গোষ্ঠী গড়ে তোলা হয়েছে শানু লাহিড়ী, সন্তোষ রোহতাজ্ঞী, শ্যামশ্রী বসু, অঞ্জলি এলা মেনন প্রমুখদের নিয়ে, তাতেও সাগ্রহে যোগ দিয়েছেন তিনি। সংবাদপত্র, দূরদর্শন সবেতেই প্রচারিত হয়েছে তাঁর নাম একমাত্র মহিলা ভাস্কর হিসেবে। তাঁদের কাজগুলি উচ্চপ্রশংসিত হওয়ায়, দেখতেও গিয়েছি সেসব প্রদর্শনী। তখনও উমাদি যেমন তা গ্রহণ করেছেন, একই স্থিরতায় বহনও করেছেন সে-দুঃখ, মতৈক্য না হওয়ায় যখন ভেঙে গেছে সে-দলটি। একক থাকার এই এক দায়িত্ব যে, সব অবস্থায় নিজের কাজটি চালিয়ে যেতে হয়। আর উমাদি সেটাই বুঝেছিলেন সর্বতোভাবে।
যে-আভিজাত্যের মোড়কে বড় হয়েছেন উমাদি, সেখানে চাকরি করতে আসাটাই একটা বাতুলতা। উদ্বাস্তু হয়ে আসা মেয়েদের চাকরি করার একটা ‘স-টীক’ অর্থ সমাজ তবু খুঁজে পেয়েছিল; কিন্তু ‘ঘরে-বরে’ বিয়ে হওয়া মেয়ে আবার চাকরি করবে কেন! শ্রী শিক্ষায়তনে পড়াতে না এলে বুঝতেই পারতাম না যে, বিশেষত সর্বস্তরের মেয়েদের মুক্তির দাবিটা কী ও কেমন! ফলে পেইন্টিং বা বাটিক নিয়ে না পড়ে ভাস্কর্য নিয়ে পড়াটা যেমন ছিল তাঁর একদিকের লড়াই, তেমনই নিজের পছন্দের একটি জীবনে টিকে থাকতে গেলে অন্তত কলেজ লেভেলের একটি চাকরিও তাঁর পক্ষে জরুরি ছিল। অন্য কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে ইচ্ছে করেনি? এমন প্রশ্ন করলে বলেছেন, ঠাঁইনাড়া হয়ে থাকতে মন চায়নি এবং কলকাতায় থাকবার সুবাদে স্বাধীন ভাবে অনেকটা সময়ও ব্যয় করতে পেরেছেন নিজের কাজে। সংসারের বন্ধন কখনওই যে ফাঁস মনে হয়নি, তার প্রধান কারণ তাঁর পরিবার-পরিজনদের সহযোগ।

অবসরের কয়েক বছর আগে, হিন্দুস্থান পার্কে তাঁর বাপের বাড়ির কিছু অংশ পেলেন কয় বোন মিলে। উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, এবার একটা এমন স্টুডিয়ো করব যেখানে বেশ হাত-পা মেলে থাকাও যায়। ভাগাভাগিতে কিছু অদলবদল হয়ে গেলেও বালিকাবয়সের সেই মাধবীলতা গাছটা যেন ফুল ফোটাতেই থাকল স্মৃতি ও স্বপ্নের মাঝামাঝি কোথাও একটা শিকড় চারিয়ে। যে-উমাদি স্টাফরুমের নির্দিষ্ট একটা সোফায় শান্ত হয়ে বসে থাকতেন নিবিড় প্রশান্তিতে, স্টুডিয়োতে দেখা উমাদি কিন্তু একেবারেই ভিন্ন; যেমন তৎপর, তেমনই ক্ষিপ্র। ক্রমে তাঁর সাজানো সংসারটি ছেলে-বউমার হাতে ছেড়ে দিয়ে, এই হিন্দুস্থান পার্কেই থাকতে শুরু করলেন উমাদি। অবাক হয়ে ভাবতাম, ওঁর কর্মক্ষেত্রের মানুষগুলি কি সত্যিই জানেন যে, কে এই উমা সিদ্ধান্ত! সেখানে তো তাঁর ভূমিকা তরোয়াল দিয়ে দাড়ি কামানোর মতো।
৩
কলেজের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় ওঠবার প্রথম ভাঁজেই একটি কাচের শো-কেসে ‘মা ও শিশু’র যে পাথরমূর্তিটি সাজানো, সেটি উমাদির করা। এই অভ্যর্থনা দিয়েই শুরু হত শ্রী শিক্ষায়তন কলেজ-পরিবারের প্রতিটি মানুষের প্রতিদিনের যাতায়াত। বছরে একবার প্রকাশ পাওয়া ‘শ্রী শিক্ষায়তন পত্রিকা’র প্রচ্ছদটিও প্রতি বছর তাঁরই করে দেওয়া। সে-সময়কার ‘আর্ট অ্যান্ড ক্র্যাফট রুম’টিও তাঁরই নিজে হাতে সাজানো। কলামন্দির প্রেক্ষাগৃহে শীতকালে কলেজের বার্ষিক অনুষ্ঠানে প্রতি বছর স্টেজ সাজানো— সেও উমাদি। এমনকী কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবসে বর্ষাকালে কলেজ অডিটোরিয়াম সাজানোর দায়িত্বেও উমাদি। এসব দায়িত্বে থাকা মানে সময়ের অনেক আগে এসে পৌঁছনো এবং নিজের বাড়ি থেকে যাবতীয় যা জোগাড় করে এনে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখা। সহযোগে হাতের সংখ্যা কম থাকলেও সমালোচক কিন্তু সবাই এবং বেশ কড়া ধাঁচেরও। উমাদি কিন্তু সেসব মানিয়ে-গুছিয়েই চালিয়ে নিতেন, সমালোচনা এবং শীত-গ্রীষ্মের তোয়াক্কা না করেই। আর এটাও বলা দরকার যে, সেই সময়ে ‘স্টেজ কমিটি’, ‘বাজেট’ বা ‘ট্রান্সপোর্ট এক্সপেন্স’ এসবের কোনও গপ্পোই ছিল না। উমাদি কিন্তু এগুলিকে গাঁটগচ্চা বলে মনে করেননি কোনওদিন। ফুলসমেত ফুলদানি এবং ট্যাক্সি ভাড়া দিয়েই আনা-নেওয়া করতেন। যাতায়াতও করতেন মিনিবাসে, গাড়িতে নয়।
আমি আবদার করায়, আমার নাচের কস্টিউম এবং খোঁপার ধরনটি বলে দিয়েছিলেন। আমি সেজেছিলাম, যাজ্ঞ্যবল্কের বিদুষী স্ত্রী মৈত্রেয়ী। মঞ্চের আলোয় আমাকে নাকি প্রাচীন কোনও ভাস্কর্যের মতোই দেখিয়েছিল। সেবারও অপূর্ব সব কাট-আউট করে এনে মঞ্চটিও সাজিয়ে দিয়েছিলেন উমাদি। ওই মঞ্চসজ্জা এবং পোশাকের আয়োজনে ক্ষণকালের জন্য আমিও হয়ে উঠেছিলাম সেই প্রতিবাদী মৈত্রেয়ী, স্বামীর কাছে যে শুধু চেয়েছিল তাঁর মেধার অধিকার।

সব থেকে মনকাড়া ছিল বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় তাঁর ‘ডিউটি’। তিনি থাকতেন ফার্স্ট এইডের দায়িত্বে। একটা ছোট্ট টেবিলের একপাশে ডেটল-ব্যান্ডেজ-আয়োডিন সাজিয়ে উমাদি কিন্তু মেতে থাকতেন তাঁর আপন কাজে। ছোট্ট একটি কাঠের বাক্স থেকে বের করে মাপ করে কাটা বাঁশের টুকরোগুলি দিয়ে বানিয়ে ফেলতেন খোঁপার কাঁটা। একটা হাত-করাত দিয়ে ছুলে-ছুলে মসৃণ করে তার একদিক ছুঁচলো আর অন্য দিকটায় হয় দুর্গা, নয়তো প্রজাপতি বা ফুল। ওখানে বসেই কালো কালির টাচ দিয়ে, লাইটার জ্বেলে সেই কালো রং এমন পাকা করে দিতেন যে মনে হত যেন বিদ্রির কাজ। কলেজচত্বর থেকে ওই অনুষ্ঠান যখন হেস্টিংস-এর বড় মাঠে চলে গেল, তখনও গাছতলার ছায়ায় টেবিল সাজিয়ে উমাদি কিন্তু একইভাবে নিমগ্ন তাঁর ‘কাটুম-কুটুম’ টুকিটাকিতে। বিএড বিভাগের বার্ষিক প্রদর্শনীতে আমরা দেখতে পেতাম তাঁর শেখানো এমব্রয়ডারি, বাটিক এবং কাঠের কাজের নমুনা। একবার তো মাটির গহনা করে এমন সাড়া ফেলে দিলেন যে, আমাদের বায়নায় সে-গহনাগুলি বিক্রিযোগ্য করা হল। এর অনেক পরে টেরাকোটার গহনা বাজারে এসেছে।
উমাদিকে যথার্থ চিনলাম তাঁর অবসরের দিনে। তাঁর পোস্টে যোগ দেওয়া কলাভবন থেকে পাশ করা আর এক চিত্রী সুনন্দা দাস যখন উমাদির মূল্যায়নটি করল। কী অপূর্ব ব্যাখ্যায় সে বুঝিয়েছিল যে তাঁর শিল্পকর্মে যে-কোনও নন মেটেরিয়ালও এক বিশিষ্ট আকর হয়ে ওঠে; দ্রব্যের এই রূপান্তরটাই উমাদি। এই কলেজের বিএড বিভাগে অল্প সময়ে ক্লাস করা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমন্ত্রিত হয়ে কলেজে আসতে রাজি হলেন; তাঁর তিন প্রিয় শিক্ষক ছায়াদি, ভারতীদি এবং উমাদি তাঁর সঙ্গে মঞ্চে থাকবেন এই প্রস্তাবে কলেজ কর্তৃপক্ষ রাজি হওয়ায়। সমস্ত মূল্যবান উপহার ফিরিয়ে দিয়ে তিনি শুধু গ্রহণ করলেন বিএড বিভাগের ছাত্রীদের করা বাটিকের উত্তরীয়টি, কারণ তাতে উমাদির শেখানো পরম্পরা আছে। রাজ্য সরকারের কাছ থেকে ‘বঙ্গবিভূষণ’ উপাধি পেয়ে উমাদি বলেছিলেন, সরকারি স্বীকৃতি ছাপিয়ে এ হল আমার এক ছাত্রীর দেওয়া সম্মান।

এসবের মধ্যে দিয়ে আরও এক দিক যা আমি দেখেছিলাম তা হল, ভাঙন ও বিচ্ছেদকে অনায়াসে জায়গা করে দেওয়া। তাঁর আর্টরুমটি বদলে গেল জেনারেল ক্লাসরুমে; যত্নে গুছিয়ে রাখা নানা আয়োজন বাতিল হয়ে চলে গেল জঞ্জালের সঙ্গে; একজন পিওন একটা বাঁধানো বাটিকের কাজ তুলে এনে কোথায় আর রাখবে ভেবে, তা লাগিয়ে দিল করিডরের এক কোণে। তার বসবার জায়গায় জুতসই এক রোদের আড়াল হিসেবে। ক্রমে বদলে গেল শ্রী শিক্ষায়তন পত্রিকার প্রচ্ছদটিও। কিন্তু কোনও উল্লেখেই কোনও আক্ষেপ শোনা গেল না তাঁর মুখে। এমনকী অকালপ্রয়াত অনুজ সহকর্মী সুনন্দার মৃত্যুসংবাদের ফোন পেয়েও একইরকম স্নিগ্ধ এবং স্থির তাঁর স্বর। প্রিয় সহকর্মী এবং বন্ধু ভারতীদি, মিনতিদি, পূরবীদির মৃত্যুতেও অবিচল ছিল তাঁর ছায়া।
ডিসেম্বর, ২০১০ আমার মায়ের কাজের দিন বিকেল নাগাদ খেয়াল হল যে, বাকি সকলেই প্রায় এলেও ভারতীদি আর উমাদি আসেননি। বাগবাজার মাল্টিপারপাস স্কুলের বড়দিদিমণি হিসেবে মা’কে চিনতেন ওঁরা। আমার মা’ও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন ওঁদের প্রতি। ফোন করতেই কত সরলভাবে উমাদি জানালেন, গাড়ির ব্যবস্থা হয়নি বলে যাওয়া হল না। সেই পড়ন্ত বিকেলে গাড়ি পাঠিয়ে দিতেই অগাধ পরিতৃপ্তিতে ভরিয়ে দিতে চলে এলেন দুজনে।
উমাদিও খানিক বদলালেন বইকি; বয়সের ভার বাড়ায় শাড়ি ছেড়ে সালোয়ার-কামিজ ধরলেন। কোনও আমন্ত্রণে কলেজে এলে তাই পরেই আসতেন। এ বড় কঠিন ছিল। কারণ আজও শ্রী শিক্ষায়তনের কোনও ‘ফর্মাল’ অনুষ্ঠানে অধ্যাপিকাদের শাড়ি পরা এক অলিখিত কিন্তু বাধ্যতামূলক নিয়ম। উমাদির মৃত্যুসংবাদ ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়তে, অনেকেই অনেক কিছু লিখছেন। সিংহভাগ অনুজ সহকর্মী এবং নানা বয়সের ছাত্রীরাও কিন্তু প্রণাম জানিয়ে লিখছে যে, তাদের মনে আছে তাঁকে। মনে আছে তাঁর আল্পনা দেওয়া। আর মনে আছে কপালের ওই গুঁড়ো টিপ। উমাদির অস্তিত্বে জাগরুক হয়ে থাক মায়ের ওই তৃতীয় নয়ন।
ছবি ঋণ: ললিত কলা একাডেমি, গ্যালারি ৮৮