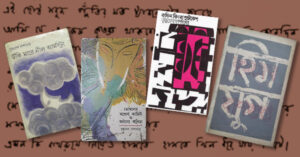ঢাকা ভাটপাড়ার নামজাদা মানুষ কালীনারায়ণ গুপ্ত। আসল নাম অবশ্য মাধবচন্দ্র সেন। বৈদ্যবংশীয় গুপ্তপরিবারে দত্তকপুত্র হিসেবে গৃহীত হবার সময় নাম হয়েছিল কালীনারায়ণ। বৈদ্যকন্যা অন্নদাসুন্দরীর সঙ্গে বিবাহসূত্রে কয়েকটি পুত্রকন্যার জনক হন তিনি। পূর্ব বাংলার সেই বাড়িতেই তাঁর দৌহিত্র অতুলপ্রসাদ সেনের জন্ম ১৮৭১ সালের ২০ অক্টোবর। আজ থেকে ১৫৪ বছর আগে।
অতুলপ্রসাদ সেন এমন এক কালখণ্ডের মানুষ, যখন আধুনিক বাঙালি সংস্কৃতির, বিশেষত নতুন ধারার বাংলা গানের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক হয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠা ঘটে গেছে। রাবীন্দ্রিক সংগীতবোধের মাধ্যমে প্রভাবিত ও পরিচালিত হলেও অতুলপ্রসাদের গানে অবধারিতভাবেই পাওয়া যায় তাঁর স্বতন্ত্র অভিজ্ঞান। তাঁর সংক্ষিপ্ত সংগীতসম্ভারের দিকে তাকালে দেখতে পাই, সেখানে বহু রঙের, বহু মেজাজের সুর। উত্তর ভারতীয় মার্গসংগীতে সুদীক্ষিত অতুলপ্রসাদ বাংলা গানের ভাণ্ডারে এনেছিলেন বিচিত্র রাগরাগিণীর মায়া। উনিশ শতকের বাংলা কাব্যগীতিতে ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, গজল সবকিছুর পাশাপাশি যে বিশেষ ধারাটি অতুলপ্রসাদের স্বতন্ত্র ও ধারাবাহিক সংযোজন, সেটি ঠুমরি। লখনউ ঠুমরির চাল খুব কাছ থেকে চেনার ফলে তাঁর গানে ঠুমরির আঙ্গিক যতটা সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ, ততটা অন্যদের গানে থাকা সম্ভব নয়। এছাড়াও কাজরী, লওনি, দাদরা, হোরি, গজল ইত্যাদি সম্ভাবনারও গ্রহণ ও স্বীকরণ ঘটেছে তাঁর গানে। বাংলা কাব্যগীতিতে এগুলি তাঁর বিশেষ অবদান। কিন্তু বাংলার বাইরে থাকার সুবাদে যে সমাদরে তিনি উত্তর ভারতীয় সংগীতভাবনাকে আত্তীকৃত করেছেন, বাংলার স্বকীয় সুর, স্বকীয় সাংগীতিক পরিমণ্ডলও সেই আদর ও সম্মানই পেয়েছে। বাউল, রামপ্রসাদী মালসী কিংবা কীর্তন, অতিনিবিড়ভাবে গেঁথে রেখেছে তাঁর গানের সুরভাষা।
আরও পড়ুন : ব্রহ্মাণ্ড ও মুণ্ডমালার রহস্যের উত্তর দিয়েছেন কালীই! লিখছেন কৃষ্ণপ্রিয় দাশগুপ্ত…
একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, বাংলা কাব্যগীতির প্রাণস্পন্দনকে পুনরাবিষ্কার ও উচ্ছ্বসিত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেই প্রয়াস ও অনুশীলনে তিনি সচেতনভাবে অঙ্গীকরণ ঘটিয়েছিলেন যে সংগীতধারার, তার নাম কীর্তন। বাঙালির একান্ত নিজস্ব মার্গসংগীত হিসেবে রবীন্দ্রনাথ চিহ্নিত করেছিলেন কীর্তনকে, আর কীর্তনের উপাদানগুলিকে আধুনিক বাংলা গানের উপযোগী চেহারায় সংস্থাপন করেছিলেন। এই বিশেষ প্রচেষ্টাটি রবীন্দ্রযুগের সংগীতকারেরা প্রায় সকলেই অনুসরণ করেন। অতুলপ্রসাদও তার ব্যতিক্রম নন।
তবে রবীন্দ্র-অনুসৃতিই কেবল এর পিছনের কারণ নয়। বালক অতুলপ্রসাদের কান আর প্রাণ শৈশব থেকেই কীর্তনের আবেশে মজেছিল, তা বহন করেছেন তিনি আমৃত্যু। তবে শুধু বহন করলে তো সংস্কৃতি জীবিত থাকে না, তার চর্চা ও পুনরায়োজন ঘটেছে তাঁর সংগীতে।
কীর্তনের সাংগীতিক সংযোজনের প্রসঙ্গে যাবার আগে বলে নেওয়া ভাল, অতুলপ্রসাদের মাতৃপক্ষ ও পিতৃপক্ষ, উভয়েই ব্রাহ্ম ছিলেন। মাতামহ কালীনারায়ণ গুপ্ত ছিলেন আদি ব্রাহ্মসমাজের সদস্য, আর বাবা রামপ্রসাদ সেন ছিলেন কেশবচন্দ্র-প্রবর্তিত নববিধান ব্রাহ্মসমাজের। রামপ্রসাদের অকালমৃত্যুর পর অতুলপ্রসাদের মা হেমন্তশশী পুনর্বিবাহ করেন যাঁকে, তিনিও ব্রাহ্মসমাজের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রচারক দুর্গামোহন দাশ, পরিচয়ে যিনি চিত্তরঞ্জন দাশের জ্যেষ্ঠতাত। কালীনারায়ণ প্রথম জীবনে শক্তিভক্ত হিন্দু ছিলেন, ২৪-২৫ বছর বয়সে অক্ষয়কুমার দত্তর অনুরাগী হয়ে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। ধর্মের পরিবর্তন ঘটলেও সংস্কৃতির অন্দরের সমক্ষেত্রগুলি তাঁর অধীত ছিল। আগে গাইতেন কালীকীর্তন, পরে লিখতে শুরু করেন বাউল, রামপ্রসাদী বা কীর্তনের সুরে ব্রহ্মসংগীত। দাদু আর বাবার সঙ্গে শৈশবে ঢাকার রাস্তায় এমন প্রভাতী কীর্তন গেয়ে-বাজিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন অতুলপ্রসাদ। মা হেমন্তশশীও ভালবাসতেন কীর্তন। অর্থাৎ, কীর্তন বিষয়টি তাঁর জীবনে অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্ত সাংস্কৃতিক প্রকাশভাষা হিসেবেই শ্রুত ও গৃহীত হয়েছিল।
ফলে অতুলপ্রসাদ যখন গান বাঁধেন,
যদি দুখের লাগিয়া গড়েছ আমায়, সুখ আমি নাহি চাই,
শুধু আঁধারের মাঝে তব হাতখানি চাহিয়া যেন গো পাই।
যদি নয়নের জল না পার মুছাতে,
যদি পরানের ব্যথা না পার ঘুচাতে,
তবে আছ কাছে আছ, হে মোর দরদী, কহিয়ো আমারে তাই…
তখন তা কেবল ব্রহ্মনামের গান থাকে না, কীর্তনের সুরনির্যাস, ছন্দসমন্বয় তাকে অনেক বেশি নির্বিশেষ করে তোলে।
এক বিচিত্র, বিক্ষত দাম্পত্যে জীবনের সুদীর্ঘ সময় কেটে গেছিল অতুলপ্রসাদের। বহু সামাজিক বিঘ্ন পেরিয়ে মামাতো বোন হেমকুসুমের সঙ্গে যে ঘর তিনি বেঁধেছিলেন, তা খুব অল্পদিনে ভেঙে যায়। বিবাহবিচ্ছেদ হয়নি বটে, তবে লখনউ শহরে বিভক্ত নিঃসঙ্গ দিন কাটিয়েছেন তিনি প্রায় সমস্ত জীবন।
ব্রাহ্মধর্মচেতনা পরমেশ্বরকে নির্দিষ্ট দেবনামে সীমায়িত করে না, কিন্তু অতুলপ্রসাদের গানে নিরন্তর উচ্চারিত, সম্বোধিত ও আহ্বায়িত হয় হরিনাম। বাংলা সংস্কৃতিতে কীর্তনগানের প্লাবন নেমেছিল যে নামে, সেই নাম অনায়াস আনন্দে ও সংস্কারহীনভাবে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত অতুলপ্রসাদ গ্রহণ করেন। কীর্তনের আঙ্গিকেই তিনি বলেন,
পরানে তোমারে ডাকিনি হে হরি, ডেকেছি শুধুই গানে,
তাই তো তোমারে পাইনি জীবনে, ফিরেছি শূন্য প্রাণে।…
প্রকৃতি পর্যায়ের গানেও এসেছে কীর্তনের ছাঁচ ও ছন্দ—
আকাশ, বল রে আমায় বল, আমার আঁখিজল,
তাদের মত জীবনখানি করবে কি শ্যামল, আমায় বল রে…
আমি তাদের মত
আমার বঁধুর সনে মধুর খেলা খেলব কি দিনের শেষে?
ও আকাশ, বল আমারে!
দ্বিজেন্দ্রগীতি-অতুলপ্রসাদী গানে অবিসংবাদিতভাবে যাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠিত, সেই কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়ের মধুকণ্ঠে প্রথম শুনেছিলাম অতুলপ্রসাদের আধ্যাত্মিক পর্যায়ভুক্ত এই গানের পঙক্তিগুলো—
যে পথে বধূরা যমুনার কূলে
যায় ফুল হাতে প্রেমের দেউলে,
যে পথে বন্ধু বন্ধুর দেশে চলে বন্ধুর সাথে,
আমি সেই পথে যাব সাথে।
যে পথে পাখিরা যায় গো কুলায়
যে পথে তপন যায় সন্ধ্যায়
সে পথে মোদের হবে অভিসার শেষ তিমির-রাতে।
ওগো সাথী, মম সাথী, আমি সেই পথে যাব সাথে…
রবীন্দ্রনাথের প্রেম-পূজা পর্যায়ের অতিলেপনের মতোই এই ‘দেবতা’ পর্বভুক্ত গানকেও প্রেমের গান বলে মনে হয়েছিল। আর একান্তভাবেই, বৈষ্ণবীয় কীর্তনের অনুষঙ্গ স্পষ্ট ধরা দিতে থাকে এই গানগুলিতে। অতুলপ্রসাদের বহু প্রেম, প্রকৃতি বা ঈশ্বরবিষয়ক গানে কৃষ্ণপ্রীতির উল্লেখ ও আভাস আছে। তথাকথিত ‘হিন্দু’ বা ‘বৈষ্ণব’ গোত্র অতিক্রম করে বাংলা সংস্কৃতির শব্দভাণ্ডার ও কল্পভাণ্ডারে এই প্রসঙ্গ যেমন আত্মপ্রতিষ্ঠা করেছে, তেমন সেই চিরন্তন ছবিটির মতোই কীর্তনের সুরবিন্যাস এসেছে অতুলপ্রসাদ-নির্মিত নতুন গানের দিগন্তে।
এক বিচিত্র, বিক্ষত দাম্পত্যে জীবনের সুদীর্ঘ সময় কেটে গেছিল অতুলপ্রসাদের। বহু সামাজিক বিঘ্ন পেরিয়ে মামাতো বোন হেমকুসুমের সঙ্গে যে ঘর তিনি বেঁধেছিলেন, তা খুব অল্পদিনে ভেঙে যায়। বিবাহবিচ্ছেদ হয়নি বটে, তবে লখনউ শহরে বিভক্ত নিঃসঙ্গ দিন কাটিয়েছেন তিনি প্রায় সমস্ত জীবন। অহং, হতাশা, অপরাধবোধ আর অনন্ত অভিমান তাঁদের এক হতে দেয়নি৷ কিন্তু প্রতীক্ষায় থেকেছেন, ‘বাদলের বঁধু’ একদিন তাঁর কাছে সত্যি করে ধরা দেবে। হেমকুসুমের নিষ্ঠুরতা, আর হেমকুসুমের ক্রুদ্ধ অভিমান, অবরুদ্ধ প্রেম তাঁকে দিয়ে লেখায়—
ঘন মেঘে ঢাকা সুহাসিনী রাকা, তুমি কি গো সেই মানিনী,
বাদল নিঝরে শুধু মনে পড়ে ও দুটি কাজল ঝরিনী।…
কাটি যাবে যবে বরষার রাত, আসিবে হাসিয়া সোনার প্রভাত,
তেমনি হাসিয়া, হৃদি বিলাসিয়া, আসিও মধুরহাসিনী।
এরও নির্ভর কীর্তনেরই মধুরতায়। এক হতে না পারা আর এক হতে চাওয়ার যে অনন্ত খেলায় রাধাকৃষ্ণ বিরহ-আখ্যান রচিত, যে বিপ্রলম্ভ কীর্তনের উৎসমূল, নির্মমভাবে সেই বেদনাবীজেই ফিরে ফিরে আসে অতুলপ্রসাদের স্বরলিপি।
১৬ শতকের বঙ্গদেশ যে সংগীতস্রোতকে মুক্ত করেছিল, তার প্রাণশক্তি এতটাই বেশি ছিল যে, দীর্ঘ কয়েকশো বছরে তা অবরুদ্ধ হয়নি, নতুনভাবে নতুন মূর্তিতে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮-১৯ শতকের নবচেতনার বাঙালিও সেই প্রবাহে যুক্ত হয়। বাংলা থেকে বহু দূরে, লখনউ শহরে থাকা এক প্রবাসী মানুষ নিজের সংস্কৃতিকে, শিকড়কে, ঐতিহ্যকে উদযাপন করেছেন বারবার। স্বাভাবিক অনুমানেই বলতে পারি, ওই উদযাপনের অন্যতম পথ হিসেবেই তিনি দেখেছেন কীর্তনকে। তার পাশাপাশি আরও একটি কথা মনে হয়। কৈশোরে মা হেমকুসুমের থেকে মানসিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন অতুলপ্রসাদ, দীর্ঘ পারিবারিক মনোমালিন্য সেই দূরত্বকে কাটাতেও পারেনি। তাই শেষ বয়সে মা যখন কাছে আসেন, মাতৃস্নেহ আঁকড়ে ধরেন তিনি। লখনউয়ে তাঁর বাড়িতে খানদানি খেয়াল ঠুমরির মহফিলের সঙ্গে সঙ্গে তাই হেমন্তশশীর অতিপ্রিয় কীর্তনের আসর প্রায়শই বসত। বাড়ির নাম দেন হেমন্ত-নিবাস, প্রয়াত মায়ের ছবি ধরে রাখেন বাড়ির দেওয়ালে। নিজের গানে ক্রমাগত কীর্তনকে ফিরিয়ে আনাও এক অর্থে তাঁর মাতৃতর্পণ নয় কি? জননী আর জন্মভূমি, দুই-ই কি ভেসে ওঠেনি কীর্তনের মধুনামে? তার শ্রীখোলস্পন্দনে? ফেলে আসা জীবনের প্রতি, স্মৃতির মায়ার প্রতি ঝরে পড়ে না একমুঠো কথা-সুরের পাপড়ি?