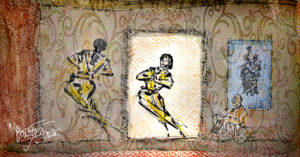‘ইন্টারস্টেলার’। একটা এমন ছবি, যা ব্ল্যাক হোলকে মেলেই শুধু ধরেনি, আইম্যাক্সের ৭০ মিলিমিটার পর্দায় বরং আমাদের অনাবিল ভ্রমণও করিয়েছিল গার্গেঞ্চুয়ার এপার-ওপারে। এই ছবি ব্যাতীত, সম্ভবত মানবসভ্যতার ইতিহাসে আর দ্বিতীয় কোনও নজির নেই, যেখানে আমরা আঁচ করতে পারি— ঠিক কেমন হতে পারে ব্ল্যাক হোল অভিযান?
এখানে মনে রাখা প্রয়োজন, জোনাথন আর ক্রিস্টোফার নোলানের এই কাহিনি, কেবল কল্পবিজ্ঞানের নিছক কোনও গল্পকথা নয়। প্রায় নিরানব্বই শতাংশ অকাট্য বৈজ্ঞানিক যুক্তির ওপর গড়ে তোলা হয়েছিল এ-ছবির ইমারত। স্বয়ং কিপ থোর্ন, যিনি গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভের ওপর বিখ্যাত লাইগো এক্সপেরিমেন্টের জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন, তিনিও পুরোদস্তুর যুক্ত ছিলেন ইন্টারস্টেলারের চিত্রনাট্য নির্মাণের সঙ্গে। নোলান ব্রাদার্স শুরুর থেকেই চূ়ড়ান্ত সচেতন ছিলেন এ-ছবির বৈজ্ঞানিক সত্যতা নিয়ে। এমনকী, নাসার সিক্রেট ফেসিলিটি সেন্টারে ডক্টর ব্র্যান্ডের গোল পড়ার ঘরে দেওয়ালজোড়া প্রতিটা ইকুয়েশন, সিনেমার প্রোডাকশন ডিজাইনিং টিমের ডিজাইন করা কোনও আলপনা নয়। খোদ কিপ স্টিফেন থোর্নের নিজের হাতে লেখা নির্ভেজাল বৈজ্ঞানিক ক্যালকুলেশন। তাই লন্ডনের রয়্যাল অ্যালবার্ট হলে ‘ইন্টারস্টেলার’ যখন প্রদর্শিত হয়, তখন তার প্রধান অতিথি হিসেবে সভা আলো করে আসেন ব্ল্যাক হোলের বরপুত্র, বিগ ব্যাং-এর আবিষ্কর্তা— স্টিফেন হকিং। পৃথিবীর একমাত্র বিজ্ঞানী, যাঁর অকেজো, অচল, প্যারালাইজড শরীর ছাপিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর চেতনা, মহাবিশ্বের আদিকালে। যিনি বস্তুবাদী বিজ্ঞানের চেতনা ও মানসকে না-মানার গোঁড়ামির বিরুদ্ধে ছুড়ে দিয়েছিলেন নিজের জীবনের উপলব্ধি, সোচ্চারে বলেছিলেন, ‘Though I can not move… but in my mind I am free’, তিনিও মন্ত্রমুগ্ধের মতো সিনেমার পর্দায় দেখেছিলেন কুপারদের ‘ইন্টারস্টেলার’ যাত্রা।

জোসেফ আর মার্ফি কুপার। পৃথিবীর অন্যতম দুই বীর সন্তান, সম্পর্কে বাবা আর মেয়ে। তারা চায়নি নিজেদের শুধু মুক্ত করতে ধ্বংসের মুখ থেকে। বরং চেয়েছিল, মুক্তিকে যদি আসতেই হয়, তবে তাকে আসতে হবে সবার জন্য। ধারণাটার মধ্যে একটা আধুনিক সাম্যবাদ বা মার্ক্সসাহেবের ছায়া দেখলে হয় প্রমাণিত হবে অজ্ঞতা, নয়তো বেইমানি করা হবে ইতিহাসের সঙ্গে। কারণ ‘মুক্তি যদি চাই তবে তা সবার জন্য চাই’ একথা কয়েক হাজার বছর আগে জীবন দিয়ে বলে গেছিল আর-একটি বাবা আর মেয়ের জুটি— অশ্বপতি ও সাবিত্রী। অশ্বপতির মতোই জোসেফ কুপারও খুঁজতে গেছিল মুক্তির পথ। খুঁজেও পেয়েছিল। কিন্তু ফিরে আসার রাস্তা ততক্ষণে বন্ধ হয়ে গেছে। তবু সে একা একা ভোগ করতে চায়নি মুক্তির স্বাদ। মুক্তির সূত্র ব্ল্যাক হোলের ওপার থেকে টেনে ছিঁড়ে আনতে চেয়েছিল পৃথিবীর বুকে। ধ্বংসের মুখোমুখি মানুষের মাঝখানে। পুরোটা সে পারেনি ঠিকই, কিন্তু বাকিটা সাবিত্রীর মতোই বাস্তবায়িত করেছিল তার কন্যা মার্ফ।

‘ইন্টারস্টেলার’ আসলে আমাদের ভাবীকালের কথা বলে। কোভিড প্যানডেমিক বা ইলন মাস্কের গ্রহান্তরের স্বপ্ন ভাইরাল হওয়ার অনেক আগে ‘ইন্টারস্টেলার’ আমাদের দেখিয়েছিল, কী কী সর্বনাশ হতে পারে আমাদের সঙ্গে, আর আমরা ঠিক কী করতে পারি, তার উত্তরে। মাইকেল হ্যানেকের ছবি থেকে শুরু করে রাজ্য সরকারের দুর্নীতি পর্যন্ত, সমস্ত বিষয়ে গলা ফাটিয়ে, ইউটিউবের ভিউ বাড়িয়ে আমরা যখন ধীরে ধীরে অনলাইন সেনসেশন হয়ে উঠছি, ঠিক তখনই অনেক দূরে হয়তো কোনও সুপারনোভার আড়ালে তৈরি হচ্ছে ভাবীকালের অস্তিত্বের ক্রাইসিস, সভ্যতার সংকট। যে সংকটের উত্তর আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ার কমেন্ট, লাইক আর সাবস্ক্রাইবের দুনিয়ায় সুনিশ্চিতভাবে অনিশ্চিত। যে সংকট কেবল অনুধাবন করতে গেলে নিজের চেতনাকে মেলে ধরতে হয় ক্লিন্ন পরশ্রীকাতরতা, পরনিন্দা আর নিজের অক্ষমতাকে ঢাকার অজুহাতের অনেক ওপরে। বিশ্বচেতনা যেখানে পৃথিবীর অলিন্দ ছাড়িয়ে নিজেকে মেলে ধরে ম্যাটার-অ্যান্টিম্যাটারের আদিম রমণকালে। নোলান ব্রাদার্সের ‘ইন্টারস্টেলার’ কিন্তু তার ১৬৯ মিনিটের গল্পে খেলাচ্ছলে আমাদের নিয়ে যায় সেই স্তরে। যেখানে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকে আমাদের অস্তিত্বের সংকট আর তার থেকে মুক্তি পাওয়ার বৈজ্ঞানিক সূত্র, যেমন সাবিত্রী দাঁড়িয়ে ছিলেন মানসের মুখোমুখি মৃত্যুকে অস্তমিত করার পর।
মহাভারতের অশ্বপতি আর সাবিত্রীর গল্পের সঙ্গে জোসেফ আর মার্ফি কুপারের কেন এত মিল, তার উত্তর খুঁজতে খুঁজতে মহাজাগতিক ধাঁধায় ধেঁধেছি অনেকবার। বুঝেছি, এর উত্তর খুঁজে পাওয়া যথেষ্ট কষ্টকল্পিতই শুধু নয়, কল্পিত কষ্টের চাইতেও অলীক। প্রাচ্যের এক আদিম মহাকাব্য আর পাশ্চাত্যের এক ভাবীকালের ডিস্টোপিয়ান গল্প— এর মধ্যে সূত্র খুঁজে বেড়ায় আমার ভারতীয় মন। আবেগকে যুক্তি ভেবে গুলিয়ে ফেলছি কি না বলে সন্দেহ জাগে যখন, তখন বারবার মনে আসে একটাই দৃশ্য। ভুট্টাক্ষেত ভেঙে ফুল স্পিডে ধেয়ে চলেছে কুপারের পিক-আপ ট্রাক। গাড়ির স্টিয়ারিং কুপারের ছেলে টমের মুঠোয়। জানলার বাইরে হাত বাড়িয়ে ছোট্ট মার্ফ ধরে আছে অ্যান্টেনা। কুপারের আঙুল ল্যাপটপের ট্র্যাকপ্যাডে। ওরা তাড়া করছে একটা উড়ন্ত অত্যাধুনিক সোলার ড্রোন। ইন্ডিয়ান সার্ভেইলেন্স ড্রোন।
যে ডিসটোপিয়ান দুনিয়ায় চাষবাস হয়ে উঠেছে আমেরিকার মুল জীবিকা, নিল আর্মস্ট্রংদের চন্দ্রাভিযানকেও আসলে সোভিয়াত রাশিয়াকে জব্দ করার অসত্য প্রোপাগান্ডা বলে যখন দাবি করছে মার্কিনি ইস্কুল, ঠিক সেই সময়ে ভারত, স্পেস রিসার্চে সকলকে টেক্কা দিয়ে ক্ষয়ে যাওয়া আমেরিকার বুকে কেন পাঠাতে গেল ইন্ডিয়ান সার্ভেইলেন্স ড্রোন? ভাবীকালের অস্তিত্বের সংকটে নোলান সাহেব ভারতবর্ষকে আদতে দেখতে চেয়েছেন ঠিক কোন আতসকাচে? জন্মদিনে রইল এই প্রশ্ন ‘ইন্টারস্টেলার’-এর পরিচালকের কাছে।