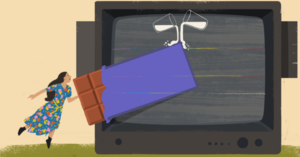ঋতুপর্ণ ঘোষ— নামটা বললে প্রথমেই কী মনে আসে? আমার অন্তত প্রথমেই মনে আসে তিনটে ব্যাপার। তাঁর লেখা একটি পত্রিকার সম্পাদকীয়, টিভিতে ‘এবং ঋতুপর্ণ’ অনুষ্ঠান এবং অবশ্যই ঋতুপর্ণর চলচ্চিত্র। আর তিনটে জুড়েই দেখি যে, রবীন্দ্রনাথ আর সত্যজিৎ এই দুইজনের কাজ কীভাবে বারবার ছায়া ফেলে যায় তাঁর মননে। এবং একটা নির্দিষ্ট ধাঁচের বাঙালিয়ানা নির্মিত হয়ে ওঠে তাঁর নানা কাজের মধ্য দিয়ে। এই যাত্রা শুরুর বিন্দুর দিকে যদি খেয়াল করতে চাই, তাহলে অবধারিতভাবেই আমাদের চোখ ফেরাতে হয় তাঁর নির্মিত প্রথম ছবি ‘হীরের আংটি’-র দিকে।
চিত্রনাট্যের সংলাপ রচনার ক্ষেত্রে অসাধারণ দক্ষতা ছিল তাঁর। কথার পিঠে কথা বসানোয় তিনি তুখড়। তাই পরবর্তীকালে ঋতুপর্ণর ছবিতে সংলাপের ব্যবহার অনেক বেশি। তার তুলনায় এই প্রথম ছবিটিতে, দৃশ্যভাষার ব্যবহার তুলনামূলকভাবে বেশি। এ-ছবির একেবারে শুরুতেই, কিছু ক্লোজ-আপের মাধ্যমে তিনি পুরনো জমিদারবাড়ি-সদৃশ এক বাড়ির পরিবেশ তৈরি করে তোলেন। তারপর আগের আমলে যেভাবে ঘোড়ায় চড়ে মশাল নিয়ে ডাকাতরা জমিদারবাড়িতে ডাকাতি করতে আসত, সেরকম ডাকাতির এক কাল্পনিক দৃশ্য। তারপরেই শুরুর টাইটেল আসার মুহূর্তে পরপর যে ল্যান্ডস্কেপগুলির ছবি আসতে থাকে, সেগুলোয় বিন্যাস ও রঙের ব্যবহার আমাদের অবধারিতভাবে মনে করিয়ে দেয় কালি ও প্যাস্টেলে বা কিছু জলরঙে আঁকা রবীন্দ্রনাথের ল্যান্ডস্কেপগুলোর কথা।
যে বাঙালিয়ানার নির্মাণ নিয়ে শুরুতেই বলছিলাম, তার চিহ্ন হিসেবে ওই শুরুর টাইটেলের শেষদিক থেকে শুরু করে আমরা বেশ দীর্ঘ সময় ধরেই শুনি রেডিওতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের পাঠ করা সেই বিখ্যাত মহালয়া আর তারপর ‘বাজল তোমার আলোর বেণু’ বা ‘জাগো, তুমি জাগো’ গানগুলির অংশ। পরেও দেখব কাঁসার থালা-বাটিতে খাওয়া, দুর্গাপুজোর আবহ, পোশাকের ব্যবহার, বঙ্কিমি ভাষার ব্যবহার— এগুলো সবই যেন একে একে সেই বাঙালিয়ানার নির্মাণের দিকেই ইঙ্গিত করে।
আরও পড়ুন : ‘জয় বাবা ফেলুনাথ’-এ দুর্গাপুজো কেবলই অপরাধের প্রেক্ষাপট তৈরি করে! লিখছেন প্রিয়ক মিত্র…
আর এই শুরুর টাইটেল শেষ হয় আধো-অন্ধকারে চলে যাচ্ছে একটি ট্রেন— এইরকম এক দৃশ্য দিয়ে। শুরুর ক্লোজ-আপগুলোর কথা যদি ছেড়েও দিই, তাহলেও এই ট্রেন চলে যাওয়ার দৃশ্যটি কি আমাদের একঝলকে সত্যজিতের ছবির স্মৃতি ফিরিয়ে দেয় না? অথবা পরে এই ছবিতে ঘাসবনের মধ্য দিয়ে হাবুল-তিন্নির দৌড়ের দৃশ্য কি আমাদের মনে করিয়ে দেয় না সত্যজিতের ‘পথের পাঁচালী’-র কথা? অথবা ঠাকুর তৈরি করার সময়ে সেই শিল্পীর সঙ্গে হাবুলের সংলাপ কি আমাদের মনে জাগিয়ে তোলে না সত্যজিতের ‘জয় বাবা ফেলুনাথ’-এ সমগোত্রীয় দৃশ্যের স্মৃতি? আমার ব্যক্তিগত ধারণা যে, সচেতনভাবেই এই নির্মাণগুলি করেছিলেন ঋতুপর্ণ, সত্যজিতের ছবির স্মৃতি জাগিয়ে তোলার জন্যই।



সত্যজিতের ‘পথের পাঁচালী’-তে অপু-দুর্গার সেই কাশবনের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ দৌড় লাগিয়ে, ট্রেন দেখতে যাওয়ার বিখ্যাত দৃশ্যটির কথা নিশ্চয়ই মনে আছে সব দর্শকের। পর্দায় সেই ট্রেনের প্রবেশমুহূর্তই যেন ছিল প্রায় প্রাগাধুনিক গ্রামবাংলার পটভূমিতে আধুনিকতার প্রবেশ। আর সেই আধুনিকতার চিহ্ন— ট্রেন— দেখে ফেরার পথেই, তারা আবিষ্কার করে যে, জীবিত মানুষের ভঙ্গিতে বসে থাকলেও, আসলে মারা গেছেন ইন্দির ঠাকরুন— আদি গ্রামবাংলার প্রতিমা। কিন্তু কেন হঠাৎ এই কথা মনে হল?
‘হীরের আংটি’-র মুক্তি পাওয়ার সময়ের দিকে একটু চোখ ফেরানো যাক। ১৯৯২ সাল। এ এক সন্ধিক্ষণ, যেখানে দাঁড়িয়ে আন্দাজ করা যাচ্ছে যে, আমাদের চেনা পৃথিবীটা আমূল পাল্টে যাচ্ছে, আগের চেনা পৃথিবীর যেন মৃত্যুঘণ্টা বেজে গেছে। অথচ নতুন সময়টার চেহারা যে ঠিক কেমন হবে, সেটাও যেন খুব স্পষ্টভাবে ঠাহর করা যাচ্ছে না, তার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে মাত্র। যে সময় আসছে, তার চেহারা তখনকার চোখে অনেকটাই বাস্তব আর কল্পনায় জড়ানো। তাছাড়া ১৯৯১-এ মুক্তি পাচ্ছে সত্যজিৎ রায়ের শেষ ছবি ‘আগন্তুক’, মৃণাল সেনের ‘মহাপৃথিবী’, ১৯৯২-এ এই ছবিটি ছাড়াও মুক্তি পাচ্ছে বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর ‘তাহাদের কথা’। কেন বলছি সন্ধিক্ষণ? ওই সময়টার আগেই ঠিক চার-পাঁচ বছর ধরে কী ঘটে চলেছে তখন চারপাশে?

১৯৮৬ : চেরনোবিল বিদ্যুৎকেন্দ্রে সোভিয়েত নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর বিস্ফোরণের দুর্ঘটনা। এ-বছরের শেষ দিক থেকে গণতন্ত্রের জন্য চিনে তৈরি হচ্ছে ছাত্র-বিক্ষোভ। বিতর্কিত রাম-জন্মভূমি ও বাবরি-মসজিদের তালা খোলা হল।
১৯৮৭ : গরবাচেভ গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রৈকার জন্য প্রচার চালাচ্ছেন। ওয়াশিংটনে রেগন-গরবাচেভ বৈঠক। গণতন্ত্রের জন্য চিনে চলছে ছাত্র-বিক্ষোভ।
১৯৮৮ : রাশিয়ায় শুরু হল পেরেস্ত্রৈকা। প্রকাশিত হচ্ছে স্টিফেন হকিং-এর ‘কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস’। ভারতে ভোটার হওয়ার বয়স ২১ থেকে কমিয়ে ১৮ করা হল।
১৯৮৯ : তিয়েনানমেন স্কোয়ারে গণতন্ত্রের জন্য ছাত্রদের বিক্ষোভ, সেনাবাহিনীর গুলিচালনা। পূর্ব জার্মানির কমিউনিস্ট সরকারের ইস্তফা। চেসেস্কু ক্ষমতাচ্যুত। কাশ্মীরে উগ্র ইসলামী সন্ত্রাসবাদ তার শক্তি বাড়াচ্ছে। আর এদিকে ভারতে উগ্র হিন্দুত্ববাদের উত্থান শুরু।
১৯৯০ : সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির রাষ্ট্রের ওপর একাধিপত্য ত্যাগ। নেলসন ম্যান্ডেলার মুক্তি। দুই জার্মানির মিলন। রাতারাতি ইরাকের কুয়েত দখল। আমেরিকা উপসাগরীয় অঞ্চলে ২ লক্ষ সেনা পাঠাল। মণ্ডল কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী সংরক্ষণ নীতি চালু হচ্ছে সারা ভারতে।
১৯৯১ : উপসাগরীয় যুদ্ধ শুরু। উপসাগরীয় যুদ্ধে বোমার আঘাতে ছিন্নভিন্ন ইরাকের মানুষের দুর্দশা, ক্ষয়ক্ষতি, মৃত্যু এসবও এক স্পেক্ট্যাক্ল-এর চেহারায় প্রদর্শিত হতে লাগল ঘরে ঘরে টিভিতে। হয়ে উঠল একধরনের পণ্য। এভাবে আস্তে আস্তে পাল্টে যাবে আমাদের দেখার চোখ। সোভিয়েত ইউনিয়নের অবলুপ্তি ও ঠান্ডা যুদ্ধের অবসানে আমেরিকার একমাত্র সুপার পাওয়ার হয়ে ওঠায় একমেরু বিশ্বের সূচনা। পরিবেশ ও উন্নয়ন নিয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের সম্মেলন। ধনতান্ত্রিক বাজার অর্থনীতির প্রতি চিনের কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেসের সমর্থন। রাজীব গান্ধী হত্যা। মনমোহনের বাজেট। উদারীকরণের হাওয়া। স্যাটেলাইট চ্যানেল চালু।
হীরের আংটি’-র মুক্তি পাওয়ার সময়ের দিকে একটু চোখ ফেরানো যাক। ১৯৯২ সাল। এ এক সন্ধিক্ষণ, যেখানে দাঁড়িয়ে আন্দাজ করা যাচ্ছে যে, আমাদের চেনা পৃথিবীটা আমূল পাল্টে যাচ্ছে, আগের চেনা পৃথিবীর যেন মৃত্যুঘণ্টা বেজে গেছে। অথচ নতুন সময়টার চেহারা যে ঠিক কেমন হবে, সেটাও যেন খুব স্পষ্টভাবে ঠাহর করা যাচ্ছে না, তার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে মাত্র। যে সময় আসছে, তার চেহারা তখনকার চোখে অনেকটাই বাস্তব আর কল্পনায় জড়ানো।
এই সময় আর তার কয়েক বছরের মধ্যেই দেখব যে, আগে যা যা উচ্চবিত্তের চিহ্ন হিসেবে গণ্য হত, সেইসব উপকরণ— যেমন টিভি-ফ্রিজ-ফোন-গ্যাস-টেপরেকর্ডার ইত্যাদি— ঢুকে পড়ছে আম-মধ্যবিত্তর ঘরে। তাদের মূল্যবোধের মধ্যেই ঢুকে পড়ছে একধরনের পণ্যরতি। যোগাযোগ ব্যবস্থায় অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যেই ঘটে যাচ্ছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। পৃথিবী জুড়েই এতদিনের বামপন্থী মতাদর্শ এবং তার অর্থনৈতিক মডেল প্রায় বাতিল হিসেবে গণ্য হচ্ছে তখন। কিন্তু এই রাজ্যে তখনও বামপন্থীরা সরকারে। একটা সময়ে বামপন্থী দল করতে আসত যারা, তারা অধিকাংশই দলকে দিতে আসত। আর মোটামুটি এই সময় থেকেই একটা বিরাট অংশ বামপন্থী দল করতে এলো শুধু দলের থেকে সুযোগ-সুবিধা শুষে নিতে। মধ্যবিত্তের সংজ্ঞা পালটে যাচ্ছে, পালটে যাচ্ছে তার মূল্যবোধ। যৌথ পরিবার ছেড়ে ঘরে ঘরে তৈরি হচ্ছে নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি, অনেক ভাড়াটের একজন হয়ে থাকার বদলে তারা খুঁজে নিতে চাইছে নিজেদের ফ্ল্যাট, সরকারি হাসপাতাল থেকে তাদের চিকিৎসা-ব্যবস্থা হয়ে উঠছে অনেকটাই নার্সিংহোম-কেন্দ্রিক, তাদের সন্তানদের শিক্ষা-ব্যবস্থা বাংলা মিডিয়াম ছেড়ে হয়ে উঠছে অনেকটাই ইংলিশ মিডিয়ামের, রান্নাঘরেও ঢুকে পড়ছে সেই বদলের চিহ্ন— উনুন থেকে গ্যাস। আগের ধাঁচের মধ্যবিত্তের মৃত্যুঘণ্টা বাজিয়ে দিয়ে, নতুন এক মধ্যবিত্ত জন্ম নিচ্ছে; তার মানসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক কাঠামো আগের মধ্যবিত্তের থেকে কিন্তু অনেকটাই আলাদা।
সত্যজিৎ রায়ের ‘আগন্তুক’, মৃণাল সেনের ‘মহাপৃথিবী’, বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর ‘তাহাদের কথা’ আর ঋতুপর্ণ ঘোষের ‘হীরের আংটি’— এই চারটে ছবিতেই দেখব যে, দিনানুদিনের স্রোতে চলা একটি স্থিতিশীল পরিবারে হঠাৎ বাইরে থেকে এসে হাজির হয় একজন। আর তারপর থেকেই যেন পরিবারের সেই স্থিতাবস্থাটা এলোমেলো হয়ে যেতে থাকে। এই সময়ে, এই যে বাস্তব জীবনে মোটামুটি স্থিতিশীল একটা জীবনধারার মধ্যে এসে পড়ছে একটা পাল্টে যাওয়া অনিশ্চিত জীবনধারার ধাঁচ, যাতে প্রায় খারিজ হয়ে যাচ্ছে আগেকার জীবনধারার আদল, অথচ নতুন এই জীবনধারার আদলটাও খুব স্পষ্ট নয় তখনও— তার সঙ্গে কি মিলিয়ে আমরা পড়তে পারি না এই ছবিগুলির এই একটি সাধারণ প্রবণতাকে? ‘মহাপৃথিবী’-তে সমসময়ের ছায়াপাত একেবারে সরাসরিই এসেছে। তবে ‘মহাপৃথিবী’ বা ‘তাহাদের কথা’-য় বাইরে থেকে যে আসছে, সে নিশ্চিতভাবে পরিবারেরই একজন, অনেকদিন পর বাড়ি ফিরছে। কিন্তু বাড়ি থেকে যে চলে গেছিল, সে মানুষটা যখন ফিরে আসছে, তখন সে যেন অনেকটাই অচেনা। পরিবারের সাম্প্রতিক মূল্যবোধের সঙ্গে যেন তার সাম্প্রতিক মূল্যবোধ আর খাপ খায় না এখন। বরং ওই দুই মূল্যবোধের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে উঠতে চায়। আবার ‘আগন্তুক’-এ বাইরে থেকে যিনি আসছেন, তিনিও নিশ্চিতভাবেই পরিবারের একজন, তবে তিনি সত্যিই তিনিই কিনা— তা নিয়ে ছবির শুরু থেকেই একটা সন্দেহ দানা বাঁধতে থাকে। ফলে তিনি যে সত্যিই ঠিক কেমন, তা নিয়ে বাস্তব আর কল্পনায় জড়ানো একটা ধারণা গড়ে ওঠে পরিবারের লোকজনের। এবং এক্ষেত্রেও তাঁর মূল্যবোধের সঙ্গে খাপ খায় না যেন পরিবারটির ও তার সঙ্গে লগ্ন লোকজনের মূল্যবোধ। ফলে এখানেও সংঘর্ষ বাধে। কিন্তু ‘হীরের আংটি’-তে ব্যাপারটা এই প্যাটার্নের থেকে খানিক আলাদা। এখানে যে বাইরে থেকে আসছে, সে নিশ্চিতভাবেই ওই পরিবারের কেউ নয়। এমনকী, যে পরিচয় নিয়ে সে আসছে, সে প্রকৃতপক্ষে সেই ব্যক্তিও নয়, অর্থাৎ একধরনের ছলনা রয়েছে তার পরিচয়ের মধ্যেই। মুখের ভাষা ব্যবহারের বদলে, কথা বলার সময়েও বঙ্কিমি ভাষা ব্যবহারের কৃত্রিমতা আশ্রয় করতে হয় তাকে। এবং কী কারণে ওই ছলনার আশ্রয় নিচ্ছে সে? না, কোনও মূল্যবোধ বা নীতিবোধ নয়। খুবই সামান্য বা তুচ্ছ একটা কারণে, কিন্তু সেটাই তার কাছে খুব জরুরি। সে কারণ হল, সে বম্বে গিয়ে সিনেমার হিরো হতে চায়; সেই বম্বে যাওয়ার খরচ তোলার জন্য তার এই ছলনা।
কিন্তু ওই সময়ে দাঁড়িয়ে, এটা কি তার আগত সময়ের চরিত্রের দিকেও খানিক ইঙ্গিত করে না? সময় কি এভাবেই পরোক্ষ টিপছাপ রেখে গেছিল ওই ছবিতে?