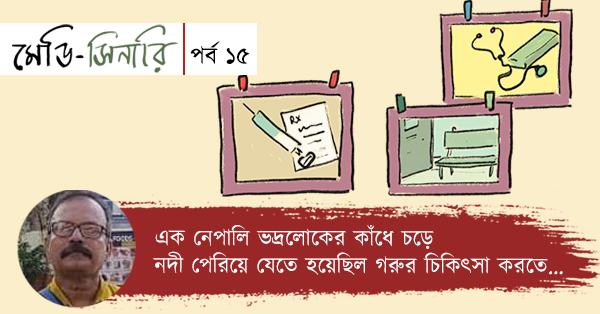সীমানা ছাড়িয়ে
তখন আমার কতই-বা বয়স! চব্বিশ-পঁচিশ বছর সবে। প্রথম পোস্টিং পেয়েছি নকশালবাড়ি পশু হাসপাতালে; পাশেই নেপাল বর্ডার। আমার যে-জায়গায় পোস্টিং ছিল, সেখানে ভারতীয় চিকিৎদকদের খুবই গুরুত্ব দেয় স্থানীয় লোকেরা। একবার এক নেপালি ভদ্রলোক এল আমার কাছে। দিনটাও মনে আছে, শনিবার। দুপুরবেলা। সমস্যা জানতে চাওয়ায় বলল, তার গরুর ডেলিভারি হচ্ছে না। আমার তখন এক বছর চাকরি হয়েছে মাত্র। একাই থাকি, বিয়ে-থা করিনি। দুপুরে খেয়েদেয়ে ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। নদী-জঙ্গলের পথ। কিছুটা রিকশায় গেলাম, হাঁটলাম কিছুটা। কিছুটা হাঁটার পর নদী পড়ল। আমি তো অবাক! পেরোব কী করে? নেপালি ভদ্রলোককে মোটেই বিচলিত দেখাল না। ওদের ভাষায় বলল, ‘আমার পিঠে উঠে পড়ুন ডাক্তার! চিন্তা নেই কোনও।’ আমিও, জামা-জুতো ভেজাব না বলে, তার পিঠে উঠেই পড়লাম। মনে-মনে যে কতরকমের ভাবনা আসছিল!
লজ্জা-সংকোচ কাটিয়ে নদী পেরোলাম। পেরিয়ে দেখি ঘোড়া রয়েছে; ঘোড়ায় চড়ে অবশেষে তাদের গ্রামে। তখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধে নামছে। গিয়ে দেখলাম, গরুটাকে তার আগে অনেকেই ঘাঁটাঘাঁটি করেছে। আমাদের ভেটেরিনারিতে নিয়মই আছে, গ্রামের যাঁরা ডেলিভারি করতে পারেন তারা আগে হাত লাগাবেন; তাঁরা না পারলে হাতুড়ে ডাক্তার; তাঁরাও ব্যর্থ হলে তখন এই আমাদের মতো পশু চিকিৎসকদের ডাকা হবে। যেহেতু পড়াশুনাটা ছিল, খুব একটা অসুবিধে হয়নি। মিনিট পনেরো-কুড়ির মধ্যে আমি ডেলিভারিটা করিয়ে দিলাম। বুঝতে পারছিলাম, গরুটা আর পারছিল না। অনেক ধকল গেছে তার আগে। দু-তিন বোতল স্যালাইন দিয়ে নির্দেশ দিলাম, একটু আগুন জ্বালিয়ে সেঁক দিতে। শীতকাল যেহেতু, আরাম লাগবে। কিছুক্ষণ সেঁক দেওয়ার পর গরুটা দিব্য উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওরাও খুশি, আমিও খুশি। তবে, এই খুশির আবহে কখন যে সন্ধে নেমে গেছে, খেয়ালই করিনি! আমার তো ফেরার পথ নেই। প্রয়োজনও খুব একটা ছিল কি? কেননা আগেই বললাম, তখনও আমি অবিবাহিত। পিছুটানহীন। রাতে থেকে পরেরদিন সকালে খচ্চরের পিঠে চেপে সোজা হাসপাতাল…
২
দার্জিলিং থেকে ফিরে আমার ইচ্ছা ছিল সার্জারিতে মাস্টার ডিগ্রি করি। করলামও। শেষ করে পোস্টিং নিয়ে গেলাম গুমা-য়। আমি স্টেশনের পাশেই থাকতাম বলে, মহম্মদ আলি নামক এক ব্যক্তি প্রায়ই আমার কাছে আসত। পেশায় সে ভ্যানচালক। খুব গরিব মানুষ। মাঠের মাঝখানে কয়েক ঘর মুসলমানবাড়ির একটায় ওরা থাকত। মহম্মদ, তার স্ত্রী-পুত্র আর দুটো গরু। একদিন মহম্মদ এসে বলল, ‘ডাক্তারবাবু, গরুটা আর উঠতে পারছে না, একবার যাবেন?’ আমি গেলাম এবং একটা স্যালাইন দিতেই গরুটা উঠে পড়ল। ওরা তো আনন্দে আত্মহারা! কিন্তু ফি-স্বরূপ আমায় যে কী দেবে, তা বুঝে উঠতে পারছে না। আমি যত বলি, ও-নিয়ে ভাববার দরকার নেই, মহম্মদ কিছুতেই শোনে না। শেষে পঞ্চাশ টাকা দেয়। ১৯৯৩ সালে পঞ্চাশ টাকা অনেকটাই টাকা। এর পর থেকে মহম্মদের সঙ্গে আমার সখ্য বেড়ে গেল। মাঝে-মাঝে এসে ওষুধ নিয়ে যায়। ভ্যানে করে বাছুরও নিয়ে চলে আসে। মহম্মদ না পারলে আসে ওর ছেলে। এই করে চলছিল। একবার, ওই ১৯৯৩ সালেই, আমার কিছু চিকিৎসক বন্ধুবান্ধব আবদার করে বসল, টেলিস্কোপ নিয়ে আমার ওখানে ধূমকেতু দেখতে আসবে। কেননা ফাঁকা জায়গা, অন্ধকার, ফলে সুবিধে। মাঠের মাঝখানে টেলিস্কোপ বসিয়ে ভাল করে দেখা যাবে। আট-ন’জন তাদের পরিবার নিয়ে চলে এল। আমি মহম্মদ আলিকে বলে রেখেছিলাম। গিয়ে দেখি, মাঠের মাঝখানে মাদুর বিছিয়ে সে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। প্রত্যেকের জন্য ডাব কেটে রেখেছে। সঙ্গে মুড়ি-সিঙাড়া-মিষ্টি। ধূমকেতু দেখে ফিরেছিলাম রাত এগারোটায়। কী যে আনন্দে কাটিয়েছিলাম ওই একটা সন্ধে!
কয়েক বছর পর আমার পোস্টিং হয় বর্ধমানে। চলে যাব-যাব অবস্থা যখন, মহম্মদ কার কাছ থেকে যেন শুনে ফেলে। আমার বাড়িতে এসে সে কী কান্নাকাটি! আসলে বুঝতে পারছিলাম, ক্রমশ ও আমার ওপর অনেকটা নির্ভর হয়ে পড়ছে। কিন্তু আমাদের যে চিরকাল এক জায়গায় থাকলে চলে না, এই কথাটাই-বা ওকে কেমন করে বোঝাই! শেষে একদিন ওর বাড়ি গিয়ে মিথ্যে বলতে হয়। বলি যে, আমার বদলি বোধহয় স্থগিত হয়ে গেছে। খুশিতে ঝলমল করে ওঠে মহম্মদের মুখ। কখনও-কখনও মিথ্যে কথায় মানুষ যেভাবে আনন্দিত হয়ে ওঠে, ভেবে বিস্মিত হতে হয়। হায়, মানবমন! আমি মহম্মদের থেকে দূরে চলে যাই। তবু, মনে পড়ে। মাঝে মাঝেই। অনেক বছর পর যাই একদিন। মহম্মদ ভ্যান রিকশা চালানো ছেড়ে দিয়েছে। খড়ের ছাউনি ছেড়ে বানিয়েছে সিমেন্টের ছাদ। আমি দেখে গেছিলাম দুটো গরু। সেখান থেকে বেড়ে হয়েছে আটটা। মহম্মদ জানায়, সে দুধের ব্যাবসা করে। আর্থিক উন্নতি হয়েছে তার। আমার মনে পড়তে থাকে কত কথা… একজন চিকিৎসকের জীবনে এর চেয়ে আনন্দের আর কীই-বা হতে পারে!