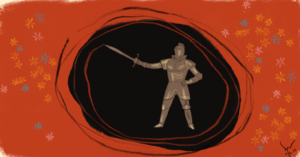ধরুন একটা সিনেমা আপনার চেয়ে বয়সে ১০ বছরের বড়। ৬০ বছর পরেও আপনি সেই ছবিটা টেলিভিশনে হইহই করে দেখছেন। আপনার সঙ্গে আরও দু’তিন প্রজন্মের দর্শকও সেই ছবি দেখতে-দেখতে একই রকম উছলে, উথলে, হেসে গড়িয়ে পড়ছে। মানে, ৭০ বছর পরেও সেই সিনেমার ব্র্যান্ড ইউএসপি-তে একটুও মরচে পড়েনি। সময়ের ধুলোময়লা, ঝুল-টুল জমতেই পারেনি। ওদেশে এমন ছবিকেই তো ক্লাসিক বলা হয়। ব্রিটিশ ফিল্ম ইন্সটিটিউট কিংবা আমেরিকান মোশন পিকচার্স আকাদেমি ১০০ বছরের সিনেমার ইতিহাস ঘেঁটে সেসব ছবির ক্রমপর্যায়ে বাছাই তালিকাও বানিয়েছে। মাঝে মাঝেই সেখানে স্থানাঙ্কের ওপর-নীচ, আগু-পিছু হয়েছে। আগের বাছাই তালিকায় আট নম্বরে থাকা ছবি পাঁচ কি তিন নম্বরে উঠে এসেছে। জনপ্রিয়তার সিঁড়িতে হড়কে দু’নম্বরি নেমে গেছে চার কি ছয় নম্বরে! শুধু হলিউড কেন, বলিউড ছবিরও এমন ‘ক্লাসিক’ মেধা তালিকাও আজকাল হরবখত দেখা যাচ্ছে। বাংলাই শুধু ঘুমায়ে রয়! যদি না ঘুমোত, তাহলে বাংলা সিনেমার ‘অলটাইম ক্লাসিক’-এর তালিকায় বেশ ওপরের দিকেই থাকত ‘সাড়ে চুয়াত্তর’।
অবশ্য লিস্টি না থাকলেও ভারি বয়েই গেছে! গত সত্তর বছর ধরে বাঙালি ‘সাড়ে চুয়াত্তর’ চুটিয়ে দেখেছে আর প্রাণভরে হেসেছে। ১৯৫৩-র ২০ ফেব্রুয়ারি যখন ছবিটা মুক্তি পাচ্ছে, তখন ছবির রোমান্টিক নায়ক উত্তমকুমারের ক্রেডিটে মাত্র দেড়খানা হিট! ‘বসু পরিবার’ পুরো হিট আর আধখানা হিট ‘কার পাপে’! ‘ফ্লপ কুমার’-এর তকমা তাঁর গা থেকে সবে উঠেছে। ওদিকে এ-ছবিতে তাঁর নায়িকা সুচিত্রা সেনের প্রথম অফিশিয়াল সিনেমা মুক্তি পেয়েছে মাত্র দু’সপ্তাহ আগে— সুকুমার দাশগুপ্তর পরিচালনায় ‘সাত নম্বর কয়েদি’। এর আগে ১৯৫২ সালে তিনি আর একখানা সিনেমার হিরোইন হযেছিলেন বটে! সে-ছবির নাম সম্ভবত ‘শেষ কোথায়’। তার পরিচালক সম্ভবত বীরেশ্বর বসু। এবং সেটা সম্ভবত মুক্তি পেয়েছিল ২১ বছর বাদে ১৯৭৪ সালে। সম্ভবত তার নাম বদলে তখন হয়েছিল ‘শ্রাবণ সন্ধ্যায়’! এবং সম্ভবত সুচিত্রা-ফ্যানেরা কেউই সে-ছবি দেখেননি। আসলে বলার কথা এটাই যে, ‘সাড়ে চুয়াত্তর’-ই উত্তম-সুচিত্রা জুটির প্রথম হিট ছবি বলে যেটা প্রচার করা হয়, সেটা আসলে একটা মিথ এবং মিথ্যে! বা বলা ভাল, কিছুটা আধা সত্যি আর কিছুটা তত্ত্ব পরিসংখ্যানের কারসাজি।
‘সাড়ে চুয়াত্তর’ ছিল অন্য ম্যাচ! উত্তম-সুচিত্রার রোম্যান্স সেখানে প্রথম একাদশে আছে বটে, কিন্তু সে স্ট্রাইক বোলারও নয়, ম্যাচ ফিনিশারও নয়। মিডল অর্ডারে স্রেফ একটা দরকারি জুটি! কিন্তু ম্যাচ জেতানোর দায়িত্ব ছিল অন্যদের।
‘সাড়ে চুয়াত্তর’ অবশ্যই হিট ছবি। তাতে রোমান্টিক জুটি হিসেবে অবশ্যই উত্তমকুমার-সুচিত্রা সেন আছেন। আর তথ্যের হিসেবেও এটাই উত্তম-সুচিত্রা জুটির প্রথম ছবি, কিন্তু তাতেই তো সবটা হয় না! উত্তম-সুচিত্রা জুটি যে অশ্বমেধের ঘোড়া হয়ে পরের দেড়-দু’দশক ধরে টালিগঞ্জের বক্স অফিসে দিগ্বিজয় করে বেড়াবে— দেশভাগের ফলে অর্থের বাজার হারানো বাংলা সিনেমাকে অক্সিজেন জোগাবে আর নতুন স্বদেশের জীবনযুদ্ধে রোজ-রোজ মার খাওয়া বাস্তুহারা মানুষের কাছেও আশা-ভালবাসার নতুন স্বপ্ন ফিরি করবে— ‘সাড়ে চুয়াত্তর’ থেকে তার যাত্রা শুরু হয়নি। তার রসায়ন-ফর্মুলা আলাদা, ফ্যান্টাসি তৈরির প্রকরণ-উপকরণ আলাদা, এমনকী সমাজ-সংস্কৃতি-অর্থনীতির যে চেনা বাইশ গজে সে-জুটি সপাটে বাণিজ্য হাঁকড়াবে, সে-উইকেটও অন্য কিউরেটরদের হাতে বানানো! ‘সাড়ে চুয়াত্তর’ ছিল অন্য ম্যাচ! উত্তম-সুচিত্রার রোম্যান্স সেখানে প্রথম একাদশে আছে বটে, কিন্তু সে স্ট্রাইক বোলারও নয়, ম্যাচ ফিনিশারও নয়। মিডল অর্ডারে স্রেফ একটা দরকারি জুটি! কিন্তু ম্যাচ জেতানোর দায়িত্ব ছিল অন্যদের। কীভাবে? আসুন দেখা যাক।
ম্যান অফ দ্য ম্যাচ: গল্প
এ-সিনেমার আসলি ম্যান অফ দ্য ম্যাচ ছবির গপ্পো। কে লিখেছেন? বিজন ভট্টাচার্য। কোন বিজন ভট্টাচার্য? এক দশক আগেই যাঁর হাতে বাংলা নাটকের নতুন ইতিহাস লেখা হয়ে গেছে। সেই ঐতিহাসিক ‘নবান্ন’ নাটকের প্রবাদপ্রতিম নাট্যকার, গণনাট্য সঙ্ঘ তথা কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের সক্রিয় সদস্য, টালিগঞ্জের মূল ধারার সিনেমার কাহিনি লিখতে এসে কী করলেন? না, ভয়ঙ্কর প্রতিবাদী বিপ্লবী, আগুনখোর আপোষহীন, প্রগতিশীল কিছু করার জন্য তিনি নিশ্চয়ই টলিপাড়ায় পা রাখেননি। কিন্তু ভাবনা-মগজ সব চুলোয় দিয়ে স্রেফ পাবলিকের ইচ্ছাপূরণের ঠিকেদারি করতেও তিনি নামেননি। তাই ‘সাড়ে চুয়াত্তর’-এ তিনি চুপচাপ কিছু নাটুকে কায়দা ব্যবহার করলেন। সেগুলোকে এত বেশি খেলালেন না, যাতে লোকে তাঁর হাতের সব তাস একবারে দেখে ফেলবে; আবার ঠিক-ঠিক জায়গায় ঠিকঠাক হিসেবের তাস ফেলে দর্শককে একদম মাত করেও দেওয়া গেল, সত্তর বছর ধরে যেটা পুরনো হল না।
এই খেলাটার মাঝখানে আছে পরিযান। মানে মাইগ্রেশন। মফস্সল থেকে সদরে— সদর থেকে মফস্সল বা গাঁয়ে— নিজের বসতভিটে স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের ছায়ায়-মায়ায়— আবার পরিজন মহানগরের অন্দরেও। কখনও উচ্ছেদের আইন পুরোদস্তুর বাড়িওয়ালার পক্ষে। এই বিনা নোটিশে দিনেদুপুরে ভাড়াটেকে ঘটি-বাটি-কলেজপড়ুয়া সোমত্ত মেয়েসুদ্ধ রাস্তায় বের করে দেওয়া যায়। রমলা, মানে সুচিত্রা সেনেরা সপরিবারে এভাবেই তো ঘরছাড়া হয়ে অন্নপূর্ণা বোর্ডিং হাউস-এ প্রায় শরণার্থীর মতো উঠে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। এখান থেকেই তো কাহানি মে টুইস্ট-এর শুরুয়াত। কাহিনিকার বিজন আর ছবির চিত্রনাট্যকার-পরিচালক নির্মল দে পরিযানকে কখনও কোথাও সামনে এনে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাননি। কিন্তু অন্নপূর্ণা বোর্ডিং হাউস-এর মতো পরিযায়ী মানুষদের মাথা গোঁজার একটা আস্তানাকে সিনেমার কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে সারাক্ষণ খাড়া করে রেখেছেন। তার একতলার রান্নাঘর-ভাঁড়ারঘর-কলতলা থেকে পাঁচতলার ছাদের ঘর, মেসের কাজের লোকের পায়ে-পায়ে একতলা থেকে তেতলা অবধি আঠেরোটা সিঁড়ি, আর সেই বোর্ডিং ভর্তি করে জনা বিশ-বাইশ পরিযায়ী মানুষজনের জীবনযাপনের সকালসন্ধে— এই মিসান-এর ভাঁজে-ভাঁজে ছড়িয়ে রেখে দেওয়া হয়েছে সিনেমার যত নাটক, যত ঝাল-মশলা-চাটনি-আচার।

এর ভেতরেও একটা নোনতা-মিষ্টি মজার প্যাঁচ আছে, যাকে পাঞ্চ-ও বলা যায়। কলকাতা শহরের মেসবাড়ি ও বোর্ডিং হাউস নিয়ে বাঙালি মধ্যবিত্তের একটা নস্টালজিয়া-মাখামাখি আদিখ্যেতা ছিল বা এখনও আছে। বাংলা সাহিত্যে অনেক বিখ্যাত কাজকর্ম আছে মেসবাড়ির পটভূমিকায়। হ্যারিসন রোডে ব্যোমকেশ-অজিত, বনমালী নস্কর লেনে শিশির-শিবু-ঘনাদারা অনেক স্মরণীয় দিনরাত্রি কাটিয়ে গেছেন। অন্নপূর্ণা বোর্ডিং হাউসও উত্তর ও মধ্য কলকাতার সেই ট্র্যাডিশনাল মেস-কালচারের জ্যান্ত টাটকা হাতেগরম নমুনা। আমরা ধরেই নিই যে, মেসবাড়িতে যারা আরও এক-দু’জন বোর্ডারের সঙ্গে একই ঘরে ঘেঁষাঘেঁষি করে, একই কমন চানঘর ভাগাভাগি করে, মেসের ঠাকুরের হাতে সকাল-বিকেল মোটামুটি একই রুটিন ‘মিল’ সোনামুখ করে খেয়ে জীবন কাটাচ্ছে, তাদের শহর কলকাতায় আর কোনও রকম মাথাগোঁজার ঠাঁই নেই! এখন মেসবাড়িতে তো আর কেউ সাধ করে সংসার পাতে না! তাই জম্ম-কম্ম সবটাই মেসবাড়িতে, এমন ঘটনাও ঘটে না বললেই চলে! তার মানে এমন কোনও দূর মফস্সলে তাদের শেকড়বাকড়, যেখান থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে কলকাতার কলেজ-আপিস-আদালতের কাজকম্ম ম্যানেজ করা যায় না। সুতরাং মেসবাড়িতে থাকাটা তাদের অনেকটাই বাধ্যতা, খানিকটা সুবিধে। কলকাতা শহরে বাসাবাড়ির চড়া ভাড়া গুনতে হয় না। নিত্যি হাটবাজার-রান্না-খাওয়ার হ্যাঙ্গামও পোহাতে হয় না। আবার সবাই মিলে হইচই করে মেখে-জুড়ে থাকার ফলে খালি বাসার সেই হা-হা করে গিলতে আসার একাকিত্বটাও তাড়া করে না। তবু তো এরই সঙ্গে নিজের ‘দেশের বাড়ি’র জন্যও এই ‘বোর্ডিং-বিহারী’দের একটা পিছুটান থাকার কথা! অন্নপূর্ণা বোর্ডিং হাউসে নিরানব্বই শতাংশ বোর্ডারই তরুণ যুবক। বা বোর্ডিং-এর বাসিন্দা দুই প্রৌঢ়ের জবানিতে নেহাতই ছেলেছোকড়া! এই দুই প্রৌঢ় শিববাবু আর পঞ্চাননবাবু মেসের ‘ঐক্যবদ্ধ যুবশক্তি’র সামনে প্রায় সবসময়ই ‘আউট নাম্বার!’ যে-কোনও তর্ক-ভোটাভুটিতে এই যৌবনজলতরঙ্গের সামনে তাঁদের খুচরো বাগড়া প্রায়ই ভেসে যায়। এই পাঁচমিশেলি নবীনদের দলে গায়ক-হঠযোগী-বেসুরে-মাতাল-কলেজছাত্র-কেরানি-বেকার সব রকম নমুনাই আছে। আর প্রবীণ ও নবীন দু’দলের মাঝখানে আছেন এক ব্যোমভোলা উদাসী কালীসাধক—যিনি পান্নালাল ভট্টাচার্যের গলায় দুর্ধর্ষ শ্যামাসঙ্গীত গান আর মাঝে মাঝেই ‘ব্যোমকালী’ বলে হাঁক পেড়ে মেসসুদ্ধ লোকের পিলে চমকে দেন।
তিনি কোনও পক্ষেই নেই বলেই বোর্ডিং-এর যাবতীয় সালিশিসভায় তিনি চেয়ারম্যান, স্পিকার, সভাপতি। কিন্তু এই সব বয়সের সব পক্ষ, এমনকী জোট নিরপেক্ষ (বা কালীপক্ষের) সাধক মানুষটি, যাদের সব্বারই মেসের বাইরে বা পেছনে একটা পিছুটানের পরিযানের জীবন থাকার কথা, ‘সাড়ে চুয়াত্তর’-এর কাহিনি-চিত্রনাট্য তাঁদের কাউকেই ঠাঁইনাড়া করেনি। মেসের বাইরে তাদের কোনও পরিচয় বা আইডেনটিটির খোঁজও করেনি। এখানে সদর থেকে মফস্সলে, দেশের বাড়ি থেকে মেসবাড়িতে আর ভাড়াবাড়ির নিজস্ব আব্রুর পাঠ চুকিয়ে বোর্ডিং হাউসের হাটের মধ্যে যাতায়াত আর মাথা গুঁজতে তিনজন বা তিনটে ইউনিটকেই দেখা গেছে। ছবির তথাকথিত রোমান্টিক নায়ক উত্তমকুমার ওরফে রামপ্রীতি অনেকদিন দেশের বাড়িতে কাটিয়ে বোর্ডিং-এ ফিরছে। বড়লোকের আদুরে ছেলে, মেসবাড়িতেও তার আলাদা সিঙ্গল রুম— ছড়ানো-গোছানো-শৌখিন। একটু দেমাকি, মেজাজি, একগুঁয়ে হলেও মেসের মালিক থেকে চাকর, সব্বার কাছে তার আলাদা খাতির। ভাড়াটে বাড়ির ছাদ হারিয়ে, ওই রামপ্রীতির পাশের ঘরেই মা-বাবার সঙ্গে পার্টটাইম ঘরকন্নার আয়োজনে সুচিত্রা সেন মানে রমলা। আর রামপ্রীতি ও রমলারা অন্নপূর্ণার মন্দিরে মানে বোর্ডিং হাউসে পা রাখার আগেই ভোরের ট্রেন ধরে গ্রামের বাড়ি-বাগান-গোয়ালঘর-পুকুরধার-ছেলেমেয়ে এবং গিন্নিসুদ্ধ ভরা সংসার পেছনে রেখে, প্রতি সোমবারের মতোই মেসবাড়ির বারোয়ারি পরিবারে ফেরত আসছেন এই বোর্ডিং হাউসের সোল প্রপাইটার রজনীবাবু।
বিজন ভট্টাচার্য-নির্মল দে কম্বোজুটি এখানটাতেই তাঁদের হাতের আর একটা তাস ফেলছেন। তাঁরা মেসবাড়ির দাঁড়ে পাকাপাকি বাসা বাঁধা রাঁধুনি বামুনের বেড়ে দেওয়া দানাপানি খাওয়া মেসপাখিদের একদিকে রেখে, উল্টোদিকে রামপ্রীতি, রমলা আর রজনীবাবুর সাবপ্লটগুলো সাজিয়েছেন। যুবক আর প্রবীণ মেসবাসীদের পরিবার-বিচ্ছিন্নতার কাউন্টার পয়েন্ট হিসেবেই যেন আসছে ‘হোমসিক’ রামপ্রীতি, যে বাড়ি গেলে আর ফেরবার নাম করে না— আর রমলার বাবা অঘোরবাবু তো মেয়ে-বউ নিয়ে মেসের হাটেই একখণ্ড সংসার পেতে বসেছেন— এবং রজনীবাবু, দামি বোর্ডার রামপ্রীতি আর বিপদে ভেসে আসা দূর সম্পর্কের আত্মীয় রমলাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ব্যালেন্সের খেলা খেলতে-খেলতে যার নিজের আটপৌরে মফস্সলি দাম্পত্যটাই ঝঞ্ঝাটে পড়ে যায়। রজনীবাবুর এই কখনও তিতকুটে-কষটা, কখনও টক-ঝাল-মিষ্টি দাম্পত্যের খুঁটিনাটি গপ্পে আমরা নিশ্চয় আসব। কিন্তু তার আগে বিজন-নির্মলবাবুর পরের দানটা একবার বুঝে নেওয়া যেতে পারে। ‘পারিবারিক’ মেসবাসী আর পরিবার ছাড়া মেসপাখিদের এই ভাগাভাগি, সেন্টিমেন্টাল টানাপড়েনের মাঝখানটায় তাঁরা এইবার জেন্ডার-কার্ডটা ফেলে দিচ্ছেন। এতদিনে স্ত্রী-চরিত্র বর্জিত মেস-নাটকে আস্ত একটি যুবতী নারী আমদানি করছেন। আর তাতেই অন্নপূর্ণা বোর্ডিং হাউসের কয়েক তলা জুড়ে আইইডি বিস্ফোরণ ঘটে যাচ্ছে! তাতে ‘হতাহত’-এর সংখ্যা, পরিচয়, বিস্ফোরণের রকমসকম নিয়েই আমরা এবার একটু নাড়াচাড়া করব।
কে বা সেই বিনোদিনী... রিনিকি রিনিকি ঝিনি
বিস্ফোরণের ছানবিন তদন্তে যাওয়ার আগে আমরা ‘সাড়ে চুয়াত্তর’-এর প্রথম দুটো সিকোয়েন্স, একটু যাকে বলে ‘রিক্যাপ’ করে নিতে পারি। এটা রবি আর সোম দু’দিনের দুটো ভোরের ছবি। লোকেশন, পাত্রপাত্রী, মর্জিমেজাজ সব আলাদা। দুয়ের মধ্যে যোগসূত্র কেবল ওই রজনীবাবু। রোববার ভোরের দৃশ্যটা শুরু হচ্ছে, রজনীগিন্নিকে দিয়ে। তিনি উঠোনে গোবরছড়া দিচ্ছেন। গোয়ালে গরুটা ডাকাডাকি শুরু করেছে। তিনি তাকেও সাড়া দিচ্ছেন— যাচ্ছি, মা যাচ্ছি! এদিকে শোওয়ার ঘরে রজনী-দম্পতির সন্তান-ব্রিগেডের সবচেয়ে ছোটটি বিছানা ভিজিয়ে ফেলে অ্যায়সা চিৎকার জুড়েছে যে আগের রাতেই বাড়ি ফেরা রজনীবাবুর ঘুমের দফারফা। তিতকুটে-তিরিক্ষি মেজাজ নিয়ে ঘুম থেকে উঠে, তারপর স্ত্রীকেও ডেকে-ডেকে সাড়া না পেয়ে, রজনীবাবুর সাধের উইকএন্ড-এ তখন ভোর সকালেই সন্ধ্যা নামে-নামে! আসলে এমনিতে রজনীবাবুর সংসার, দাম্পত্য এবং সপ্তাহে একদিন দেশে ফেরা, মাঝারি বয়েস, মাঝারি বিত্ত, বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের বাসিন্দা যে-কোনও হপ্তাবাবুদের মতোই। প্রথম সন্তান একটু বেশি বড়। শেষেরটি একটু বেশি ছোট। মাঝের দু-তিনজন প্রায় মাথায়-মাথায়। ছেলেমেয়েদের ঝক্কি সামলাতে-সামলাতেই গিন্নির বয়স-ওজন-মেজাজ সবই বেড়েছে। সেই ভারিক্কি, খ্যাঁকখ্যাঁকে, খিটখিটে ভদ্রমহিলার মধ্যে প্রথম যৌবনে সেই আদুরে-আহ্লাদি-প্রেয়সী স্ত্রীকে স্বভাবতই খুঁজে পাওয়া মুশকিল। হপ্তাবাবুরা তেমনটা খোঁজেনও না। তাদের অত ধৈর্য-সময় নেই। সপ্তাহান্তে মোটামুটি রুটিন শরীরের চাহিদা মিটে গেলেই চলে যায়।
কিন্তু রজনীবাবু তাঁর মাথাজোড়া টাক, ফতুয়া, মাঝে মাঝেই কোমরের কাছে আলগা হয়ে যাওয়া ধুতির কুচির আড়ালে আস্ত একটা রসের ভাঁড়ার সামলেসুমলে বাঁচিয়ে রেখেছেন। সেই মাঝ বয়সের গেঁয়ো মফস্সলি আটপৌরে দাম্পত্য রোমান্সের দাবি তেমন বেশি নয়। এই একটু কাছাকাছি গা ঘেঁষে বসা, একটু হেসে দুটো কথা বলা, সকালের সামান্য পরোটা-আলু ছেঁচকির জলখাবারটাতেও একটু ভালবাসা ঢেলে দুজনে একসঙ্গে খাওয়া, ছেলেমেয়েদের লুকিয়ে রাতের বেলা পুকুরপাড়ে একটু নিরিবিলিতে বসা— ব্যস, এইটুকুই তো! কিন্তু রজনী-গিন্নি তাতেও খ্যাঁকখ্যাঁক করেন! বুড়ো বয়সে এত ঢং-আদিখ্যেতা তার অসহ্য মনে হয়। কিন্তু তার পতিদেবতাটি তো কলেজ-কালের বিরহী প্রেমিকটির মতো রোববার রাতে বাড়ির দাওয়া আর উঠোনে ছটফটিয়ে পায়চারি করেন আর গুনগুনিয়ে কীর্তনের কলি ভাঁজেন— ‘কেন সে আসিল না/ ওগো আসি বলে গেল চলে সই!’ গিন্নির পাষাণ হৃদয় সে-আকুলতার সাড়া দিল কই! রজনীর হিসেবে বউ মানে কি? বউ মানে গাছতলা! পুরুষ মানুষ সারাদিন বা সারাহপ্তা খেটেখুটে, তেতেপুড়ে সেই গাছের ছায়ায় দু’দণ্ড একটু জুড়োবে! নিজের বউয়ের প্রতি তার অনুযোগ— ‘তুমি আমার খেজুড় গাছ। কাঁটা আছে। ছায়া নেই।’
দশ আনা ভিক্টোরিয়ান পিউরিটান নীতিবাগিশপনার সঙ্গে ছ’আনা মিল-বেন্থামের উপযোগবাদ মিলে উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে নবজাগ্রত বাঙালি মধ্যবিত্তের যে দাম্পত্য-রুটিন লেখা হয়ে গিয়েছিল, এই বউ-কাম-গাছতলার আইডিয়াটা ওখান থেকেই আসছে। কিন্তু রজনী-গিন্নি যেই পালটা মুখ ঝামটা দিয়ে বলেন, ‘ছায়া আছে অমন গাছ খুঁজলেই তো পারো’, আর রজনীবাবুও গেয়ে ওঠেন ‘কিন্তু বটবৃক্ষ পাই কোথা?’ অমনি ওই ঘোর মফস্সলি দাম্পত্য-কমেডিও একটু অন্যমাত্রা পেয়ে যায়। টালিগঞ্জ হয়তো হলিউডের মতো ‘সেভেন ইয়ার্স ইচ্’ বানাতে যাচ্ছে না। তবু দাম্পত্য-সংলাপে মিঠেকড়া খুনসুটিতে পরকীয়ার একটা হালকা মৌতাত রেখে দেওয়া হচ্ছে সেটাই বা কম কী!
তাছাড়া প্রথম সিকোয়েন্সেই এই কাহিনি চিত্রনাট্যের ‘মাউন্টিং’ আর ক্লাইম্যাক্সেরও দু-চারটে সুতো ছেড়ে যাওয়া হল। সে তো পরের ব্যাপার। আমরা সেখানটায় অবশ্যই আসব। রজনী চাটুজ্জে ও তার পরিবারের মিষ্টি-ঝালে মেশানো দাম্পত্যের পিছুও নেব। তবে তার আগে বিজন-নির্মল জোট অনন্নপূর্ণা বোর্ডিং হাউসের ভেতরে ‘জেন্ডার’-প্রশ্নের যে-বলটা গড়িয়ে দিলেন, এবং পলিটিকালি কারেক্ট থাকার একটুও চেষ্টা করলেন না— তার ফলটা কী ফলল, সেটাও একটু বুঝে নেওয়া দরকার।
আমরা এর আগে রবিবার আর সোমবার দু’দিনের দুটো ভোরের কথা বলছিলাম। রজনী চাটুজ্জের দেশের বাড়ির একদিন সকাল থেকে রাতের গপ্পো তো হয়েই গেল। সোমবারের ভোর হচ্ছে মেসবাড়ির রান্নাঘরে। মেসের ছাই-ভাঙতে-ভাঙা-কুলো, রজনীবাবুর ‘ম্যান ফ্রাইডে’, তার নিজের ভাষায় ‘চাকর মনিষ্যি’ মদন দ্য গ্রেট থালায় চায়ের কাপ সাজাচ্ছে। মদনের সেই চা দেওয়ার সূত্রেই মেসের সব বোর্ডারদের সঙ্গে আমাদের চেনাজানা হয়ে যায়। কেউ ভৈরবী সুরে গলা সাধছে। কেউ শীর্ষাসন করছে। কেউ ডন বৈঠক। বাথরুম বন্ধ পেয়ে কেউ পেট চেপে প্রাণপণে হাঁটাহাঁটি করছে। কারোর আবার আগের রাতের খোঁয়ারিই ভাঙেনি! সব মিলিয়ে টিপিক্যাল পাঁচমেশালি বোর্ডিং হাউসের স্কেচ— যার একতলা থেকে তিনতলা, পা থেকে মাথা অবধি বোঁটকা-বদখত পুরুষালি গন্ধ!
ততক্ষণে তার আধুরা দাম্পত্যপ্রেম ফেলে রেখে, দেশের বাড়ি থেকে রজনী চাটুজ্জে আর মেসের বাজার সেরে সরকারমশাই বোর্ডিং-এ ফিরেছেন। তারপরেই তো শুরু হয় নবীন বোর্ডারদের যৌবন-বন্দনার অমরগীতি— ‘আমার এ যৌবন/চম্পা চামেলী বনে/অকারণ উচ্ছল দিন গো’! যে-গানের পিকচারাইজেশন-এ ভানু-জহর রায়-শ্যাম লাহাদের পাশাপাশি পর্দায় প্রথম ও সম্ভবত শেষবারের মতো মুখ দেখান গানের প্লে-ব্যাক গায়করাও— মানবেন্দ্র, শ্যামল মিত্র, সনৎ সিংহ এমনকী মতান্তরে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যও। এই গানেরই লিরিকে যৌবনের বাসনা কোরাসে বেরিয়ে আসে। এবং সেখানে ঘুরেফিরেই আসে কোনও এক স্বপ্নসুন্দরীর কথা। তিনি এখনও মেসপাখিদের কল্পনার আঁচে একটু-একটু করে তৈরি হচ্ছে। এখনও তার নূপুর পরা পা, এই মাটির দুনিয়ার জমিনে পড়েনি। তবু তার ‘রিনিকি ঝিনিকি ঝিনি’ শোনা যাচ্ছে! ‘তার কালো চোখে হায়/ আলো ছায়া খেলে যায়’!
কিন্তু সকালের রোমান্টিক গানে যে ছিল স্রেফ স্বপনচারিণী, যুবক মনের কবিতাকল্পনালতা, সন্ধেবেলায় আপিস-কলেজ থেকে মেসে ফিরেই সেই ‘বিদ্যুৎবরণা চম্পকবরণী’-কেই মেসের তেতলার বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাবে, বোর্ডিং-এর তরুণ-ব্রিগেড বোধহয় এতটা ভাবতে পারেননি। রমলারা এল— ফতুয়া-গেঞ্জি-খালি গা-গামছা-সর্ষের তেল-নস্যির ডিবে-নাকঝাড়া সমেত যাবতীয় বেটাছেলেমার্কা বেআদব, বেআক্কেলে, উড়নচণ্ডী মেসজীবন আচমকা নড়েচড়ে, গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসল। সেই সময়ের গড়পরতা হিন্দু বাঙালি মধ্যবিত্তবাড়ির ছেলেদের অচেনা-অনাত্মীয়া মেয়েদের সম্পর্কে আড়ষ্ঠতা, অনভ্যাস, নার্ভাসনেস— আবার একই সঙ্গে ভয়ানক কৌতূহল, ছুঁকছুঁকানি, একবার একটু কাছাকাছি আসার, দুটো কথা বলার ভয়ানক দুর্নিবার লোভ— এই সবসুদ্ধ মেসবাড়ির এতকালের নারীবর্জিত জীবনযাত্রা, রমলা ও তার পরিবারের একফালি গেরস্থালির চারপাশে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

এই যে মেসবাড়ির ভেতর গেরস্থবাড়িকে এনে ফেলার অসম্ভব, অথচ পরিস্থিতির বিচারে ততটা অবিশ্বাস্য নয়, এমন একটা প্রবল গোলমেলে ডায়ালেকটিক বিজন-নির্মলরা ফাঁদলেন, সেই খেলা সামলানোর তরিকাটা কী দাঁড়াল? প্রথমের দিকটায় তো গোটা মেসের মন পবনের নাও খানিক মানবিকতা, শিভালরির ঘাটেই বাঁধা ছিল। বিশেষ করে প্রবীণদলের শিববাবু যেভাবে যৌবন-ব্রিগেডকে ‘অবিবাহিত ছেলেছোকড়া’ বলে তাদের চরিত্র তুলে ঠেস দিয়েছিলেন, সেখানে তরুণ বোর্ডার কেদারের ভাষায় যুববাহিনীরও একটা প্রমাণ করার দায় ছিল— ‘বিয়া না কইরাও আমরা চরিত্রবান।’ কিন্তু তাদের ‘ড্রিমগার্ল’, কল্প-ললনা গানের মতোই চোখের সামনে দিয়ে ছন্দের ঝর্না ঝরিয়ে পাঁচতলা থেকে একতলা পেখম পেলে নেচে বেড়াচ্ছে, তারপরেও কি অত নীতিকথা, এথিকস-টেথিকস মনে রাখা যায়? সুতরাং সকাল থেকেই গলা সাধা, সেতারে পিড়িং-পিড়িং, বারান্দার রেলিং-এ ভিড়, চোখ টেপাটেপি, বেসুরো গলায় রোম্যান্স ঢেলে বিলিতি সুর ভাঁজা, এমনকী রমলার যাতায়াতের রাস্তায় একটু-আধটু আওয়াজ দেওয়া— সবটাই চলতে থাকে।
কিন্তু বোর্ডিং হাউসের পুরুষ-পৃথিবী একটিমাত্র যুবতীর মোকাবিলায় কেবলই এলোমেলো ঘেঁটে গেলে তো আর ছবি হবে না। তাই হঠাৎ আসা বিনোদিনীর গ্ল্যামার-আলোর ঝলকানিতে সাময়িক হকচকিয়ে যাওয়া অন্নপূর্ণা বোর্ডিং-এ অনিবার্য ভাবেই প্রেম আসে। শুরুর ঝগড়াঝাঁটি-ভুল বোঝাবুঝির পরে রামপ্রীতি যথারীতি প্রেমে পড়ে রমলার। ‘বেহিসেবি ভালবাসা’ ভেসে যেতে আপত্তি থাকে না মেয়েটিরও! কিন্তু মেসের সবচেয়ে বড়লোক, সবচেয়ে সুপুরষ, সবচেয়ে ‘এলিজেবল ব্যাচেলর’ এক টুসকিতে বাকি সবার ‘বিনোদিনী’কে তুলে নিয়ে গেলে ব্যাপারটা কেমন ফ্যাটফ্যাটে পানসে মতো হয়ে যায় না? তাই যোগ্যতায় ‘সুটেব্ল বয়’-এর নখের যুগ্যি না হলেও বাঙালের গোঁ নিয়ে রমলা-রামপ্রীতি প্রেমের কিস্সার মাঝখানে ঢুকে পড়ে রোগা ডিগডিগে কেদার। প্রেমের ডুয়েলে কেদারের এই হঠাৎ রামপ্রীতির চ্যালেঞ্জার হিসেবে দাঁড়িয়ে যাওয়া, চিত্রনাট্যের মাঝামাঝি জায়গায় এসে এটাও বিজন-নির্মল দে-র তরফে একটা মোক্ষম দান। যেটা একই সঙ্গে কমেডি-চরিত্রাভিনেতা হিসেবে টালিগঞ্জে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা পাকাপাকি জায়গা করে দেয়।
কেদার আমার নেমে আয় নেমে আয়...
কেদার যে তার ৩৬ ইঞ্চি বুকের ছাতি নিয়েও রামপ্রীতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রমলার জন্য লাইন লাগাল, সেখানে কামাখ্যা–টামাক্ষাদের মতো অন্যান্য বোর্ডারদের উসকানি তো ছিলই। রামপ্রীতির রোম্যান্স-পথে কাঁটা বিছোতেই কেদারকে যাকে বলে পিনিক খাইয়ে রমলাদের ঘরে পাঠানো হয়েছিল। এটা একেবারে পুরুষের চিরকেলে অবদমিত হিংসুটেপনা! মেয়েটাকে দল পাকিয়ে দূর থেকে হিড়িক মারব, কিন্তু কাছে গিয়ে আলাপ করা হিম্মতে কুলোবে না। বন্ধুদের মধ্যে কেউ সেই সাহসটা দেখালে, তাকে টুক করে ল্যাং-টা মারব! তবে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কেদার কিন্তু স্রেফ বুকভরা হিংসে নিয়ে রমলাদের ঘরের দরজায় টোকা মারছে না। তার মনের মধ্যে একটু প্যাঁচ, খানিকটা কুচুটেপনা যে ছিল না, তা নয়। মেয়েদের প্রতি তেমন একটা শ্রদ্ধাভক্তি, সম্মান-টম্মান দেখানোর শিক্ষাদীক্ষা, কায়দা-পালিশও ছিল না। বরং সেজেগুজে গ্যাটম্যাট করে কলেজে যাওয়া, ছেলেদের মুখে-মুখে ফটাফট তর্ক করা, ঘোর আধুনিকা ‘বাত্তিওয়ালা মাইয়া’ মানে তথাকথিত ‘এনলাইটেন’ মেয়েদের সম্পর্কে সেকালের (একালেও নয় কি?) গড়পরতা পুরুষের মতোই কেদারেরও চালু কিছু ধারণা বা সংশয় ছিল। যেমন, এইসব মেয়েরা বিয়ের পরে এয়োতির চিহ্ন শাঁখা-সিঁদুর এসব থেকে দূরে থাকবে— শ্বশুরবাড়িকে পাত্তা দেবে না— বরের যত্নআত্তি করবে না— আরও কত কী!
রমলাও তার হিসেবে ‘বাত্তিওয়ালা মেয়ে’ই বটে! তবু যে কেদার সেদিকে গুটিগুটি এগোয়, সেখানে মেসের বন্ধুদের (রামপ্রীতিসুদ্ধ) টেক্কা মারা দেখিয়ে দেওয়ার একটা ব্যাপার তো ছিলই। তার সঙ্গে আরও দু’একটা ফ্যাক্টর ছিল। আর সেখানটাতেই অভিনেতা ভানু বন্দোপাধ্যায় উত্তম-সুচিত্রার নাকের ডগা দিয়ে ডাবল সেঞ্চুরি মেরে বেরিয়ে গেছেন! যে-কেদার প্রথমদিন রমলাদের ঘরে গিয়ে সুন্দর গন্ধওয়ালা দামি চা খেয়ে, রমলার সঙ্গে একটা-দুটো কথা বলে বন্ধুমহলে ফিরে এসে লাফিয়ে নেচে প্রায় ট্রফি জেতার উল্লাস করে আর মালপোয়া খাওয়ার পর যে কেদারকে রমলা ছাদে ওঠানামার কাঠের সিঁড়িটা অবধি এগিয়ে দেয়, সেই দুজন ঠিক এক লোক নয়। ভানু খুব ছোট-ছোট কয়েকটা টাচে এই তফাতটা তৈরি করে দেন।
প্রথমবার কেদার যখন ‘তা-না-না-না-না-না-না’ সুর ভাঁজতে-ভাঁজতে ঘরে ঢোকে, তারপর সেই সুর-তালেই ‘কইসে কথা আমার লগে, আমার লগে কইসে কথা’ গাইতে-গাইতে একপাক নেচে নেয়— তখন চোখে-মুখে, ধুতি-শার্ট পরা শরীরের ভাষায় একটা বোকা, গেঁয়ো ছেলেমানুষিভরা বারফাট্টাই ছিল। সেই রোয়াবেই সে কামাখ্যার পিঠে চাপড় মেরে বলে, ‘যা আগে এক গেলাস জল নিয়ে আয়!’ বন্ধুরা রেগেমেগে চলে গেলেও সে তাদের ফেরাবার খুব একটা চেষ্টা করে না। নিজের সদ্য গজানো আত্মবিশ্বাসেই সে তখন মশগুল ।
এই চেষ্টা করেও সামলাতে না পারা, উপচে পড়া খুশিয়াল ভাবটার পেছনে ঢাকার ভানু আর একটা ন্যারেটিভও তৈরি করছিলেন। ১৯৫৩ সালে এপার বঙ্গের কোনায়-কোনায় যে বাস্তুহারা জনতার কোনও রকমে বেঁচেবর্তে থাকার দাঁতে-দাঁত চেপা লড়াই চলছিল, মেসের পুরোদস্তুর ঘটি-আবহে একমাত্র বাঙাল কেদারের মুঠোতেও যেন সেই লড়াইটার একটা অদৃশ্য নিশান ধরা ছিল। এঁটে ওঠার কোনও চান্স নেই জেনেও, সে তাই অবুঝ-নাছোড় মরিয়া ঢাকাইয়া বাঙালের গোঁ আর রোখ নিয়ে রমলা-রামপ্রীতির সম্পর্কের মাঝখানে নিজেকে গুঁজে দেয়। বিরহী-বিরহী মুখে বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকা রামপ্রীতির সামনে দিয়ে বিলিতি ‘শ্রাগ’ বা কাঁধ ঝাকানো আর খাঁটি দেশি বগল বাজানোর মাঝামাঝি একটা ভঙ্গি করে মুখে অনেকটা গর্ব মেখে হেঁটে যাওয়াটাও ভানুর স্ল্যাপস্টিক-এর একটা মাস্টার স্ট্রোক।
কিন্তু ধুতি-পাঞ্জাবিতে সেজে যে কেদার যেচে রমলাদের ছাদের ঘরে মালপোয়া খেতে যায়, সে গোড়ায় ‘মাসিমা মালপোয়া খামু’ গোছের কথা বলে একটা স্ট্রিট স্মার্টনেস দেখানোর চেষ্টা করলেও আসলে ভেতরে-ভেতরে বেশ একটু ঘাবড়েই আছে। আসলে সে তো নিজের মতো একটা হেস্তনেস্ত করতে এসেছে। খাস কলকাত্তাইয়া শিক্ষিতা ‘বাত্তিওয়ালা মাইয়া’র সৌজন্য ভদ্রতার প্যাকেজিং-এ, কোথাও তার জন্য একটুও রোম্যান্সের ছিটেফোঁটাও আছে কি না, সেটা সে বুঝে নিতে চায়। ভানু এখানে একসঙ্গে কয়েকটা মুড নিয়ে জাগলিং করেছেন। রমলা মালপোয়া আনতে যাওয়ার ফাঁকে ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় ঝট করে একবার চুল আঁচড়ে নিয়েছেন। খোলা জানলা দিয়ে একফাঁকে রামপ্রীতি-সহ বন্ধুদের জমায়েতটাও দেখে নিয়েছেন। তাই তাদের দেখিয়ে-দেখিয়েই জানলার ধারে ‘খাড়াইয়া খাড়াইয়া’ই তার মালপোয়ায় পয়লা কামড়।
তবে কেদারের পাশে রমলাকে দেখে গৌর-কামাখ্যারা বাড়াবাড়ি রকমের আদেখিলাপনা শুরু করলে রমলা যখন ঠাস করে তাদের মুখের ওপর জানালাটা বন্ধ করে দেয়, তখন থেকেই পরিস্থিতিটা কিন্তু একটু বদলে যাচ্ছে। বিদ্যুৎলতার মতো ঝকমকানো ‘বাত্তিওয়ালা’ যুবতীটির সঙ্গে সে তখন একা। ঘোর কলকাত্তাইয়া ঘটি বাড়ির মাইয়াটির শিক্ষা, সহবত, স্বাধীনতার সামনে তার তখন ল্যাজেগোবরে অবস্থা। একে তো বন্ধুদের চ্যাংড়াসুলভ অসভ্যতা, বন্ধ জানালার ওপাশ থেকেও তাকে অস্বস্তিতে ফেলছে। এদিকে এই মেয়েটির ভদ্রতার মাধুর্য, সৌজন্যের যত্ন, তার মতো চালচুলোহীন, মেসের ‘তিতা’ চা খাওয়া বহুকাল ঘরের লোকের হাতের রান্না ‘সোয়াদ’ না পাওয়া পরিযায়ী মেসপাখির মনের অন্দরে কোথাও ‘ঘর’-এর লোভ জাগাচ্ছিল। আর সেই ইচ্ছেটাকে মালপোয়ার মতোই গবগবিয়ে হজম করে ফেলাটা তার পক্ষে তখন একটুও সহজ ছিল না।
এই জয়গায় ভানুর অভিনয় স্ক্যানিংটা দেখার মতো। নিজের বারান্দারা গৌর-কামাখ্যারা কীর্তনের সুরে গান ধরেছে— ‘কেদার আমার নেমে আয়, নেমে আয়...।’ কেদারের কাছে ওই হাঁকডাক তখন শুধু সিঁড়ি বেয়ে নিজের তলায় নেমে আসা নয়! রমলার চোখে তার বাকি ইভটিজার বন্ধুদের সঙ্গে সমান-সমান একই মাটিতে নেমে আসা! কেদার সেটা এক্ষুনি কিছুতেই হতে দিতে পারে না। তাই খেতে-খেতেই খানিকটা ঢোঁক গেলা, একটু বিব্রত, অনেকটা আমার-কোনও-দোষ-নেই গোছের মুখ করে ভানু বলেন— ‘দ্যাখছেন, দ্যাখছেন কাণ্ডটা!’
রমলা তখনও মধুর ভদ্রতায় কেদারের অভব্য বন্ধুদের অশালীনতাকে একটুও পাত্তা না দিয়ে তাকে খাবারটা শেষ করতে বলে। ভানু মালপোয়া খেতে-খেতে বারদুয়েক তারিফের ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়েন। খাওয়ার পরে আঙুল চাটতে-চাটতে বলেন— ‘বেশ খাইলাম। প্যাটটা একদম ভইরা গ্যাছে।’ এই বলাটার মধ্যে কোনও সাজানো, মেকি কলকাত্তাইয়া ভদ্রতা ছিল না। বরং ঘরোয়া যত্নআত্তিসুদ্ধ বাড়িতে বানানো খাবার স্বাদ করে খাওয়ার তৃপ্তি ছিল। আঙুলের ডগায় লেগে থাকা সেই ভাললাগার স্বাদ আর রসটুকু সুরুত করে চেটে নিয়ে, সেই এঁটো আঙুলটাই আধখাওয়া জলের গ্লাসে চুবিয়ে ধুয়ে নিয়ে টেবিল-ম্যানার্সের দফারফা করে ধুতির কোঁচায় হাতমুখ মুছে, তিনি যেন একটু আকুল-করুণ চোখেই রমলার দিকে ফের তাকান। কিছু একটা বলতে চেয়েও ‘না কিছু না’ বলে সামলে নেন।
এরপর রমলা যখন তাকে এগোতে আসে, ভানু তখনও আর একবার থমকে রমলার দিকে মরিয়া সতৃষ্ণ তাকান। যুবতীর মন জানার আর নিজের মনটা চেনানোর এটাই তো তার শেষ সুযোগ। কিন্তু রমলার চোখ, শরীরের ভাষা খুব ভরসা জোগায় না। তবু তারপরেও রমলা যখন সিঁড়ির কাছে এসে বলে ‘সাবধানে নামবেন, কাঠের সিঁড়ি’, ভানু তখন হালকা একটু সেন্টু খেললেন— ‘পড়লামই বা। কেউ তো কান্দব না!’ বিশ শতকের মাঝ বয়সের গড়পরতা ঘ্যানঘ্যানে, ন্যাকা বাঙালি পুরুষ মানুষের কমন, আনাড়ি আদিখ্যেতা! কেদারের সঙ্গে একটু বেমানান— তবু হাতের সব তাস যখন ফুরিয়ে যাচ্ছে, তখন বেসামাল রোমিও-র হয়ে মরিয়া এই দানটাও ফেলছেন ভানু। রমলা তার পরেও সৌজন্যের আস্ত প্রতিমা হয়ে জিজ্ঞেস করে— ‘কেন বাড়িতে কেউ নেই আপনার?’
এইবার, এইবার শ্রীভানু বন্দ্যোপাধ্যায় কমেডি চরিত্রাভিনয়ের ইতিহাসে সোনার জলে লিখে রাখার মতো কয়েকটা মুহূর্ত রচনা করছেন। চার আনা ফিচলেমোর সঙ্গে ছ’আনা উদাসী বিষাদ মিশিয়ে তিনি বললেন— ‘আছে, আবার নাই-ও।’ আর তারপর বাকি ছ’আনা কামাল করছে তার কামাল করছে তাঁর আয়ত দুটো চোখে। অনেকটা হয়তো-যদি-কিন্তু-তবু মেশানো কী আকুল প্রত্যাশা নিয়ে তিনি শেষ বারের মতো রমলার দিকে তাকান! ফিরবে না জেনেও কোথাও একটা ক্ষীণ দ্বিধাগ্রস্থ শিকে ছেঁড়ার আসা।
এই পুরো ব্যাপারটা ভানু তাঁর চোখ-মুখের পেশিগুলোয়, দাঁড়ানোর একটা থতমত ভঙ্গিতে ফুটিয়ে তোলেন। যে অভিনেতা ভানুকে তিনি ছ’বছর পরে তাঁর ‘নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে’ ছবিটায় পুরোদস্তুর ব্যবহার করবেন, তাকে সম্ভবত এই গোটা মালপোয়া-পর্বেই হাড়ে-হাড়ে চিনে নিয়েছিলেন নির্মল দে। এতক্ষণ পর রমলার সাজানো ভদ্রতারও ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। সারাক্ষণ একটা আনাড়ি, সুর-তোলা গোছের অভিনয় করে গেলেও এইখানে শরীরের একটা বিরক্ত ঝাঁকুনিতে সেটা নির্ভুল বোঝাতে পারেন সুচিত্রা সেনও। এরপর তো রামপ্রীতি-রমলার তেতলা-পাঁচতলা প্রেমপত্র চালাচালি পাকড়াও করে কেদার মেস-রোম্যান্সের হিংসুটে কাঁটা হবে। কিন্তু তার আগে হার নিশ্চিত জেনেও খেলতে নামা ‘প্রেমিক’ কেদারের জন্য কথাও একটু-একটু মন খারাপও বাঁচিয়ে রাখেন ভানু দ্য গ্রেট।
প্রেমপত্রের ‘কমেডি অফ এররস’ অথবা গোপনীয়তার দিব্যি রোম্যান্সের দুনিয়াজোড়া ইতিহাসে প্রেমপত্র একটা চিরকেলে ঘটনা। ‘কবুতর যা যা যা’ করে পায়রার পায়ে বেঁধে উড়িয়ে দেওয়া থেকে বাদশা হারেমের বাঁদি গেরস্থবাড়ির কাজের মাসি থেকে সরকারি ডাকপিওন— প্রেমপত্র-বাহক কে নয়! ‘সাড়ে চুয়াত্তর’-এ এই প্রেম-চালাচালির দূত মেসের সর্বঘটের কাঁঠালিকলা মদন চাকর। হিন্দু দেবদেবীর লিস্টে পুরাণকথা-মাফিক যিনি কামদেব। পুষ্পধনু থেকে কামশর ছুঁড়ে যুবক-যুবতীদের হৃদ মাঝারে কুছ-কুছ রোম্যান্স-চুলকুনি জাগানোই যাঁর স্বর্গীয় অফিশিয়াল অ্যাসাইনমেন্ট! মেসের মদনদেব অবশ্য গুষ্টির কাজ সেরে তারপর রমলা-রামপ্রীতির প্রেমের ফরমাইশ খাটে দুটো বাড়তি বকশিসের জন্য। এই ভূমিকায় চল্লিশ-পঞ্চাশ-এর দশকের বিখ্যাত কমেডিয়ান নবদ্বীপ হালদার তাঁর সব ম্যানারিজমসুদ্ধ একদম টেলার-মেড। তবে মদন যে প্রেমপত্রের বামাল-সহ ধরা পড়ছে, সেটা ঘটনাচক্রে রমলার লেখা। এবং তার লাইনে-লাইনে যুবকের মেয়ের তাজা বেপরোয়া উচ্ছ্বাস! প্রেমিককে ‘বেহিসেবি’ হওয়ার খুল্লমখুল্লা ইশারা, উসকানি! সব মিলিয়ে সেকালের কলকাতার ঘটিবাড়ির লজ্জাবতী মেয়েদের তুলনায় একটু বেশিই বেপরোয়া, নির্লজ্জ, ঘন বাসনার আভাস।
বোঝাই যাচ্ছিল, বোর্ডিং হাউসের নির্ভেজাল পুরুষতন্ত্র সে চিঠি নিয়ে প্রচুর আমোদ আর গসিপ করবে এবং করেছেও। আর তারপরে মেসের নৈতিক পরিবেশ দূষণের ওজর তুলে রজনীবাবুকেই সেটার বিহিত করার ভার দেয়। বউ-এর রাগি-হাঁড়ি মুখের কথা ভেবে বাড়ি ফেরার তাড়ায় রজনী চাটুজ্জে, রামপ্রীতিকে লেখা রমলার যৌবনসরসীনীড়ে সপসপে প্রেমপত্রটি তার বাংলা শার্টের পকেটে রেখেই রওনা দেন এবং চিঠির কথাটা বিলকুল ভুলে যান। আর এটাই বিজন ভট্টাচার্য-নির্মল দে-র শেষ মোক্ষম তাস। প্রেমপত্রের ‘কমেডি অফ এররস’।
যে-রজনীবাবু আনমনে অন্যের প্রেমপত্র পকেটে করে দেশের বাড়ি আসছেন, তিনি নিজেই গিন্নির কাছ থেকে এই বয়সেও একটা প্রেমপত্র পাওয়ার জন্য ব্যাকুল। গাঁ-মফস্সলের পরিযায়ী বাঙালি মধ্যবিত্তের দাম্পত্যপ্রেমে ভারতীয় ডাকবিভাগ আর চিঠির একটা মস্ত রোম্যান্টিক ভূমিকা ছিল। পাড়াগেঁয়ে বধূটি যদি কাজ চালাবার মতো বাংলা লেখাপড়া জানতেন, তাহলে রুজিরুটির জন্য শহরে পড়ে থাকা স্বামীটির বিরহজ্বালা একটু হলেও জুড়োতে পারতেন ওই চিঠির কাগজ-কালিতেই। সেখানে ‘অপুর সংসার’-এর অপর্ণার মতো নরম-মিঠে অভিমান মোড়া থাকতে পারে, ‘প্রতিমাসে আটটা চিঠি লিখবে বলেছিলে... গত মাসে সাতটা লিখেছ... মিথ্যুক...!’ কিংবা রজনী-গিন্নির মতো গন্ধমাখা গোলাপি খামে পাঠানো বিকশিতহেম— যার সম্বোধনে লেখা থাকত, ‘প্রিয়’, ‘প্রাণনাথ’, আরও কত কী!
যৌবনকালের সেই পত্রপ্রেমের নস্টালজিয়ার কথা বলতে বলতেই রজনী চাটুজ্জের প্রৌঢ় মুখও ভরিয়েও কীভাবে হাজার ওয়াটের সুখ-আহ্লাদ-রোম্যান্স উথলে উঠতে পারে, তুলসী চক্রবর্তী দুটো আঁচড়ে সেটা দেখিয়ে দেন। আর চাটুজ্জেগিন্নি মলিনাদেবী মুখ ফুলিয়ে, গোঁজ করে, ঝামটা আর ঝাঁকুনি দিয়ে প্রত্যেকবারেই তুলসীর ওই ‘বুড়ো বয়সের আদিখ্যেতা’র বেলুনে সমানতালে পিন ফুটিয়ে যান।
উত্তম-সুচিত্রাকে ফ্যাকাসে বেপাত্তা করে তুলসী-মলিনার মাঝবয়সি তালমিল এখানে সাতরাজার ধন মানিক খুঁজে আনার মতোই নির্মল দে-র আর এক ‘এক্সক্লুসিভ’ আবিষ্কার। সকালবেলায় জলখাবারের থালা নিয়ে মলিনার পিছু-পিছু তুলসীর অনন্ত ঘোরাঘুরি— বউকে নিজের হাতে একটু খাইয়ে দেওয়ার জন্য কী রমণীয় ঝোলাঝুলি— রাগ করতে-করতেও নাছোড় সেই স্বামী-সোহাগেই শেষ অবধি আলতো সাড়া দিয়ে খুকিবেলার মতো মলিনা দেবীর আদুরে-আহ্লাদি ছোট্ট হাঁ করে একটু খেয়ে নেওয়া— সব মিলিয়ে মলিনা-তুলসী জুটি সারা ছবি জুড়ে বেলাশেষের দাম্পত্যে এমনই হালকা-ভারী, মিষ্টি-ঝালে মাখো-মাখো রাশি-রাশি কোলাজ তৈরি করেন। এত সহজ, স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ততায় দুজনে চিত্রনাট্যময় নেচে-ভেসে-উড়ে বেড়ান, যেন তুলো-পালক!
সেখানটাতেই গোপন বোমার মতো এসে পড়ে ওই প্রেমপত্তর! কর্তার জামা কাচতে দেওয়ার আগে পকেট হাতরাতে গিয়েই গিন্নি যেটা পেয়ে যান। এবং ভুল বোঝাবুঝির সিলসিলা সেই শুরু! এখানেও বিজন-নির্মলরা আর একটা মজা করেছেন। রজনীবাবু গিন্নির প্রেমপত্রের নস্টালজিয়ায় ডুবে যেতে-যেতে বলেছিলেন, মুখবন্ধ গোলাপি খামে শুধু ভুরভুরে সুবাসই থাকত না। খামের ওপরে লেখা থাকত ‘সাড়ে চুয়াত্তর’— গোপনীয়তার খাস দিব্যি! সেই কোথাকার রাজস্থান থেকে উত্তর ভারত হয়ে রাজস্থানী লোকগাথার কড়া শপথ, বাংলার গাঁয়ের বধূর বা কোনও লাজুক কিশোরীর ভালবাসার গোপন কথাটি আড়ালেই রেখে দেওয়ার দিব্যি হয়ে উঠেছিল। শহরের মেয়ে রমলা তার চিঠিতে কোনও সাড়ে চুয়াত্তরের দিব্যি দেয়নি। সে-চিঠি প্রেমিকের হাতে পৌঁছনোর আগেই হাটের কিস্সা হয়ে গেল!
আর সেই শহুরে মেস বাড়ির টাটকা গসিপই পরিযায়ী পকেটে চড়ে যৌবন ফুরনো এক মফস্সলি গৃহবধূর ভরন্ত ঘরকন্নায় উড়ে-এসে-জুড়ে-বসে মহা হাঙ্গামা বাঁধিয়ে দেয়। এ যেন সেই ‘ব্যাপিকা বিদায়’ নাটকের অমর সংলাপ— ‘গোপন গোপন গোপন, কলহের বীজ রোপন’। আর রজনীবাবুর পকেট থেকে রমলার প্রেমপত্র উদ্ধারের পর থেকেই সিনেমা তো মোটামুটি মলিনা দেবীরই দখলে। শহরে থাকা পরিযায়ী পুরুষের গেঁয়ো মফস্সলি বউদের চিরকেলে বিপন্নতার বারোমাস্যা তিনি তখন পরতে-পরতে মেলে ধরছেন।
নির্মল-বিজনের ‘অল ওয়েদার প্রুফ’ চিত্রনাট্য অবশ্য রম-কমের চেনা ফর্মুলাতেই সেটাকেও মধুরেণ সমাপয়েৎ করে নেয়। শেষ দৃশ্যে রজনী চাটুজ্জের মলিন মেসবাড়ির ঘরে, সব ভুল বোঝাবুঝি সাঙ্গ করে তুলসী আর মলিনা যখন বিয়েবাড়ির বাড়তি মালা গলায় দিয়ে নিজেদের অনেক বছর আগের ফেলে আসা ফুলশয্যার রাতের কথা সবে ভাবতে যাচ্ছেন, তখন ভেজানো দরজা সপাটে ঠেলে কে আর রসভঙ্গ করতে পারেন কেদাররূপী ভানু ছাড়া!
কখনও ‘বেপথু’ বরের মন ভোলাতে লিপস্টিক-কাজল-পমেটমের বেমানান সাজগোজ, কেশবাহার— কখনও গুণিন ডেকে তন্ত্র-মন্ত্র-বশীকরণের এলাহি আয়োজন। কর্তা শহুরে রাক্ষুসীর মায়ার ফাঁদে পড়ে গাঁয়ের বধূটিকে ভূলে যাবেন, এই ভয় থেকেই তো সব কিছু! কিন্তু রজনীবাবু তো গিন্নির স্বাভাবিক আদর-ভালবাসা চান। তাই মাঝরাত্তিরে মলিনার গায়ে-পড়া বাহারি সোহাগ এক ঝটকায় ঠেলে সরান তিতিবিরক্ত তুলসি। মাঝবয়সি বর-বউ-এর এত সাহসী স্বাভাবিক বেডসিন ‘সাড়ে চুয়াত্তর’-এর আগে তো বটেই, পরেও এভাবে বাংলা সিনেমায় কেউ দেখেছে কি? মনে তো পড়ে না।
‘পরশপাথর’-এর পাঁচ বছর আগেই ‘সাড়ে চুয়াত্তর’-এ তুলসী চক্রবর্তী তাঁর তেপান্তরের মতো মস্ত লম্বাচওড়া অভিনয়ের রেঞ্জটা দেখিয়ে দিয়েছিলেন। আর সোয়ামির ওপর বাৎস্যায়নি চৌষট্টি কলার দাওয়াই ‘মিস ফায়ার’ হওয়ার পরে নিশুতি রাতে বিছানায় এলোমেলো-উসকোখুসকো প্রসাধনসুদ্ধ মলিনা দেবীর একলা অসহায় বসে থাকার দৃশ্যটাও দর্শক কখনও ভুলতে পারবেন না। কিংবা বশীকরণ যজ্ঞের সময় পুজোর ডালি হাতে, বিগতযৌবন ভারী শরীর আর বাতের ব্যথা নিয়ে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকার মরিয়া চেষ্টার মুহূর্তটাও। মেসবাড়িতে মেরাপ বাঁধা হচ্ছে, এই উড়ো খবর পেয়ে রামপ্রীতি-রমলার বিয়ের রাত্রেই শ্রীমতি রজনী চাটুজ্জের ছানাপোনাসুদ্ধ অন্নপূর্ণা বোর্ডিং হাউসে হামলাও তো গাঁয়ের বধূর নিরাপত্তাহীনতারই সর্বোচ্চ পর্যায়।নির্মল-বিজনের ‘অল ওয়েদার প্রুফ’ চিত্রনাট্য অবশ্য রম-কমের চেনা ফর্মুলাতেই সেটাকেও মধুরেণ সমাপয়েৎ করে নেয়। শেষ দৃশ্যে রজনী চাটুজ্জের মলিন মেসবাড়ির ঘরে, সব ভুল বোঝাবুঝি সাঙ্গ করে তুলসী আর মলিনা যখন বিয়েবাড়ির বাড়তি মালা গলায় দিয়ে নিজেদের অনেক বছর আগের ফেলে আসা ফুলশয্যার রাতের কথা সবে ভাবতে যাচ্ছেন, তখন ভেজানো দরজা সপাটে ঠেলে কে আর রসভঙ্গ করতে পারেন কেদাররূপী ভানু ছাড়া! ভানুর সেই কান ধরে, চোখ বুজে, জিভ কেটে বলা ‘ই-ই-শ দেখি নাই, আমি দেখি নাই’ সংলাপ তাই টালিগঞ্জে একদা রসচর্চার চিরদিনের সিগনেচার টিউন হয়ে থেকে গেছে। এই দৃশ্যের পরে ছবির থিম সং ‘আমার এ যৌবন’ আর একবার না বাজলেও চলত।